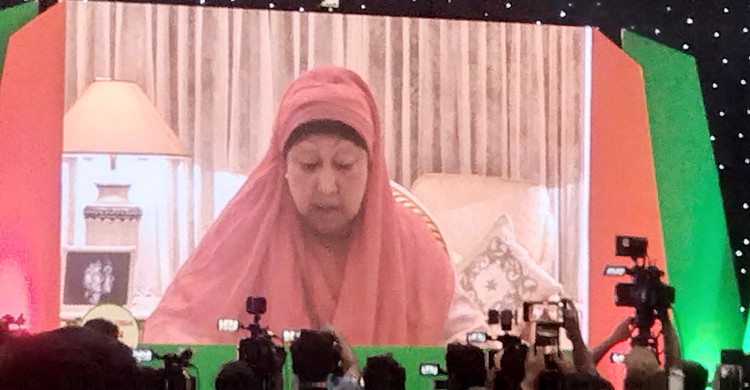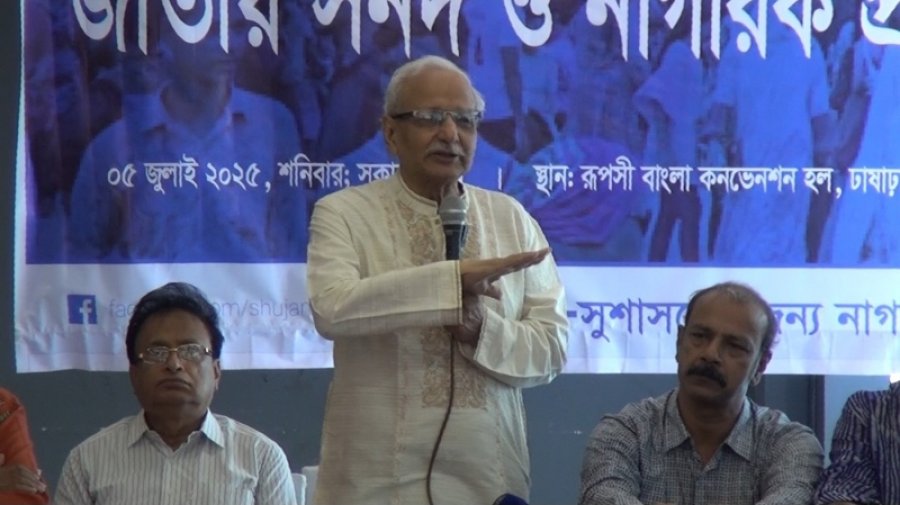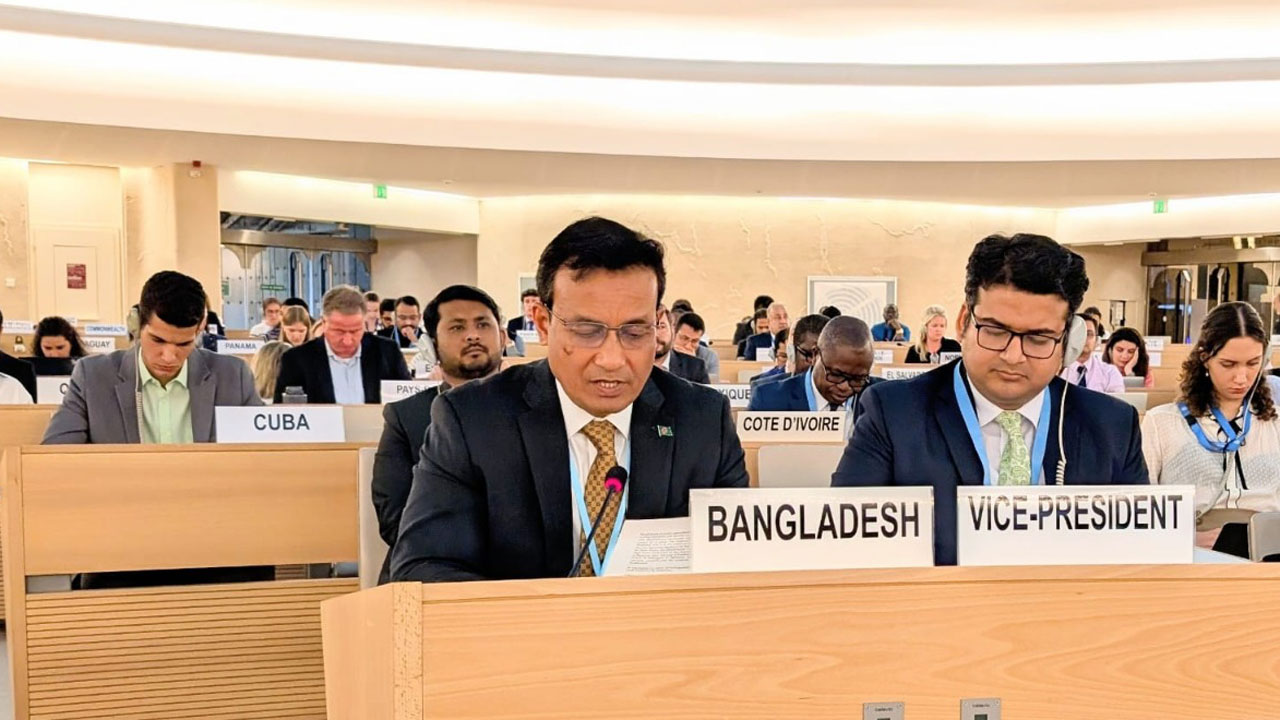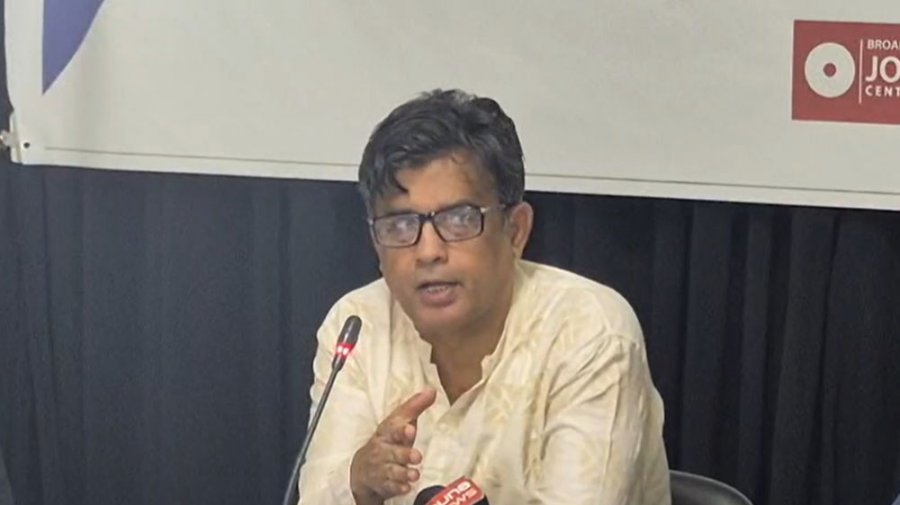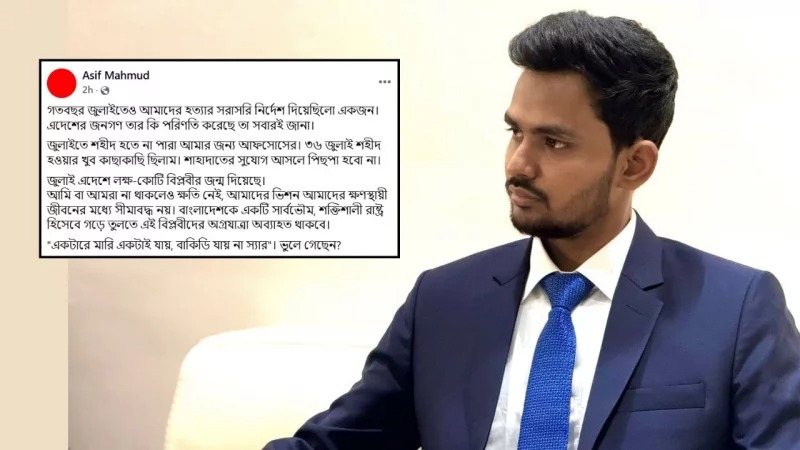অজয় দাশগুপ্ত : একসময় যে প্রকৃতির সাথে শারদীয় উৎসব আসত তার কিছুটা এখন বদলে গেছে। জনসংখ্যার ভীড়ে নীলাকাশ এখন ধূসর। সবুজ উধাও। ফুলেরা ফোটে আতঙ্কে। পাকিস্তান আমলেও যা দেখিনি তাই দেখতে হয়েছে, দেখতে হচ্ছে। ভাঙ্গা মূর্তি, মাঝে মাঝে ভেসে আসা দুঃসংবাদ আর গেলবারের পূজার সময় যা ঘটেছিল এসব মিলিয়ে বড় ভয় আর নিরাপত্তাহীনতায় আসে শারদীয়া। অথচ এর মূল বার্তাই হচ্ছে আনন্দ আর মিলন। ওই বার্তা ঢাকা পড়ে যাবে এমন আতঙ্কে? নাকি দীর্ঘ ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির আলোয় সবকিছু চলবে তার আপন গতিতে? এ প্রশ্নই এখন সবার মনে।
শারদীয়ার আবহগুলো দেখলে বা এর অনুষঙ্গের দিকে তাকালেই বুঝবেন এর পরতে পরতে আবহমান বাংলা এবং বাঙালির রূপ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যে দুর্গা এভাবে বন্দিত হন না। এক এক জায়গায় একেকরকম ভাবে অর্চনা করা হলে ও বাংলায় দুর্গার ধারণাই ভিন্ন। এখানে তিনি অসুররূপী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে নারী শক্তির প্রতীক। তার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয় নারীর জাগরণ। তিনি কালক্রমে হয়ে উঠেছেন বিজয়া। যার সাথে আমাদের আনন্দ আর জয়ের যোগ অভিন্ন। ওই দুর্গা দশভুজা। যেমন দশভুজা ঘরে ঘরে বাংলার মায়েরা। তারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অদৃশ্য দশহাতে ঘর সংসার সামলান। সামলান সব সমস্যা। যারা দেবী দুর্গার দশভুজা বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তারা এভাবে ভেবে দেখলেই উত্তর পাবেন।
আরেকটি বিষয় হলো এর সাথে সংস্কৃতির নিবিড় যোগাযোগ। সরস্বতী বিদ্যাদেবী। তিনি সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক– তার বাহন হাঁস, হাতে বীণা। অথচ দুর্গাপূজাতেই আমাদের শিল্প-সাহিত্য জেগে ওঠে নতুন আনন্দে, নতুন শক্তিতে। দৈনিক থেকে সাময়িকী সাহিত্য পত্রিকা সবকিছু রঙিন হয়ে ওঠে। সেই কবে থেকে শারদীয় সংখ্যার রমরমা। তখনকার দেশ, আনন্দবাজারের কথা ভুলবে না বাংলা সাহিত্য। এই শারদীয় সংখ্যার হাত ধরে উঠে এসেছেন, মন জয় করেছেন, বিখ্যাত হয়ে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন অজস্র লেখক, কবি। গানের জগত তখন পুরোটাই ছিল পূজানির্ভর। একেকটা পূজায় একেক ধরনের গান আর গানের ডালি নিয়ে হাজির হতেন হেমন্ত, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র, সন্ধ্যা, আরতি আর উৎপলার মতো শিল্পীরা। ইউটিউব, স্মার্টফোন, কম্পিউটারহীন জগতে এসব গান ভেসে আসত আকাশপথে। রেডিও ক্যাসেটের ওই জমানায় গানগুলো মানুষকে যে আনন্দ, যে বৈভব দিয়েছিল আজও তা প্রবহমান। সেই অম্লান গানের জগত নাই আর। টেকনোলজি, কারিগরি উৎকর্ষ বা যন্ত্রের এই যুগে গান আর গান নাই। ওই আলোচনা এখানে নয়। বলছিলাম সংস্কৃতির সাথে শারদীয়ার সম্পর্কের কথা।
দু-যুগ আগের এমন কোনো বাঙালি পাবেন যিনি মহালয়া শোনেননি? এই মহালয়া মূলত একটি গীতিআলেখ্য। কিন্তু এর ইতিহাস একেবারেই ভিন্ন ধরনের। এর সাথে বাঙালির বিদ্রোহ জড়িয়ে। তখনকার আমলে সর্বজনশ্রুত রেডিও মাধ্যম আকাশবাণী কলকাতা ছিল অসম্ভব শক্তিধর একটি মিডিয়া। ওই মিডিয়ায় মহালয়া নিয়ে যে নীরব আন্দোলন বা আবেগ তৈরি হয়েছিল তা এখন ইতিহাস। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের চ-ী পাঠে নাখোশ ছিলেন। তাদের কথা হলো অব্রাহ্মণ কেউ তা করতে পারবেন না। কিন্তু মহান গায়ক সুরকার পঙ্কজ কুমার মল্লিক এবং বিখ্যাত গীতিকার বাণীকুমার ছিলেন অটল। তারা কথিত উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের কথায় কান দেননি। বরং মুসলিম সংস্কৃতির সানাই বাজিয়ে শুরু করা হয়েছিল মহালয়া। যা পরিষ্কারভাবে একটি বিদ্রোহ। অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িকতার নিদর্শন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তার নিজস্ব ধারায় চ-ীপাঠ করছিলেন সুরেলা কণ্ঠে। হঠাৎই অলস রসিকতার ছলে বাংলা ভাষ্যটিও স্তোত্রের সুরের অনুকরণে বলতে শুরু করলেন। তাতে চারিদিকে বেশ একটা মৃদু হাসির ভাব জাগল। কিন্তু বাণীকুমার দ্রুত রেকর্ডিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, “আরে আরে থামলে কেন? বেশ তো হচ্ছিল! হোক! হোক না ওই ভাবেই …।” বীরেন্দ্রকৃষ্ণ হেসে বললেন, “আরে না না একটু মজা করছিলাম!” কিন্তু বাণীকুমার গভীর আগ্রহ নিয়ে বললেন, “মোটেই না! দারুণ হচ্ছিল! ওইভাবেই আবার করো তো।” বীরেন্দ্রকৃষ্ণ আবার শুরু করলেন, “দেবী প্রসন্ন হলেন …।” সেদিনই বাংলার ইতিহাসে সংযুক্ত হল এক নতুন মাত্রা।
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সুনাম আর ক্যাসেটে শোনার আগ্রহ নিয়ে কিছুই বলতেন না। দেশে-বিদেশে মহিষাসুরমর্দিনী নিয়ে এত উচ্ছ্বাস, অথচ তিনি কিন্তু সে সবে বিন্দুমাত্র সাড়া দিতেন না। বলতেন, “বেশ মজা আর কি, পুরাণ পড়ব না, চ-ীপাঠ করব না, শুধু বৈঠকখানায় বসে স্টিরিয়োতে মহিষাসুরমর্দিনী শুনে কর্তব্যকার্য শেষ। কাজীদা (নজরুল) হলে কী বলতেন জানো? বলতেন, দে গরুর গা ধুইয়ে, যত্তোসব!”
শারদীয়া দুর্গাপূজা আমাদের অতীত আর ইতিহাসের এক অনিবার্য অংশ। তার সাথে বর্তমান, আর তার সাথেই জড়িয়ে আছে অনাগত ভবিষ্যত। এই কারণে তার নিরাপত্তা আর যথাযথ মর্যাদা বিধান করা জরুরি। হঠাৎ করে বাংলাদেশে এমন কিছু ঘটনার জন্ম দেয়া হয়েছে যাতে এই বিশ্বাস টাল খাচ্ছে রীতিমতো। যা কারো কাম্য না। এই সমাজে এই জাতিতে দীঘর্কাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করা হিন্দু-মুসলমান বা অন্যদের বিশ্বাস ও ধর্ম আচরণে বাধা দেবার মানেই হলো সম্প্রীতি বিনাশ। এই অপচেষ্টা রুখতে হবে সবাই মিলে। নয়তো আমাদের বিপর্যয় ও সর্বনাশ ঠেকানো যাবে না।
শারদীয়া দুর্গাপূজা বাঙালির উৎসব হলেও এর আবেদন সর্বজনীন। ম-পে ম-পে সব ধর্মের মানুষের আগমন আর দেশে-বিদেশে বাঙালির এই উৎসব আয়োজন আজ এক অসাধারণ ইতিহাসের অংশ। এর যথাযোগ্য নিরাপত্তা আর সম্মান যেন অটুট ধাকে। নিছক ধর্মের নামে যারা উৎপাত করে বা সংখ্যালঘু নামের মানুষজনকে বিপদে ফেলে তাদের আমরা চিনি। যুগে যুগে এরাই অসুর। এরাই তারা যারা গান-বাজনা, নাটক, শিল্প কিছুই ভালোবাসে না। তাদের চোখের বিষ সংস্কৃতি। তাদের রাগের কারণ নারী স্বাধীনতা। শারদ উৎসব এই দুটি শক্তি ধারণ করেই বেড়ে উঠেছে। নারী স্বাধীনতা বা তার শক্তি দেবী দুর্গাতেই পরিস্ফুট। এছাড়াও তার দুহিতা কন্যা ধনের দেবী লক্ষ্মী, বিদ্যার দেবী সরস্বতী, দুই পুত্র সাহস শৌর্যের প্রতীক কার্তিক আর সিদ্ধদাতা গণেশ পরিপূর্ণ এক প্যাকেজ। যার বাইরে কিছু নাই থাকতে পারে না।
রবীন্দ্রনাথের একটি ঘটনা দিয়ে শেষ করব যাতে বোঝা যায় কতটা প্রভার রাখে এই শারদ উৎসব: ১৯৩৫ সালে ‘আনন্দবাজার’ ও ‘দেশ’ পত্রিকার পক্ষ থেকে পূজার সংখ্যায় লেখা দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ‘একশো টাকা বায়না’ দেওয়া হয়। ঘটনাটির উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫ সালের ২৯ অগাস্ট শান্তিনিকেতন থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন “এখানকার বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ-চেষ্টায় ছিলুম। ব্যক্তিগতভাবে আমারও দুঃসময়। কিছু দিতে পারছিলুম না বলে মন নিতান্ত ক্ষুব্ধ ছিল। এমন সময় দেশ ও আনন্দবাজারের দুই সম্পাদক পূজার সংখ্যার দুটি কবিতার জন্যে একশো টাকা বায়না দিয়ে যান, সেই টাকাটা বন্যার তহবিলে গিয়েছে। আগেকার মতো অনায়াসে লেখবার ক্ষমতা এখন নেই। সেইজন্যে ‘বিস্ময়’ কবিতাটি দিয়ে ওদের ঋণশোধ করব বলে স্থির করেছি।”
জয়তু শারদীয়া দুর্গাপূজা।
লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিস্ট