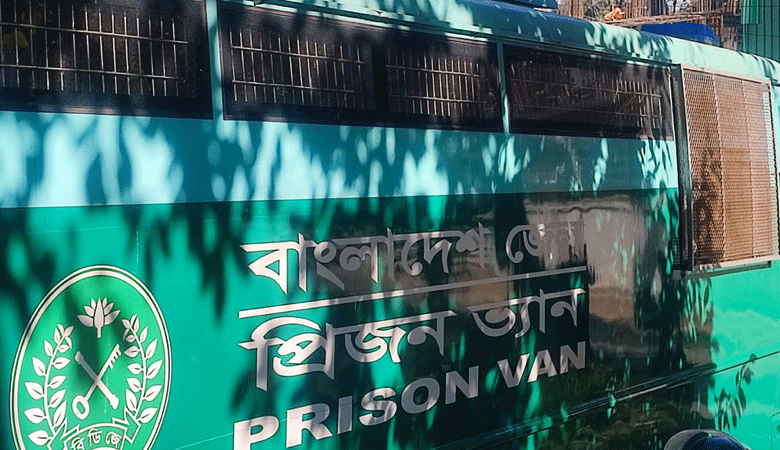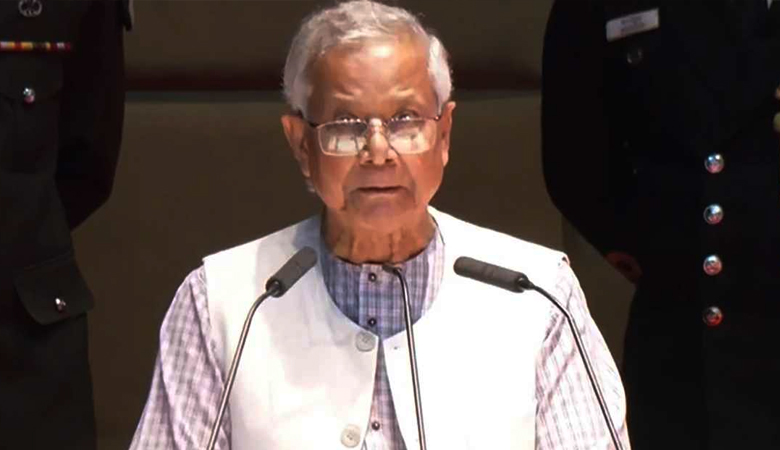প্রত্যাশা ডেস্ক :নিরাপদ সড়কের দাবিতে পুরো বাংলাদেশকে অচল করে শিক্ষার্থীদের সেই আন্দোলনের পর চার বছর পেরিয়ে গেছে। এই সময়ে দেশের মানুষ সরকারের তরফ থেকে পেয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি; চাপের মুখে একটি আইন হয়েছে, তাতে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী চালকের শাস্তি বেড়েছে।
কিন্তু পরিস্থিতি বদলেছে সামান্যই। বাংলাদেশে সড়কে মৃত্যু যেন এক নীরব মহামারীতে পরিণত হয়েছে।
‘নিরাপদ সড়ক চাই’ আন্দোলন বলছে, প্রতি বছর চার হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ যাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনায়। আরও অগুনতি মানুষ গুরুতরভাবে আহত হচ্ছে, মেনে নিতে হচ্ছে পঙ্গু জীবন।
২০১৮ সালের ২৯ জুলাই ঢাকার শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের কিছু শিক্ষার্থী কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের সামনে ফুটপাথে বিমানবন্দর সড়কে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একটি বাস থামলে সেটায় ওঠার চেষ্টা করেন তারা। ঠিক ওই সময় জাবালে নূর পরিবহনের দুটি বাস আগে যাত্রী তোলার জন্য নিজেদের মাঝে প্রতিযোগিতা করতে করতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসে এবং একটি বাস বেপরোয়াভাবে ফুটপাতে দাঁড়ানো শিক্ষার্থীদের ওপর উঠে যায়। ওই ঘটনায় দুই শিক্ষার্থীর প্রাণ যায়, ১২ জন গুরুতর আহন হয়। বিক্ষুব্ধ সহপাঠীরা রাস্তায় নেমে আসে, নিরাপদ সড়কের দাবিতে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে পুরো দেশে। শিক্ষার্থীদের সেই আন্দোলন দেখিয়ে দেয়, আইনের রক্ষক যে পুলিশ, তাদের চালকও লাইসেন্স ছাড়া, চলার অনুপযোগী গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামছে।
সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের হিসাবে, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে নিবন্ধিত যানবাহনের সংখ্যা ছিল ৪৫ লাখ। অথচ লাইসেন্সধারী চালক আছে মোটাদাগে তার অর্ধেক। এর মানে হল, বাংলাদেশের অর্ধেক যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ এখন লাইসেন্সবিহীন চালকের হাতে। আর সঠিক প্রশিক্ষণের প্রশ্ন তুললে চিত্রটা হবে আরও উদ্বেগজনক। অথচ চালকদের প্রশিক্ষিত করেও বহু প্রাণ বাঁচানো সম্ভব।
এইত সপ্তাহ দুই আগে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় এক দিনেই ২৯ প্রাণ ঝরে দেখেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে ময়মনসিংহের ত্রিশালে এক ঘটনায় মহাসড়ক পার হওয়ার সময় স্বামী, স্ত্রী আর ছয় বছরের সন্তানের প্রাণ যায় দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায়। সেই নারী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা; তার মৃত্যুর সময়ই জন্ম নেয় তার গর্ভের শিশু। সেই ঘটনা পুরো দেশকে নাড়িয়ে দেয়। জন্মমুহূর্তে পুরো পরিবারকে হারানো শিশুটি এখন আছে বৃদ্ধ দাদা-দাদির কাছে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে তার জন্য ৫ লাখ টাকা দিতে বলেছে হাই কোর্ট। দুর্ঘটনায় প্রাণহানির পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিবারকে একটি নামমাত্র টাকা ধরিয়ে দেওয়া লাশ দাফনের জন্য। সেই পরিবার পরে আর বিচারও পায় না, ক্ষতিপূরণ তো দূরের কথা।
সড়ক কি নিরাপদ হয়েছে? পুলিশের পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৮ সালে দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ হাজার ৬৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। পরের বছর সেই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে হয় ৪ হাজার ১৩৮ জন। এসব দুর্ঘটনার বেশিরভাগ ঘটে মহাসড়কে, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার পর চালক পালিয়ে যান।
২০২০ সালে মহামারীর কারণে দীর্ঘ লকডাউনে মৃত্যুর সংখ্যা সামান্য কমে ৩ হাজার ৯১৮ জন হয়। আর এ বছর সাত মাসেই সে সংখ্যা পৌঁছেছে ৩ হাজার ৫০২ জনে। অর্থাৎ প্রতিদিন সড়কে প্রাণ গেছে অন্তত ১৪ জনের। বুয়েটের অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, গত ৭ বছরে সারাদেশে ১৫ হাজার ১৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৭ হাজার ৮৮৬ জনের; আরও ৩২ হাজার ৩৩০ জন আহত হয়েছেন। বাংলাদেশ রোড সেইফটি ফাউন্ডেশনের হিসাবে ২০২১ সালে দেশে ৫ হাজার ৩৭১টি দুর্ঘটনায় অন্তত ৬ হাজার ২৮৪ জনের মৃত্যু হয়; আহত হন আরও ৭ হাজার ৪৬৮ জন। প্রতিবছর বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতি লাখে যত মানুষের মৃত্যু হয়, সেই সংখ্যা ধনী দেশগুলোর গড় সংখ্যার দ্বিগুণ, সবচেয়ে কম দুর্ঘটনার দেশগুলোর প্রায় পাঁচগুণ।
বিশ্ব ব্যাংক বলছে, সড়কে যেসব হতাহতের ঘটনা ঘটছে তার একটি বড় অংশে থাকছে শিশু আর কর্মজীবী মানুষ। তবে প্রিয়জনকে হারিয়ে পরিবারগুলেকে কতটা শোক আর আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়, সেই চিত্র এসব পরিসংখ্যানে আসে না।
দক্ষিণ এশিায়ায় বিশ্ব ব্যাংকের আঞ্চলিক পরিচালক (অবকাঠামো) গুয়াংশি চেন গত এপ্রিলে এক ব্লগে লেখেন, “সড়ক দুর্ঘটনা যে কেবল পরিবারের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে তা নয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তা বাধাগ্রস্ত করে। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু আর পঙ্গুত্ব বরণ করে নেওয়ার সেই সব ঘটনার পর পরিবারের সদস্যদের যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবেলা করতে হয়, তা আরও করুণ।”
পরিবারের লড়াই : মহামারীর শুরুর দিকের কথা, ২০২০ সালের ১৪ জুন। কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের ছাত্রী বর্ষা রায় চৌধুরী সুনামগঞ্জের নবীনগরে তাদের বাড়িতে তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যা দিচ্ছিলেন। লকডাউনের মধ্যে জরুরি সেবা ছাড়া প্রায় সব কিছু তখন বন্ধ। হঠাৎ এক প্রতিবেশী এসে খবর দেন, বর্ষার বাবা নৃপেন্দ্র রায় চৌধুরী সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন, তাকে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নৃপেন্দ্র একটি ইউনানী ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করেন। সেদিন সকালে তিনি পাশের উপজেলা দিরাইয়ে গিয়েছিলেন ওষুধ পৌঁছে দিতে। সব কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে তার লেগুনার সঙ্গে একটি বাসের সংঘর্ষ হয়।
দুর্ঘটনার খবর শুনে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ঘরে যা টাকা পয়সা ছিল, তাই নিয়ে হাসপাতালে ছোটেন বর্ষারা। পৌঁছে দেখেন, হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে তার বাবা। বর্ষা বলেন, “বাবার নাক দিয়ে রক্ত পড়তেছিল, সেন্স ছিল না। বাঁ পা পুরো বাঁকা হয়ে গেছিল। বাবা প্রায় অচেতন। তারপরও জানি না, কেন যেন সে আমার দিকে হাত বাড়ালেনৃ ওখানে প্রাথমিক চিকিৎসাটাও পায়নি আমার বাবা। তাকে জাস্ট অবহেলায় ফেলে রাখা হইছেৃ।”
সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের চিকিৎসকরা নৃপেন্দ্রকে সিলেটে নিয়ে যেতে বললেন। বর্ষার মা স্মৃতি চৌধুরী কাঁদছিলেন। কিন্তু বর্ষার ভাই শারদ যেন ঘটনার আকস্মিকতায় পাথর হয়ে গিয়েছিল। কোভিডের ভয়ে আত্মীয়-স্বজনরা কেউ হাসপাতালে যাননি। একা কীভাবে সব সামলাবেন, দিশেহারা বোধ করছিলেন বর্ষা। এর মধ্যেই তিনি কোনোভাবে একটি অ্যাম্বুলেন্স ঠিক করেন, সেই অ্যাম্বুলেন্সে আবার অক্সিজেন নেই। অথচ নৃপেন্দ্র রায় চৌধুরীর তখন অক্সিজেন দরকার।
“-বাবা কাতরাইতেছিল, নাক দিয়া রক্ত পড়তেছিল, পায়ে ব্যথা লাগতেছিল প্রচ-ৃ সিলেট ওসমানী মেডিকেলে যখন পৌঁছালাম, তখন রাত সাড়ে ৯টার মতনৃ বাবাকে স্ট্রেচারে করে নামাইতেছিল, আমি ভর্তির ফর্মালিটিজ করতেছিলাম। তখন ৯টা ৫০। শুনলাম যে উনি আর নাই।”
বর্ষা এখনও বিশ্বাস করেন, সেদিন যদি তার বাবাকে সরাসরি ওসমানী মেডিকেলে নেওয়া যেত, সেখানে যদি চিকিৎসা শুরু করা যেতে, তাকে হয়ত ওভাবে মরতে হত না। কিন্তু সেই শোক সামলে ওঠার আগেই টিকে থাকার এক নতুন সংগ্রামের মধ্যে পড়তে হয় বর্ষা, তার মা, আর ভাইকে। নৃপেন্দ্রর স্ত্রী স্মৃতি চৌধুরী একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করতেন। কিন্তু মহামারীর মধ্যে স্কুল বন্ধ থাকায় ২০২০ সালের মার্চ থেকে তার বেতন ছিল বন্ধ। বর্ষা তখন নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষে। কিন্তু কঠিন বাস্তবতায় পড়ে লেখাপড়া স্থগিত রেখে তিনি ঢাকায় এসে মাসীর বাড়িতে ওঠেন, মাসে ৯ হাজার টাকা বেতনে ট্যুর গাইডের চাকরি নেন। শারদের তখন সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা। ওই টাকা দিয়েই তাকে কোচিং করালেন বর্ষা, ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ালেন। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কমে এলে বর্ষার মায়ের স্কুল খুলে যায়, তিনি আবার নিয়মিত বেতন পেতে শুরু করেন। নিজের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়ার জন্য বর্ষাও চাকরি ছেড়ে দেন। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার ধাক্কা সামলে না উঠতেই বর্ষাদের ঘাড়ে এসে পড়ল বন্যা। “ঘরের বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র, ফার্নিচার সব নষ্ট হয়ে যায়। কীভাবে এসব ঠিক করব জানি নাৃ ওই মুহূর্তে আমরা জাস্ট একটু স্টেবল হচ্ছিলাম, তখন আবার এই ধাক্কাটাৃ।”
বাংলাদেশের মত দেশে, যেখানে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়মিত একটি বিষয়, সেখানে বর্ষাদের দুর্দশা অসংখ্য করুণ গল্পের কেবল একটি। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ, কোনো না কোনো অঞ্চলে আহত কিংবা নিহত হচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বিচার পাচ্ছে না। সমস্যারও সুরাহা হচ্ছে না। মাসখানেক আগে সাভারের বলিয়ারপুরে এক সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীসহ চারজন নিহত হন এবং অনেকে আহত হন।
তাদের মধ্যে পরমাণু শক্তি কমিশনের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পূজা সরকার ছিলেন ৬ মাসের অন্তসঃত্বা। মাত্র দুই বছর আগে চিকিৎসক তন্ময় মজুমদারের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল।
পূজার ভাই বিজয় সরকার বলেন, “আমার বয়স যখন দুই বছর, তখন আমি মাকে হারাই, দিদির বয়স তখন আট বছর। বড় হওয়ার পর আমি দিদিকেই মা জেনেছি। ও শুধু আমার দিদি না, মায়ের মত আগলে রাখত আমায়। বিজয় বলেন, “দিদি চাইত আমি যেন উচ্চ শিক্ষা পাই। সে অনুযায়ী আমায় গাইড করত। দিদির ইচ্ছে রাখতেই আমি এখন কানাডায় পড়তে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।”
সমাধান কি নেই? বছরের পর বছর গেলেও লাইসেন্সবিহীন চালকের হাতে স্টিয়ারিংয়ের বিপদ থেকে পরিত্রাণ পায়নি বাংলাদেশ। অথচ কেবল পথচারীদের নিরাপত্তা দিতে পারলেই সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করেন বুয়েটের অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক হাদিউজ্জামান। তিনি বলছেন, দেশে দুর্ঘটনায় বছরে যত মানুষ মারা যায়, তার ৪৯ শতাংশ পথচারী। এসব দুর্ঘটনার একটি বড় অংশ ঘটে মহাসড়কে। ৫৯ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভারী যানবাহনের নিচে পড়ে পথচারীর মৃত্যু হচ্ছে। এক্ষেত্রে অবকাঠামো নির্মাণের সময় পরিকল্পনার দুর্বলতার বিষয়টি তুলে ধরে অধ্যাপক হাদিউজ্জামান বলেন, “আমরা যখন কোনো প্রকল্প নিই, সেই প্রকল্পের মূল পরিকল্পনায় অবকাঠামোর বিষয়টা থাকছে না বলে আমি মনে করি। ট্রাফিক ওরিয়েন্টেড পরিকল্পনা করছি এবং সেটা করতে গিয়ে আমরা শুধুমাত্র যানবাহনকে প্রাধান্য দিচ্ছি। কিন্তু ট্রাফিক বলতে পথচারীকেও বোঝায়। পরিকল্পনায় পথচারী গুরুত্ব পায় না।”
গলদটা কোথায় থাকছে? এখন এক্সপ্রেসওয়ে হচ্ছে, কীভাবে রাস্তায় যানবাহনের গতি আরও বাড়ানো যায়, কীভাবে একটি গাড়িকে ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার গতিতে ছোটার সুযোগ দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু পথচারীদের কথাটা মাথায় রাখা হয় না, আন্ডারপাস আর ফুটব্রিজ পরিকল্পনায় থাকে না। ভারী যানবাহনের দক্ষ চালকের যে ঘাটতি দেশে আছে, সেখানেও দুর্ঘটনার ফাঁদ তৈরি হচ্ছে বলে মনে করেন এই প্রকৌশলী। “আমাদের এ মুহূর্তে প্রায় আড়াই লাখ নিবন্ধিত ভারী যানবাহন আছে বাস ও ট্রাক মিলে। তার বিপরীতে আমাদের ভারী গাড়ি চালানোর লাইসেন্সধারী চালক আছে দেড় লাখ। তার মানে আমরা সাদা চোখেই দেখতে পাচ্ছি, প্রায় এক লাখ চালকের একটা ঘাটতি আছে।”
আন্তর্জাতিক মানদ- অনুযায়ী, প্রতিটি ভারী বাহনের বিপরীতে দেড় থেকে দুইজন চালক থাকতে হয়। ওই আদর্শ মান ধরে যদি হিসাব করা হয়, বাংলাদেশে নিবন্ধিত ভারী যানবাহনের ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী চালকের ঘাটতি বেড়ে হবে প্রায় তিন লাখ। তবে সড়ক নিরাপত্তার কথা যখন আসে, সেটা শুধু সড়ক আর যানবাহনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিশ্ব ব্যাংকের কর্মকর্তা গুয়াংশি চেন বলেন, জরুরি চিকিৎসা, ট্রমা কেয়ার, ট্রাফিক পুলশ, আইনের প্রয়োগ, সড়ক নির্মাণের প্রকৌশলের মত বিষয়গুলোও এখানে যুক্ত। আর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল বেসরকারি খাতের অংশীজনদের যুক্ত করা।