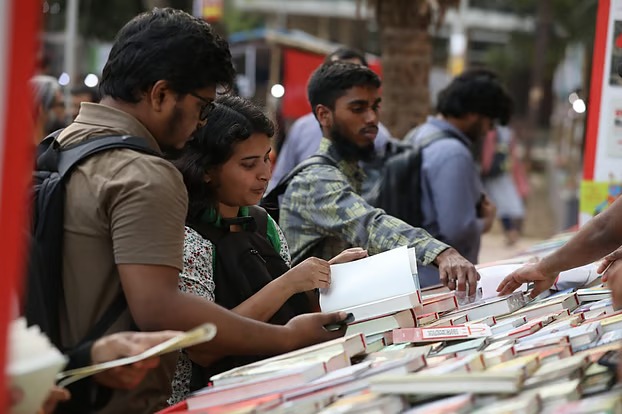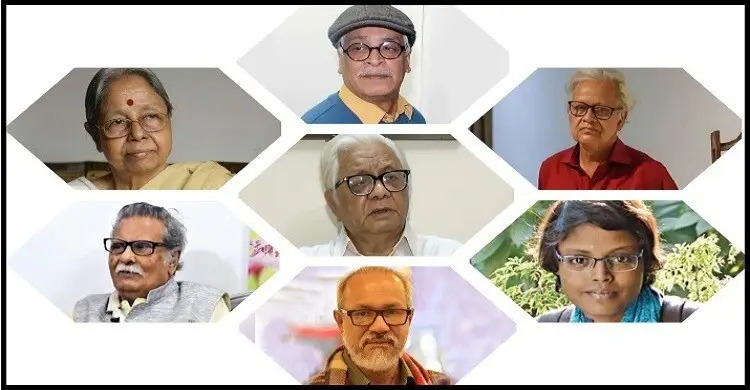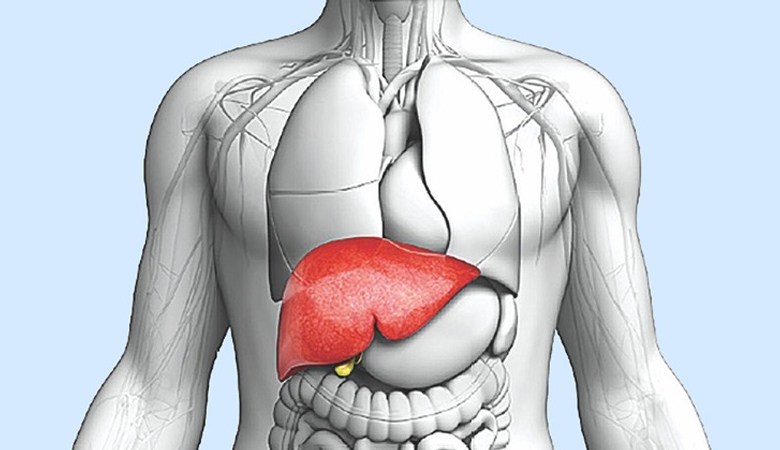মুনীর চৌধুরীর নাট্যচিন্তা দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল ইউরোপীয় নবনাট্যের ধারা। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইউরোপজুড়ে নতুন ঘরানার নাটকের প্রচণ্ড দাপট চলছিল। এটি ছিল মূলত একটি সাহিত্যিক ও শৈল্পিক আন্দোলন। এতে বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গিসহ পুরোনো নাট্যরীতি বর্জন করে নতুন রীতির নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন হতে থাকে। ইউরোপে নাটকের ধরনও ছিল এমন- পুরোনোকে অভিঘাত করে নতুনের আবাহন। এই নবনাট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বাস্তববাদ ও প্রকৃতিবাদ, সমাজ এবং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিষয় নির্বাচন, যৌক্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের সংশ্লেষ এবং নতুন কলাকৌশল। এ বিষয় নিয়েই এবারের সাহিত্য পাতার প্রধান রচনা
নাটক ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য হলেও আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব ইউরোপ থেকে। এক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীর যখন আবির্ভাব ঘটে, বাংলা নাটকের শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে এবং তা পুষ্ট ও পরিণত ধারা হয়ে উঠেছে। মুনীর চৌধুরী মনে করতেন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ উনিশ শতকের বাংলা নাটক, আর একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বিশ শতকে নাটকের উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা কেউ করেননি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া উনিশ ও বিশ শতকে পার্থক্যও বিশেষ নেই। আর তত দিনে বাংলা নাটক বিষয়, প্রকরণ ও মঞ্চায়নের দিক থেকেও ক্লিশে হয়ে উঠেছিল। কেননা তখনকার নাটক পেশাদার রঙ্গমঞ্চের স্থূল আবেদনে অর্থহীন, অশ্লীল ও উদ্ভট হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়া তাতে জীবনের কোনো সত্যতা ও গভীরতা ছিল না। অবশ্য এর বিপরীতে জীবন ও সমাজঘনিষ্ঠ নাটকের আরেকটা ক্ষীণ ধারা বহমান ছিল। তাও প্রকরণগত দিক থেকে ছিল অনুকরণমূলক ও অনেকটা অস্বাভাবিক। এসব নাটকে কাহিনি ও প্লটের সরলতা জীবনের বিচিত্র রহস্যকে প্রকাশের পক্ষে বাধা হিসেবে কাজ করত। চরিত্রায়ণও ছিল একমাত্রিক, অগভীর ও গতানুগতিক। গভীরতর জীবনবোধেরও ছিল তাতে বড় অভাব। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুনীর চৌধুরী চেয়েছিলেন বাংলা নাটকের পুনর্জাগরণ এবং নতুন শিল্পরীতিতে নবজীবনের উদ্বোধন। তার নাট্যচেতনার মূলে ছিল কমিউনিস্ট আদর্শ, শ্রেণিসংগ্রাম ও মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা। একই সঙ্গে ঐতিহ্যের মূলধারার সঙ্গে পরিবর্তনশীল জীবন ও পরিবেশের শিল্পসম্মত মিলন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন বাঙালির বিপুল বিচিত্র ঐতিহ্যের সঙ্গে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিজীবনে রয়েছে নানা ঘটনার দ্বান্দ্বিকতা এবং স্বপ্নময় অফুরন্ত জীবনতৃষ্ণা। সুতরাং এসব নাটকীয় উপাদান নাট্যরচনায় ব্যবহার করে বাংলা নাটককে যুগোপযোগী শিল্পমাধ্যমে পরিণত করা সম্ভব।
ইউরোপীয় নবনাট্যের পেছনে অর্থনৈতিক, সমাজ-রাজনৈতিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও দার্শনিক নানা কারণ বিদ্যমান ছিল। বিশেষ করে শিল্পবিপ্লব, নগরায়ণ, শ্রমিক অধিকার, নারী-স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, মার্ক্সবাদ, ডারউইনবাদ, ফ্রয়েডবাদ, ধর্মনৈতিকতা বিষয়ে প্রশ্নবিদ্ধতা, বাস্তবতার বহুস্তরবাদ, নিরাশাবাদ, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি নাট্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্মাণরীতিকে পাল্টে দেয়। এই প্রক্রিয়ার প্রথম দিকে নরওয়েতে হেনরিখ ইবসেন, রাশিয়ায় আন্তন চেখভ, ব্রিটেনে জর্জ বার্নাড শ, সুইডেনে অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ প্রমুখ নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে। বলতে গেলে এঁদের হাত ধরে ইউরোপীয় আধুনিক থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরে এ ধারাটি আরও শক্তিশালী ও বিচিত্রিমুখীন হয়ে ওঠে। ফরাসি প্রতীকবাদ ও অভিব্যক্তিবাদী শিল্প-আন্দোলন প্রভৃতি হয়ে নাট্যধারাটি পরিণতি পায় এপিক ও অ্যাবসার্ড থিয়েটারে। এমন নাট্যরীতির উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে দর্শকের সংযোগ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ দর্শকের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক উদ্দীপনা সৃষ্টি। এ ক্ষেত্রে বেলজিয়ামে মরিস মেটারলিঙ্ক, জার্মানিতে জর্জ কাইসের ও বার্টল্ড ব্রেখট, ফ্রান্সে জ্যঁ আনুই, ইতালিতে লুইজি পিরান্ডেলো, আয়ারল্যান্ডে স্যামুয়েল বেকেট, রোমানিয়ায় ইউজিন লোনেস্কো, ফ্রান্সে জ্যঁ পল সার্ত্র ও আলবেয়ার কামু প্রমুখ বিশেষ অবদান রাখেন।
প্রায় শত বছরজুড়ে তারা সবাই মিলে নাট্যরীতি, মঞ্চ ও অভিনয়ে বড় ধরনের পরিবর্তন ও রূপান্তর আনেন। নাট্যরীতিতে প্রচলিত পাঁচ অঙ্কের কাঠামো ভেঙে টুকরো টুকরো দৃশ্য পরিকল্পনা, লিনিয়ার কাহিনি ত্যাগ, অ-নায়ক চরিত্রের সৃষ্টি এবং বহুনির্দেশী সমাপ্তি যোজনা করে পূর্বের ঐতিহ্যকেই প্রত্যাখ্যান করলেন। মঞ্চায়নে প্রতীকী আলো ও আঁধার, চিত্রকল্পকেন্দ্রিক কৌশলসহ প্রপসকে কম গুরুত্ব দিয়ে নান্দনিকতাকে প্রাধান্য দিলেন। আর অভিনয়রীতিতে ক্রমান্বয়ে যোজিত করলেন স্ট্যানিস্লাভ্স্কির বাস্তববাদী অভিনয়-পদ্ধতি, মেয়েরহোল্ডের বায়োমেকানিকস এবং ব্রেখটের বিচ্ছিন্নতা অভিনয়-পদ্ধতি। ইউরোপের যুগোপযোগী এই নাট্যান্দোলন দ্রুতগতিতে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, ঔপনিবেশিত বাংলায়ও তার ব্যতিক্রম ছিল না।
মুনীর চৌধুরী ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইউরোপে যেমন পড়াশোনা করেছেন, তেমনিভাবে থিয়েটারও উপভোগ করেছেন। ফলে ইউরোপীয় নবনাট্য উপভোগ ও পর্যবেক্ষণ করে এবং বাংলা নাটকের সুপরিসর ঐতিহ্যের সামনে দাঁড়িয়ে অবলোকন করেছিলেন সমকালীন বাংলা নাটককে। তার মনে হয়েছিল নবনাট্যকলার উদ্ভাবনে বাঙালি নাট্যকাররা কেবল উদাসীনই নন। এক্ষেত্রে চলছে উষর কালও। মুনীর চৌধুরীর দৃষ্টিতে, এমনকি ক্ল্যাসিক্যাল ধারার জ্যঁ রাসিন, পিয়ের কর্নিল অথবা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের আদর্শও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি বাংলা নাটকে। ইবসেন, বার্নার্ড শো, ব্রেখট প্রমুখের আদর্শ তো দূরের কথা। অথচ মুনীর চৌধুরীর সমকালেও চলছিল ইউরোপে নতুন নতুন রঙ্গমঞ্চীয় কলাকৌশল আবিষ্কারের নেশা। তিনি দেখেছিলেন পিরান্ডেলো, আনুই, ব্রেখটও জীবনতৃষ্ণ দর্শকের দাবি মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছেন এবং তাদের জায়গা দখল করছেন নতুন নতুন নাট্যকার। তিনি ফরাসি ভাষার ইউজিন আইনেস্কো ও ইংরেজি ভাষার স্যামুয়েল বেকেটকে নবতর রীতির পুরোধা মনে করতেন। এ ছাড়া হ্যারল্ড পাইন্টার, এডওয়ার্ড অ্যালবি, জন আর্ডেনের মধ্যেও নতুনত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন। অথচ এসব ইউরোপীয় নাট্যধারার সঙ্গে বাংলা নাটকের ছিল বিশাল ফারাক। ব্যথিতও ছিলেন তিনি এ ব্যাপারে আক্ষেপ করে বলেছিলেন একদা- ‘পশ্চিমি নাটকের এই নবরূপের আস্বাদন কি আমাদের চেতনায় বিবর্তন ঘটাবে? সে বিবর্তন কি আমাদের জন্য সত্য হয়ে উঠতে পারবে? পারলে কি তা পরিগণিত হবে? কেবল প্রশ্নই করা যায়, সৃষ্টি প্রত্যক্ষ না করা অবধি উত্তর অনিশ্চিত হতে বাধ্য।’ অবশ্য মুনীর চৌধুরী এসবের উত্তর খুঁজেছিলেন নিজের নাট্যপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই।
মুনীর চৌধুরীর নাট্যপ্রচেষ্টা তিন ধরনের ছিল—মৌলিক নাটক, রূপান্তর ও অনুবাদমূলক নাটক। এই তিন প্রকার নাটকে তিনি যেমন মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি তাতে ইউরোপীয় নবনাট্যের প্রভাবও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ একঘেয়েমি-ভরা, ক্লিশে ও বাংলা নাটকের বন্ধ্যা-পরিস্থিতিতে মুনীর চৌধুরী নতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠায় উদ্গত হলেন। তাই বিষয় নির্বাচন, ভাষা প্রয়োগ, চরিত্র নির্মাণ, জীবনদৃষ্টি, নাট্যরীতি, মঞ্চায়ন ও অভিনয়ে যোজনা করলেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাকৌশল তার নাটককে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল এবং উত্তরকালে বাংলাদেশের নাট্যরীতিকে প্রভাবিতও করেছিল।
মুনীর চৌধুরীর মৌলিক নাটকের মধ্যে দুটি ধরন রয়েছে- একটি ধরন একাঙ্কিকা এবং অন্যটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। প্রকাশিত বারোটি একাঙ্কিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ‘মানুষ’, ‘কবর’, ‘পলাশী ব্যারাক’, ‘দণ্ডকারণ্য’, ‘মিলিটারি’ প্রভৃতি। এসব প্রচেষ্টায় তার মেজাজ, চিন্তা, আদর্শ ও নাট্যস্বভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। এ ছাড়া নিজের অভিজ্ঞতা ও দেশের সমকালীন ঘটনা নিয়ে একাঙ্কিকাগুলো রচিত হয়। মার্ক্সীয় চিন্তা, পুরোনো মূল্যবোধকে আঘাত, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভাষা আন্দোলনসহ সমকালীন জীবনের উত্তাপ একাঙ্কিকাগুলোর প্রধান দিক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রবল সমাজবোধ, রঙ্গব্যঙ্গ, মননশীল সংলাপ, যুক্তিশীলতাসহ নবনাট্যের মঞ্চায়ন ও অভিনয়রীতি। উদাহরণ হিসেবে ‘কবর’ নিয়ে দু-একটি কথা বলা যায়।
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় রনেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে মুনীর চৌধুরী ‘কবর’ নাটক লিখেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ভাষা আন্দোলনকে বেগবান এবং সামষ্টিক চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে কারাগারের ভেতরে গোপনে তা অভিনীত হবে, যদিও এতে ছিল নানা সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকি। নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল হারিকেনের আলোই হবে মঞ্চের একমাত্র ব্যবস্থা; আর এসব শর্ত মাথায় রেখে নাটকটি রচিত হয়। পরে এটি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ও ব্যতিক্রমী নাটক হিসেবে নন্দিত হয় এবং চরিত্রায়ণ, দৃশ্যায়ন ও বক্তব্যে বাঙালি জাতীয়তাবদী রাজনীতির ভাষ্য হয়ে ওঠে।
ভাববস্তু ও নির্মাণরীতিতে ইউরোপীয় নবনাট্যের সরাসরি প্রভাব ‘কবর’ নাটকে দেখা যায়। রাজনৈতিক বক্তব্য, প্রতীকধর্মিতা, অ্যাবসার্ডিটি ও অস্তিত্ববাদী চেতনায় ঋদ্ধ ‘কবর’ ভাষা আন্দোলনের প্রতিরোধ ও জাতীয় আত্মবোধের রূপক হিসেবে রচিত হয়েছিল। ইউরোপীয় নবনাট্য প্রভাবিত আমেরিকান নাট্যকার আরউইন শো-র বিখ্যাত ‘ব্যুরি দ্য ডেড’ (১৯৩৬) নাটকের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। মুনীর চৌধুরীও অবচেতনগত প্রভাবের কথা প্রকারান্তে স্বীকার করেছেন। কারণ, নাটকটি তিনি পড়েছিলেন ‘কবর’ রচনার খানিক আগে। ‘কবরে’ যেমন কবরস্থানকে কেন্দ্র করে ভাষাশহীদ ও গুম-হওয়া লাশ এবং অন্যান্য চরিত্রের মিথস্ক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের প্রতিবাদ রয়েছে, ‘ব্যুরি দ্য ডেডে’ও তিরিশের দশকের আমেরিকার সামরিক হত্যাযজ্ঞের বিপরীতে যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক সমাধিতে ছয় মৃত সৈন্যের কবরে যেতে অস্বীকৃতি নিয়ে লেখা। দুই নাটকেই মৃতদের বিদ্রোহ রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ। মুনীর চৌধুরী আরউইন শোর যুদ্ধবিরোধী মনোভাবকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় সৃষ্টিশীলভাবে রূপান্তর করেছেন। অবশ্য নাট্যরীতির দিক থেকে দুটিতে পার্থক্য হচ্ছে শোতে যেখানে অ্যাবসার্ডধর্মিতা বেশি, মুনীর চৌধুরীতে প্রতীকবাদ ও রূপকধর্মিতা বেশি। মঞ্চায়নের ক্ষেত্রেও স্ট্যানিস্লাভ্স্কির বাস্তববাদী অভিনয়-পদ্ধতি ‘কবরে’ প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। হারিকেন, প্রদীপ ও দিয়াশলাইয়ের আলোয় মঞ্চে এক প্রকার অতিপ্রাকৃত ও রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। সেট পরিকল্পনায় আলো-অন্ধকারের মিশ্রণে নাটকের আবহ সৃষ্টি করা হয়। মঞ্চে গোরস্তানের শেষ রাতের আবহ, লাশের মুখে রহস্যাবৃত কথা ও প্রতিবাদী মিছিল মঞ্চে ভয়াল পরিবেশ সৃষ্টি করে; যা অভূতপূর্ব। এ ছাড়া বিষয়-পরিকল্পনা, সংলাপের শাণিত ভাষা ও নাট্যায়নে ‘কবর’ নতুন ধারার মৌলিক ও শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে পরিগণিত।
পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটকের মধ্যে মুনীর চৌধুরীর ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নাটকটির বিষয় পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ; অবশ্য ঘটনাগুলো তিনি নিয়েছেন কায়কোবাদের ‘মহাশ্মশান’ কাব্য থেকে। যুদ্ধবিরোধী চেতনা নিয়ে মুনীর চৌধুরী মূলত ট্র্যাজেডি রচনা করতে চাইলেও নির্মাণরীতিতে সেই ইউরোপীয় নবনাট্যের প্রভাব ছিল। নাটকে ইতিহাস ও ট্র্যাজেডিকে প্রধান না করে নাট্যকার আরোপণ করেছেন আধুনিক জীবনচেতনা, ব্যক্তিমানুষের ব্যর্থতা ও জীবনের সুগভীর রহস্য। বাংলা ঐতিহাসিক নাটক থেকে তাই এটি যেমন ভিন্ন, ট্র্যাজেডি থেকেও। ট্র্যাজেডির নিয়ামক হিসেবে গ্রিক ও শেক্সপিয়ারীয় ট্র্যাজেডির যথাক্রমে নিয়তিবাদ কিংবা কর্মবাদকে মুনীর চৌধুরী অনুকৃত না করে ঘটনাপরম্পরা ও জীবনের রহস্যকে অনুসৃত করেন ‘রক্তাক্ত প্রান্তরে’। অর্থাৎ ট্র্যাজেডির উৎকর্ষ, বিকাশ ও পরিণতিতে ‘ইনসলিউবল মিস্ট্রি অব ইভেন্টস’ এবং ‘আদার কন্ডিশন বিয়িং দ্য সেম’কে তিনি প্রাধান্য দিয়ে নব্যনাট্যরীতিকে বাংলা নাটকে প্রতিস্থাপিত করলেন। সবচেয়ে বড় বিষয়, ইতিহাসের চরিত্রকে ধূসর জগতে ফেলে না রেখে সমকালীন মানুষের অবয়বে নির্মাণ করলেন। তাই জোহরা, ইব্রাহিম কার্দি, জরিনা, নজীবদ্দৌলা প্রমুখ চরিত্র চেনা মুখ হয়েই ধরা দেন। অন্যদিকে মুনীর চৌধুরী ইতিহাসের দ্বন্দ্বের চেয়ে সমকালের দ্বন্দ্বকে প্রতিষ্ঠিত করলেন নাটকে। পানিপথের যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের রক্তপাত ও অর্থহীনতা সমকালীন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ও অর্থহীনতায় প্রতিমূর্ত হয়েছে নাটকে। যুদ্ধ শেষে বিজয়ী আহমদ শাহ আবদালির যে উপলব্ধি, ‘রক্তে রক্ত মিশেছে। কার সাধ্য এই রক্ত-মাংস-অস্থি হাতড়ে শত্রু-মিত্র বেছে বেছে আলাদা করে।’ এই জীবনোপলব্ধি আধুনিক মানবতাবাদী জীবনদর্শনকেও মূর্ত করে। এমন চেতনার রূপায়ণ ইউরোপীয় নবনাট্য থেকে শেখা।
মুনীর চৌধুরীর রূপান্তরমূলক নাটক দুটি হচ্ছে জর্জ বার্নার্ড শর ‘ইউ নেভার ক্যান টেল’ অবলম্বনে ‘কেউ কিছু বলতে পারে না’ এবং জন গল্সওর্দির ‘দ্য সিলভাব বক্স’ অবলম্বনে ‘রূপার কৌটা’। নাট্যকারদের নাট্যরীতি বজায় রেখে উভয় নাটকে মুনীর চৌধুরী আরোপ করেছেন নিজস্বতা; প্রেক্ষাপট, বাস্তবতা, চরিত্র-নাম, স্থান-নাম, বিষয় ইত্যাদি পরিবর্তন করে দেশীয় আবহ ও ভাষায় এমন চমকপ্রদ রূপান্তর বাংলা নাটকের ইতিহাসে ব্যতিক্রমীই ছিল। কেউ বলে না দিলে বোঝার উপায় নেই নাটকগুলোর মূল বার্নার্ড শ কিংবা গল্সওর্দি থেকে নেওয়া। তবে মুনীর চৌধুরী মূলের কাঠামোকে যথাযথ রেখেই রূপান্তর করেছিলেন। বার্নার্ড শর নাটকের যে প্রবণতা তর্কপ্রিয়তা, বৈদগ্ধ ও তির্যক সংলাপ—তারও বিচ্যুতি ঘটাননি তিনি। অন্যদিকে গল্সওর্দিতে জীবনঘনিষ্ঠ ও বাস্তবনিষ্ঠ করার অভিপ্রায়ে ‘ককনি’ ভাষার প্রয়োগ যেমন সংলাপে, মুনীর চৌধুরীও কিছু ক্ষেত্রে ঢাকাই উপভাষার ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া গল্সওর্দির প্রতিবাদী কণ্ঠও নাটকে অক্ষুণ্ন রেখে আত্মীকৃত করার যে কৌশল, তা অভিনবই বলা যায়। রূপান্তরমূলক অপরাপর একাঙ্কিকা যেমন ইডেন ফিলপটসের ‘সামথিং টু টক অ্যাবাউট’ অবলম্বনে ‘মহারাজ’, অ্যালান মঙ্কহাউসের ‘দ্য গ্রান্ড চ্যামস ডায়মন্ড’ অবলম্বনে ‘গুর্গন খার হীরা’, রিচার্ড হিউজের ‘দ্য ম্যান বর্ন টু বি হ্যাঙ্গড’ অবলম্বনে ‘ললাট লিখন’, অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গের ‘দ্য ফাদার’ অবলম্বনে ‘জনক’ প্রভৃতিতেও মূলের মেজাজ ও পদ্ধতি বজায় রেখে সাংস্কৃতিক রূপান্তর করেছেন। বিচিত্র সংস্কৃতির বিচিত্র চরিত্রকে দেশীয় প্রেক্ষাপটে পুনর্নির্মাণ সহজসাধ্য বিষয় ছিল না, কিন্তু মুনীর চৌধুরীর সহজাত প্রতিভার পক্ষে তা নিপুণভাবে সাধিত হয়। এসব নাটকের মঞ্চ-পরিকল্পনা, দৃশ্যসজ্জা ও আলোকবিন্যাসেও তিনি ইউরোপীয় প্রভাবজাত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। মুনীর চৌধুরীর উদ্দেশ্য ছিল নতুন ধারার নাটক বাংলা সাহিত্যে উন্মোচিত করা এবং একই সঙ্গে নাটককে নতুন খাতে প্রবাহিত করা। রূপান্তরমূলক নাট্যসৃষ্টিগুলো এর বড় প্রমাণ।
ক্ল্যাসিক ধারার নাট্যকার হিসেবে শেকসপিয়ারের প্রতি বরাবর মুনীর চৌধুরীর একটা আকর্ষণ ছিল। রূপান্তরের পরে তিনি অনুবাদে হাত দিলে প্রথমেই বেছে নিলেন তাই শেক্সপিয়ারকে। ‘দ্য টেমিং অব দ্য শ্রু’র অনুবাদ করেন ‘মুখরা রমণী বশীকরণ’ নামে, আর ‘ওথেলো’ অনুবাদ করতে পারলেন তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য অবধি। শেক্সপিয়ারের ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট’ ও ‘মাচ আডো অ্যাবাউট নাথিং’ নাটক দুটিও আংশিক অনুবাদ করেন মুনীর চৌধুরী। ইউজিন ও-নিল তার প্রিয় আরেকজন নাট্যকার ছিলেন, ও-নিলের ‘মাউরনিং বিকামস ইলেক্ট্রা’কে ‘ইলেক্ট্রার জন্য শোক’ নামে প্রথম খণ্ডের আংশিক অনুবাদ করেছিলেন। আবার টেনেসি উইলিয়ামসের ‘আ স্ট্রিটকার ন্যামড ডিজায়ার’কে ‘গাড়ির নাম বাসনাপুর’ নামে কিছতা এগিয়েছিলেন।
প্রথম অনুবাদ ‘মুখরা রমণী বশীকরণে’ই মুনীর চৌধুরীর বিশিষ্টতা ধরা পড়েছিল। মূলের গদ্য-পদ্য থেকে গদ্যে অনুবাদ করতে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি শেক্সপিয়ারের মেজাজ ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। নাটকীয় সংলাপের স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে বাক্ভঙ্গির প্রয়োজনীয় অদল-বদলও করে নিয়েছিলেন। শেক্সপিয়ারের কাব্যবোধ ও মননের প্রতি অত্যন্ত সজাগ থেকেই ভাষাভঙ্গি বজায় রাখেন তিনি। ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে স্থানকালগত বিষয়েও যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দেন। ‘ওথেলো’র অনুবাদেও তেমন স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে; অন্য সব আংশিক অনুবাদের ক্ষেত্রেও তাই। অনুবাদে পরাধীন হওয়া সত্ত্বেও মুনীর চৌধুরীর সৃজনশীলতা বিস্ময়কর ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলা নাটকের যে তিনি অনেক কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।
মুনীর চৌধুরী চেয়েছিলেন বাংলা নাটক বিশ্বমানের হোক, বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হোক। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা নাট্যসাহিত্য ও বিশ শতকের রবীন্দ্রনাথসহ দু-একজন বাদে সেই প্রচেষ্টা কারও মধ্যে দেখতে পাননি তিনি। এদিকে ইউরোপের নবনাট্য নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যেভাবে অগ্রসরমাণ ও যুগোপযোগী ছিল তার সঙ্গে বাংলা নাটকের ছিল দুস্তর ব্যবধান। অথচ দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন, জাতীয় জীবনের নানা ঘটনা, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের জীবন, পাকিস্তান আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, দাঙ্গা, দেশভাগ, ভারত-স্বাধীনতা, ভাষা-আন্দোলন, ষাটের স্বৈরশাসনসহ পাকিস্তানি বৈষম্যবাদী শাসন-শোষণজনিত বাঙালি জীবন নাট্য-উপাদানে ভরপুর। কেবল নতুন নাট্যরীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবর্তিত জীবনবোধ দিয়ে তার প্রয়োগ প্রয়োজন। দরকার নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে বাংলার নাটকে প্রবাহিত এবং গ্রহণযোগ্য করে তোলা। তাই নিজেই এক সময় শুরু করেন নিরীক্ষা, আর যত দিন বেঁচেছিলেন চালিয়ে যান নাটকের মৌলিক সৃজন, রূপান্তর কিংবা অনুবাদ। এ ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী নিজেদের ঐশ্বর্যের সঙ্গে ইউরোপীয় নবনাট্যের ধ্যানধারণা ও রীতিকে সাঙ্গীভূত করে বাংলা নাটকে সত্যিকার অর্থে নব-উল্লাস আনতে পেরেছিলেন।
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ