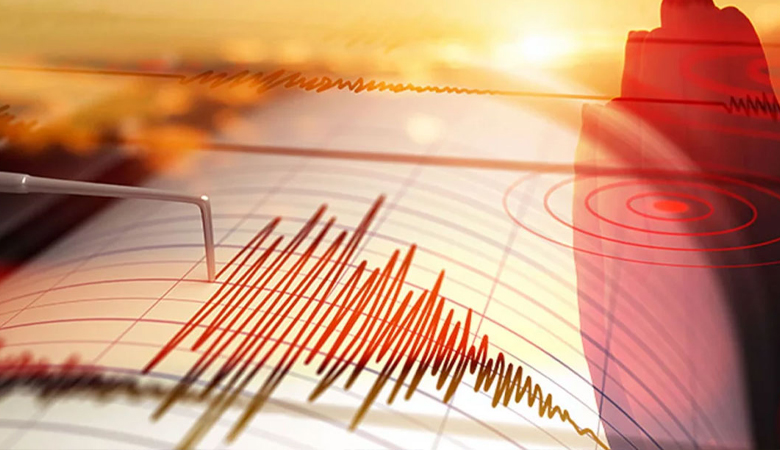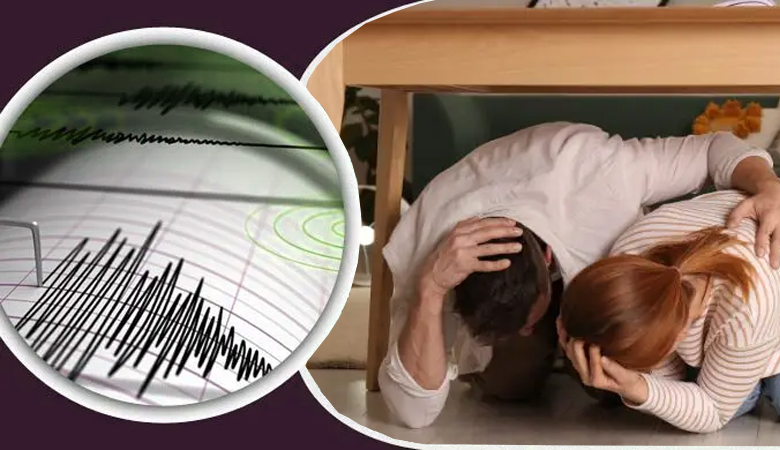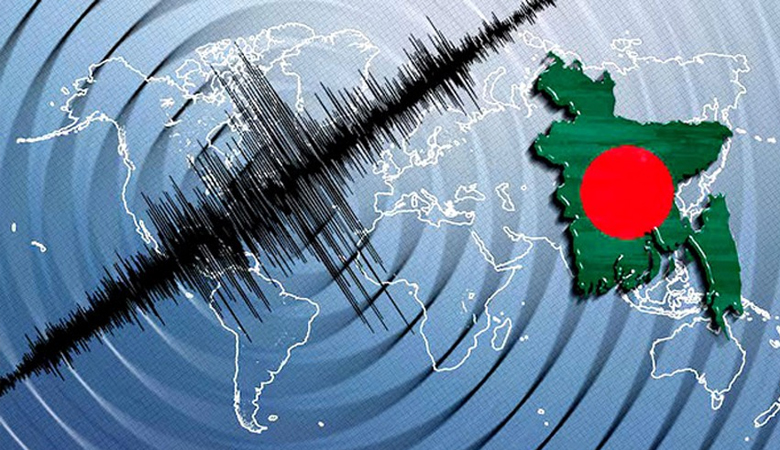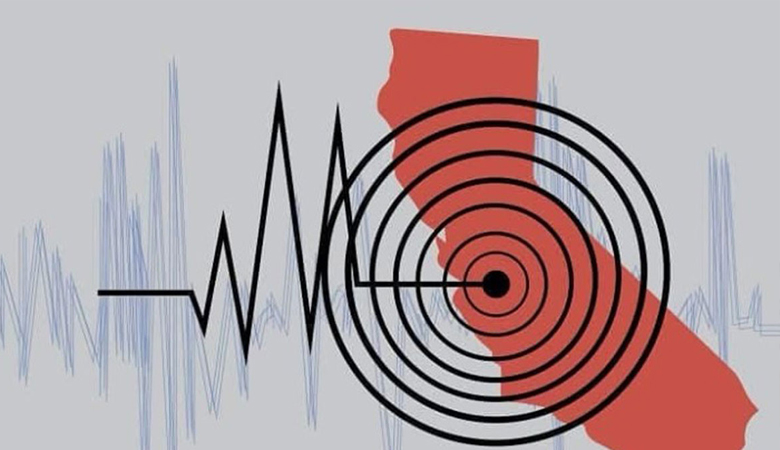ড. এম মেসবাহউদ্দিন সরকার
গত শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের আমরা বিপদ গ্রহণ করেছি। নিহত, আহত, বিল্ডিং ধসে পড়েছে এ ধরনের খবরে সয়লাব প্রিন্টিং ও মিডিয়া জগৎ। ফেসবুকে এক শ্রদ্ধাভাজন সাংবাদিক লিখেছেন তার ৭০ বছর বয়সে এত তীব্রমাত্রার ভূমিকম্প দেখেননি। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধারণত ১০০-১৫০ বছর পর কোন একটি অঞ্চলে এত তীব্রমাত্রার ভূমিকম্প হয়।
বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সক্রিয় ফল্ট লাইনের ওপর অবস্থিত। ফলে এখানে মাঝারি বা বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি সবসময়ই থাকে। ঢাকা এবং সিলেট অঞ্চল ভূমিকম্পের ‘রেড জোন’ হিসেবে চিহ্নিত আছে। কিন্তু এই মহাবিপদ থেকে রক্ষার কোনো প্রস্তুতি নেই আমাদের। তবে আধুনিক প্রযুক্তি ভূমিকম্পের পূর্বাভাস, ঝুঁকি মূল্যায়ন, ভূমিকম্প-সহনশীল স্থাপত্য নির্মাণ এবং দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধারকাজকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছে।
ভূমিকম্প পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এটি পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের নিচে টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়া, আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ কিংবা ভূগর্ভস্থ ভাঙনের ফলে ঘটে। এই অদৃশ্য কম্পনকে শনাক্ত, পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করার জন্য যে প্রযুক্তি সেটিই সিসমোগ্রাফ বা ভূকম্পমাপক যন্ত্র। এর মাধ্যমে ভূমিকম্পের তীব্রতা, উৎসস্থল, গভীরতা ও সময় সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়। সিসমোগ্রাফ মূলত একটি সংবেদনশীল যন্ত্র, যা ভূমিকম্পের সময় ভূকম্পন বা ভূমিকম্পীয় তরঙ্গ। যেমন- চ-ধিাব, ঝ-ধিাব ও ঝঁৎভধপব ধিাব ধরে রাখে এবং সেগুলোর নড়াচড়া গ্রাফের মাধ্যমে রেকর্ড করে।
এই রেকর্ডকৃত গ্রাফকে সিসমোগ্রাম বলা হয়। ভূমিকম্পের উৎস থেকে নির্গত তরঙ্গ যখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সিসমোগ্রাফে পৌঁছে, তখন যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই কম্পনের বিন্যাস নথিবদ্ধ করে। প্রাথমিকভাবে সিসমোগ্রাফ ছিল যান্ত্রিক পেন-অ্যান্ড-ড্রাম সিস্টেম; যেখানে একটি স্থির ফ্রেমের সঙ্গে সংযুক্ত ভারী পেন্ডুলাম ভূমিকম্পের তরঙ্গ অনুসারে কাঁপত এবং ঘূর্ণায়মান কাগজে কম্পনের চিহ্ন রেখে যেত। তবে আধুনিক সিসমোগ্রাফ এখন ডিজিটাল, যেখানে ডেটা ইলেকট্রনিক সেন্সর ও কম্পিউটারের মাধ্যমে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়।
প্রকৃতপক্ষে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণরূপে ঠেকানো না গেলেও ডিজিটাল সিসমোমিটারের সহায়তায় এর প্রভাব অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। এটি পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কম্পন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ধারণ করতে পারে এবং তাৎক্ষণিকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে পাঠাতে পারে। এ ছাড়া গভীর সমুদ্রেও স্থাপন করা হচ্ছে ওশান-বটম সিসমোমিটার; যা সাবমেরিন ভূমিকম্প বা সুনামির প্রাথমিক সংকেত শনাক্ত করতে সক্ষম। ভূকম্পন মাপার এসব সেন্সরের নেটওয়ার্ক একটি বৈশ্বিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করেছে। ফলে টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়া, ফল্ট লাইনের সক্রিয়তা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য ভূমিকম্প সম্পর্কে অনেক আগেই সতর্ক করা সম্ভব হচ্ছে।
সিসমোগ্রাফের কার্যপ্রণালি পদার্থবিজ্ঞানের জড়তা সূত্রের ওপর নির্ভর করে। যে কোনো বস্তু স্থির থাকলে বাহ্যিক বল না লাগা পর্যন্ত সেটি স্থিরই থাকে, এই নীতিই সিসমোগ্রাফের মূল ভিত্তি। যন্ত্রটি সাধারণত দুটি অংশে বিভক্ত- ১. স্থির কাঠামো- যা ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে; ২. ঝুলন্ত বা পেন্ডুলাম অংশ- যা তুলনামূলকভাবে স্থির থাকে।
ভূমিকম্পে ভূমি নড়ে উঠলেও পেন্ডুলাম ঠিক একই অনুপাতে নড়ে না। ফলে স্থির কাঠামো এবং পেন্ডুলামের মধ্যে সৃষ্ট আপেক্ষিক নড়াচড়া সেন্সর ধরে ফেলে এবং সেটিকে গ্রাফ আকারে সংরক্ষণ করে। এভাবেই ভূমিকম্পের মাত্রা ও তরঙ্গের ধরন রেকর্ড হয়।
ডিজিটাল সিসমোগ্রাফে অ্যানালগ-টু-ডিজিটাল কনভার্টার এই আপেক্ষিক নড়াচড়াকে ডিজিটাল ডেটায় রূপান্তর করে। এরপর কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিল্টারিং, অ্যামিপ্লফিকেশন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভূমিকম্পের সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করে। সাধারণত ভূমিকম্পের তরঙ্গ পৃথিবীর বিভিন্ন দিক ও স্তর দিয়ে যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে, হলো-
ভার্টিকাল সিসমোগ্রাফ: উপরের দিক থেকে নিচের কম্পন ধরে।
হরাইজন্টাল সিসমোগ্রাফ: পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ দিকের কম্পন মাপা হয়।
ব্রডব্যান্ড সিসমোগ্রাফ: খুব কম ও খুব বেশি উভয় ফ্রিকোয়েন্সির ভূকম্পনী তরঙ্গ শনাক্ত করতে সক্ষম।
স্ট্রং-মোশন সিসমোগ্রাফ: শক্তিশালী ভূমিকম্পে বড় মাত্রার নড়াচড়া রেকর্ড করতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে ভূমিকম্প-প্রবণ শহর ও উচ্চ-তলার ভবনে। এই ভিন্ন ভিন্ন সিসমোগ্রাফের ডাটা মিলিতভাবে ভূমিকম্পের উৎস, গভীরতা এবং মাত্রা নির্ধারণে সহায়তা করে।
আধুনিক যুগে সিসমোগ্রাফ শুধু ভূমিকম্প শনাক্তকরণেই সীমাবদ্ধ নয়, এর ব্যবহার বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক। যেমন- ভূমিকম্প পূর্বাভাস ও সতর্কতা ব্যবস্থা। পৃথিবীর অনেক দেশ এখন আরলি ওয়ার্নিং সিস্টেম ব্যবহার করে; যেখানে সিসমোগ্রাফিক নেটওয়ার্ক ভূমিকম্পের প্রথম ধরনের তরঙ্গ (চ-ধিাব) শনাক্ত করে ঝ-ধিাব-এর আগেই সতর্কতা পাঠাতে পারে। এতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মানুষ আশ্রয় নিতে পারে এবং গ্যাস লাইন, পানি ও অন্যান্য ধার্য সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
ভূমিকম্প প্রতিরোধ ছাড়াও সিসমোগ্রাফ আরো যেসব কাজে ব্যবহৃত হয়, তা হলো-
ভূগর্ভস্থ সম্পদ অনুসন্ধান: তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ বা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নির্ণয়ে সিসমিক সার্ভে করা হয়। এতে আর্টিফিশিয়াল কম্পন তৈরি করা হয় এবং সিসমোগ্রাফ ওই তরঙ্গের প্রতিফলন বিশ্লেষণ করে ভূগর্ভস্থ কাঠামো চিহ্নিত করে।
অগ্ন্যুৎপাত ও আগ্নেয়গিরি পর্যবেক্ষণ: আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে ম্যাগমা চলাচলের ফলে ক্ষুদ্র ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। সিসমোগ্রাফ ওই কম্পন ধরে আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তা পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে।
ভূ-অভ্যন্তর গবেষণা: পৃথিবীর ম্যান্টল, কোর, ভূত্বক ইত্যাদি স্তরের গঠন ও প্রকৃতি নির্ণয়ে সিসমিক তরঙ্গের আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিসমোগ্রাফিক তথ্যের মাধ্যমে ভূতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালিত হয়।
বড় নির্মাণ প্রকল্পে নিরাপত্তা মূল্যায়ন: বাঁধ, সুড়ঙ্গ, সেতু, মেট্রো, পারমাণবিক কেন্দ্র ইত্যাদির আশপাশে সিসমোগ্রাফিক নেটওয়ার্ক বসানো হয় যাতে নির্মাণকাজ ভূমিকম্প-সহনশীল কিনা তা নিশ্চিত করা যায়।
আধুনিক সিসমোগ্রাফ প্রযুক্তি ১৯ শতকের শেষ দিকে জাপান ও ইউরোপের বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে উন্নত হয়। বর্তমান ডিজিটাল সিসমোগ্রাফে রয়েছে অত্যন্ত সংবেদনশীল সেন্সর, স্যাটেলাইট লিংক, রিয়েল-টাইম ডেটা শেয়ারিং, কম্পিউটারভিত্তিক বিশ্লেষণ, ক্লাউড-ভিত্তিক মনিটরিং সিস্টেম ইত্যাদি। ফলে বিশ্বব্যাপী সিসমোগ্রাফের নেটওয়ার্ক মিলিতভাবে পৃথিবীর প্রতিটি ভূমিকম্প রেকর্ড করে। এতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভূমিকম্পের তথ্য বৈজ্ঞানিকদের কাছে পৌঁছে যায়। আগামী দিনের সিসমোগ্রাফ হবে আরো দ্রুত, সেনসিটিভ এবং এআইনির্ভর।
গবেষকরা এখন স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, ফাইবার অপটিক কেবল, এমনকি গভীর সমুদ্রের কেবল ব্যবহার করে ভূমিকম্প শনাক্ত করার প্রযুক্তি তৈরি করছেন। ফাইবার অপটিকভিত্তিক উরংঃৎরনঁঃবফ অপড়ঁংঃরপ ঝবহংরহম (উঅঝ) ভবিষ্যতে ভূমিকম্প নির্ণয়ে বিপ্লব আনতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিংও ভূমিকম্পের পূর্বাভাসে অনন্য ভূমিকা রাখবে। মিলিয়ন মিলিয়ন সিসমিক ডেটা, স্যাটেলাইট ডেটা বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য ঝুঁকির এলাকা আরও নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।
ভূপৃষ্ঠের মাপজোক, ফল্ট লাইন বিশ্লেষণ, মাটির প্রকৃতি, জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভবনগুলোর পুরানো-নতুন অবস্থা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করে এআই মডেল সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পূর্বাভাস দিতে পারে। ড্রোন প্রযুক্তি দুর্যোগ-পূর্ব ও পরবর্তী এলাকায় দ্রুত তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করে। প্রযুক্তির এই সমন্বিত ব্যবহার মানুষের জীবন রক্ষার পাশাপাশি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে আরও বিজ্ঞানসম্মত করে তুলছে।
সিসমোগ্রাফ প্রযুক্তি শুধু একটি যন্ত্র নয়, বরং মানব জীবনের সুরক্ষার অন্যতম প্রধান সহায়ক। পৃথিবীর ভেতরে কী ঘটছে তা চোখে দেখা যায় না। কিন্তু সিসমোগ্রাফ ওই অদৃশ্য কম্পনের ভাষা পড়ে আমাদের সামনে সত্য তুলে ধরে। ভূমিকম্প পূর্বাভাস, গবেষণা, নির্মাণ নিরাপত্তা, আগ্নেয়গিরি পর্যবেক্ষণ- সব ক্ষেত্রেই এর অবদান অসামান্য।
প্রযুক্তির অগ্রগতি সিসমোগ্রাফকে আরো শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান করে তুলছে; যা ভবিষ্যতের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করবে। তাই বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল ভূমিকম্প-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে এসব প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। এর পাশাপাশি জনসচেতনতা, সরকারি উদ্যোগ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মিলেই গড়ে উঠবে একটি ভূমিকম্প সহনশীল আধুনিক বিশ্ব।
লেখক: তথ্যপ্রযুক্তিবিদ ও অধ্যাপক, আইআইটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
(মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব)
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ