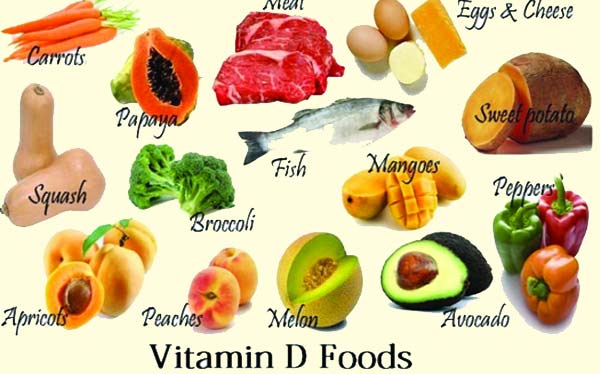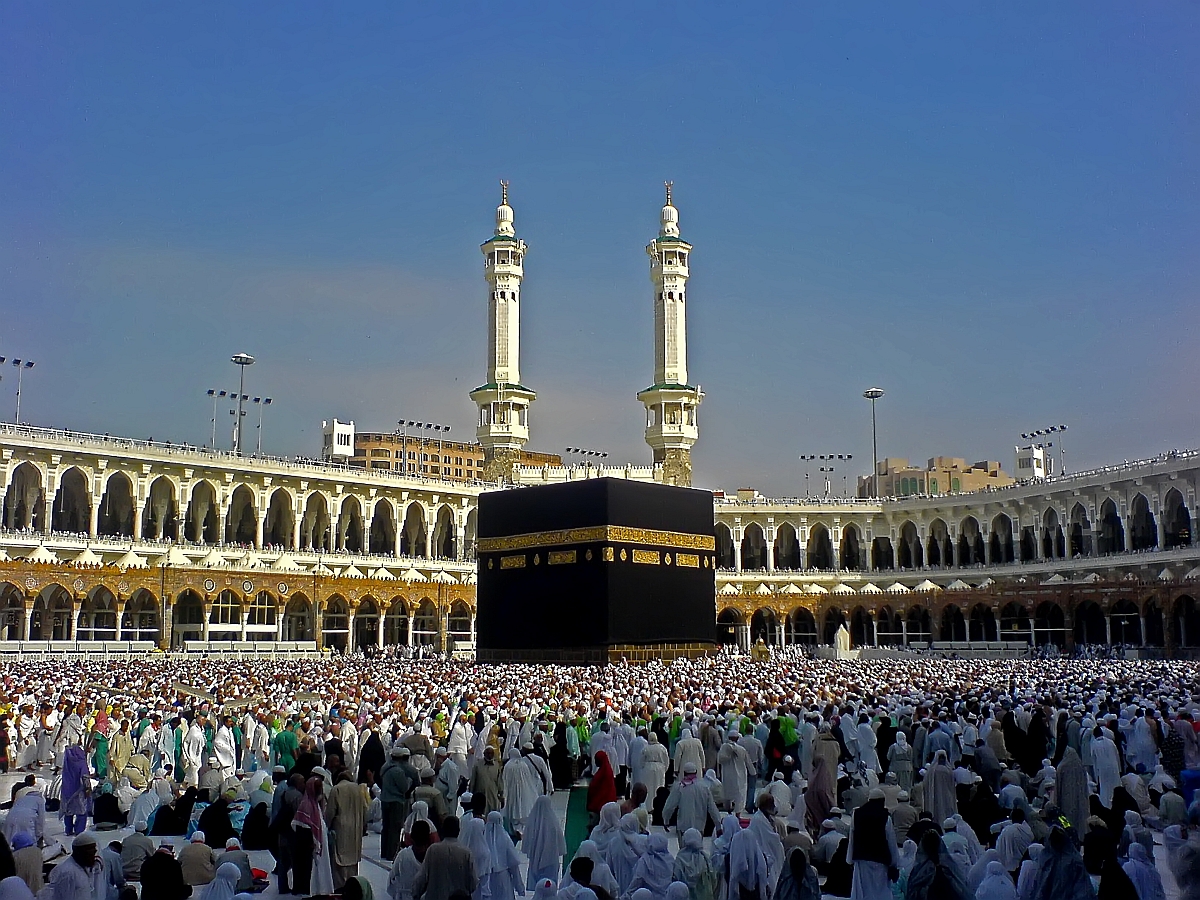মাহাদী হাসান
এক সময় সাংবাদিকতা পড়া মানে ছিল এক ধরনের স্বপ্নে পা রাখা। সংবাদ কক্ষের ভেতরে ঝড়ের মতো কাজ, প্রেস কার্ড ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো, প্রথম পাতায় নাম ছাপা হওয়ার উত্তেজনা-এসব মিলেই সাংবাদিকতা অনেককে টেনেছে। এক সময় এই ‘গ্ল্যামার’ এর সঙ্গে যোগ হতো তারুণ্যের বিদ্রোহ; যেন সমাজকে নাড়িয়ে দেওয়ার এক অনন্য অস্ত্র হাতে পাওয়া। সেই আগ্রহ থেকে অনেক তরুণ এ বিষয়ে পড়াশোনা করতে আসতেন।
গ্ল্যামার শব্দটা নিয়ে খটকা লাগতে পারে। পরিষ্কার করে বলা দরকার যে, আমি যখন ‘গ্ল্যামার’ বলছি, তখন শুধু ঝলমলে আলো বা ফ্যাশনের ব্যাপার বোঝাচ্ছি না। এখানে গ্ল্যামার মানে হলো, সাংবাদিকতার চারপাশে তৈরি হওয়া আকর্ষণ, জনপ্রিয়তা, আর এক ধরনের সামাজিক মর্যাদা। টিভি পর্দায় দেখা যাওয়া, খবরের কাগজে নাম ছাপা হওয়া-এসবই তরুণদের কাছে সাংবাদিকতাকে একসময় দারুণ মোহনীয় করে তুলেছিল। সেই দৃশ্যমানতা, সামাজিক প্রভাবই আসলে গ্ল্যামারের অন্য নাম। একাডেমিক ভাষায় এটিকে বলা যেতে পারে সাংবাদিকতার সামাজিক আকর্ষণ বা দৃশ্যমান মর্যাদা। তবে সাধারণ পাঠকের কাছে ‘গ্ল্যামার’ শব্দটি বেশি পরিচিত বলে সেটিই ব্যবহার করছি।
এক দশক আগেও সাংবাদিকতার ক্লাসে ঢুকলেই বাতাসে একটা রোমাঞ্চ মিশে থাকত। শিক্ষকরা বলতেন, ‘তোমাদের হাতে আছে কলম, আর সেই কলমই পারে রাষ্ট্রকে নাড়িয়ে দিতে।’ ওই কথাগুলো আমরা বিশ্বাসও করতাম। টিভি চ্যানেলের ঝলমলে স্টুডিও, সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় নিজের নাম দেখা, বড় কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের পর হইচই- এসব ছিল সেই গ্ল্যামারের আসল উপাদান।
সত্যি বলতে, সাংবাদিকতা আর আগের মতো চকচকে নেই। টেলিভিশন রিপোর্টার বা পত্রিকার সাংবাদিক হওয়ার রোমান্স অনেকটাই মøান। বেতন কম, কাজের চাপ আকাশ ছোঁয়া আর চাকরির নিশ্চয়তা বলতে যা বোঝায়- সেটি প্রায় অদৃশ্য। তরুণরা তাই দ্বিধায় পড়ে যান। সাংবাদিকতা নিয়ে পড়বেন, নাকি অন্য কোনো ‘নিরাপদ’ পেশার দিকে ঝুঁকবেন? অথচ এ বিষয়ে পড়াশোনা একসময় অনেক আগ্রহের ছিল।
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তো আছেই। কিন্তু সেই ‘আলোর’ টানেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও একে একে খুলতে শুরু করে সাংবাদিকতা বা গণমাধ্যম বিভাগ। প্রথম শুরু হয় ২০০২ সালে ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমন্টে অল্টারনেটিভে (ইউডা)। এর পরপরই আসে স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর একে একে অনেকগুলো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিভাগ যুক্ত হতে থাকে। কমিউনিকেশন বা গণযোগাযোগ আকারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো শুরু হয়, যার একটা অংশ সাংবাদিকতা। তবে বাস্তবে এই ‘অংশই’ হয়ে ওঠে প্রাণ ও মূল আকর্ষণ। তাই কোথাও বিভাগের নাম কমিউকেশন, কোথাও জার্নালিজম আবার কোথাও মিডিয়া স্টাডি। নাম আলাদা। তবে টান একটাই- সাংবাদিকতার চকচকে মোহ। সবাই ভেবেছিল, এ বিষয়ে ভর্তিচ্ছুদের ভিড় লেগেই থাকবে। কারণ তখন প্রায় অর্ধশত বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ঝকঝকে স্ক্রিন, হাতে বুম।
মুন্নি সাহা, শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম, শাহানাজ মুন্নি, সামিয়া জামান, সামিয়া রহমান, হারুন উর রশিদ, শাহেদ আলম, মঞ্জুরুল করিম পলাশদের মতো তারকা সাংবাদিক তখন ঘরে ঘরে পরিচিত নাম। ওই জায়গা থেকে ক্রমেই দীর্ঘ হতে থাকে এই বিভাগ যুক্ত করা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা। আজ তালিকা করলে অবাক হতে হয়। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস (ইউল্যাব), ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ), স্টেট ইউনিভার্সিটি, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি-কোথায় নেই? প্রায় সব বড় বেসরকারিতেই কোনো না কোনো আকারে আছে এই বিভাগ।
হ্যাঁ, একটা কিন্তু আছে সবখানে। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা সেভাবে বাড়ছে না, বরং এইচএসসি পাস শিক্ষার্থীদের অনুপাত হিসেব করলে গাণিতিকভাবে সেই সংখ্যা কমছেই বলা যায়। আগের মতো ভর্তিচ্ছুদের ভিড় আর নেই। দুই-তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া কারোরই তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী নেই। একসময় যে গ্ল্যামার ভিড় টানতো, সেটাই আজ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।
অন্তত চারটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সবার মন্তব্য প্রায় একই, শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে আগ্রহ কমছে। আবার যারা পড়ছেন, তাদের অনেকেরই পড়াশোনা শেষ করে সাংবাদিক হওয়ার ইচ্ছেও নেই। এটা শুধু সংখ্যা কমার গল্প নয়, এটা আসলে পরিবর্তিত সময়ের প্রতিচ্ছবি। চাকরির বাজার অনিশ্চিত, বেতন কাঠামো দুর্বল, ভবিষ্যতের স্থিরতা নেই- এসব মিলিয়ে তরুণরা ভাবছেন অন্যভাবে। আসল প্রশ্ন হলো- সাংবাদিকতা কি সত্যিই তার গ্ল্যামার হারিয়েছে? নাকি আমাদের চোখে তার সংজ্ঞাই বদলে গেছে?
হয়তো আমরা যে গ্ল্যামারের কথা বলি, সেটি আসলে ছিল বাহ্যিক। টেলিভিশনে দেখা, খবরের কাগজে নাম ওঠা। এখন তো ওই জায়গাটা দখল করেছে সোশ্যাল মিডিয়া। একটা ফেসবুক পোস্ট বা ইউটিউব ভিডিও কখনো কখনো কয়েক লাখ মানুষ দেখে ফেলে। ফলে সাংবাদিকতার ওই পুরোনো রোমান্স, ‘আমি রিপোর্টার’- এই পরিচয়ের ঝলক একটু মøান হয়েছেই। তাই বলে কি সাংবাদিকতার মূল্য কমেছে? বরং দায়িত্ব বেড়েছে।
আগে গ্ল্যামার মানে ছিল কাগজে নাম ছাপা, পরে টিভিতে মুখ দেখানো। এখন সেটা হয়তো ভাইরাল স্টোরি। একটা ইউটিউব ভিডিও বা ইনস্টাগ্রাম রিল-হয়তো কয়েক ঘণ্টায় লাখো মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তরুণরা গ্ল্যামার দেখছেন সেখানে, এবং এটা সাংবাদিকতার ভেতর থেকেই বের হচ্ছে। কিন্তু একটা সত্যও আছে, গ্ল্যামার আসলে কখনো সাংবাদিকতার মূল উদ্দেশ্য ছিল না।
সাংবাদিকতা টিকেছিল দায়িত্ববোধে। টিকেছিল সমাজের সামনে সত্য তুলে ধরার নেশায়। তবে আজকের সাংবাদিককে শুধু খবর জানালেই হয় না। তাকে জানতে হয় ডিজিটাল টুলস, বুঝতে হয় ডেটা, সামলাতে হয় ভুয়া তথ্যের স্রোত। তাকে যেমন মাঠে গিয়ে রিপোর্ট করতে হয়, তেমনি অনলাইনে গল্প বলতে হয় নতুন ফরম্যাটে।
গ্ল্যামারের জায়গাটা হয়তো বদলেছে। কিন্তু সমাজে প্রভাব তৈরি করার ক্ষমতা এখনো অক্ষুণ্ন, বরং আরো বিস্তৃত। গ্ল্যামার হয়ত দরকারও নেই। কারণ গ্ল্যামার অনেক সময় বিভ্রান্তি তৈরি করে। সাংবাদিকতা কখনো শুধুই ঝলক দেখানোর জায়গা ছিল না, এটা ছিল দায়বদ্ধতার জায়গা, সত্য প্রকাশের জায়গা, ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার সাহসের জায়গা। তবে হ্যাঁ, আরেকটা দিকও আছে। শিক্ষার্থীরা যেহেতু চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চিত, সেহেতু বিষয় হিসেবে সাংবাদিকতা হয়তো কিছুটা পিছিয়ে পড়ছে- এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু গ্ল্যামার নেই মানে এই নয় যে, এর গুরুত্ব কমে গেছে। বরং যারা এই সময়েও সাংবাদিকতা পড়তে আসছেন, তাদের আমি বেশি সম্মান করি। কারণ তারা আসছেন প্রভাব খুঁজতে, দায়িত্ব নিতে, পরিবর্তনের পথে দাঁড়াতে।
আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, সাংবাদিকতার পড়াশোনা আসলে এক ধরনের প্রস্তুতি, সমাজকে দেখার চোখ তৈরি করা, ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার সাহস গড়ে তোলা। এসবের দাম কোনো হিসেবে মাপা যায় না।
লেখক: জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, যোগাযাগ ও গণমাধ্যম বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ
(মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব)
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ