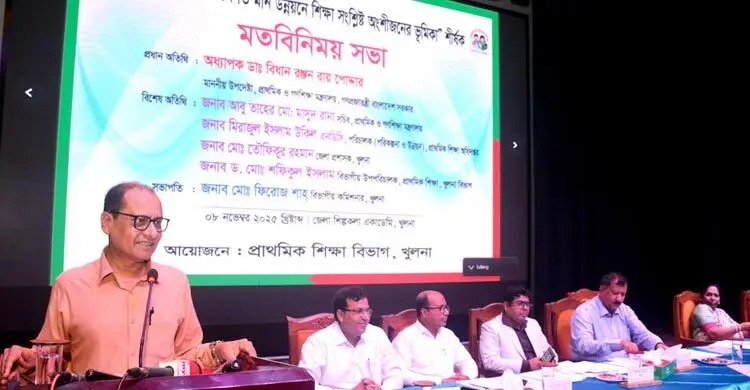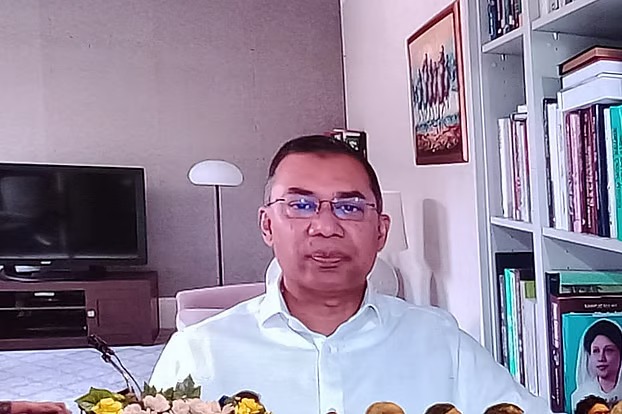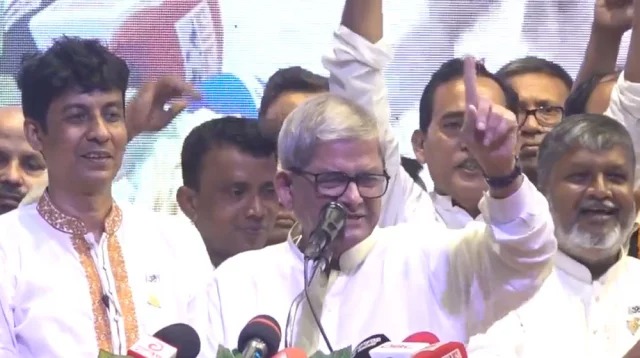আব্দুল বায়েস : ‘বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না । ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না; তাই নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে। নূতনের জন্য ইচ্ছা খুবই হইতেছে অথচ ভরসা কিছুই হইতেছে না …’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , ‘শিক্ষা’।
সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত সাতটি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এক বিশাল বিক্ষোভে নীতিনির্ধারকদের ঘুম হারাম হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চটজলদি পদক্ষেপ আপাতত আগুনের লেলিহান বিস্তার দমন করেছে; তবে ছাইচাপা আগুন হিসেবে থাকছেই। বলে রাখা দরকার যে, এই সাতটি কলেজ এক সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল, তারপর ক্ষমতার লড়াইয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চলে যায়। যাকে বলে পাটাপুতার ঘষাঘষি মরিচের মরণ এবং এই টানাপড়েনে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাজীবন জেরবার! আমরা মনে করি ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগগুলো যথাযথ তদন্তের দাবি রাখে। অবশ্য পরবর্তী দাবি দাঁড়ায় কারও অধিভুক্ত হওয়া নয় বরং সাতটি কলেজসমেত একটা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। এরই মধ্যে তিতুমির কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার ঘোষণায় অবিচল।
অবশেষে সুসংবাদ এই যে, এই কলেজগুলো নিয়ে একটা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এবং আমরা অবশ্যই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টির কল্যাণ কামনা করি। আমার নিবন্ধের মূল বক্তব্য হলো আসলে এসব কলেজের হোক ঢাকা, স্বতন্ত্র কিংবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কী এবং নিবন্ধটির স্বার্থে আমি বিআইডিএস এর গবেষক বদ্রুনেসা আহমেদ, জুলফিকার আলি এবং রিজয়ানুল ইসলামের এক গবেষণার সাহায্য নেব।
দুই.
বলা বাহুল্য যে, তারুণ্যের উচ্ছ্বাস আর উদ্দীপনা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সঠিকভাবে কাজে লাগানো আমাদের এই মুহূর্তের আশু করণীয়। কারণ আমরা জানি যে আমরা আমাদের জনমিতিক সুফল (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ হোঁচট খাবে। তবে দেশের শ্রমশক্তির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা দেয় দুঃখজনক দৃশ্য- আমাদের দেশের উৎপাদনশীল শ্রমশক্তির মধ্যে ‘নিট’ তরুণদের (শিক্ষা, কাজ বা প্রশিক্ষণে যুক্ত নেই এমন) সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।
এক হিসাব বলছে, দেশের ১৫-২৪ বছরের জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০ শতাংশই নিট জনগোষ্ঠী; যা বৈশ্বিক গড়ের প্রায় দ্বিগুণ এবং এর বড় অংশই নারী (৬২ শতাংশ)। এ পরিসংখ্যান আমাদের একটি রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি করিয়ে দেয় আর সেটি হলো এই যে, আমরা তরুণদের জন্য যথেষ্ট কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছি না। অথচ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হলেও কর্মসংস্থান তেমন সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং হতাশ তরুণ সমাজ জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থান ঘটালো যদিও অনেক কারণেই সেটা মুখ দেখেছিল।
তিন.
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত অনার্স ও মাস্টার্স কলেজ অসংখ্য অথচ এসব কলেজে অধিক বিষয়ে (অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে) পর্যাপ্ত যোগ্য শিক্ষক আছেন কি না তা নিয়ে সন্দিহান সবাই। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মাহবুব উল্লাহর পর্যবেক্ষণ অনেকটা এরকম- ‘কখনো কখনো দেখা যায়, একজন শিক্ষককে উচ্চ মাধ্যমিক পাস ও অনার্স কোর্সে পাঠদান করতে হয়। তাকে দিনে কমপক্ষে তিন-পাঁচটি পর্যন্ত ক্লাস নিতে হয়। এই শিক্ষক নিবেদিতপ্রাণ হলেও ছাত্রদের কতটুকু দিতে পারবেন, তা বলাই বাহুল্য। কলেজগুলোতে ভালো লাইব্রেরি নেই, নেই ল্যাবরেটরি। লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি ছাড়া উচ্চশিক্ষা কী করে সম্ভব বুঝে ওঠা মুশকিল।’
চার.
বদ্রুন্নেসা আহমেদ ও অন্যান্য গবেষকদের মতে বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষিত বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক বেশি এবং তা ঊর্ধ্বমুখী- ২০১৬-১৭ সালের ১১ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ১২ শতাংশ। জাতীয় গড় বেকার থেকে শিক্ষিত বেকার দ্বিগুণেরও বেশি। অবস্থা অনেকটা ‘হীরক রাজার দেশে’- ‘লেখাপড়া করে যে, অনাহারে মরে সে !’
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত আছে ৬০৮টি মাস্টার্স এবং অনার্স স্তরে থাকা কলেজ (সরকারি ২৮, বেসরকারি ৭৮ শতাংশ) এবং গবেষণা পরিচালিত হয় মোট কলেজের এক-দশমাংসের ওপর । প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোতে যারা পড়াশোনা করেছেন তাদের ৫৮ শতাংশ ছেলে, ৪২ শতাংশ মেয়ে ; ৩৮ শতাংশ মাস্টার্স এবং ৬২ শতাংশ অনার্স ডিগ্রিধারী; গড় সিজিপিএ উভয় ক্ষেত্রে ৩ এবং প্রায় তিন-চতুর্থাংশ গ্র্যাজুয়েট নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা।
ট্রেসার স্টাডি বা ফলোআপ অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে, যদিও বাংলাদেশে বেকারত্বের জাতীয় গড় ৪-৫ শতাংশ, শিক্ষিত বেকার ১২ শতাংশ; তবুও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের বেকারত্বের হার ২৮ শতাংশ বলে জানান গবেষকরা (ছেলে ২০ এবং মেয়ে ৩৪ শতাংশ; ৩৫ শতাংশ পল্লীতে, ২৪ শতাংশ নগরে)। অর্থাৎ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো থেকে পাস করা ১০০ জন গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে ২৮ জন উপার্জনক্ষম কোনো কাজে নেই।
উল্লেখ করা যেতে পারে, শিক্ষিত বেকারের হার সবচেয়ে বেশি (৪৭ শতাংশ) যে খানার মাসিক আয় ৬০ হাজার টাকার উপরে, এবং ৩৭ শতাংশ যার মাসিক আয় ৪০-৬০ হাজার টাকা। অবশ্য গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে যারা কাজে রয়েছে তাদের মধ্যে ৪২ শতাংশ বেতনভুক্ত কাজে, ১৬ শতাংশ স্বনিয়োজিত এবং ১৩ শতাংশ খ-কালীন কাজে কিংবা পড়াশোনায় লিপ্ত রয়েছে। অথচ প্রত্যাশার খামতি নেই- ৪৩ শতাংশ চায় পূর্ণকালীন সরকারি চাকরি, ৩৬ শতাংশ থাকায় পূর্ণকালীন ব্যক্তি খাতের কাজ। কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, এমনকি বিদেশে যাওয়ার বাসনা খুব কম গ্র্যাজুয়েটদের।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের একটা বড় অংশ (৩৭ ভাগ) শিক্ষক অথবা সহকারী শিক্ষক হিসে নিয়োজিত, কিছু আছে ছোটখাটো পদে। যেখানে নিয়োগকর্তাদের প্রায় শতভাগ চান আইসিটি ও ইংরেজিতে পারঙ্গম প্রার্থী এবং অনেকের চাহিদা যোগাযোগ, সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম এবং দলগত কাজে পারদর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম গ্র্যাজুয়েট, সেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থাকা কলেজগুলোয় এসব বিষয়ে জ্ঞান দান প্রায় অনুপস্থিত। তাই অনার্স কিংবা মাস্টার্স করে স্কুলের শিক্ষক হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না এবং এসব কলেজের গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে বেকারত্বের হার কেন এত উঁচুতে তাও বোধকরি বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।
চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নরূপ-
১. অধিভুক্ত কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি খুবই কম; প্রতিকূল শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত। ২. শিক্ষকদের জন্য প্রণোদনার অভাব; শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের অভাব। ৩. বক্তৃতা, পরীক্ষা এবং যোগাযোগে বাংলা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যদিও এটি একটি সমস্যা হওয়া উচিত নয়, তবে এটি নিয়োগকর্তাদের প্রত্যাশার সাথে সম্পূর্ণভাবে সই নয়। ৪. শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত, সফট স্কিল এবং সামাজিক-মানসিক দক্ষতা প্রদানের ব্যবস্থার অভাব। ৫. কলেজগুলো অফার করে এমন অনেক বিষয়ের চাকরির বাজারে খুব কম চাহিদা রয়েছে (সাধারণ ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ইত্যাদি তাদের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ)। শিল্পের সাথে সহযোগিতা কার্যত অস্তিত্বহীন। এবং ৬. অন্য সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের অভাব, প্রাক্তন ছাত্র সমিতির অনুপস্থিতি, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং পরিষেবার অনুপস্থিতি ইত্যাদি।
সবচেয়ে বড় কথা, শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, যা অবশ্য অনেক উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। এত কিছুর পরও উত্তরদাতা গ্র্যাজুয়েটদের ৭০-৮০ শতাংশ তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী এবং মনে করে তাদের পিতামাতার চেয়ে অনেক, অনেক ভালো আছে।
পাদটীকা: “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহীদের বলেছিলেন, ‘ধন চাহো তো তাহা হইলে এই পথে আসিও না। মান চাহো তো তাহা হইলে এই পথে আসিও। তিন্তিড়ি বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করত জীবন ধারণ করিতে চাহো, তাহা হইলে এই পথে আসিও।’ তিন্তিড়ি বৃক্ষের অর্থ হলো তেঁতুলগাছ। দার্শনিক ডায়োজেনিস বলেছিলেন, প্লেইন লিভিং—হাই থিংকিংয়ের কথা। একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ইমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন, তার বিষয় ছিল ইসলামিক স্টাডিজ। তিনি ছিলেন ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহর জামাতা। তিনি এক সেমিনারে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, নাপিতের দোকানে যে কয় রকমের ক্ষুর পাওয়া যায়, সে কয়টা বই অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের বাসায় পাওয়া যায় না। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে!” (ড. মাহবুব উল্লাহ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ)
লেখক : অর্থনীতিবিদ, কলামিস্ট। সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়