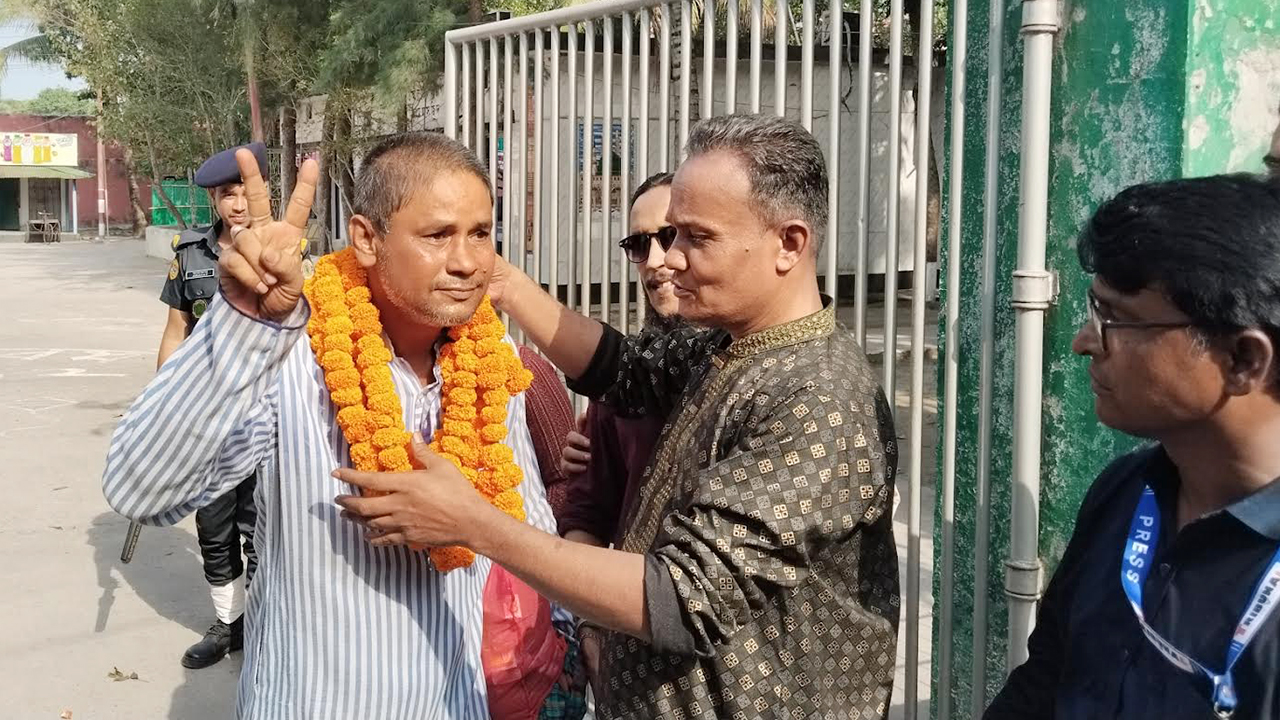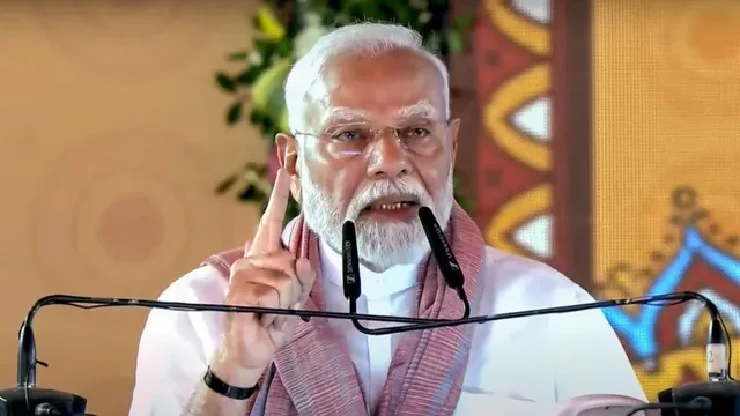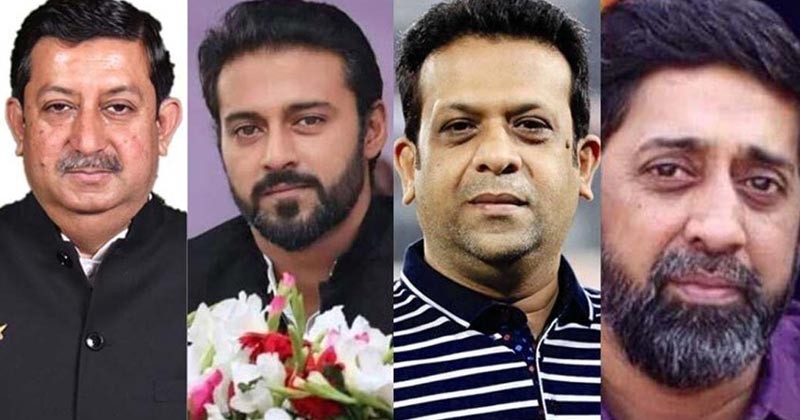ড. হারুন রশীদ :চিরাচরিত প্রবাদের ‘মাছে ভাতে বাঙালি’র মাছ নিয়ে গৌরবের অন্ত নেই। বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে চারশ’ প্রজাতির অধিক মাছ পাওয়া যায়। বলা যায় বাঙালির জীবনযাপন এক রকম মাছকেন্দ্রিক। কিন্তু মাছের দেশে মাছের আকাল চলছে। হারিয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক মাছ। চাষের মাছের অবস্থা আশানুরূপ নয়। মাছ হয়ে পড়ছে স্বাদহীন।
মাছ চাষ করতে হলে তো জল বা জলাশয়ের দরকার। জলই যদি না থাকে তাহলে মাছ থাকবে কোত্থেকে। জলের আধার হচ্ছে নদী-নালা-খাল-বিল। কিন্তু নদী দখল দূষণে হারিয়ে যাওয়ায় প্রাকৃতিকভাবে মাছের উৎপাদন অনেক কমে গেছে। এখন মাছ উৎপাদনে একটি বিপ্লব ঘটলেও তা হয়েছে ‘নিছক বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ’ থেকে। এটা অনেকটা ‘কাজির গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নাই’র মতো। কারণ বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হলেও সেই মাছে বাঙালির রসনা তৃপ্ত হয় না। এছাড়া মাছের উৎপাদন বাড়লেও তাতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা মিটছে না। এজন্য দেশীয় মাছের উৎপাদন বাড়াতে হবে। প্রাকৃতিকভাবেই যেন দেশি মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। মাছে-ভাতে বাঙালিকে প্রাকৃতিক মাছের অমৃতের স্বাদ দিতে হলে নদী-নালা-খাল-বিল বাঁচাতে হবে সবার আগে।
বাংলাদেশের ২০১২ সালের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের রক্ষিত বন্যপ্রাণীর তালিকার তফশিল ১ অনুযায়ী ২৫টি প্রজাতি এবং তফশিল ২ অনুযায়ী ২৭টি প্রজাতির, মোট ৫২ প্রজাতির মাছকে সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ আইন অনুসারে এই ৫২ প্রজাতির মাছ শিকার, বিক্রয় ও বিপণন বাংলাদেশের আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।
বাংলাদেশে স্বাদুপানির মৎস্য প্রজাতিসমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা শুরু হয় ১৮২২ সালে। ২০০৫ সালে একে আতাউর রহমান বাংলাদেশের স্বাদুপানির মাছকে ৫৫টি পরিবারের অধীনে ১৫৪ ধরনের ২৬৫টি প্রজাতিকে তালিকাভুক্ত করেছিলেন যার ভেতরে কয়েক প্রজাতির সামুদ্রিক মাছও ছিল। সর্বশেষ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষের ২৩ নং খণ্ডে ১৭টি বর্গের অধীন ৬১টি পরিবারের ২৫১টি প্রজাতিকে স্বাদুপানির মাছ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
এক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, দেশে ৫৪ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ প্রায় বিলুপ্ত, ২৮ প্রজাতির মাছ চরম বিপন্ন এবং ১৪ প্রজাতির মাছ সংকটাপন্ন অবস্থায়। এর প্রধান কারণ বাংলাদেশ এখন প্রায় খাল-বিল-নদী-নালাশূন্য। খাল-বিল ভরাট করে চলছে নানান স্থাপনা তৈরির মহোৎসব। প্রশ্ন হচ্ছে, খাল-বিল না থাকলে মাছ থাকবে কোত্থেকে? আর যেসব নদী অবশিষ্ট রয়েছে, সেগুলোতে দূষণের মাত্রা এত বেশি যে মাছের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন। বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর অবস্থা আরও নাজুক। হাজারীবাগের ট্যানারি শিল্প সাভারে স্থানান্তরের পর বুড়িগঙ্গার দূষণ আশানুরূপ কমেনি। অন্য নদীগুলোও দূষণ থেকে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক।
পৃথিবীর আশ্চর্যতম এক নদীর নাম হালদা। চট্টগ্রামের ব্যতিক্রমী এই নদীতেই পূর্ণিমা-অমাবস্যার একটি বিশেষ সময়ে মাছ ডিম ছাড়ে। বহু সংখ্যক মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহ হয় এই নদীকে কেন্দ্র করেই। নদীর পানিও ভূউপরিস্থ জলের আধার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শহরে এই নদী থেকেই পানি শোধন করে তা পানের জন্য সরবরাহ করা হয়। অথচ দখল দূষণে এই নদীও মৃতপ্রায়।
হালদা দখল করে হচ্ছে ইটভাটা, বসতবাড়ি। এটা এক আত্মঘাতী প্রবণতা; যেখান থেকে শত শত মণ মাছের ডিম উৎপাদন হয় সেখানে এখন মাছের এক মণ ডিম পাওয়াও দুষ্কর। ফলে মাছের অভাব যেমন দেখা দিচ্ছে, তেমনি নদী তীরবর্তী বহুসংখ্যক মানুষ তাদের জীবিকা হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে।
এটা মনে রাখা দরকার হালদা নদী বাঁচলেই প্রাকৃতিক মাছের বিশাল এক ভান্ডার রক্ষা পাবে। হালদা একটি বিশেষ ধরনের নদী একে রক্ষা করতে হবে যে কোনো মূল্যে। সুন্দরবন যেমন অনন্য, আমাদের দেশকে পৃথিবীর বুকে তুলে ধরবে এর রূপ-রস-গন্ধ দিয়ে। তেমনি হালদাও। একটি সুন্দরবন যেমন সৃষ্টি করা সম্ভব না কৃত্রিমভাবে। তেমনি হালদাও। এই বিশিষ্টতার মূল্য দিতে জানতে হবে।
কৃষিজমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে এই কীটনাশক বৃষ্টির পানি বা সেচের মাধ্যমে বিল, জলাশয়গুলোতে গিয়ে পড়ে এবং মাছের বেঁচে থাকার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানা কারণে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে মাছ। বর্তমানে মৎস্যচাষিরাও এমন প্রজাতির মাছ চাষ করছেন, যেগুলো অতি অল্প সময়ে দ্রুত বর্ধনশীল। বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক শুধু সেইসব মাছ চাষের কারণে এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে দেশি মাছ চাষ করার ব্যাপারে অনীহার কারণেও আমরা হারিয়ে ফেলছি দেশীয় নানা মাছ।
উইকিপিডিয়ার মতে, প্রায় চার শতের অধিক নদী, অসংখ্য খাল, বিল, হাওর, বাঁওড়, ডোবা, নালার বাংলাদেশে পাওয়া যায় নানা রং ও স্বাদের মাছ। আকার আকৃতিতেও এরা যেমন বিচিত্র, নামগুলোও তেমনি নান্দনিক। রুই, কাতল, বোয়াল, শৈল, মৃগেল, বৌরাণী, গুলশা, তপসে, চিতল, কাকিলা, কই, শিং, পাবদা, টেংরা, পুঁটি আরও কত কী!
বাংলাদেশে ২৬০ প্রজাতির স্বাদুপানির (মোহনাজলসহ) এবং ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া ১২-এর অধিক প্রজাতির চাষ করা বিদেশি মাছ চাষের জলাশয়ে এবং ৭০-এর অধিক জাতের বিদেশি বাহারি মাছ অ্যাকুয়ারিয়ামে পাওয়া যায়। আইইউসিএন’র (২০০৩) তথ্যানুসারে বাংলাদেশে স্বাদুপানির ৫৪ প্রজাতির মাছ হুমকির সম্মুখীন। এর মধ্যে ১২ প্রজাতির মাছ ভয়ংকর বিপদাপন্ন এবং ২৮ প্রজাতির মাছ বিপদাপন্ন হিসেবে চিহ্নিত।
মৎস্য অধিদপ্তরের (২০০৯) তথ্যানুসারে বাংলাদেশে জনপ্রতি বাৎসরিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ ১৭ দশমিক ২৩ কেজি, মাছের বাৎসরিক চাহিদা ২৫ দশমিক ৯০ লাখ মেট্রিক টন, জনপ্রতি মাছের বাৎসরিক চাহিদা ১৮ কেজি, প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে অবদান ৫৮ শতাংশ। বাংলাদেশে মাছের মোট উৎপাদন ২৫ লাখ ৬৩ হাজার ২৯৬ মেট্রিক টন। যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত) থেকে আসে ১০,৬০,১৮১ মেট্রিক টন, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত) থেকে আসে ১০,০৫,৫৪২ মেট্রিক টন এবং সমুদ্র থেকে আসে ৪,৯৭,৫৭৩ মেট্রিক টন। তবে দেশীয় অনেক মাছই এখন বিলুপ্তির পথে। এছাড়া প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা, জাটকা নিধনের কারণে রুপালি ইলিশও হুমকির মুখে।
ইলিশ রক্ষার বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা শোনা যায় নানা সময়ে। ইলিশের ব্যবস্থাপনা নিয়ে এর আগে ‘আন্তঃসীমান্ত সংলাপ’ও হয়েছে ভারতের সঙ্গে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে ভারতের সঙ্গে কার্যকর সহযোগিতা ছাড়া ইলিশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সম্ভব নয়। কারণ বাংলাদেশ ও ভারতের বেশকিছু অভিন্ন নদী রয়েছে। পদ্মাসহ বেশকিছু নদী ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে এসেছে। দু-একটি নদীর উজানে বাঁধ দেওয়ায় স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
সাধারণত স্রোতস্বিনী নদীতে ইলিশ বেশি থাকে। আর নদীতে স্রোত তো দূরের কথা, যদি পর্যাপ্ত পানি না থাকে, তবে ইলিশ বাঁচবে কীভাবে? ফারাক্কা বাঁধের কারণে পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রায়শই বন্যা ও নদীভাঙনের ঘটনা ঘটছে। অথচ এ বাঁধের কারণে বাংলাদেশের পদ্মাসহ কয়েকটি নদীর শীর্ণদশা। বর্ষা মৌসুম ছাড়া নদীতে পানি থাকে না। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে ইলিশের উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ শুরু হলে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। সাধারণত বর্ষা মৌসুমে বাজারে ইলিশের ছড়াছড়ি থাকার কথা থাকলেও অনেক সময় সে তুলনায় মাছ পাওয়া যায় না। কেউ কি কখনো ভেবেছিল ইলিশের এমন দুর্দিন আসবে? আর তা হবেই না বা কেন? যে পদ্মা নদী ছিল ইলিশের জন্য বিচরণ ক্ষেত্র, সেই নদীই এখন প্রায় মৃত।
এখানে-ওখানে বড় বড় চর পড়ে একদার প্রমত্তা পদ্মার মৃত্যুপ্রায় ঘনিয়ে এসেছে। শুধু বর্ষাকালের তিন-চার মাস ছাড়া সারা বছর নদীতে পানি থাকে না বললেই চলে। দেশের অন্য নদীগুলোরও একই অবস্থা। তাহলে আমাদের প্রিয় মাছ ইলিশ কোথায় যাবে? কোথায় অবাধে তার বংশবৃদ্ধি হবে? যেখানে ছোট জাটকা সহজেই বেড়ে একটি উপাদেয় ইলিশে পরিণত হবে? আসলে গত প্রায় দুই যুগ ধরে যেন ইলিশের জন্য একটি প্রতিকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে ইলিশ একদিন বিলুপ্ত হতে পারে। এ ব্যাপারে এখনই ইলিশবান্ধব একটি প্রতিবেশ তৈরির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
শুধু মৎস্যসম্পদ বিলুপ্ত হওয়াই নয়, নদী দখল-দূষণের বহুমাত্রিক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে জনজীবনে; বিশেষ করে শিল্প-কারখানার আশপাশ এলাকার কৃষকরা এ নিয়ে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন। শিল্প-কারখানার অপরিশোধিত তরল বিষাক্ত বর্জ্য স্থানীয় খাল-বিলে মিশে পানিদূষণ তো করছেই, ছড়াচ্ছে আবাসিক এলাকায় ও আবাদি জমিতেও। ফলে শুধু নদী-নালার পানিই দূষিত হচ্ছে না, দূষিত পানি আশপাশের মাটিতে মিশে সেখানকার জনজীবনকে করে তুলছে মারাত্মক বিপর্যস্ত।
বিষাক্ত পানির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে আর্সেনিক, পচা জৈব উপাদান, দ্রবীভূত ও অদ্রবীভূত লবণ, সোডা, ক্ষতিকারক ক্রোমিয়াম; যা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এসব পদার্থ আবাদি জমিতে মিশে মারাত্মক দূষণের ফলে ধানের ফলন অর্ধেকে নেমে এসেছে। ফলদ গাছেরও ফলন হ্রাস পেয়েছে। গাছগাছালি জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়েছে। উৎপাদিত ফসলের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে। গবাদিপশুর ঘাস পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজন।
অন্যদিকে নদীদূষণও অব্যাহত আছে। কিন্তু এগুলো দেখার যেন কেউ নেই। নদীদূষণ নিয়ে এত কথা, এত লেখালেখি, পরিবেশ সংগঠনগুলোর আন্দোলন, এমনকি খোদ হাইকোর্টের নির্দেশনা সত্ত্বেও তা বন্ধ হচ্ছে না। ঢাকার পাশে চার নদীর দূষণ বন্ধে এ পর্যন্ত কম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কিন্তু দূষণ অব্যাহত আছে। বুড়িগঙ্গায় যাতে কেউ বর্জ্য ফেলতে না পারে, এ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। বর্জ্য ফেলা রোধে নদীর দু’পাড়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। এছাড়া সিটি করপোরেশনের গাড়ি বা ভ্যানের মাধ্যমে নদীতীরে ময়লা ফেলাও বন্ধ করতে হবে।
নদীদূষণ এখন শুধু নদীর পানিতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, তা আশপাশের জনপদকেও করে তুলছে মারাত্মক দূষিত। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিল্প কারখানার বর্জ্য গিয়ে নদীর পানি দূষণ করছে। দূষিত পানি ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশের আবাসিক এলাকা, আবাদি জমিতে। ফসলি জমি এমনভাবে নষ্ট হয়ে কালো হয়ে গেছে যে তা খালি চোখেই দেখা যায়। এছাড়া মাটি পচে গিয়ে মারাত্মক দুর্গন্ধও ছড়ায় তা। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজনের স্বাস্থ্যঝুঁকি তো রয়েছেই, জমিতে ফসলও ফলছে না। পরিস্থিতি এতাই খারাপ যে এখনই এর একটা বিহিত করা দরকার।
অভিযোগ রয়েছে, নদী ও আবাদি জমি দূষণের সঙ্গে জড়িত অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ অধিদফতরের কোনো ছাড়পত্র নেই। বছরের পর বছর কোনো ইটিপি ছাড়াই তা চলছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাধ্য করতে হবে, যাতে অপরিশোধিত বর্জ্য কোনো অবস্থায়ই তারা ফেলতে না পারে। এজন্য পরিবেশ অধিদফতরকে সক্রিয় হতেই হবে। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান চালাতে হবে।
হারানো নদী পুনরুদ্ধার, নদীর নাব্য বৃদ্ধি, নদীদূষণ রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মৎস্যচাষীদের দেশীয় মাছ চাষের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি। এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে- এটিই দেখতে চায় দেশের মানুষ। লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট
ফৎযধৎঁহ.ঢ়ৎবংং@মসধরষ.পড়স