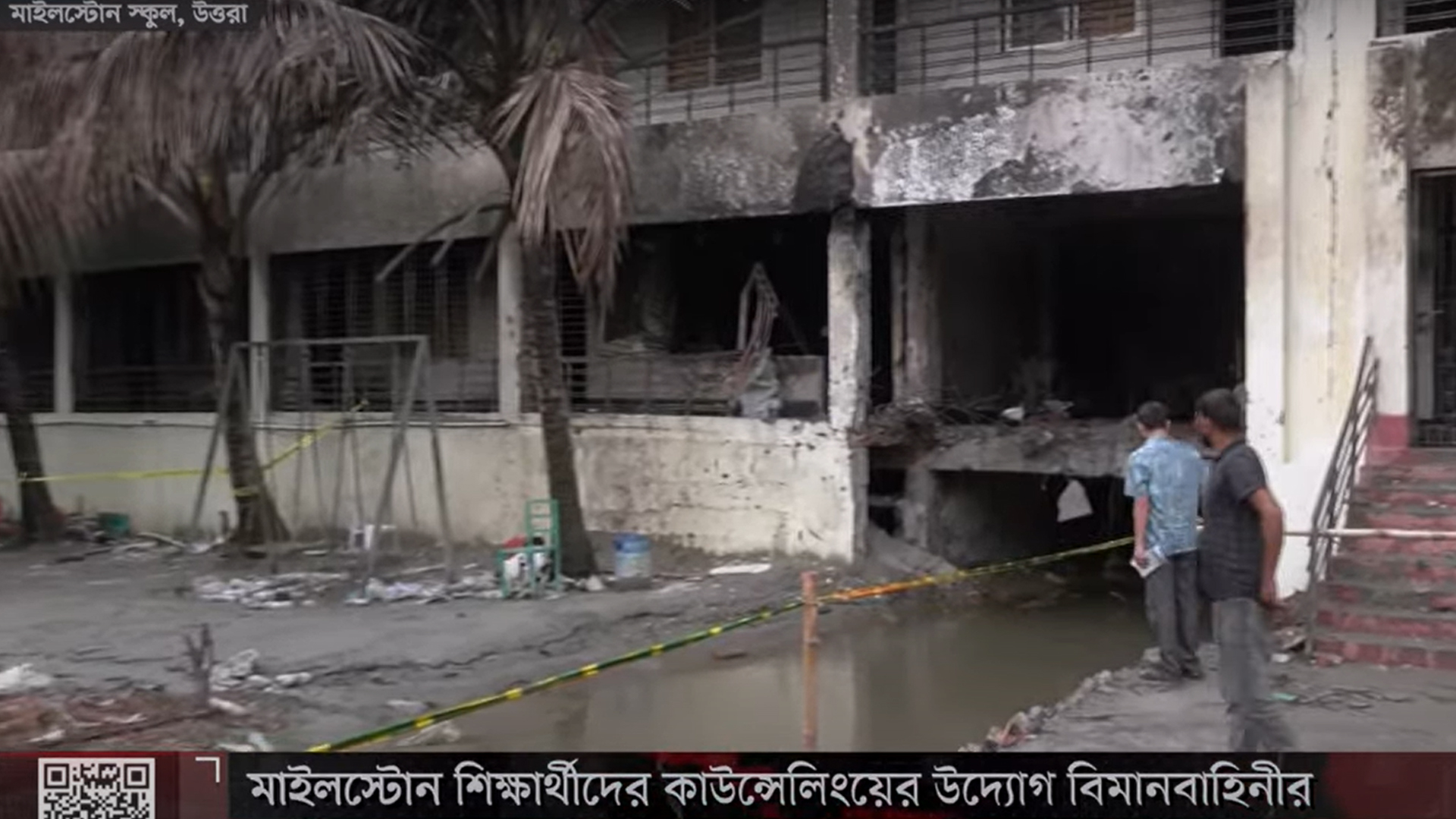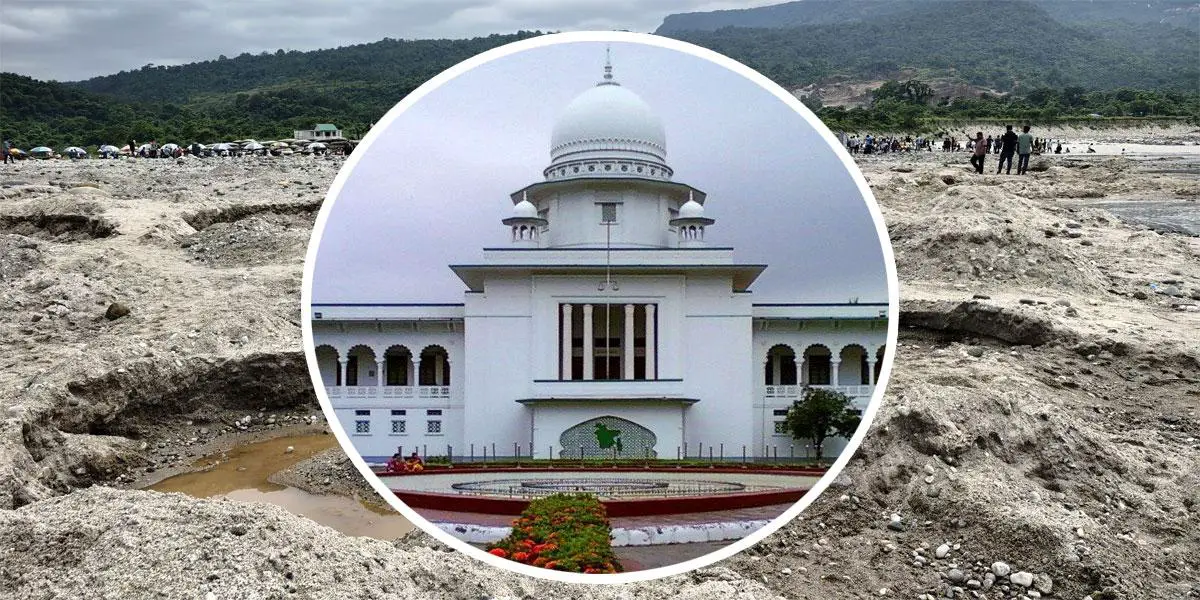ইমতিয়াজ মাহমুদ
সকালের নাস্তায় পান্তা ভাত খাবারটা অতি সুস্বাদু। কেউ কেউ বলেন সেটা নাকি স্বাস্থ্যের জন্যও নানাভাবে উপকারী। স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা আমি নিশ্চিত নই, আমাকে তো ডাক্তার সকাল বেলা ভাত খেতেই নিষেধ করেছেন। তবুও আমি মাঝে মাঝে পান্তাভাত খেতে চাই নিতান্ত স্বাদের কারণে। কিন্তু আজকাল তো পান্তাভাত খাওয়া মুশকিল হয়ে গেছে কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজের দামের ভয়ে।
আজকের বাজারে কাঁচা মরিচের দাম কত? পেঁয়াজ? আমরা তো ছাত্রজীবনে সস্তার হোটেলে খাওয়া দাওয়া করতাম, চাইলেই ওরা একটা প্লেটে করে কাটা পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ দিয়ে যেত। এখনো কি সেইসব রেস্টুরেন্টে সস্তার হোটেলে চাইলেই ফ্রি কাঁচা মরিচ দেয়? পেঁয়াজ কাটা? বাজারে পেঁয়াজ কাঁচা মরিচের যা দাম! কারা নাকি সিন্ডিকেট করে সব শাকসবজির দাম বাড়িয়ে রেখেছে! এই সিন্ডিকেট জিনিসটা কী?
সিন্ডিকেট শব্দটা তো আমরা প্রতিদিন শুনি। টেলিভিশন খুললে আপনি বাজারে দ্রব্যমূল্যের হালচাল নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই একটা রিপোর্ট দেখতে পাবেন। রিপোর্টে দেখা যায় একজন টেলিভিশন রিপোর্টার ঢাকার কারওয়ান বাজারে বা অন্য কোনো বাজারে দাঁড়িয়ে কোন কোন পণ্যের দাম বাড়ল সেটি খুব সবিস্তারে বলে। এরপর কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নেয়Ñ দোকানদার, খুচরা ক্রেতা, বিশেষজ্ঞ ধরনের কেউ এবং কখনো কখনো ভোক্তা অধিকার সংস্থার কর্মকর্তা ধরনের লোকজন। তাদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে অনিবার্যভাবে আসবে এই শব্দটা, ‘সিন্ডিকেট’।
ডিমের দাম, শাকসবজির দাম, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজের দামÑ সবই নাকি সিন্ডিকেট করে মূল্যবৃদ্ধি করছে একদল লোক। সরকারের কর্তাব্যক্তিদের মুখেও আমরা এ কথাটি শুনেছিÑ সাবেক সরকারের প্রধানমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রীদেরও দেখেছি সিন্ডিকেটের কথা বলতে।
একবার তো দেখলাম যে, সিন্ডিকেট ভাঙা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় এইরকম একটা কথা বলার জন্যে বাণিজ্যমন্ত্রীকেও নাকি প্রধানমন্ত্রী বকে দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের সেই সরকার অবশ্য এখন আর নেই কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি মোটেও থামেনি। এখনো নাকি সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্য বিরাজমান, সিন্ডিকেটের কারণে নাকি বাজারে জিনিসপত্রের দাম আগুন হয়ে আছে।
এই সিন্ডিকেট ব্যাপারটা বোঝা দরকার। রাষ্ট্র হিসেবে আমরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির পথ গ্রহণ করেছি। বাজার অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্যের মূল্য নির্ধারণ হওয়ার কথা সরবরাহ ও জোগানের ভারসাম্যে। বাজার অর্থনীতির মৌলিক নিয়ম হচ্ছে যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘমেয়াদে একটি পণ্যের খুচরা মূল্য থাকার কথা সর্বনিম্ন, যেখানে উৎপাদন বা সরবরাহকারীর মুনাফা থাকে একদম ন্যূনতম।
বাস্তবে তো আর পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার সাধারণত মিলে না। ফলে সেই সমীকরণটিও বাস্তবে মেলার কথা না, কার্যত সরবরাহ ও জোগানের ভারসাম্যেই বাজারে জিনিসপত্রের দাম নির্ধারিত হওয়ার কথা। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় যে সরবরাহে কমবেশি না হলেও দাম কমে যাচ্ছে বা বেড়ে যাচ্ছে। বাজারে সরবরাহ না কমলেও যখন দাম বেড়ে যায় সেই এই অবস্থাটি আমরা চট করে মিলাতে পারি না কেন পণ্যের দাম কমে গেল বা বেড়ে গেল, তখন আমরা বলি যে এটা নিশ্চয়ই সিন্ডিকেটের কারসাজি।
বাজারে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের শক্তি বা প্রভাবক হিসেবে সিন্ডিকেট কথাটা অর্থনীতিতে সেইভাবে খুব বেশি ব্যবহৃত কোনো শব্দ না। ইংরেজিতে কারটেল (ঈধৎঃবষ) বলে একটা শব্দ আছে। কারটেল মানে হচ্ছে কোনো একটি পণ্য বা সেবার বাজার কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে গঠিত কয়েকজন সরবরাহকারীর একেকটা গ্রুপ।
কখনো কখনো এমন হয় যে, কোনো পণ্যের উৎপাদক বা সরবরাহকারীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম থাকে, অল্প কয়েকজন এবং সেই অল্প কয়েকজনেরই হাতে থাকে বাজারের সরবরাহের বা জোগানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-এই অবস্থাটাকে অলিগোপলি (ঙষরমড়ঢ়ড়ষু) বলি আমরা। অলিগোপলি বাজারে সরবরাহকারীরা মিলে সেই বিশেষ পণ্যটির দাম নির্ধারণ করতে পারে নিজেদের ইচ্ছামতো।
অনেক সময় লিখিত চুক্তি করে নেয় সরবরাহকারীরা, কখনো সে রকম অনানুষ্ঠানিক কোনো চুক্তি থাকে না। কিন্তু ওই সরবরাহকারীরাই নিয়ন্ত্রণ করে বাজার। এ রকম বন্দোবস্ত হচ্ছে কারটেল। কারটেলটাই আমাদের এখানে সাংবাদিকদের কল্যাণে সিন্ডিকেট নাম পেয়েছে। উদাহরণ হলো, বিশ্বজুড়ে একটা খুব চেনা কারটেল আছে যেটাকে আমরা সবাই চিনিÑ সেটি হচ্ছে ওপেক (ঙচঊঈ)।
আমাদের দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য যেগুলো আছে তার মধ্যে বেশ কয়েকটা আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে সরবরাহকারীরা চাইলেই এইরকম কারটেল বা সিন্ডিকেট করতে পারে। যেমন চিনি-বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান চিনি আমদানি বা উৎপাদন করে ওদের সংখ্যা খুব বেশি না। ওরা চাইলেই চিনির দাম নিজেরা এমনভাবে ঠিক করে নিতে পারে যাতে করে মুনাফার হার একটু বেশি হয়।
একই রকম আরও কিছু পণ্য আছে। যেমনÑ সয়াবিন তেল, আমদানিকৃত খাদ্যশস্য ইত্যাদি। ডিমের ক্ষেত্রেও আমাদের বাজারের অবস্থা ওই রকমই। প্রায় অলিগোপলি, কয়েকটা বড় কোম্পানি ডিম উৎপাদনের মূল অংশ নিয়ন্ত্রণ করে ওদের সাথে কিছু ক্ষুদ্র পোলট্রি ব্যবসায়ীও আছে বটে কিন্তু বাজারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।
আরও কিছু পণ্য আছে; যেগুলোর আমদানিকারকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এইসব সরবরাহকারীরা চাইলেই নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতা করে বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এইরকম কারটেল করার ক্ষেত্রে আইনের বিধিনিষেধ আছে-সেই বিধিনিষেধ আছে প্রতিযোগিতা আইনে। প্রতিযোগিতা কমিশনে যদি আপনি অভিযোগ করেন তাহলে ওরা কারটেল ভাঙার ব্যবস্থা করবে।
একটা কথা মনে রাখবেন, কারটেল বা সিন্ডিকেট যেই নামেই ডাকেন, এদের নিয়ন্ত্রণের জন্য ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত সরকারি সংস্থার আসলে করার কিছু নেই। আইনেই তাদের সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কারণ এগুলো নিয়ন্ত্রণের কাজ হচ্ছে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য যেসব আইন আছে সেসব আইনে। সেইসব আইন ব্যাখ্যা বিচার ও প্রয়োগ করে প্রতিযোগিতা কমিশন।
সরকার চাইলে প্রতিযোগিতা কমিশনকে শক্তিশালী করে, তাদের দক্ষ জনবল দিয়ে এ রকম কারটেল ভাঙার চেষ্টা করতে পারে। কিছু কাজ হয়তো হবে: কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ঐসব কারটেল বা সিন্ডিকেট আপনি ঐভাবে আইন করেও ভাঙতে পারবেন না। সিন্ডিকেট ভাঙতে হলে আপনাকে অলিগোপলি বা মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ভাঙতে হবে। সেটা কীভাবে সম্ভব? সরকার তো চাইলেই একশ লোককে বলতে পারে না যে, আপনারা চিনি আমদানি করেন বা চিনিকল বসান। সরকার যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে নিজেই বাজারে সরবরাহকারী হিসেবে প্রবেশ করতে পারে।
টিসিবির নাম আপনারা সবাই জানেন। টিসিবি এখন সস্তায় পণ্য বিক্রি করে ট্রাকে করে। টিসিবি গঠন করা হয়েছিল স্বাধীনতা পরপর, বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেই। উদ্দেশ্য ছিল যে টিসিবি হবে সরকারের পণ্য বাণিজ্যের কোম্পানি। এরা চাল, ডাল, তেল, লবণ, জামাকাপড় সবকিছু যখন যা দরকার সব আমদানি করবে আর আমদানিকৃত পণ্য বাজারে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করবে।
স্বাধীনতা-পরবর্তী ন্যায্যমূল্যে খুচরা পণ্য বিক্রয়ের জন্য সরকারি মালিকানায় একটা সংস্থা করা হয়েছিল, এর নাম ছিল কসকর (ঈড়ংপড়ৎ)। এখানে যেকোনো ভোক্তা থানকাপড়, গৃহস্থালি জিনিসপত্র এবং নানা ধরনের ভোগ্যপণ্য সরকারের নির্ধারিত দামে কিনতে পারত। কসকর এখন বন্ধ। সেটিই হচ্ছে পথ।
টিসিবি যদি পণ্য আমদানি করে একটা ন্যূনতম মুনাফায় বাজারে বিক্রি করে তাহলে ওইসব সিন্ডিকেটের ক্ষমতা কমে যাওয়ার কথা। বাজারে যতটুকু চাহিদা আছে তার সবটুকু সরকারের সরবরাহ করার দরকার নেই; একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারের হাতে থাকেলই ওদের পক্ষে আর সিন্ডিকেট করা সম্ভব হবে না। তখন চাইলে সরকার আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক কর ইত্যাদি এসবও খুব বেশি হ্রাস করার বা ছাড় দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। এমনিতেই বাজার খানিকটা নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
সরকারি সংস্থাগুলো ব্যবসা-বাণিজ্য করুক এটা আমাদের রাজনীতিবিদরা খুব পছন্দ করেন না। কেন? মুক্ত বাজার অর্থনীতি কথাটাকে কি তারা খুব সিরিয়াস একটা আদর্শ হিসেবে মানেন? না। কোনো আদর্শ বা নীতির প্রশ্ন নয়। ব্যবসায়ীরা রাজনীতিবিদদের টাকা দেয় এবং কখনো কখনো নিজেরাই রাজনীতিতে নেমে যায়। এই রাজনীতিবিদরা হচ্ছে সিন্ডিকেটের রক্ষক। সরকার বাজারে অংশগ্রহণ করুক সেই কাজটা এরা কখনোই হতে দেবে না।
আরেকটা সমস্যা আছে। সরকারি সংস্থার মধ্যে দুর্নীতি থাকে, টিসিবি নিজেই একটা দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান। এরা যে প্রকৃত বাজারমূল্যে জিনিসপত্র কিনতে পারবে সেটা হবে না। যেমন ধরেন টিসিবি যদি একশ টন চিনি আমদানি করতে চায়, ওরা টেন্ডার আহ্বান করবে। ব্রাজিলে যদি চিনির দাম হয় একশ টাকা, টেন্ডারে সেটা টিসিবি কিনবে আরও বেশি দামে। ঐ যে চিনি অলিগার্করা আছে, ওরাই টিসিবির কাছে বিক্রি করবে। তাহলে টিসিবি বাজারে কমদামে কীভাবে বিক্রি করবে? হয়তো দেখা যাবে যে, ব্যবসায়ীরা চিনি বিক্রি করছে খুচরা একশ দশ টাকা করে আর টিসিবির কেনা দামই পড়ছে একশ পনের টাকা। তখন?
এ জন্যই দেশে গণতন্ত্র দরকার। পূর্ণ গণতন্ত্র এবং সর্বত্র গণতন্ত্র। গণতন্ত্র যদি ঠিকমতো কাজ না করে তাহলে সেই সমস্যাও সমাধান করতে হয় অধিক গণতন্ত্র দিয়ে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা থাকে এবং আইনের শাসন থাকে। তখন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে চাইলে খুব বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব হবে না।
পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যতদিন প্রতিষ্ঠিত হবে না, ততদিন আপনি কোনোভাবেই বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। ভোক্তা অধিকার সংস্থা, তথাকথিত বাজার মনিটরিং এইসব দিয়ে মানুষের চোখে ধোঁয়া দিতে আসবে। কিন্তু কারটেল বলেন আর সিন্ডিকেট বলেন, এইগুলো মোটেই বন্ধ হবে না।
লেখক: আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট।
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ