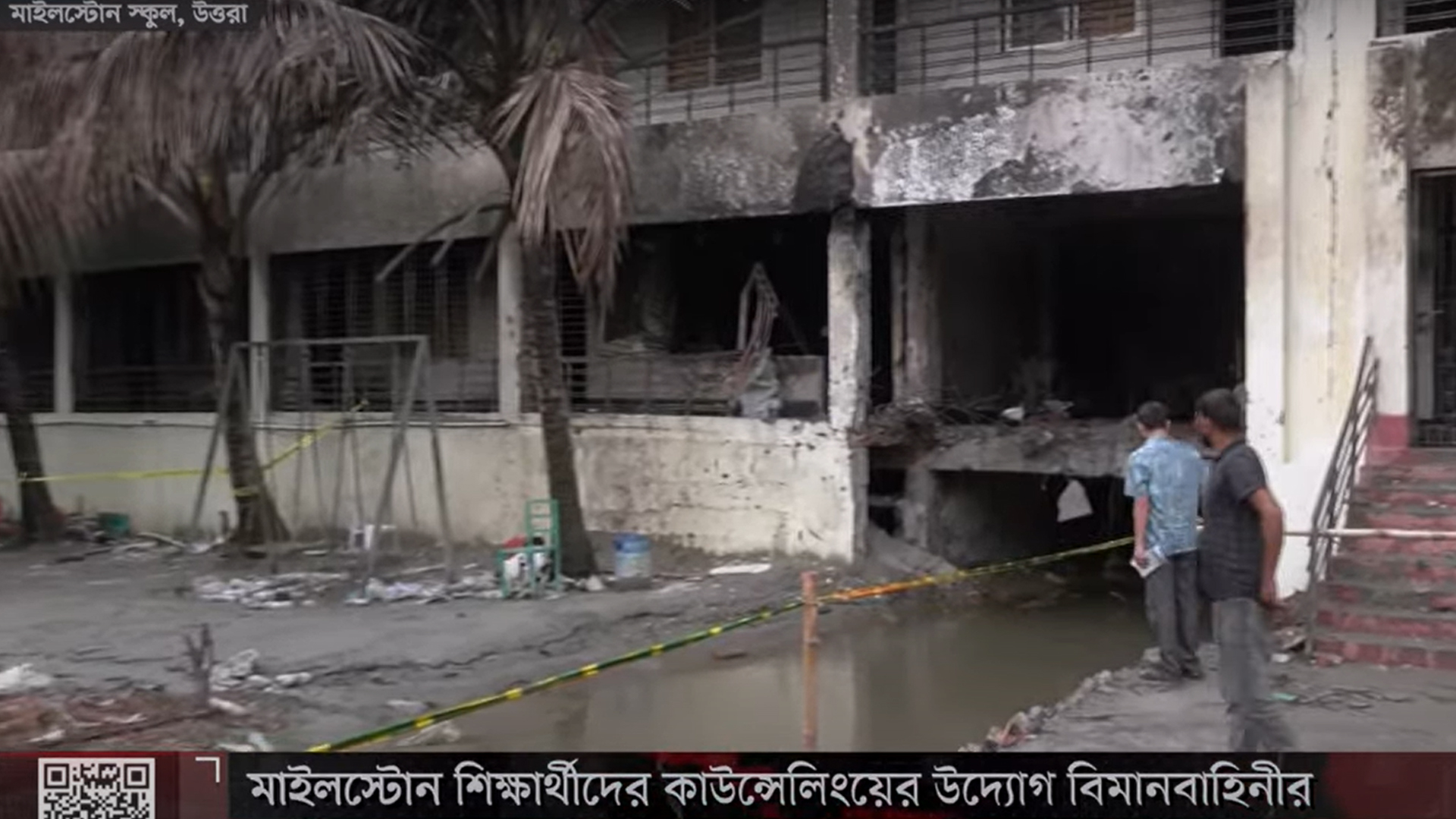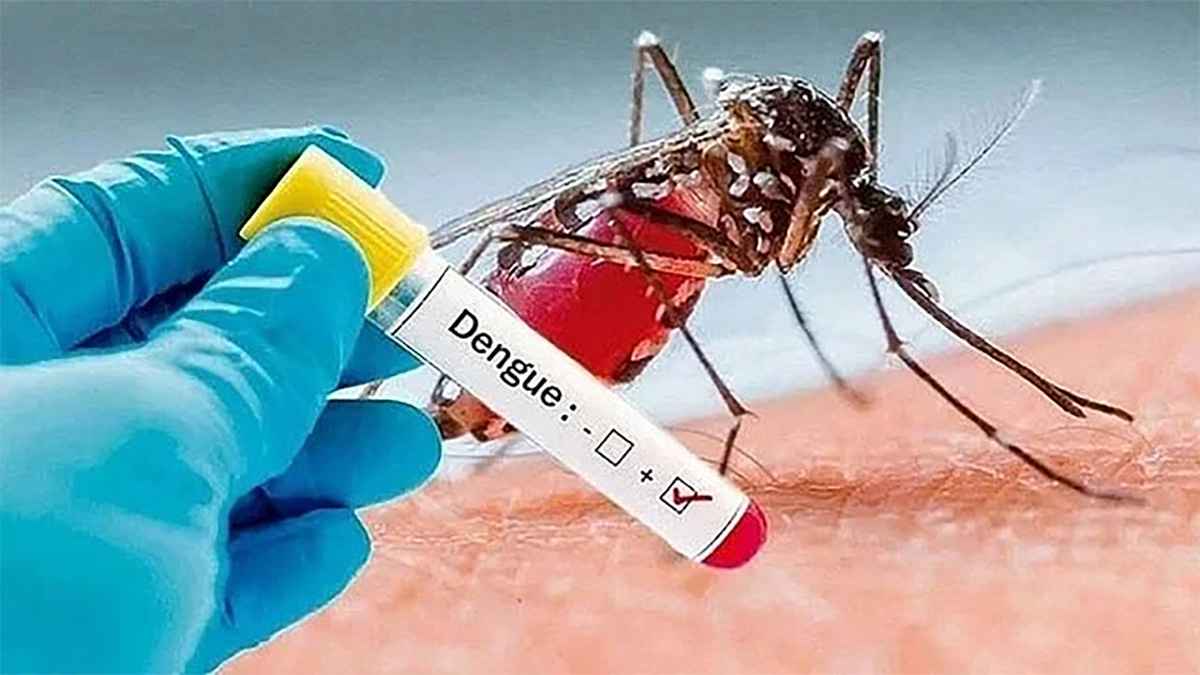সৈকত মল্লিক :৪০ বছর ধরে দেশের অর্থনীতি বিনির্মাণে প্রধানতম ভূমিকা পালনকারী খাত হিসেবে নিশ্চয়ই পোশাকশিল্প বিশেষ মনোযোগ ও গুরুত্বের দাবিদার। সারা বিশ্বের অ্যাপারেল মার্কেটে ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ লেবেলের প্রতাপের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এত বছরের, এত বিশাল এই শিল্প খাতের স্থিতিশীল ক্রমবিকাশের যাত্রাপথ মাঝেমাঝেই বন্ধুর হয়ে ওঠে কেন, প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী, দীর্ঘস্থায়ী সমাধানই বা কোথায়— এগুলো বোধ করি, অতীতের কোনো সরকারই আলোচনার টেবিলে তোলেন নাই; বরং মালিকের স্বার্থকেই প্রাধান্যে রেখে শ্রমিক ও গোটা খাতকে ‘অস্থিতিশীল এবং অনিশ্চিত’ করে রেখেছেন। যে শিল্পখাতের সাথে ৪০ লাখেরও বেশি শ্রমিক এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেড়-দুই কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে যুক্ত, সেই খাতকে স্থিতিশীল রেখে নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন অব্যাহত রাখা- দেশের জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থেই গুরুত্বপূর্ণ। পোশাক শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার স্বার্থে প্রাথমিক কয়েকটা প্রস্তাবনা আলোচনার টেবিলে বা নীতিনির্ধারকদের মনোযোগের জন্য পেশ করতে চাই। নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, ওই চ্যালেঞ্জগুলো ‘সমাধান অযোগ্য’ নয়।
শুধু আশু নয়, দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর স্থিতিশীলতা আনার জন্য সবচেয়ে প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো পোশাকখাতের জন্য একটা ‘জাতীয় তদারকি সংস্থা’ বা ‘নিয়ন্ত্রক সংস্থা’ গঠন করা। এর মাধ্যমে মালিক-শ্রমিকের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য ‘স্টেক হোল্ডার্স’ যারা আছেন তাদের যুক্ত করে গোটা পোশাকশিল্পের উন্নয়নসহ সার্বিক তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন। এই শিল্পের সাথে যুক্ত প্রত্যেকে সেই তদারকি কমিশনের আন্ডারে চলবে, ৪০-৫০ লক্ষ শ্রমিকের জীবন-জীবিকা-ভবিষ্যতকে শুধু মালিক ও মালিকের স্বার্থ রক্ষাকারী সংগঠনগুলোর হাতে ছেড়ে দেওয়া কোনোভাবেই একটা ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক’ সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাক্সক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।
এই ‘সম্মিলিত তদারকি সংস্থা’র প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে সাম্প্রতিক চলমান শ্রমিক অসন্তোষের সময়ে। শ্রমিকদের দাবি ও বাস্তবতা, দাবিনামা পেশ করার প্রক্রিয়া ও দরকষাকষির টেবিল… এসব বিষয় তদারকি করবে কে? বর্তমানে যেমন পোশাকখাতে একটা অস্থির ও অরাজক অবস্থা বিরাজ করছে, কোনো সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সমন্বয় করবে কে? কোন সংস্থা এই খাতের সকল স্টেকহোল্ডারদের একটা কমন গ্রাউন্ডে আনতে পারবে? এই প্রশ্নগুলোর স্থিতিশীল সমাধান জরুরি। তা শুধু মালিকদের সংগঠন বা শুধু শ্রমিকদের ইউনিয়ন বা কেবল সরকার ও সরকারি সংস্থাগুলোর একক কাজ নয়; এটা যৌথ ও ঐক্যবদ্ধ কর্মকাণ্ড। ‘জাতীয় তদারকি সংস্থা’ এই কাজটাই করতে পারে এই খাতের সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রতিনিধিত্বশীলদের সমন্বয়ে।
এখন যেমন সাম্প্রতিক সংকটের আশু সমাধানের জন্য সরকার একটা কমিটি করে সুপারিশ নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে, এর ফলে ‘কমিটি উত্থিত ১৮ দফা দাবি’ মেনে নিয়ে সেগুলো বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছে। এই উদ্যোগ নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু কেবল সংকট সৃষ্টি হলেই ‘টোটকা সমাধান’ হিসেবে ক্ষণস্থায়ী কমিটি নয়; দরকার একটা স্থায়ী কাঠামো, দীর্ঘমেয়াদি সমাধান।
২০২৪ সালে এসেও পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা তাদের বেতন-পাওনা পান ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে; হয় নগদ টাকায়, নয়তো মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। ফলে একজন শ্রমিকের কাছে কারখানার সাথে তার আর্থিক লেনদেনের রেকর্ডস যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকে না, ফলে হিসেব গরমিলের সমূহ আশঙ্কা থাকে এবং সেই গ্যাপ ব্যবহার করেই মালিকপক্ষ শ্রমিককে ঠকানোর সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে।
ধরেন, একজন শ্রমিক যদি কোনো কারখানায় ১০ বছর কাজ করেন; তাহলে তার টোটাল ট্রানজেকশন হিস্টরি ব্যাংকের সার্ভারে সংরক্ষিত থাকবে। তিনি কোন বছরে কোন মাসে চাকরিতে ঢুকেছেন, কত বেতন পেয়েছেন, কত টাকা ইনক্রিমেন্ট হয়েছে, চাকরি সমাপ্তিতে কত টাকা সার্ভিস বেনিফিট পেলেন এবং সেটা আইনের ধারা অনুযায়ী সঠিক কি না… ইত্যাদি কিছু অনায়াসে ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে বের করতে পারবেন।
ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সবধরনের লেনদেন করা বাধ্যতামূলক হলে, তা লিগ্যাল এবং স্বচ্ছ হওয়ার পাশাপাশি আরেকটা খুব বড় কাজ হবে। সেটি- হলো, শ্রমিকদের কষ্টার্জিত উপার্জনে কোনো ‘অযাচিত ভাগ’ বসানোর ঘটনা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পাবে। বাংলাদেশে এই পোশাকশিল্প সেক্টরে শত শত শ্রমিক সংগঠন ‘কাজ’ করে, যেগুলোর বেশিরভাগেরই অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে মালিকের সাথে দেনদরবার করে একটা ‘যেনতেন সমঝোতা’ করে আইনত যা পাওনা তারচেয়ে কম অর্থ শ্রমিককে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং সেই অর্থেরও একটা অংশ শ্রমিকের কাছ থেকে ‘সমঝোতা বাবদ পার্সেন্টেজ’ আদায় করা। কিন্তু ওই পেমেন্টটা যদি ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে করা যায় তাহলে প্রথমত সার্ভিস বেনিফিট বা টার্মিনেশন/রিজাইন বেনেফিট বাবদ শ্রমিকের আইনত পাওনা কত দেওয়া হচ্ছে, তার যেমন হিসেব পাওয়া যাবে; এবং দ্বিতীয়ত সরাসরি অ্যাকাউন্ট-পে হবার কারণে প্রাপ্য পুরো টাকাটাই শ্রমিক পেতে পারবেন। শুধু তাই নয়, পাওনা অর্থের পরিমাণ যদি আইনের ধারা মতে না হয়; তাহলে শ্রমিক প্রমাণসহ পুনরায় দাবিও করতে পারবেন, আইনের আশ্রয়ও নিয়ে পারবেন।
গার্মেন্টস শ্রমিকরা রাস্তায় নামেন প্রধানত তাদের বেতনের দাবিতে, বকেয়া আদায়ের জন্য। তারা রাস্তায় নামেন। কারণ তাদের কথা শোনানোর মতো কোনো জায়গা নেই তাদের কারখানায়। মূলত কারখানায় তাদের কথা শোনেন না কেউ। তাদের দাবি বিষয়ে জানতেও পারে না কেউ। রাস্তায় নামলেই কেবল তাদের দাবির বিষয় সামনে আসে, নচেৎ নয়। শ্রমিকরা যখনই রাস্তা অবরোধ করেন, খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে তাদের বেতন বাকি পড়েছে বা বেতন না দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে মালিক। শ্রমিকরা টাকার জন্যই কারখানায় অমানবিক পরিশ্রম করে, অন্য সবকিছুর আগে তাদের এক নম্বর বিবেচনা হলো নিয়মিত বেতন। প্রতিমাসের বেতন যদি মাসের সাত কর্মদিবসের মধ্যেই পরিশোধ করা হয়, তাহলে ৯০ শতাংশ সমস্যা মিটে যাবে, সন্দেহ নাই।
এটাও ঠিক যে, যে কোনো সময় অনাকাক্সিক্ষত কোনো সমস্যা আসতেই পারে, হোক সেটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো ব্যবসায়িক কারণে। যার দায় কোনোভাবেই শ্রমিকের না এবং শ্রমিক সেই দায়ভার বহনও করতে পারবে না; কারণ খুব সোজা-কোনোমতে বেঁচে থাকার মতো বেতন ছাড়া তাদের অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত সংকটে মালিককেই শ্রমিকের দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে সমাধান সহজÑ প্রত্যেক মালিককে তার সব শ্রমিকের দুই মাসের সমপরিমাণ অর্থ ‘সিকিউরিটি মানি’ হিসেবে সরকারি তদারকি সংস্থার কাছে জমা রাখতে হবে; যাতে সংকটকালীন সময়ে শ্রমিকের বেতন যেন আটকে না যায় এবং কারখানা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলে আবার মালিককে ওই সিকিউরিটি ফান্ড পূরণ করতে হবে। এতে শ্রমিকদের মধ্যে সদাবিরাজমান অনিশ্চয়তা ও বেতন না পাওয়ার শঙ্কা দূর হবে, ফিরে আসবে আস্থা। তাদের আর অন্তত বেতনের দাবিতে রাস্তায় নামতে হবে না, কোনো তথাকথিত শ্রমিক সংগঠনকেও মালিকের সাথে দেনদরবারের প্রয়োজন হবে না। শ্রমিক সংগঠনগুলো তখন সত্যিকারের শ্রমিক স্বার্থের ইউনিয়ন আকারেই কাজ করতে পারবে, ইউনিয়নগুলোর প্রতি শ্রমিকদের আস্থা ফিরে আসবে; আসবে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা।
লেখক: শ্রমিক অধিকার কর্মী
পোশাক শিল্পের দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা: তিনটি প্রস্তাবনা
জনপ্রিয় সংবাদ