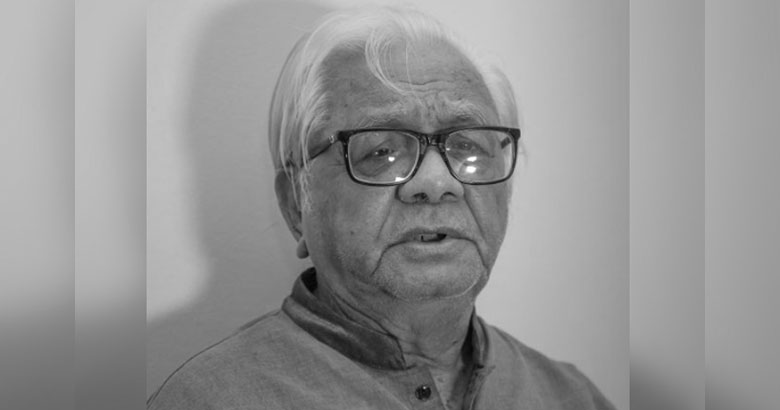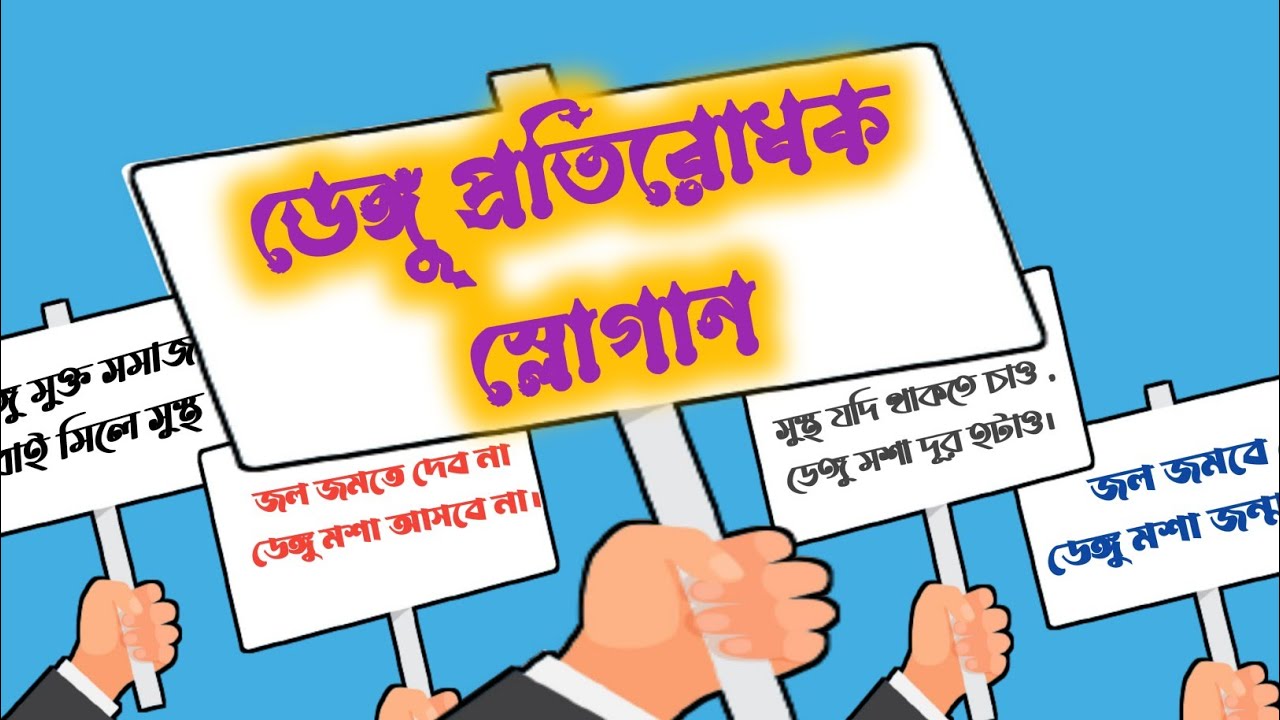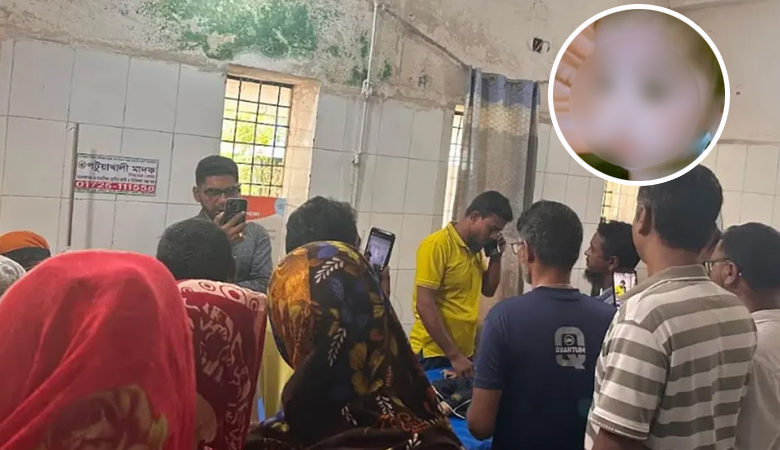ড. হেলাল মহিউদ্দীন : বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে কম আলোচিত বিষয় কী? নেতৃত্ব। অথচ সবচেয়ে বেশি আলোচিত হওয়ার বিষয় কী হওয়া উচিত? নেতৃত্ব। মূলত ‘বিকল্প নেতৃত্ব’। যদি প্রশ্ন করা হয় গণতন্ত্রের বেলায় রাজনীতির মূল প্রতিষ্ঠান কী? উত্তরÑ‘বিকল্প নেতৃত্ব নির্মাণ’। কারণগুলো কী?
প্রথম কারণ প্রাকৃতিক। মানুষ মরণশীল। এমন কোনো গ্যারান্টি ওয়ার্যান্টি কোথাও নেই যে মূল নেতা অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন। এক সেকেন্ড আগেও নেতা কর্মমুখর, এক সেকেন্ডে পর তিনিই ঢলে পড়তে পারেন মৃত্যুর মুখে। দুই, স্বাভাবিক মৃত্যু ছাড়া অপঘাত-মৃত্যুর সম্ভাবনাও কম নয়।
সংগঠনের মনস্তত্ব বিষয়ে গবেষণার কমতি নেই। সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোয় দুইটি বিষয়ের প্রাধান্য দেখা যায়। একটি ‘প্লুরাল লিডারশিপ’, অন্যটি ‘ওয়ান-ম্যান শো’। দুইটির পরিণতি বিপরীত। ‘ওয়ান-ম্যান শো’ এর অনিবার্য পরিণতি বিপর্যয়। সময়ে সময়ে মহাবিপর্যয়।
‘প্লুরাল লিডারশিপ’ এর চূড়ান্ত পরিণতি সুরক্ষা। জার্মান ভাষায় লেখা সিগ্রিদ এন্দ্রে এবং ইয়্যুর্গেন ভিবল্যার-এর ২০১৯ সালের একটি বই সম্প্রতি সাড়া ফেলেছে। স্প্রিংগার প্রকাশনীর এই প্রকাশনাটির বিষয়টি চমকপ্রদ। বক্তব্য স্পষ্ট।
এক, শুধু শিল্প বা ব্যবসায় ব্যবস্থাপনায় তো বটেই, রাষ্ট্র-রাজনীতিতেও বিকল্প ‘নেতৃত্ব নির্মাণ’ একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠতে হয়। তা না হলে গায়ের জোর, টাকার জোর পর্বত সমান হলেও সংগঠন টিকবে না।
দুই, ‘ওয়ান-ম্যান শো’ মানেই কোনো না কোনো এক পর্যায়ে নিশ্চিত বিপর্যয়। এটি নিজেদের জন্য নিজেদের খোঁড়া ফাঁদ। তিন, ‘প্লুরাল লিডারশিপ’ মানেই জায়গায়-জায়গায়, হাটে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে অলিতে গলিতে অতিনেতা পাতিনেতা তৈরি বোঝায় না।
মনে পড়ে ওবায়দুল কাদেরের একটি ভিডিও দেখলাম মঞ্চভর্তি নেতার গাদাগাদি দেখে তিনি বিরক্ত। বলেছিলেনÑ‘এত নেতা! সবাই নেতা! কর্মী কই?’ নেতায় ভরপুর মঞ্চ ভেঙে পড়ার উদাহরণও আছে। যাই হোক, সত্য কথা এই যে স্বাধীনতার বায়ান্ন বছর পরও শীর্ষ নেতারা ‘কাল্ট ক্যারেক্টার’ হয়ে থাকতে চান।
তারা চান তাদের স্তুতি-বন্দনা চলবে অহর্নিশ। হয়ও তাই। তারা আরও চান পরিবার-সদস্যরাই হবেন তাদের সুকর্ম-দুষ্কর্ম সব বিষয়ের উত্তরাধিকার। তারা সুকর্মকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে হাউই (আতশবাজি) বানাবে। দুষ্কর্মকে মিথ্যা বলে, অজুহাত তুলে প্রমাণ করে দেখাবেন দুষ্কর্মগুলো কতটা দরকারি ও উপকারী ছিল।
পরিবার মানে কতগুলো রক্তসম্পর্কের সম্পর্কই তো! সেইখানে ভালো সদস্য, মন্দ সদস্য, অথর্ব সদস্য, বর্জ্য সদস্য, পরিত্যাগযোগ্য সদস্য সবই থাকে। ভাল-মন্দের মিশেল মানুষ। তবু, সবার গায়ে সোনা মুড়ে দেবত্ব আরোপের চেষ্টায় আধুনিক ধাঁচের রাজতন্ত্রের নমুনা যত ভাড়ে, রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের কা-ারি মেলার সম্ভাবনা তত কমে।
বাংলাদেশের বড় দুই দলের কথায় ধরা যাক। একটি দলেও বিকল্প নেতৃত্ব নির্মাণের কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। গরজ-বালাই নেই। আগ্রহের চেয়ে অনাগ্রহই বেশি। পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই মূল উদ্দেশ্য। আওয়ামী লীগে শেখ হাসিনার ‘বিকল্প দেখান’ বক্তৃতা এতটাই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে সবার হাবভাব এটা যেন ছাতি ফোলানো গর্বের কথা। এটা যে আসলে সংকট-সমস্যার নেতিবাচক প্রকাশ এই বোধটিই লুপ্ত হয়ে গেছে।
বিএনপি, জিয়া পরিবারের বাইরে দল রক্ষার বিকল্প নেতৃত্ব হিসেবে কাউকে উঠে আসতে দিয়েছে কি? বুঝলাম, পারিবারিক ঐতিহ্য, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও অন্তরে ধারণ করা আবেগ দলের কর্মীবাহিনীদের ভরসা, নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস জোগায়। কিন্তু কর্মী হলেই সংগঠন চলে না। বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, শিক্ষা, সৌজন্য, কূটনীতিবোধ, আন্তর্জাতিকতাবোধ ইত্যাদি ছাড়াও অনুপ্রাণিত ও উদ্বেলিত করতে জানা শীর্ষ পর্যায়েই বিকল্প নেতৃত্ব দরকার। এই বিষয়ে দুটো ধারণা নিয়ে দুটো কথা বলা দরকার।
ধারণা দুটো শক্তিশালী। দুটোর পাশাপাশি অবস্থান দরকার। সিংহভাগ (ধরা যাক আশি ভাগ) অত্যাবশ্যক ‘রানিং মেইট’ ধারণাটি। নিদেনপক্ষে একজন সহযোগী, বন্ধু, সমমনা, সমভাবে প্রাজ্ঞ দ্বিতীয় নেতা দরকার। তিনি হবেন স্বাধীনচেতা। দাস-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বহীন মোটেই নন। অপর রানিং মেইট ভুল করলে ভুল ধরিয়ে দেবেন। সঠিক পথ দেখাবেন। তিনি উপদেষ্টা থেকে ভিন্ন। শীর্ষ পদাধিকারী তাকে নিয়ে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ভয়ে থাকবেন না। বিকল্প নেতাও নিয়মের বাইরে গিয়ে ছল-চাতুরি-ষড়যন্ত্রের পথ ধরে উচ্চাভিলাষ-খায়েস মেটাবেন না।
বিভিন্ন আসরে আলাপচারিতায় অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেনÑএটা কি সম্ভব? উত্তর অসম্ভব হওয়াই অসম্ভব। অর্থাৎ সম্ভব তো বটেই অপরিহার্যও। সবগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই এটিই সাধারণ চর্চা। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপের দেশগুলো ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া ইউরোপে বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি করা একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাজ।
এশিয়ায় দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, জাপান, সিঙ্গাপুরেও এটিই চর্চিত। বলা বাহুল্য এসব দেশই অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, মৌলিক মানবাধিকারে সেরা, এবং স্থিতিশীল জীবনমানের নিশ্চয়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের চেয়ে অগুয়ান।
বিভিন্ন আসরে এমন প্রশ্নও অনেকের কাছ থেকে এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্রগুলো বা চীন বা উত্তর কোরিয়ায় বিকল্প নেতৃত্ব না থাকায় দেশগুলো কি চলছে না? অবশ্যই চলছে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের মধ্য থেকে একজনও কি সেইসব কর্তৃত্ববাদী, একচ্ছত্রবাদী একনায়কী মডেলগুলো নিজেদের জন্য যথার্থ মনে করেছে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র কি কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠা ছিল? আমাদের সংগ্রাম, গণতন্ত্রের সংগ্রামই যদি হবে, এইরকম প্রশ্নই বা কারও মনে আসে কীভাবে?
দুটি ধারণার প্রথমটি ‘রানিং মেইট’ হলে দ্বিতীয়টি ‘ক্যারিশমা’। ক্যারিশমা বা বিশেষ আকর্ষণী ক্ষমতা নেতৃত্বের অনেক বড় গুণ। ইতিহাসের নানা পর্বে পৃথিবীর নানা দেশেই ক্যারিশম্যাটিক নেতার উত্থান ঘটেছে। জনগণের মন জয় করা এবং তাদের মনে নির্ভরতা ও বিশ্বাসবোধ তৈরি করতে হলে নেতৃত্বকে ক্যারিশম্যাটিক হতে হয়।
বাংলাদেশের রাজনীতির শীর্ষ পর্যায়ে ক্যারিশমা নির্মাণের ক্ষুধাটি অশ্লীল ধরনের। তাই তারা ক্যারিশম্যাটিক না হয়ে কাল্ট চরিত্র হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশের রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার-ব্যানারের মাথায় নেতা-নেত্রীদের আতাফলের মতো গুচ্ছবদ্ধ ছবির অনাবশ্যক বহুল ব্যবহার থেকেই বিকল্প ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বের বদলে কাল্ট নেতৃত্ব নির্মাণের বাস্তবতাটি ফুটে ওঠে।
রাজনীতিতে রানিং মেইট নেতৃত্বের ক্যারিশমা কতটুকু দরকার? বড়জোর কুড়ি ভাগ। অথচ ক্যারিশম্যাটিক দেখিয়ে কোনো নেতৃত্বকে মাথায় তুলে ফেললে শতভাগ পূজনীয় নেতাও একসময় কালের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হন। মালয়েশিয়ার লি ক্যুয়ানসম মাহাথির ইব্রাহিমের কোনো শত্রুও কখনো ভাবেননি, জনগণ একসময় তাকেও রাষ্ট্রপরিচালনার অনুপযুক্ত ভাবতে পারে।
ঠিক এক বছর আগে, ২০২২ সালের ১৯ নভেম্বরে, সাধারণ নির্বাচনে ৫৭ বছরের জ্বলজ্বলে ক্যারিশমার মানুষটি শুধু পরাজিতই হননি, তার জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। মুসোলিনি, ফ্রাংকো, স্ট্যালিনও ক্যারিশম্যাটিক ছিলেন। ক্যারিশমাই টিকে থাকার বা দল রক্ষার শর্ত হলে সাদ্দাম, গাদ্দাফি, হোসনি মুবারক, বেন আলি, চসেস্কু, জুয়ান পেরন, ইভা পেরন এবং অং সান সু চির দলকে জল হয়ে যেতে হতো না। তাদের জীবনের নির্মম পরিণতিময় ঘটনাগুলোও ঘটত না। ম্যাক্স ভেবার ক্যারিশমার দরকার আছে মনে করতেন। তার শিষ্যদ্বয় জর্জ সিমেল ও জর্জ ফিশেল কিন্তু জানালেন বিপ্লবীদের বেলাতেই ক্যারিশমার অপরিহার্য। নেতৃত্বের বেলায় দরকার নেতৃত্বের গুণাবলী ও দায়িত্ববোধÑক্যারিশমা ততটা দরকারি নয়। ক্যারিশমা যে আসলেই সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের বাহন তার প্রমাণ গান্ধী, চে গেভারা, ফিদেল ক্যাস্ত্রো, সুভাষ বসু, ম্যালকম এক্স, মার্টিন লুথার।
জন গ্যাসেলের একটি বহুলপঠিত প্রবন্ধ ‘অ্যা ডেফিনিশন অ্যান্ড ইলাস্ট্রেশন অব ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট’। তার বক্তব্য ‘দায়িত্ব সমবন্টনই গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ’। মূল কথা, বিকল্প নেতৃত্ব নির্মাণই গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ। আমাদের সেইসব নেই।
বাংলাদেশে দ্বাদশ সংশোধনী নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। রাজনৈতিক জল-হাওয়া যতদূর যেদিকে গড়িয়েছে, ভূ-রাজনৈতিক খেলা যেভাবে জমে ওঠেছে, সামনের দিনগুলো ক্ষমতাসীন বা বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দলের জন্যই সুখকর হবে না। ক্ষমতায় কে এলো না এলো, টিকল কি টিকল না এই বিষয়ের চেয়ে বড় বিপদ বড় দুটি রাজনৈতিক দল সুসংহত থাকার বদলে নানারকম বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। বিকল্প নেতৃত্ব না থাকার কারণে গৃহদাহ শুরু নিজ নিজ ঘর হতেই।
লেখক: অধ্যাপক, রাজনীতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়