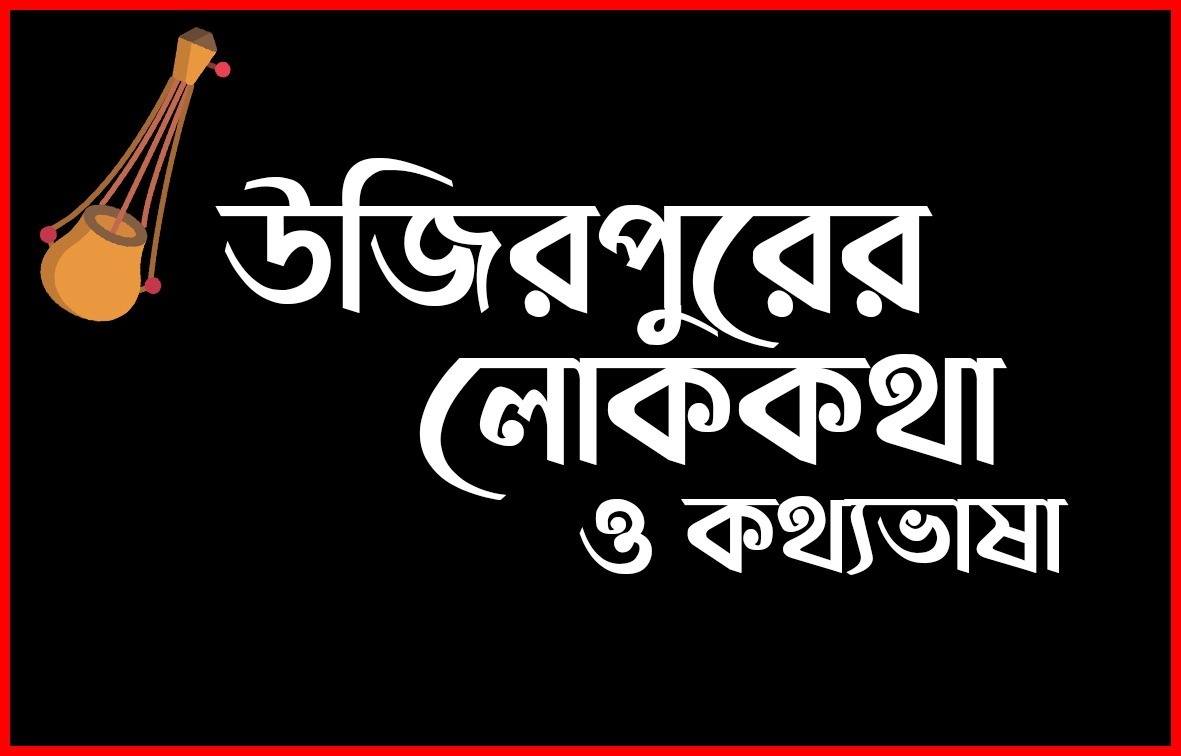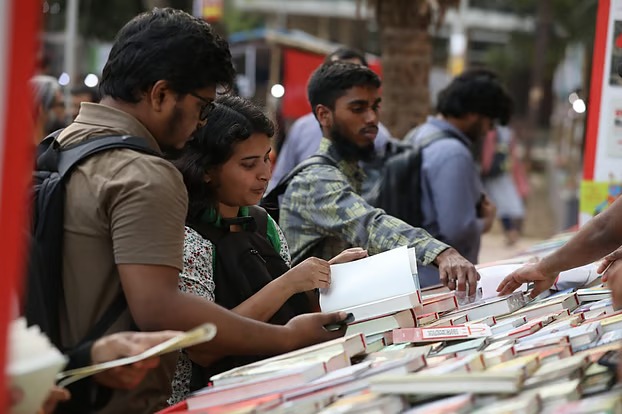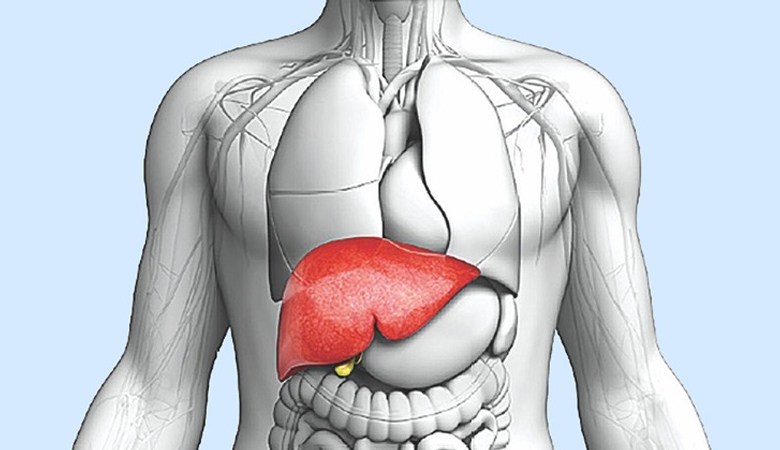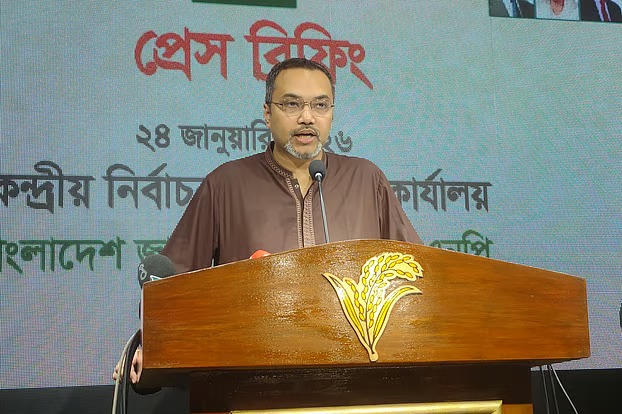মোস্তফা তারিকুল আহসান
হুমায়ূন আহমেদ সম্ভবত বাংলাদেশের প্রথম লেখক; যিনি জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পর সমান চঞ্চলতার সৃষ্টি করেছেন পাঠকের হৃদয়ে। সেই চঞ্চলতার বড় অংশজুড়ে আছে যদিও সৃজনশীলতা তবুও অন্য প্রসঙ্গগুলো কম তাৎপর্য পূর্ণ নয়। জীবিত অবস্থায় তিনি যা ছিলেন মৃত্যুর পরও সেরকম আছেন আপাতত। আরো কিছুকাল পরে হয়তো সে অবস্থার পরিবর্তন হবে। তার যে প্রধান চৌম্বক ব্যাপার ছিল পাঠকপ্রিয়তা বা জনপ্রিয়তা তা এখনো সে রকম আছে বলে অনেকে মনে করেন
হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুকেন্দ্রিক নানা আনুষ্ঠানিকতা ও তার ব্যাপকতা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বাংলাদেশে কোনো লেখককে নিয়ে এত হইচই আগে কখনো হয়নি। যারা হুমায়ূনের ভক্ত তাদের কাছে এটা স্বাভাবিক এবং তারা আনন্দিত ও পুলকিত। বিশেষ করে সপ্তাহব্যাপী যে আলোচনা, মিডিয়ায় যে প্রচার স্মৃতিচারণ-আলোচনা-বন্দনা তাতে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন লেখক হুমায়ূন আহমেদ বিশাল উচ্চতার একজন মানুষ ছিলেন। তার মেয়ে শীলা আহমেদ সিলেটে এক শোকসভায় বলেছিলেন যে, বাবাকে এত মানুষ ভালোবাসে আগে বুঝতে পারিনি, যে বাবাকে আমি কষ্ট দিয়েছি। হুমায়ুন আহমেদকে যারা চিনতেন, সামান্য বা বেশি তারা সবাই তাকে নিয়ে কথা বলেছেন, লিখেছেন। অতিউৎসাহী হয়ে কেউ কেউ তার মৃত্যুকে মেনে নিতে না পেরে আদালতে মামলা পর্যন্ত করেছেন। কোনো কোনো ট্যাবলয়েড জাতীয় পত্রিকা তার মৃত্যুকে হত্যা বলে দাবি করে এর পক্ষে অনেক অসার যুক্তি তুলে ধরেছেন। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের মানুষ বিশেষ করে পাঠক হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হয়েছেন। পাঠক হিসেবে আমার জিজ্ঞাসা হলো এভাবে কি হুমায়ূন আহমেদের মূল্যায়ন সম্ভব? তিনি লেখক, হোক জনপ্রিয় বা অজনপ্রিয় তার মূল্যায়ন হতে হবে অ্যাকাডেমিক জায়গা থেকে। যে-সব আলোচনা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তা তার মূল কাজে লেখালেখিকে পাশ কাটিয়ে গেছে। এভাবে হুমায়ূন আহমেদ সত্যিকার অর্থে আঁধারে থেকে গেছেন। যদিও তাকে নিয়ে মূল্যায়নের দিন শেষ হয়ে যায়নি, হয়ত বড় কাজ ভবিষ্যতে হবে।
বাংলাদেশের লেখক ও সমালোচকদের নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ কি ধারণা পোষণ করতেন তা তিনি খোলাখুলি তেমন কিছু বলেননি। তবে এদের সম্পর্কে তার ধারণা খুব ভালো ছিল না অর্থাৎ তিনি এদের ওপর কিছুটা নাখোশ ছিলেন তা বলা যায়। এই অসন্তুষ্টি থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ আমাদের সমালোচকরা বা অন্য লেখকরা তাকে নিয়ে অনেক বাজে বাজে মন্তব্য করেছেন। হুমায়ূন আহমেদের দুর্বল দিকটাই তারা বরাবরই প্রচার করেছেন উচ্চস্বরে। বিশেষ করে সমসাময়িক বা প্রবীণ লেখকেরা তাকে নিয়ে বেশ কড়া মন্তব্য করেছেন। হুমায়ূনের জনপ্রিয়তা তাদেরকে ঈর্ষান্বিত করত। হুমায়ূন জীবদ্দশায় সেসব শুনেছেন, কষ্ট পেয়েছেন হয়ত তবে খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাননি। তিনি মারা যাবার পর সেই সব লেখকরা তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হুমায়ূনের বন্ধু ও অন্যতম লেখক হুমায়ূন আজাদ একবার বলেছিলেন (আমি স্মরণ থেকে উল্লেখ করছি), হুমায়ূন যা লেখেন একে উপন্যাস বলা যায় না, এ হলো অপন্যাস। সকালে এর জন্ম হয়, আর বিকালে এর মৃত্যু হয়। হুমায়ূন, আমরা যতদূর জানি, এসব খুব গায়ে মাখেননি। তিনি নিজের কাজ করে গেছেন। হুমায়ুন আজাদের জবাবও কখনো দেননি। তবে মাঝে মাঝে তিনি স্যাটায়ারের সুরে দু-একটা জবাব দিয়েছেন। হুমায়ূন নিয়ে একটা অনুষ্ঠানে উপস্থাপক হুমায়ূন আহমেদকে বড় লেখক বলে উল্লেখ করেছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ তার কথা বলার সময় (তিনি বক্তৃতা খুব কমই করতেন) তিনি বলেছিলেন, আমি উপস্থাপকের একটি ভুল সংশোধন করতে চাই, আমি কোনো বড় লেখক নই। কারণ বড় লেখকরা যখন কোনো পুরস্কার পান তখন তারা মুখটি আমসত্ত্ব করে রাখেন, যেন কোথাও কিছু ঘটেনি। আর আমি ছোটখাটো পুরস্কার পেলেও খুব পুলকিত হই। কাজেই আমি বড় লেখক নই।’ ময়মনসিংহ জেলায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমি নিয়ে তিনি বেশ বড় আকারের একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। ‘মধ্যাহ্ন’ নামের এই উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি কিছুটা স্যাটায়ারের সুরে বলেছিলেন, ‘আমার সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা তার নিজের লেখার একটা নাম দিযেছে ’আবজাব’। সে যা-ই লেখে তা-ই নাকি আবজাব। আমি আমার লেখার আলাদা কোনো নাম দিতে পারলে খুশি হতাম। ‘যেমন খুশি তেমন সাজো-এর মতো যেমন খুশি লেখা।’ আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সে রকমই। আমি লিখি নিজের খুশিতে। আমার লেখায় সমাজ, রাজনীতি, কাল, মহান বোধ(!) এই সব অতি প্রয়োজনীয়(?) বিষয়গুলি এসেছে কি আসেনি তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি। ইদানীং মনে হয়-আমার কোনো সমস্যা হয়েছে। হয়তোবা ব্রেনের কোথাও শর্ট সার্কিট হয়েছে। যে কোনো লেখায় হাত দিলেই মনে হয়Ñ চেষ্টা করে দেখি সময়টাকে ধরা যায় কিনা। মধ্যাহ্নেও একই ব্যাপার হয়েছে। ১৯০৫ সনে কাহিনি শুরু করে এগোতে চেষ্টা করেছি। পাঠকরা চমকে উঠবেন না। আমি ইতিহাসের বই লিখছি না। গল্পকার হিসেবে গল্পই লিখছি। তারপরেও…’ তার লেখায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই বা তিনি সিরিয়াস লেখক নন এ ধরনের অভিযোগ প্রায়শ করা হয়। তবে ‘মধ্যাহ্ন’-এর মতো সামাজিক-ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে তিনি আরো উপন্যাস লিখেছেন এবং সেই পটভূমিকে উপন্যাসের রূপ দিয়েছেন ভালোভাবে। দিল্লির সম্রাট হুমায়ূনকে নিয়ে তার লেখা উপন্যাস ‘বাদশাহ নামদার’ কিংবা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিশাল কলেবরে লেখা ‘জোছনা ও জননীর গল্প’-এর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় এবং এখানে হুমায়ূনের সৃজন-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই তিনি সমালোচকের দিকে আঙুল দিয়ে পরিহাসের সুরে মন্তব্যও করতে পারেন।
নিজের লেথা নিয়ে তিনি খোলামেলা মন্তব্য করতেন, মজা করতেন, সরল স্বীকারোক্তি করতেন। এটা তার চরিত্রের একটি অন্যতম লক্ষণ বলা যায়। এবং তার বেশির ভাগ মন্তব্যে মিশে থাকত কৌতুক, স্যাটায়ার। ‘এলেবেলে-১’ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন, (হুবহু উদ্ধৃতি নয়) ‘এই প্রকাশক আমাকে বহুদিন ধরে একটি এলেবেলে ধরনের বই লিখতে বলেছেন। আমি তাকে বলেছিলাম, নতুন করে আর কি এলেবেলে লিখব, আমার সব লেখাই তো এলেবেলে।’ এই মন্তব্যকে সত্যি ভাবার মতো বোকা সমালোচক আছেন কিনা আমাদের জানা নেই তবে হুমায়ূনের এসব কৌতুকপূর্ণ মতামতকে অনেকে বিবেচনায় নিয়েছেন। এটা ঠিক যে তার বহু গল্প উপন্যাসে বেশ অবাস্তব বা অবিশ্বাস্য কিছু বিষয় ও চরিত্র আছে। কিছু কিছু জায়গাতে বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে ধরে নিলেও তিনি যে উদ্দেশে এ সব উপস্থাপন করেছেন তা গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন। বিশেষত বাঙালি পাঠক (উল্লেখ করা প্রয়োাজন নানাবিধ বাধা থাকা সত্ত্বেও হুমায়ূন পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। ‘দেশ’ পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় পর পর আট বছর তার উপন্যাস ছেপেছে; এমনকি হিমু সিরিজের উপন্যাসও ছেপেছে) যখন তার লেখাকে মাথায় তুলে নিয়েছেন তখন ভেবে দেখা প্রয়োজন কেন তিনি নন্দিত এবং কেন তিনি এ জাতীয় রচনা তৈরি করেছিলেন।
আমি নিজে হুমায়ূনের একজন নিবিষ্ট পাঠক। তার বহু গ্রন্থ আমি পড়েছি, তার নাটক-সিনেমা দেখেছি। এক অর্থে আমি তার ভক্ত পাঠক, তবে অন্ধ ভক্ত নই। তার যাবতীয় লেখা ও শিল্পময় কর্মকাণ্ড বিবেচনায় রেখে আমি মনে করি তিনি অসম্ভব প্রতিভাবান একজন সৃজনশীল ব্যক্তি। মানুষ হিসেবেও তিনি অসাধারণ ও বিচিত্র। তার বিচিত্র মানবিক গুণাবলি, রসবোধ, তীক্ষè বুদ্ধি-প্রতিভা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। যদিও আমি ক্লাসিক ধারার লেখা বেশি পছন্দ করি তবে জীবনের যে বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছেন আপাতভাবে তা কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও তা সাহিত্য হিসেবে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ভুবনে অতুলনীয়। তিনি যে বিষয় নিয়ে লিখেছেন তা তার মতো, অন্য কারো রচনার সাথে তার রচনার কোনো সম্পর্ক বা মিল নেই। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও তরুণ শ্রেণিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন ভিন্ন এক কৌশলে। একে কৌশল বলছি এজন্য যে এভাবে না বললে হয়ত তাদের গল্প কেউ শুনতে আগ্রহী হতেন না। আপাতভাবে অসম্ভব এক জীবনের গল্প তিনি অনেক সময় ফ্যান্টাসির মত করে লেখেন। আপাত অসম্ভব মনে হলেও এই সব গল্পতে যে জীবনের ছবি তিনি আঁকেন সহজ সরলভাবে তা এক সময় অনিবার্য জীবন সংকেত নির্দেশ করে। যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা যাই তার উপন্যাসে তা এক সময় ব্যক্তিগত মনে হয়, চরিত্রগুলো চেনা মনে হয়। তাদের কর্মকাণ্ড আমাদের সমগ্র আশা আকাক্সক্ষার প্রতীকী রূপ হিসেবে চিহ্নিত হয়। জীবনের যে সম্ভাবনার কথা তিনি রোমান্স বা ফ্যান্টাসির আদলে বর্ণনা করেন তাতে জীবনের একটি গভীর নিরীক্ষা ধরা পড়ে। সাহিত্য বা শিল্পের একটি মৌল উদ্দেশ্য হলো জীবনের সম্ভাব্যতার নিরীক্ষা করা।
উননব্বই সালের বইমেলায় সম্ভবত হুমায়ূনের ‘নিষাদ’ নামক উপন্যসটি বের হয়। মেলাতে উপন্যাসটি বিশ বারের অধিক রিপ্রিন্ট হয়। আমি তখন কেবল এইচএসসি পাশ দিয়ে ঢাকায় ঘুরে বেড়াই। দেখেছিলাম কি রকম ভিড় সেই বই কেনার জন্য। তারপর প্রতিবার মেলায় গিয়ে একই রকম দৃশ্য দেখেছি। একসময় তো মেলায় তিনি নিষিদ্ধ হলেন অন্য প্রকাশকের অনুরোধে। আমার মনে পড়ে তার একটি উপন্যাসের কথা। আমার ভালোলাগা নিশ্চয় অন্যদের মতো হবে না। তবে তার জনপ্রিয় হয়ে ওঠার বা পাঠকের ভালো লাগার জায়গাটা নিশ্চয় কিছুটা ব্যাখ্যা দেয়া যাবে। উপন্যাসের নাম ছিল ‘সমুদ্র বিলাস’। মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট নিয়ে লেখা। উপস্থাপনে খুব বেশি নতুনত্ব নেই। তবু আমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম সেই উপন্যাস। আমি স্মৃতি থেকে বর্ণনা দিচ্ছি সেজন্য সামান্য ভুল হতে পারে। একজন স্কুল শিক্ষক তার দুই সন্তান আর সুন্দরী স্ত্রীকে (ধনী বাবার মেয়ে) নিয়ে প্রথমবারের মতো বিয়ের দশ বছর পর গেছেন কক্সবাজার বেড়াতে। কক্সবাজার গিয়ে ছেলেমেয়েরা হৈচৈ শুরু করে দিয়েছে। শিক্ষকের স্ত্রীর সঙ্গে তার কলেজ জীবনের এক ধনী বন্ধুর দেখা হয়ে যায় কাকতালীয়ভাবে। বন্ধু ধনী, তার নিজের কাছে গাড়ি আছে। সে পুরোনো বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাল তার সাথে বেড়াতে যেতে। স্বামীকে বললে স্বামী রাজি হলো। শিক্ষক ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিজেদের মতো করে আনন্দ করল। স্ত্রী ফিরল অনেক রাতে। সে ফিরে স্বামীকে অনেক কথা বলল, যা সে কখনো বলেনি বিয়ের দশ বছরের মধ্যে। সে বলল, তুমি একটা কাপুরুষ। আমি তোমাকে, ছেলেমেয়েকে রেখে বন্ধুর সাথে মজা করে এলাম আর তুমি কিছুই বললে না। আমি বলার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি রাজি হয়ে গেলে। তুমি গরীব বলেই, আর বাবার ছাত্র ছিলে বলেই বাবা তোমাকে বাধ্য করেছিল আমাকে বিয়ে করতে। তুমি কখনো কি ভেবে দেখেছ যে আমার সাথে তোমার বিয়ে কেন হলো। আমাদের মতো উচ্চবিত্ত পরিবারের একটা মেয়ের সাথে তোমার মতো নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলের কীভাবে বিয়ে হয়? তুমি আমার আগের জীবন সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানতে না। তুমি কি জান বিয়ের আগে আমার কি হয়েছিল? যার জন্য বাবা তোমাকে ডেকে আমার সাথে বিয়ে দেয়। তুমি কি জানো বিয়ের আগে আমি একটা ছেলের সাথে পালিয়ে গিয়েছিলাম? শিক্ষক তখন বলে, জানতাম। মেয়েটি বলে, জানতে? এটা কী জানতে যে আমি তার সাথে একমাস একটা হোটেলে ছিলাম? শিক্ষক বলে, জানতাম। মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে বলে, এটা কোনো পুরুষ মানুষের পক্ষে সম্ভব? এতকিছু জানার পরেও তুমি গত দশ বছরে আমাকে এসব নিয়ে একটা কথা জিজ্ঞেস করনি, এটা কীভাবে সম্ভব? তুমি কি বাবার আদেশ পালন করেছ কাপুরুষের মতো? তখন শিক্ষক বলে, তুমি আমাকে কাপুরুষ ভাবতে পার। আমার তাতে কোনো আফসোস নেই । তবে সত্য হলো আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে বিয়ে করেছি। তোমার বাবা আমাকে বাধ্য করেননি বরং তোমার সব বিষয় আমকে সবিস্তারে বলেছিলেন। আমার অবস্থা তিনি জানতেন, তোমাদের অবস্থাও আমি জানতাম। জানতাম তোমার আমার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। তবু তোমার বাবা যখন তোমার বিষয়টি আমাকে বলেন, আমি মনে করেছিলাম আমার কিছু করা উচিত। আমি তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিই। তিনি আমাকে বাধ্য করেননি। বলতে পারো অনুরোধ করেছিলেন পরোক্ষভাবে। আর এসব বিষয় নিয়ে বিয়ের পরে আলাপ করা তো নিরর্থক। কারণ এতে তো দুজনের ক্ষতি। তাছাড়া আমি তো সব জেনে শুনেই বিয়ে করেছি। তোমাকে মানসিকভাবে কষ্ট দেবার তো কারণ আমি খুঁজে পাই না। মেয়েটি বলে, আমি জানতাম তুমি কিছুই জানতে না। শেষ পর্যন্ত মেয়েটা শিক্ষককে মহৎ মানুষ হিসেবে ভাবে।
এই নয় যে, গল্পটিতে এক ধরনের উদারতা বা ক্ষমার বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে বলে এটি আমাদের ভালো লাগে বরং এই জন্য ভালো যে একজন শিক্ষিত গরীব স্কুল মাস্টার জীবনকে যে গভীর থেকে দেখেছে, যে পজিটিভ বোধ থেকে দেখে তা অসাধারণ। গল্পটি সাধারণ উদারতার গল্প নয় বেশ পরিচিতও বটে। এরকম ঘটনা এদেশে অহরহ ঘটে তবে হুমায়ূন তার নিজস্ব যুক্তি দর্শন আবেগ ব্যবহার করেছেন। হয়ত মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার কারণে এটা আরো গভীরভাবে পাঠককে স্পর্শ করে। সহজ সরল নিরাভরণ ভাবে তিনি গল্প বলেন তবে জীবনের উত্তাপ আকাক্সক্ষা যন্ত্রণা মোক্ষম মানসিক সামর্থ্য সেখানে থাকে। এটা জীবনের ধনাত্মক দিকের গল্প, পরাজয়ের গল্প নয় সেটা ও একটা বড় ভূমিকা রাখে পাঠককে স্পর্শ করতে। মধ্যবিত্তের সংসারের নানামুখী সংকটকে তিনি উপজীব্য করেন তার রচনায় তবে তার সুর কখনো উচ্চগ্রামে বাজে না। একটা নিস্তরঙ্গ ভাব থাকে সেখানে, কোন তাড়াহুড়ো নেই, নদীর প্রবাহের মতো তার গল্প বিস্তার লাভ করে। এরকম কিছু উপন্যাস তার রয়েছে যা পাঠককে ছুঁয়ে যায় শুধু গল্পের কারণে বা হৃদয়ের গভীর ও আনুভূতিক বোধকে স্পর্শ করার জন্য। এগুলো এক অর্থে তার জনপ্রিয় উপন্যাস নয়। তার প্রথম দিকের উপন্যাস ‘নন্দিত নরকে’ বা ‘আগুনের পরশমণি’ ও সে অর্থে জনপ্রিয় হয়নি। তার জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে শুরু হয় মিসির আলি বিষয়ক উপন্যাস ও হিমু বিষয়ক উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর। এর সাথে অবশ্য আরো কিছু বিষয় অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল।
শিল্পী হুমায়ূনের মানস গঠিত হয়েছে জীবনকে সহজ অথচ তীক্ষèভাবে দেখার ঔৎসুক্য নিয়ে। বাবার চাকরির সুবাদে বাংলাদেশের উত্তর দক্ষিণ পশ্চিমের বহু অঞ্চল তিনি কাটিয়েছেন। মানুষ ও জনপদের বিচিত্র রূপ তিনি অবলোকন করেছেন। মেধাবী ও দুষ্ট প্রকৃতির হুমায়ূন বাবার কাছ থেকে জীবন সম্পর্কে ভাবতে শেখেন। বাবা শিল্পানুরাগী ছিলেন, স্বপ্ন-কল্পনা বিলাসী ছিলেন। বাবা লেখক ছিলেন, তার একটি গল্পের বইও বের হয়েছিল; যদিও তা খুব বেশি প্রচারিত হয়নি বা পাঠকপ্রিয়তা পায়নি। একাত্তরে শহিদ বাবার মহান আত্মত্যাগ ও চেতনা দ্বারা হুমায়ূন প্রভাবিত হয়েছিলেন, বাবা তার চেতনার অন্যতম উৎস ছিলেন। বাবা শহিদ হওয়ার ঘটনা কিংবা যুদ্ধচলাকালীন সময়ে তার ওপর পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতন, পরবর্তীকালে বাবাহীন বড় পরিবার যেভাবে কষ্টে বেড়ে ওঠে এসব হুমায়ূনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। লেখাপড়া সংসার অভাব অনটন এসবের মধ্য দিয়েও লেখক হুমায়ূন নিজেকে তৈরি করে নেন। নেত্রকোনাই তার রচনার মূল ভূগোল হলেও জীবনের নানামুখী ও নানা সময়ের অভিজ্ঞতা তাকে সাহায্য করে। বিচিত্র ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার সমন্বয় দেখা যায় তার রচনায়। যে দৃষ্টি নিয়ে তিনি মানবজীবনকে দেখেছিলেন তা ছিল কৌতূহলে ভরা এবং সদর্থক। বিজ্ঞান, জিজ্ঞাসা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, পুলক বা আনন্দ, বেদনা, কৌতূহল, বিস্ময়বোধ, অসম্ভাব্যতা, কল্পনা, অসংলগ্ন-অবিশ্বাস্য বা অবাস্তব আচরণ, লোকজীবন-বিশ্বাস-আচার এসবকে তিনি নিজের মতো জড়িয়ে নিতে পেরেছিলেন তার শিল্পমানসে। জীবন নিয়ে তিনি ছিলেন অকপট, যা সত্যতা বলতে দ্বিধা করতেন না, প্রচণ্ডসাহসী ছিলেন এবং তার মধ্যে কোনো ভণিতা ছিল না। জীবন সম্পর্কে এক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্ভাবনার কথা তিনি বলতে চাইতেন সব সময়। মানুষকে ভালোবেসেছেন অসম্ভব মমতা দিয়ে, পাগলের মতো। সততা, সরলতা, সৎ চিন্তা ও বিচিত্রভাবনা এক সাথে হলে যে রসায়ন তৈরি হয় তাই তার শিল্পমানস। এমন এক শক্তিশালী শিল্প মানস তিনি তৈরি করতে পেরেছিলেন যে তার চারপাশে আগে পরে প্রায় সব ভালো লেখকদের লেখা পড়লেও কারো দ্বারা প্রভাবিত হননি। বলা যায় রবীন্দ্রনাথকে তিনি ব্যবহার করেছেন তবে তার লেখায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েনি। জীবনানন্দ দাশের কবিতার ভক্ত ছিলেন, তার লেখায় ব্যবহার করেছেন। ‘নন্দিত নরকে’ এর সেই সৎ ভাই মন্টু যে মানুষ খুন করে জেলে গিয়েছিল, যে গোপনে কষ্ট পেত তবে মানসিকভাবে অত্যন্ত সৎ থাকার কারণে এতবড় একটা কাজ সে করতে পেরেছিল। হুমায়ূনের চরিত্ররা বেড়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত সব বাধা পেরিয়ে জীবনের প্রকৃত সিঁড়িতে। অনেকের ধারণা এ্যাবনরমাল সাইকোলজি তার প্রিয় বিষয় এবং সে কারণে তার বেশির চরিত্র এ্যাবনরমাল। এটা বোধ হয় ঠিক নয়। তিনি না-বাচক দৃষ্টি থেকে হ্যাঁ-কে দেখেছেন যেভাবে দেখলে জীবনকে গভীরভাবে বোঝা যায়, পর্যবেক্ষণ করা যায়। জীবনকে সদর্থকভাবে বড় করে তোলার জন্য জাগতিক মোহভঙ্গ করতে পারে তার চরিত্র। একটি উপন্যাসে (ময়ূরাক্ষী) হিমু চরিত্রকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার নাম কি? সে বলে, পুরো নাম হিমালয়, সংক্ষেপে হিমু। প্রশ্নকর্তা আবার বলেন, হিমালয় কারো নাম হতে পারে? আগে পিছে কিছু নেই? হিমু বলে, বাবা চেয়েছিলেন তার ছেলে মহাপুরুষ হবে। তিনি আরো বড় নাম রাখতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত হিমালয় রাখলেন। এই বোধের ভেতরও হুমায়ূনের মানস খুঁজে পাওয়া যায়।
প্রায় চল্লিশ বছরের লেখক জীবনে তিনশ’র বেশি উপন্যাস লিখেছেন। প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। উপন্যাসের সংখ্যাই বেশি। গল্প লিখেছেন বেশ কিছু। সিনেমা নিয়ে একটি গ্রন্থ রয়েছে; রয়েছে কয়েকটি ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থ। নাটক লিখেছেন টিভির জন্য (মঞ্চের জন্য নাটক লেখেননি), নাটক পরিচালনা করেছেন, সিনেমা বানিয়ছেন, কিছু গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, গ্রামবাংলার লোকসংগীতকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন, শেষের দিকে ছবি এঁকেছেন। সব মিলিয়ে বিপুল তার কর্মযজ্ঞ। লেখালেখির বাইরের কাজে ও তিনি ঈর্ষণীয় সফলতা পেয়েছেন। তার উপন্যাসের পাঠক একটি নির্দিষ্ট বলে মনে করা হলেও সব শ্রেণির দর্শক তার নাটক ও সিনেমা দেখেছেন। নন্দিত নরক থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং নিউইয়র্কে অসুস্থ অবস্থায় লেখা (কলাম জাতীয় লেখা) ধরলে তিনি সব সময় জনপ্রিয় ও পাঠক নন্দিত ছিলেন। তিনি কেন পাঠক নন্দিত ছিলেন তা নিয়ে অনেক সমালোচক বিশ্লেষণমূলক মতামত দিয়েছেন। আমার ধারণা, তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। তবে সেটি সব শ্রেণির পাঠকের জন্য নয়। তার পাঠক শ্রেণি অল্প ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাদের বয়স পঁচিশের অধিক হবে না। প্রথম দিকে যে সম্ভাবনা তার লেখায় ছিল শেষের দিকে বা মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে তা প্রায় নিঃশেষ হতে থাকে, তখন তিনি কাঁচা পাঠকের খাদ্য তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি কার্যত পৌনঃপুনিকতার নির্বেদে গা ভাসিয়ে দেন বা টাইপড হয়ে যান বলা যায়। যদিও এসব সত্ত্বেও তার পাঠকপ্রিয়তা কমেনি। তবে যারা পরিণত পাঠক ছিলেন তারা কষ্ট পেয়েছেন। তারা অপেক্ষায় ছিলেন যে আবার তিনি স্বমহিমায় মৌলিক রচনা নিয়ে হাজির হবেন। মাঝেমধ্যে সে চেষ্টাও তিনি করেছেন। ‘মধ্যাহ্ন’ বা ‘জোছনা ও জননীর গল্প’-এর মতো বৃহৎ ক্যানভাস নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। তবে শিল্পের রং চেনার পর যিনি বেপথ হন তিনি আর সত্যিকার অর্থে সে পথে ফিরে আসতে পারেন না সেটা বোধ করি নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ সত্যিকারের ঔপন্যাসিক হওয়ার সমস্ত শক্তি তার ছিল। সে প্রমাণও তিনি দিয়েছেন। তবে পরে তিনি ব্যবসায়ী প্রকাশকের প্ররোচনার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। এক সময় অভাবের জন্য তিনি লিখেছেন, নাটক তৈরি করেছেন। পরে তিনি প্রকাশকের ও পাঠকের বিপুল চাহিদার বস্তুতে পরিণত হলেন। এই জনপ্রিয়তাকে প্রকাশক পুঁজি করে তাকে সত্যিকারের লেখকের সোপান থেকে নামিয়ে ফেলছেন সেটা তিনি হয়ত বুঝতে পারেননি। বুঝলেও হয়ত তার কিছু করার ছিল না। ইমদাদুল হক মিলন আমাদের জানাচ্ছেন আশির দশকেই তিনি সেখান থেকে তিনি আর ফিরতে পারেননি। তবে বাংলাদেশে নতুন পাঠক প্রজন্ম তৈরি করতে ও প্রকাশনা জগতকে শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করাতে তার ভূমিকা একক। যে পাঠক এক সময় আশা, বিমল, শংকর, নীহাররঞ্জন, ফাল্গুনির বই পড়ত পাগলের মতো তারা হুমায়ূন পড়া শুরু করলেন। পশ্চিম বাংলার বইয়ের ব্যবসা এদেশে বন্ধ হয়ে গেল। একটা বিষয় এখানে তাৎপর্যপূর্ণ যে, যে পাঠক পশ্চিম বাংলার সস্তা বই পড়ত, ক্লাসিক বই পড়ত না, তারাই হুমায়ূনকে পছন্দ করল, পশ্চিম বাংলার ক্লাসিক ধারার বই আসা বন্ধ কখনো হয়নি। তবে এর পাঠক উভয় দেশেই সীমিত। বলতে দ্বিধা নেই যে তরল আবেগময় কাহিনি পশ্চিম বাংলার ঔপন্যাসিকেরা লিখতেন হুমায়ূনের লেখা জনপ্রিয় হলেও তাদের লেখার চেয়ে হুমায়ূনের লেখা স্বতন্ত্র।
বাংলাদেশের সমাজ জীবন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সামগ্রিক চরিত্র বিচার করলে হুমায়ূন আহমেদের কৃতিকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। হয়ত সমালোচনা করা যাবে তবে অস্বীকার করা যাবে না। যেসব চরিত্র হুমায়ূন তৈরি করেছেন, যেসব বিষয়ে আলো ফেলেছেন কিংবা যে বিষয়ে গভীর আগ্রহের সাথে কাজ করেছেন, মনোনিবেশ করেছেন; তা অনেকের আগ্রহের বিষয়। স্বভাবতই সে ধরনের মানুষরা তাকে একটু বেশি পছন্দ করেন। গড় পাঠকরা বা দর্শকরা তাকে পছন্দ করেন হয়ত তবে এভাবে তার সৃষ্টিকে মূল্যায়ন করা ঠিক নয়। কারণ সাহিত্য বা যেকোনো ধরনের সৃষ্টি মহৎ হয়ে ওঠে তার নিজস্ব গুণে; কারা তাকে কতটুকু পছন্দ করল বা করল না তার ওপর নির্ভর করে না। আমরা পৃথিবীর বিখ্যাত লেখকদের রচনার দিকে লক্ষ করলে দেখব প্রথম দিকে তাদের লেখা জনপ্রিয় ছিল না কিংবা অন্য কথায় বলা যায় তাদের লেখা পাঠকের গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার জন্য অনেক সময় লেগেছে। আমরা লিও টলস্টয়ের কথা স্মরণ করতে পারি। এর হয়ত দুটো কারণ ব্যাখ্যা দেয়া যায়। প্রথমত লেখাগুলো কাঁচা অথবা পাঠকরা কাঁচা। দ্বিতীয়ত, লেখা উত্তীর্ণ বা ক্লাসিক ধারার তবে পাঠক এত পাকা লেখা পছন্দ করতে সময় নিতে পারে। তবে শেষ ধারার লেখা সত্যি কারের লেখা। হুমায়ূন আহমেদ অনেকটা মধ্যপন্থি। তার বেশির ভাগ লেখা কাঁচা এবং তার পাঠকও অধিকাংশ কাঁচা। তিনি প্রথম দিকে এবং শেষের দিকে কিছু সিরিয়াস লেখা লেখার চেষ্টা করেছেন তবে জনপ্রিয় ধারার উপন্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে তিনি সেটা সঠিকভাবে করতে পারেননি। টিভি নাটক সিনেমা গান রচনা ইত্যাদি মাধ্যমে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন সেসব বিবেচনা করলে তাকে অন্যতম প্রতিভা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। তবে তার যে প্রতিভা তার সঠিক পরিচয় আমরা পাইনি। অর্থাৎ তিনি নিজে তার প্রতিভার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন, এটাই তার রচনারীতি। প্রশ্ন হতে পারে এই সাহিত্য যে হাস্যরস উৎপাদন করেছে, সাহিত্যের মৌল বৈশিষ্ট্যকে প্রায় অস্বীকার করে এক বিশেষ শ্রেণির পাঠকের চাহিদা পূরণ করে যে জনপ্রিয় ধারা তৈরি করেছে তার আয়ু কতদিন?
বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে কাঁচা কলার সাথে তুলনা করেছিলেন। তবে নিজে যা রচনা করেছিলেন তা কাঁচা কলা নয় বরং তা আজও বাঙালি পাঠকের কাছে অন্যতম আরাধ্য। হুমায়ূন আহমেদ হয়তো এসব জানতেন। এবং তিনি হয়ত ক্লাসিক ধারার সাহিত্য রচনা করতে চাননি। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে তিনি জনপ্রিয় ধারায় থেকে গেছেন। যে সব লেখা জনপ্রিয় হওয়ার কথা নয় তাও জনপ্রিয় হয়েছে তার জনপ্রিয়তার প্রবল স্রোতের কারণে বা প্রভাবে। আমরা তার গল্প উপন্যাস নাটক সিনেমা গানসহ নানা প্রকার বিপুল কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে আশ্চর্য না হয়ে পারি না; সহজভাবে জীবনের গল্প রসময় করে বলার যে কৌশল তিনি প্রায় চার দশক ধরে রেখেছিলেন সেটাও রীতিমতো বিস্ময়ের ব্যাপার। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে তিনি রীতিমতো জাদুকর (জাদুকর হওয়া ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য হতে পারে না কোনোভাবে) হয়েছিলেন। আর জাদু যে মানুষকে খানিকটা হতবিহ্বল করে, ভাঁড়ামির জন্ম দেয়, বোকা বানায়, খাঁটি জিনিস না দেখিয়ে ভুল পথে নিয়ে যায় সে তো সবার জানা।
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ