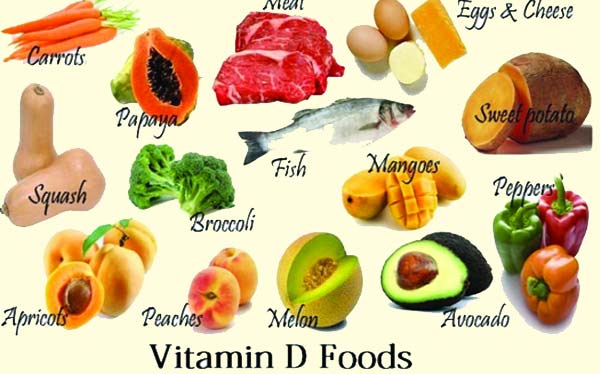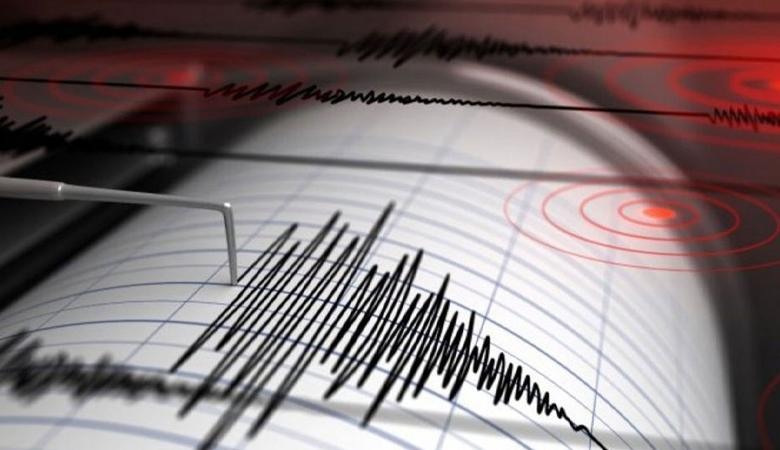- মাহফুজা অনন্যা
কিশোররা জাতির ভবিষ্যৎ। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ যদি বিপথগামী হয়, যদি কিশোর বয়সে তারা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে তবে তা কোনো সমাজের জন্যই শুভ সংবাদ নয়। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই কিশোর অপরাধ একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি শুধু আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন নয় বরং একটি বৃহত্তর মানবিক ও সামাজিক সংকট। কিশোর অপরাধ বলতে ১৮ বছরের নিচে কোনো কিশোর বা কিশোরী যখন সমাজবিরোধী, অবৈধ বা অপরাধমূলক কাজে জড়ায়, তখন তাকে কিশোর অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন: মাদক সেবন ও বিক্রি, ছিনতাই, চুরি, মারামারি, যৌন সহিংসতা, গ্যাং সংশ্লিষ্টতা, ডাকাতি এবং খুন।
বাংলাদেশের বেশ কয়েকমাসের অপরাধবিষয়ক ভিডিও ফুটেজ দেখে মানুষের মনে কিশোর গ্যাং সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, খুন কী করছে না কিছু উঠতি বয়সী কিশোরেরা। এই তো, কয়েকদিন আগে সাভারে একটি মেয়ে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে নিজের বাবাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, সেই খুনের দৃশ্য ভিডিও করে রেখেছে মেয়েটি। এছাড়াও রাজধানীর মোহাম্মাদপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় চুরি, ছিনতাই, খুন হওয়ার দৃশ্য দেখে না কোনো পরিবার শান্তিতে ঘুমাতে পারে, না স্বস্তি পায় আগামীর সম্ভাবনাময় কিশোররা। অনেকের একই প্রশ্ন, কেন এমন হচ্ছে? সন্তানের এমন অবক্ষয়ের জন্য কারা দায়ী?
অভিভাবকদের বিচ্ছিন্নতা, অনুপস্থিতি, সহিংস পরিবেশ বা অতিরিক্ত শাসনের ফলে কিশোরদের মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। কিশোররা সহজেই প্রভাবিত হয়। খারাপ বন্ধুরা, অপরাধে প্রশ্রয় দেওয়া সিনিয়ররা বা আশপাশের অপরাধী চক্র কিশোরদের অপরাধে ঠেলে দেয়। বর্তমানে ‘কিশোর গ্যাং’ নামে পরিচিত কিছু গোষ্ঠী শহরাঞ্চলে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার, অস্ত্র ব্যবহার, এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অনেক কিশোর ভার্চুয়াল গেম, সহিংস ভিডিও, পর্নোগ্রাফি বা অপরাধ উৎসাহিত করে এমন কনটেন্টে আসক্ত হয়ে বাস্তবে তা অনুকরণ করে। দারিদ্র্য, অভিভাবকের কর্মব্যস্ততা বা অবহেলা এবং শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া কিশোরদের অপরাধে জড়ানোর ঝুঁকি বেশি।
একবার অপরাধে জড়ালে কিশোরটির মানসিক ও সামাজিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। সে সমাজে অবজ্ঞার শিকার হয় এবং অপরাধচক্র থেকে বের হতে পারে না। অপরাধী কিশোর পরিবারে কলঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত হয়। পরিবার লজ্জা এবং অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। একটি সমাজে কিশোরদের অপরাধে জড়িয়ে পড়া মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিপন্ন। এটা সমাজে নিরাপত্তাহীনতা, অস্থিরতা এবং অসহনশীলতা তৈরি করে। বাংলাদেশে ‘কিশোর গ্যাং’ নামক শব্দটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাপক আলোচিত। ঢাকার মতো শহরগুলোতে ‘ডন’, ‘টাইটান’, ‘ক্যাসিনো বয়েজ’… ইত্যাদি নামে কিশোর গ্যাং গড়ে উঠেছে। তারা ছুরি, চাপাতি ব্যবহার করে অপরাধে জড়ায়। স্কুল-কলেজের ছাত্ররাও এদের অংশ হয়। প্রশাসনের নজরদারি বাড়লেও এর মূল শিকড় এখনো সমাজে বিদ্যমান।
শিশুদের মানসিক যত্ন, ভালোবাসা ও সময় দেওয়া, কিশোরদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরি। বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা, সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রম, কাউন্সেলিং ও মনোবিদের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কিশোর অপরাধ দমনে কিশোর সংশোধনাগারগুলোর কার্যকারিতা বাড়ানো, পুলিশি হস্তক্ষেপে শিশু-সুলভ আচরণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
গণমাধ্যম, সামাজিক সংগঠন ও নাগরিকদের সম্মিলিত উদ্যোগে কিশোর অপরাধ সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে। অভিভাবকরা যেন সন্তানদের অনলাইন কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন থাকেন ও প্রয়োজনীয় সীমাবদ্ধতা তৈরি করেন। কিশোর অপরাধ কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের একক সমস্যা নয়, এটি একটি সর্বজনীন সামাজিক ব্যাধি। সময় থাকতেই আমাদের সচেতন হতে হবে, কারণ একজন কিশোর যখন অপরাধী হয়ে ওঠে, তখন সে কেবল নিজেকে নয়-সমগ্র সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ, দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতা, যেন কিশোররা অপরাধের নয়-ভালোবাসা, মূল্যবোধ ও স্বপ্নের পথ বেছে নেয়। একজন কিশোর যখন অপরাধের পথে পা বাড়ায় তখন তার পেছনে প্রাথমিক দায়ভার পরিবারের ওপর বর্তায়। কারণ পরিবারের কাছেই শিশুর প্রথম সামাজিকীকরণ ঘটে একজন শিশুর চারিত্রিক গঠন মূল্যবোধ নৈতিকতা সহনশীলতা এবং দায়িত্ববোধ শেখার জায়গা হলো পরিবার।
অভিভাবকরা যদি সন্তানদের পর্যাপ্ত কোয়ালিটি সময় না দেন, তাহলে তারা একাকিত্ব, অবহেলা এবং ভালোবাসার ঘাটতিতে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই শূন্যতা পূরণ করতে গিয়ে অনেক সময় তারা ভুল সঙ্গ বেছে নেয়, যা ক্রমশ অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। তাই সন্তানকে সময় দেওয়া, তাদের সঙ্গে কথা বলা, অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া প্রতিটি পরিবারের তথা বাবা-মায়ের জন্য অত্যন্ত জরুরি। পরিবারের অভ্যন্তরে যদি সহিংসতা, কলহ, অবজ্ঞা ও চিৎকার-চেঁচামেচির পরিবেশ থাকে, তবে তা শিশুর মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শান্তিপূর্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ কিশোরদের সঠিক পথে রাখে। প্রতিদিনের জীবনচর্চায় নৈতিকতা, সততা, দয়া, সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ শেখানো জরুরি। এটি শুধু বই পড়ে হয় না, অভিভাবকদের নিজেদের আচরণ দিয়েও সন্তানদের শেখাতে হয়। অনেক কিশোর তাদের সমস্যার কথা পরিবারের সাথে শেয়ার করতে ভয় পায়, কারণ তাদের কথা কেউ শোনে না বা শাসন করে। কিন্তু যদি বাবা-মা বন্ধুর মতো শোনেন, বোঝেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন, তাহলে কিশোর অপরাধ থেকে তারা অনেক দূরে থাকতে পারে।
বর্তমানে কিশোররা প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন নেতিবাচক কনটেন্টে সহজেই প্রবেশ করে। তাদের মোবাইল, ইন্টারনেট ব্যবহারে নজর রাখা ও কার সঙ্গে মিশছে তা পর্যবেক্ষণ করা অভিভাবকের দায়িত্ব। তবে এই নজরদারি যেন আস্থা ভেঙে ফেলার মতো না হয়-বরং দায়িত্বশীল ভালোবাসা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে হতে হবে। পরিবার যদি দায়িত্বশীল, যত্নবান ও সহানুভূতিশীল হয়, তাহলে কিশোরেরা অপরাধ নয়, আলোকিত জীবনের পথ বেছে নেয়। একজন ভালো মানুষ তৈরির বীজ রোপণ শুরু হয় পরিবার থেকেই।
কিশোর অপরাধ শুধু পরিবার বা ব্যক্তি বিশ্বাসের সমস্যা নয়- এটি এককথায় একটি সামগ্রিক সামাজিক ব্যাধি। একটি শিশু বা কিশোর যখন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তখন সেটি সামাজিক সমাজের মূল্যবোধ কাঠামো এবং সহানুভূতির অভাবকেই ইঙ্গিত করে তাই সমাজের প্রত্যেক সদস্য প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর রয়েছে বড় একটি ভূমিকা। সমাজকে এমন হতে হবে যেখানে কিশোরেরা নিরাপদ বোধ করে, অবজ্ঞা বা অবহেলার শিকার না হয়। প্রতিবেশী, শিক্ষক, দোকানি, সমাজপতি-সবারই দায়িত্ব, তারা যেন কিশোরদের আচরণে নজর রাখেন এবং প্রয়োজন হলে পরামর্শ দেন, ভালো পথে ফিরে আসতে উৎসাহ দেন।
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর উচিত কিশোরদের জন্য খেলাধুলা, নাটক, বিতর্ক, কবিতা, সংগীতসহ নানান গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা। এসবের মাধ্যমে তারা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়, নেতিবাচক পথে যাওয়ার সময় বা আগ্রহ হারায়। মিডিয়ার উচিত কিশোর অপরাধকে গ্লোরিফাই না করে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও দায়িত্বশীল আচরণ জরুরি, যাতে কিশোররা নেতিবাচক আদর্শ বা সহিংসতা না শিখে বরং মূল্যবোধ ও ইতিবাচকতা শেখে।
পুলিশ, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি করপোরেশন, এনজিও ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো কিশোর অপরাধ রোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে কাউন্সেলিং, পুনর্বাসন এবং বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। যেসব কিশোর আর্থিক অনটনের কারণে অপরাধে জড়ায়, তাদের জন্য সমাজভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র কাজের সুযোগ তৈরি করা দরকার। এটা তাদের অপরাধ থেকে দূরে রাখে এবং আত্মসম্মানবোধ বাড়ায়।
একটি দায়িত্বশীল সমাজই পারে একজন বিপথগামী কিশোরকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে। যদি সমাজ কিশোরদের শত্রু না হয়ে বন্ধু হয়-তাহলে অপরাধ নয়, সম্ভাবনা জন্ম নেয়। তাই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অবহেলা করার নয়।
কিশোর অপরাধ দমনে রাষ্ট্রের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক কারণ রাষ্ট্র একটি দেশের আইন শিক্ষা প্রশাসন নীতি ও কল্যাণমূলক কাঠামোর নিয়ন্ত্রক। তাই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে রাষ্ট্রকে সক্রিয় মানবিক এবং সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নিতে হয়। রাষ্ট্রের উচিত কিশোর অপরাধ সংক্রান্ত একটি স্বচ্ছ, আধুনিক ও মানবিক আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকা। শিশু আইন ২০১৩-এর মতো আইনের প্রয়োগ যেন হয় যথাযথভাবে-যেখানে কিশোর অপরাধ যেন সমাজ থেকে চিরতরে নির্মূল হতে পারে। অপরাধীর প্রতি আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে, কিন্তু তা সংশোধনের উদ্দেশ্যে, শুধু শাস্তির জন্য নয়।
বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক সংশোধনাগারেই সুযোগ-সুবিধার অভাব, যা কিশোরদের আরো ক্ষুব্ধ ও অপরাধপ্রবণ করে তোলে। রাষ্ট্রের উচিত সংশোধনাগারগুলোকে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, কাউন্সেলিং, মনোবিদ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সমৃদ্ধ করা, যাতে তারা অপরাধী নয়, একজন নতুন মানুষ হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে।
রাষ্ট্রের উচিত শিক্ষা নীতিতে এমন উপাদান যুক্ত করা, যাতে কিশোরদের মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহানুভূতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ গড়ে ওঠে। স্কুলে নিয়মিত কাউন্সেলিং ব্যবস্থা, মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সহপাঠভিত্তিক কার্যক্রম চালু করতে হবে। বর্তমানে অনেক কিশোর প্রযুক্তির মাধ্যমে সাইবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। রাষ্ট্রকে চাই প্রযুক্তি ব্যবহারে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ‘সাইবার সিকিউরিটি ফর কিডস’ জাতীয় কর্মসূচি, ইন্টারনেট ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ ও সচেতনতা তৈরি করা।
গরিব ও ঝরে পড়া কিশোরদের জন্য টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করতে হবে। এতে তারা আয় করতে শেখে, আত্মনির্ভরশীল হয় এবং অপরাধ থেকে দূরে থাকে। রাষ্ট্রের উচিত গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও এনজিওদের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা। একইসঙ্গে কিশোর অপরাধ বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা চালিয়ে তার ধরন ও প্রতিকার নিয়ে নীতিনির্ধারণ করা জরুরি।
রাষ্ট্র যদি মানবিকতা, সুযোগ এবং সঠিক দিকনির্দেশনার হাত প্রসারিত করে, তবে একজন কিশোর অপরাধী নয়-নতুন সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। তাই কিশোর অপরাধ দমনে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কেবল আইন প্রয়োগে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা একটি সহানুভূতিশীল, কল্যাণমুখী এবং প্রগতিশীল ব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্যে নিহিত।
লেখক: কবি ও কথাসাহিত্যিক।