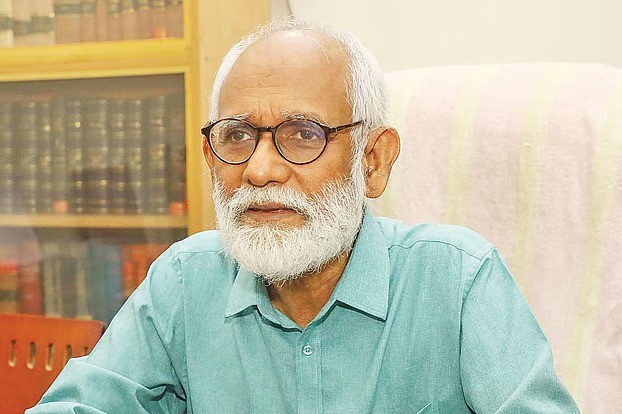মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম : এ লেখাটি যখন লিখছি তখন ফিরে গেছি আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে। আমি তখন ঢাকার শাহবাগে আজিজ সুপার মার্কেটের ওপরে অবস্থিত একটি আবাসিক ফ্ল্যাটে থাকতাম। রুম ভাগাভাগি করতাম এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে। সেখানকার ফ্ল্যাটগুলোতে মূলত এমবিবিএস পাস করার পর উচ্চশিক্ষারত ডাক্তাররই থাকেন। আমি তাদের কাছে একরম ভিন গ্রহের মানুষ। ডাক্তারদের মাঝে ভিনগ্রহী হিসেবে কেন সেখানে থাকতাম সেই প্রশ্নের উত্তর পরে অন্য কোনো প্রসঙ্গে দেবো।
আজ মূল গল্পে আসি। তো সেদিন একটু বেলা করে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার ডাক্তার বন্ধুটির মুখ ভার। সকালে সে (ডাক্তার) বাইরের একটি একটি জেলা থেকে এসেছে। মাসে কয়েকবার সেখানকার হাসপাতালে যায়। কয়েক দিন থাকে। টানা চব্বিশ ঘণ্টা, কখনো আটচল্লিশ ঘণ্টা, কখনো বা তারও বেশি সেখানে কাজ করেন। সেখান থেকে প্রাপ্য যৎসামান্য অর্থ দিয়েই তার মাসের খরচ চলে। শুধু আমার বন্ধুটিই নয়, বরং বেশিরভাগ ডাক্তারই অমানবিক পরিশ্রম করে চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। ডাক্তার হয়ে ওঠেন। তো, একটু ধাতস্থ হয়ে কারণ জানতে চাইলাম, ‘কী হয়েছে।’ বন্ধুটি আমার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন, চিকিৎসাবিদ্যায় তিনি আর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবেন না। ডাক্তারি পেশাতেই আর থাকবেন না। বরং জনস্বাস্থ্যবিদ্যায় ডিগ্রি নিয়ে অন্য পেশা গ্রহণ করবেন। তিনি বলেন, ‘ডাক্তার হওয়ার খায়েশ আমার মিটে গেছে।’ তার এই কথার সুরে আমিও একটু আহত হই। যতটা সম্ভব শান্ত হয়ে আমি জানতে চাই, ‘আসলে কী হয়েছে।’
তারপর তিনি যা জানান তা আমার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। তিনি যে হাসপাতালে কাজ করতেন, সেখানে কোনো এক কর্মীর সঙ্গে এক রোগীর স্বজনের কথা কাটাকাটি হয়। পরে রোগীর স্বজনরা দলবেঁধে হাসপাতালে আসে। হইচই করে। ভুল চিকিৎসার অভিযোগ তুলে হাসপাতাল ভাঙচুর করে। গায়ে হাত তোলে হাসপাতাল কর্মীদের। ডাক্তার ও নার্সরাও বাদ যাইনি। এর মধ্যে আমার বন্ধুটিও ছিলেন। হাসপাতালে সহিংসতার এই চিত্র আজও বদলায়নি। পত্রিকার পাতা উল্টালেই ভুল চিকিৎসা কিংবা অন্য কোনো অভিযোগে রোগীর স্বজন ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক হাসপাতাল ভাঙচুর, ডাক্তার, নার্স ও অন্য সেবাকর্মীদের মারধর, হুমকি-ধমকি, লাঞ্ছনা, নিগ্রহের খবর ভূরি ভূরি।
এই লেখায় সেই সহিংসতার বিভিন্ন মাত্রা অনুসন্ধান করা হয়েছে। খতিয়ে দেখা হয়েছে এর কারণ। খোঁজা হয়েছে এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান।
যাহোক, প্রতিদিন দেশের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে হাজার হাজার রোগী আসে। এসব রোগী নানান কিসিমের হয়ে থাকে। তাদের সবার ক্লিনিক্যাল অবস্থা, আচরণ ও আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা আলাদা। আলোচনা সুবিধায় এসব রোগীকে বিভিন্ন বর্গে ভাগ করা যায়। ক্লিনিক্যাল দিক বিবেচনায় হাসপাতালে আগত রোগী হলো: তীব্র রোগাক্রান্ত রোগী, দীর্ঘস্থায়ী রোগাক্রান্ত রোগী, মৃত্যুপথযাত্রী রোগী, বৃদ্ধ রোগী ও শিশু রোগী। এসব রোগীর শারীরিক অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হয়। তাদের তাৎক্ষণিক শারীরিক ও মানসিক সেবার প্রয়োজন পড়ে। আরেক ধরনের রোগী দীর্ঘ সময় ধরে নির্দিষ্ট কোনো রোগ ভোগেন। এসব রোগীর চিকিৎসা বহুদিন, মাস ও বছর ধরে চলতে থাকে। আর জীবন সংকটাপন্ন রোগীরা জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে থাকেন।
অন্যদিকে বয়স্ক রোগীরা একই সঙ্গে বহুসংখ্যক রোগ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তাদের এক ধরনের সমন্বিত চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। আর শিশু রোগীরা নানান রোগ নিয়ে হাসপাতালে আসে। এক্ষেত্রে তাদের অভিভাবক ও বাবা-মা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকেন। যাহোক, আচরণের দিক থেকে বিচার করলে রোগীর ধরনগুলো হলো আক্রমণাত্মক রোগী, অত্যধিক দাবিকারী বা মনোযোগ প্রত্যাশী রোগী, অনুগত নয় এমন রোগী, উদ্বিগ্ন রোগী ও বিষণ্ন রোগী।
আক্রমণাত্মক রোগীরা তাদের শারীরিক যন্ত্রণা, ভয় ও মানসিক সমস্যার কারণে প্রায়ই সহিংস আচরণ প্রদর্শন করেন। অন্যদিকে অতিরিক্ত দাবিকারী রোগীরা স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের কাছ থেকে বিশেষ চিকিৎসা বা অতিরিক্ত মনোযোগ আশা করেন। আর অনুগত নয় এমন রোগী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসা পরামর্শ ও পরিকল্পনা মেনে চলতে অস্বীকার করে।
অন্যদিকে উদ্বিগ্ন রোগী তাদের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা প্রক্রিয়া সম্পর্কে অতিরিক্ত চিন্তা ও ভয় অনুভব করে এবং তার প্রকাশও ঘটায়। বিষণ্ন রোগীরা উদাস থাকেন, হতাশাবোধ করেন ও জীবন সম্পর্কে আগ্রহ ও প্রেরণা হারিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে অর্থনৈতিক বিবেচনায় সাধারণত দুই ধরনের রোগী হাসপাতালে আসেন। আর তা হলো নিম্ন আয়ের রোগী ও উচ্চ আয়ের রোগী। নিম্ন আয়ের রোগীরা ভালো মানের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ ও ব্যয় বহন করতে সংগ্রাম করেন। আর উচ্চ আয়ের রোগীরা খুব সহজেই উন্নত ও বিশেষায়িত চিকিৎসা নিতে পারেন। এসব রোগী ও তাদের স্বজনরা অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা চান। কারণ তারা মনে করেন যে নিজের যত্নের প্রশ্নে তারাই সবচেয়ে ভালো জানেন। অন্যদিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা মেডিক্যাল গাইডলাইন মেনেই চিকিৎসাসেবা দিতে চান। ফলে রোগীর প্রত্যাশা ও মেডিক্যাল গাইডলাইনের মাঝে এক ধরনের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সেই দ্বন্দ্ব রোগী ও তার স্বজনদের মাঝে এক ধরনের হতাশাবোধের জন্ম দেয়। আর সেই হতাশাই চূড়ান্তরূপে সংঘাত ও সহিংসতার পরিণত হয়। আবার অনেক সময় কোনো কোনো রোগী ডাক্তারের পরামর্শ মতো ওষুধ খাওয়া ও অন্যান্য নিয়ম মেনে চলতে চান না। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবাকর্মী, রোগী ও স্বজনদের মাঝে এক ধরনের ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশ্বাসবোধ ও অহমবোধ কাজ করে। পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধাও হারিয়ে ফেলেন তার। ফলে রোগী ও তার স্বজনরা চিকিৎসা কর্মীদের প্রতি রাগ, ক্ষোভ ও সহিংস আচরণ প্রদর্শন করেন। আবার অনেক সময় রোগীর শারীরিক অবস্থা জটিল হলেও তীব্র ব্যথা অনুভব করলে রোগী ও তার স্বজনরা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যান, কান্নাকাটি শুরু করেন, নিজেরা খুব অসহায়বোধ করেন। এসব ক্ষেত্রে তাদের আবেগের মাত্রা ও প্রকাশ খুব তীব্র হয়। এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসাসেবা দেওয়া জটিল হয়ে পড়ে।
অন্যদিকে কোনো কোনো রোগী ও তার স্বজনরা অত্যধিক অভিযোগপ্রবণ হয়ে থাকেন। হাসপাতালের সেবা ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে প্রতিনিয়তই অভিযোগ জানাতে থাকেন। ফলে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের কর্মপ্রবাহে ব্যাঘাত ঘটে। চূড়ান্তরূপে যা ডাক্তার-নার্স ও অন্যান্য কর্মী এবং রোগীর মাঝে এক ধরনের নেতিবাচক আবহের জন্ম হয়। এছাড়া সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, যোগাযোগ শৈলীর ভিন্নতা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সেবা প্রাপ্তির প্রত্যাশার ভিন্নতাও রোগী ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি ও দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি করে। এই ভুল বোঝাবুঝির কারণে রোগী ও তার স্বজনরা মনে করে যে হাসপাতালে তাদের কথা কেউ শুনছে না; তাদের সমস্যা ও আবেগকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, কিংবা ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। ফলে তাদের মাঝে একরকম হতাশবোধের জন্ম হয়। যা পরবর্তীতে সংঘাত ও সহিংসতার রূপ নেয়।
এবার হাসপাতালে রোগী ও তাদের স্বজনদের সহিংসতার সুলুক সন্ধান করা যাক। হাসপাতালে রোগী ও তার স্বজনদের পক্ষ থেকে সহিংসতার ঘটনাগুলো হলো মৌখিক সহিংসতা, শারীরিক সহিংসতা, মনস্তাত্ত্বিক সহিংসতা ও যৌন সহিংসতা। মৌখিক সহিংসতার মধ্যে রয়েছে হুমকি-ধমকি, অপমান করা, গালিগালাজ করা, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা, চিৎকার চেঁচামেচি করা, হইচই করা ইত্যাদি। হাসপাতালে সহিংসতার কারণগুলো আমরা কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি। রোগীকেন্দ্রিক সহিংসতা, কাজের চাপ থেকে উদ্ভূত সমস্যা, হাসপাতালের কাঠামো ও কর্ম প্রক্রিয়া, সামাজিক অনুঘটক এবং বাহ্যিক অনুঘটক।
রোগীকেন্দ্রিক সহিংসতার উৎস মূলত রোগীর মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা, মাদক গ্রহণ, রোগীর অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, চিকিৎসা পাওয়ার প্রশ্নে রোগীকে অতি দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করা; চিকিৎসা প্রক্রিয়া সম্পর্কে রোগী-রোগীদের স্বজন ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি; হাসপাতালে সেবার মান নিয়ে হতাশাবোধ এবং সেবাকারী আত্মীয়স্বজনের মানসিক চাপ ও যন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত ক্ষোভ।
অন্যদিকে হাসপাতালে অধিক কাজের চাপের কারণে ডাক্তার-নার্স ও অন্যান্য সেবাকর্মী রোগী বা তাদের স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ করেন। ফলে রোগী ও সেবাকর্মীদের মাঝে এক ধরনের সহিংস পরিবেশ তৈরি হয়। আর তাদের সেই রূঢ় আচরণের মূলে থাকে অতি দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অত্যধিক মানসিক চাপ নিয়ে কাজ করা; হাসপাতালের সপ্তাহে সাতদিনই ২৪ ঘণ্টা কর্ম পরিচালনার ধরন; হাসপাতালে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী না থাকা, কর্তৃপক্ষের দিক থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা, সমর্থন ও সুবিধাদি না থাকা এবং নিচু মানের সাংগঠনিক সংস্কৃতি।
অন্যদিকে সামাজিক অনুঘটকের মধ্য রয়েছে সমাজে সামগ্রিকভাবে সহিংসতার মাত্রা বেড়ে যাওয়া; স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মাঝে শ্রদ্ধাবোধ কমে যাওয়া; স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্পর্কে ভুয়া তথ্য, অপতথ্যের বিস্তার এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা সম্পর্কে জনমানসে আস্থাহীনতা, ভয়, সংশয় ও অবিশ্বাস। এছাড়া চিকিৎসাসেবা পেতে অত্যধিক অর্থনৈতিক চাপও এই সহিংসতার অন্যতম কারণ।
গবেষণায় দেখা গেছে, প্রত্যাশা মতো চিকিৎসা ও সেবা না পেলেই কোনো কোনো রোগী ও তার স্বজনরা রাগ করেন, ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং মেজাজ দেখান। এছাড়া স্বাস্থসেবা কর্মীরা রোগীর সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ করতে না পারলে কিংবা রোগীদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ না দিলে সহিংসতার সূত্রপাত হয়। অন্যদিকে রোগীর দেহে ও মনে চরম ব্যথা অনুভব কিংবা অস্বস্তি; শারীরিক অবস্থা কিংবা চিকিৎসা সম্পর্কে প্রবল ও দুশ্চিন্তা থেকেও নানান ধরনের রাগ ও ক্ষোভের প্রকাশ হয়। আবার কোনো কোনো রোগী ও তার স্বজনরা অতিরিক্ত মনোযোগ, তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ও সেবা প্রদান প্রত্যাশা করে। এর মূলে রয়েছে তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান। এই অবস্থানের কারণে তারা মনে করে যে তাদের ইচ্ছে ও চাওয়া মতো যেকোনও চিকিৎসা ও সেবা স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা দিতে বাধ্য। আর এই চাওয়াটা তাদের অধিকার। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবাকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার প্রতি আস্থার ঘাটতি থাকলেও রোগী ও তার স্বজনরা অতিরিক্ত প্রত্যাশী ও দাবিকারী হয়ে ওঠেন। আর প্রত্যাশা মতো চাহিদা না মিটলেই তারা সহিংসতা প্রদর্শন করেন। ক্ষমতার জোর দেখান। আর সেই ক্ষমতার জোরেই বিশেষ চিকিৎসা ও সেবা পাওয়ার প্রত্যাশা করেন। আবার অনেক রোগী ডাক্তার ও নার্সের পরামর্শ মতো ওষুধ খাওয়া, বিধিনিষেধ মেনে চলা কিংবা শারীরিক সক্রিয়তা বজায় রাখেন না। এর মূলে রয়েছে ডাক্তারের সেই পরামর্শ ঠিকমত বুঝতে না পারা; চিকিৎসা সম্পর্কে ভয় ও আশঙ্কা; চিকিৎসা পদ্ধতি ও পরামর্শের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাসের মিল না পাওয়া।
এখন প্রশ্ন হলো হাসপাতালে এই সহিংসতার স্বরূপটা আসলে কী? জবাবে বলা যায়, হাসপাতালে সহিংস ঘটনার প্রভাব বহুমাত্রিক। কোনো রোগী বা তার স্বজন যদি স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের প্রতি সহিংস আচরণ করে তাহলে দ্বিপাক্ষিক রাগ ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে ক্ষুব্ধ কথা চালাচালি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে শারীরিক আঘাতে রূপ নেয়। ফলে হাসপাতালে চিকিৎসা পরিবেশ বিঘ্ন ঘটে। কোনো ডাক্তার, নার্স কিংবা অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবাকর্মী মৌখিক, শারীরিক, মানসিকভাবে লাঞ্ছিত হলে পেশাগত মনোবল ভেঙে পড়ে। যা চূড়ান্তভাবে রোগীর সেবার মানকে প্রভাবিত করে নেতিবাচকভাবে। আবার কোনো রোগী বা তার স্বজন যদি অতিরিক্ত মনোযোগ প্রত্যাশী হয় তাহলে হাসপাতালের কর্মপ্রবাহ ব্যাহত হয়। যার ফল ভোগ করেন অন্যান্য রোগী।
স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের ওপর শারীরিক ও মানসিক চাপ বেড়ে যায়। তাদের মাঝে কাজ করে হতাশা। এর ফলে তারা অনেক সময় অন্যান্য সহকর্মীর সাথে সামান্য বিষয় নিয়ে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। আবার হাসপাতালে সহিংসতার কারণে কোনো রোগী যদি চিকিৎসা পরামর্শ যদি ঠিকমতো মেনে না চলে তার আরোগ্য অত্যন্ত দেরিতে হয়। অন্যান্য শারীরিক জটিলতা বেড়ে যায়। এবং আরোগ্য লাভ করার পরও সমস্যা ও জটিলতা ফিরে আসে।
ডাক্তার-নার্স ও অন্যান্য সেবাকর্মীর প্রতি সহিংসা বাংলাদেশে বর্তমানে দুশ্চিন্তার বিষয়। তবে এসব ঘটনা মনিটর করার জন্য বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট কোনো উপাত্ত ভাণ্ডার বা ডাটাবেজ নেই। বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদন থেকে এই সমস্যার গভীরতা, প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে আঁচ করতে পারা যায়। বিভিন্ন গবেষণার থেকে দেখা যাচ্ছে, ৪০-৫০ শতাংশ স্বাস্থ্যসেবাকর্মী পেশাগত জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন। সাধারণত জরুরি বিভাগ, মানসিক রোগ চিকিৎসা বিভাগ ও ওয়ার্ড, মাদকাসক্তি চিকিৎসাকেন্দ্র, বৃদ্ধ চিকিৎসাকেন্দ্র, নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে এই সহিংসতার ঘটনাগুলো ঘটে। এখন প্রশ্ন হলো হাসপাতালের এসব স্থানেই কেন বেশি সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এই প্রশ্নে উত্তরটি খোঁজা যাক একটু তলিয়ে।
প্রথমত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগী ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মাঝে মনোমানিল্য হয়, কারণ এখানে অত্যধিক রোগীর চাপ থাকে, একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে সেবা পাওয়ার জন্যও অতি দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয় এবং এখানে আগত বেশিরভাগ মানুষই অত্যধিক মানসিক চাপ, অস্থিরতা, ভয় ও আশঙ্কায় থাকেন। অন্যদিকে মনোরোগ চিকিৎসা ওয়ার্ডে চিকিৎসারত রোগীদের মানসিক অবস্থার কারণেই সহিংস আচরণের আশঙ্কা থাকে। আর শারীরিক অবস্থা অতি নাজুক, জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ হলেই রোগীকে নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এখানে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের কাজের চাপ প্রবল। আর রোগীর আত্মীয় স্বজনদের মানসিক অবস্থাও থাকে নেতিবাচক আবেগে পূর্ণ। প্রতিক্ষণে তারা অত্যধিক ভয় ও আশঙ্কায় থাকেন। ভর করে মানসিক চাপ।
সহিংসতার শিকার হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের ওপর বহুমাত্রিক প্রভাব পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়ে থাকেন। কখনো কখনো পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার ও বিষণ্নতায় ভোগেন। কখনো আবার আত্মপীড়ন ও কাজে অসন্তুষ্টিতে ভোগেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে চিকিৎসাসেবা পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো পেশা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে সহিংসতার প্রভাব পড়ে রোগীর ওপরও। তাদের চিকিৎসার গুণগত মান কমে যাওয়া; চিকিৎসাসেবায় রোগীর সন্তুষ্টির মাত্রা কমে যাওয়া; চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় ভুলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া; এবং রোগীকে সেবা দিতে ইচ্ছাকৃত দেরি করার মতো ঘটনা ঘটে। এছাড়া সহিংসতার প্রভাব হাসপাতালের ওপরও পড়ে বিভিন্নভাবে। যেমন, কোনো হাসপাতালে সহিংসতার ঘটনা ঘটলে ডাক্তার-নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মাঝে চাকরি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। বাড়ে অসুস্থতাজনিত ছুটি নেওয়ার মাত্রা; মামলা মোকদ্দমায় খরচের মাত্রা বাড়ে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় হাসপাতালের ইমেজে, ভাবমূর্তিতে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হাসপাতালে সহিংসতার বিষয়টি মোকাবিলা করার প্রশ্নে বহুমাত্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এসব পদক্ষেপে বিভিন্ন স্তরে তথা পর্যায়ে হতে হবে। আর সেই পর্যায়গুলো হলো, নীতিনির্ধারণী পর্যায়, হাসপাতালের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়, ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের ব্যক্তিগত পর্যায়। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তা হলো: হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের আইনি সুরক্ষা বাড়ানো ও নিশ্চিত করা; হাসপাতালে যেকোনও সহিংসতার ঘটনা নথিবদ্ধ করা বাধ্যমূলক করা; দেশের সব হাসপাতালে সহিংসতা প্রতিরোধে একটি সমন্বিত প্রোটোকল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
অন্যদিকে হাসপাতালগুলো নকশা ও সজ্জায় এমনভাবে করা উচিত, যাতে সেখানে রোগী, রোগীর স্বজন ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মানসিক উত্তেজনা, অস্থিরতা ও সামান্যতেই রেগে যাওয়ার প্রবণতা কমে। স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো। আক্রান্ত কর্মীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা বাড়ানো। হাসপাতালে কর্মরত সব কর্মীর জন্য রোগী ও তার স্বজনদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মোকাবিলা ও নিরসনের ওপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া; শারীরিক ও মানসিক আত্মসুরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া; মানসিক চাপ মোকাবিলার সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া; এবং কোনো রকম সহিংসতার মুখোমুখি হলে তাৎক্ষণিক রিপোর্ট করার জন্য উৎসাহিত করা। এছাড়া আরও কিছু উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। যেমনÑ হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; রোগী ও স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ; জনপরিসরে যোগাযোগ। হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের অংশ হিসেবে সুনির্দিষ্ট রিপোর্টিং প্রোটোকল থাকতে হবে।
প্রত্যেক স্তরের কর্মীবাহিনীকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা যাতে তাদের পেশাগত সমস্যা ও অভিজ্ঞতার কথা নীতিনির্ধারকদের বলতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আর রোগীর সঙ্গে যোগাযোগের প্রশ্নে হাসপাতালে সহিংসতার ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি-সংবলিত বার্তা বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করতে হবে। সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কত সময় অপেক্ষা করতে হবে সে সম্পর্কে প্রতিনিয়ত রোগী ও তার স্বজনদের জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
হাসপাতালে অধিকার, শিষ্টাচার, করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে বিভিন্ন বার্তা রোগীর ও স্বজনদের জানাতে হবে। রোগী ও স্বজনদের রাগ, ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি প্রশমনের প্রশ্নে নির্দিষ্ট নীতিমালা ও প্রোটোকল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। হাসপাতালের সব কর্মীকে সাংস্কৃতিক সক্ষমতা ও সংবেদনশীলতায় দক্ষ করে তুলতে হবে। এছাড়া হাসপাতালগুলো বিভিন্ন জনসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।
হাসপাতালের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার প্রশ্নে গণমাধ্যমকে সম্পৃক্ত করতে পারে। পরিচালনা করতে পারে বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে রাখতে হবে নিবিড় যোগাযোগ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেও ব্যবহার করতে হবে বেশ কৌশলী পন্থায়।
কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসাসেবা কর্মীদের ওপর সহিংসতা ঘটনা মোকাবিলায় হাসপাতালগুলো আরও কিছু পদক্ষেপে নিতে পারে। সেগুলো হলো, ডাক্তার-নার্স ও অন্যান্য চিকিৎসাসেবা কর্মীদের কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া; সুস্পষ্ট যোগাযোগ চ্যানেল স্থাপন; রোগীর প্রেক্ষাপটে চিকিৎসা ও সেবা দেওয়ার প্রশ্নে সমানুভূতি ও মমতাবোধের বিকাশ ঘটানো; ত্বরিত সমস্যা চিহ্নিত করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে যেসব বিষয়ে জোর দিতে হবে তা হলো: সক্রিয় ও মনোযোগ দিয়ে শোনার দক্ষতা; রোগী ও স্বজনদের রাগ, ক্ষোভ ও অন্যান্য নেতিবাচক আবেগ প্রশমনের কৌশল জানা; ইতিবাচক ও আবেগমথিত যোগাযোগ; ও সংঘাত নিরসন কৌশল।
অন্যদিকে সুস্পষ্ট যোগাযোগ চ্যানেল স্থাপনের প্রশ্নে হাসপাতালে খোলা দুয়ার নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে। হাসপাতালে কর্মরত সেবাকর্মীদের মাঝে নিয়মিত মিটিংয়ের ব্যবস্থা থাকা। এবং নাম ও পরিচয় গোপন রেখে অভিযোগ, অনুযোগ, ক্ষোভ, রাগ ও অভিমান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারার সুযোগ থাকা। সমানুভূতি ও মমতাময় সেবা দেওয়ার প্রশ্নে রোগীর প্রেক্ষাপট থেকে সমস্যাকে উপলব্ধি করতে পারা; রোগীর সঙ্গে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলা; এবং রোগীর আবেগকে খারিজ না করে বরং যৌক্তিকভাবে বিবেচনা করা। কাজেই চিকিৎসা প্রদানের প্রশ্নে সেবাকর্মীদের কেবল রোগের চিকিৎসা করলেই চলে না, বরং রোগীর সেবাও করতে হয়। এবং সামলাতে হয় রোগীর স্বজনদের।
একজন রোগী যে দল বা বর্গেরই হোক না কেন, গুণগত মানসম্মত সেবা প্রদানের প্রশ্নে একজন সেবাকর্মীর কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হয়, সমানুভূতি ও মমতাবোধ থাকতে হয় এবং রোগীর প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই রোগ ও রোগীর চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করতে হয়। আর হাসপাতালে এরকম সংঘাতময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় ডাক্তার-নার্স ও অন্যান্য কর্মীর ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রথমেই যে কাজটি করা উচিত তা হলো যতটা সম্ভব নিজেকে শান্ত রাখা।
রোগী ও স্বজনদের এরূপ আচরণের সম্ভাব্য কারণটি উপলব্ধির চেষ্টা করা। বুঝতে হবে এই আচরণের কারণ কি রোগী নিজে, হাসপাতালের কোনো কর্মী, কিংবা হাসপাতালের পুরো ব্যবস্থা। রোগী ও তার স্বজনদের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ না করে তাদের প্রেক্ষাপট থেকে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করতে হবে। উদ্ভূত ঘটনা বা পরিস্থিতিকে ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া যাবে না। কোনোভাবেই যাতে মুখ ফসকে হলেও কোনো কটু কথা, কিংবা অশ্লীল ভাষা বের না হয়। এছাড়া নিজের শারীরিক ভাষার প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে, যাতে আক্রমণাত্মক ভঙ্গির প্রকাশ না ঘটে।
পেশাদারি সীমার মধ্য থেকেই রোগী ও স্বজনদের সব ধরনের সহায়তা করতে হবে। এরকম পরিস্থিতিতে রোগী ও স্বজনের প্রতি উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও অবহেলার প্রকাশ না করে বরং তাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে। মনোযোগ দিয়ে তাদের প্রতিটি কথা ও আবেগ উপলব্ধির চেষ্টা করতে হবে। তাদের রাগ ও ক্ষোভের সম্পূর্ণরূপে প্রকাশের সুযোগ দিয়ে সমব্যথী মন ও আবেগে নিয়ে কথা বলতে হবে।
লেখক: সিনিয়র লেকচারার, মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)