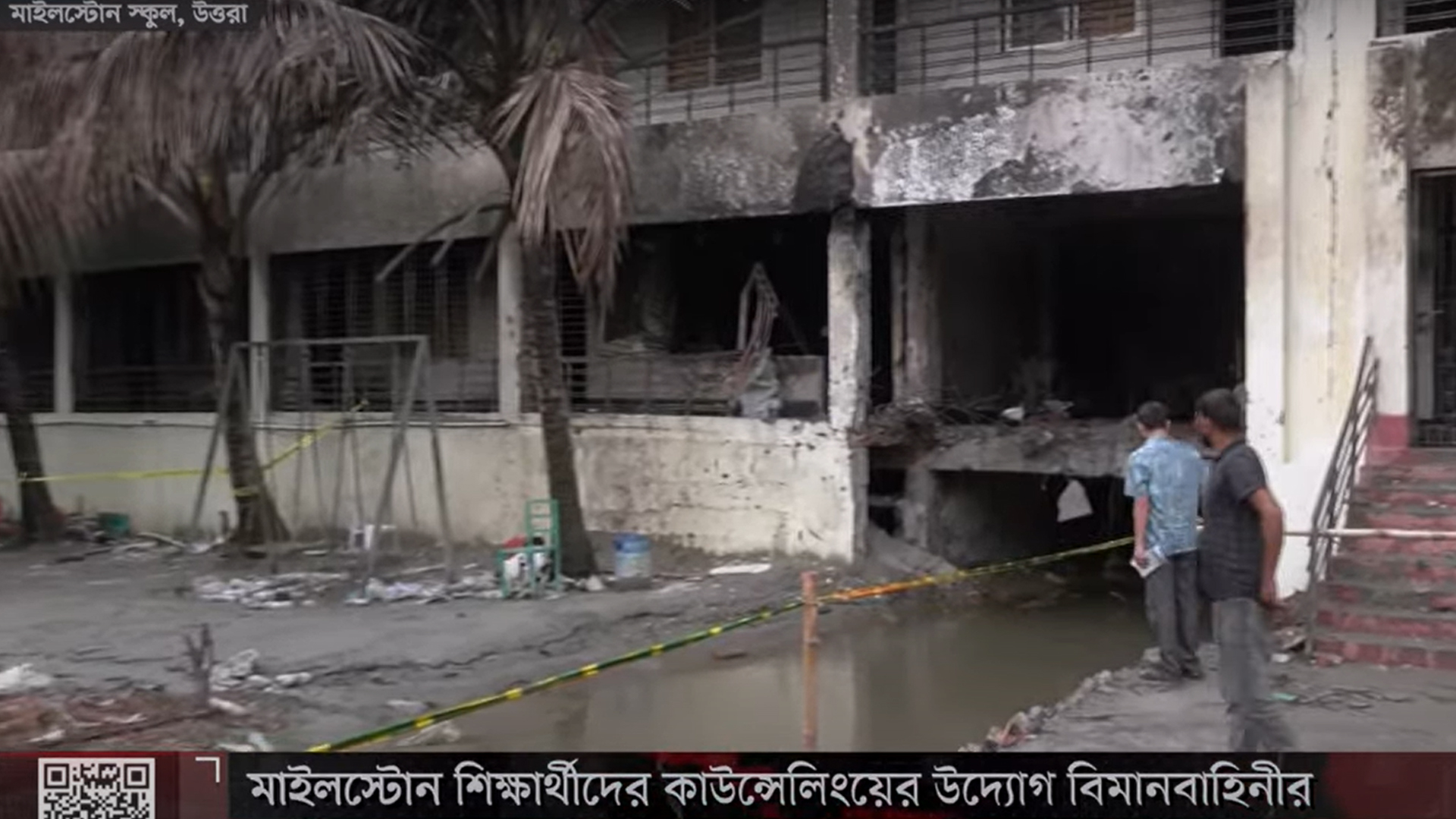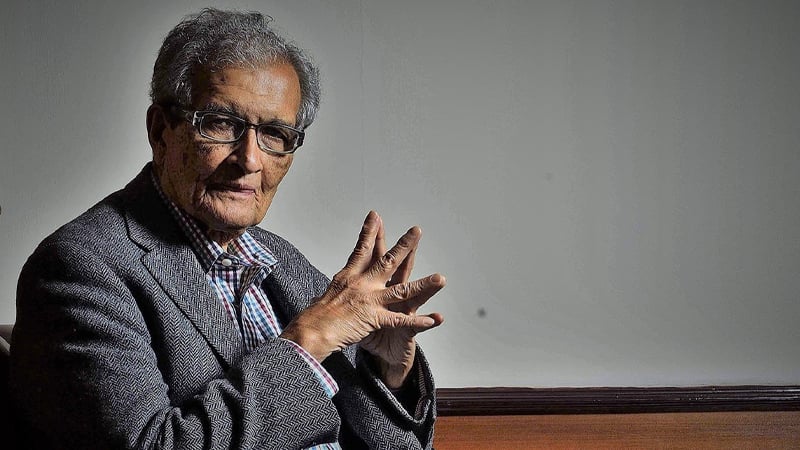মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন : সাংবাদিকতা অত্যন্ত মহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি পেশা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বে সাংবাদিকতাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বর্তমান আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ইলেকট্রনিকমাধ্যম প্রিন্টমাধ্যম এবং অনলাইনমাধ্যমে যারা সংবাদ সংগ্রহের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্রকাশের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকেন তারাই সাংবাদিক এবং তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের পেশাটাই সাংবাদিকতা।
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গণমাধ্যম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদমাধ্যম গণমাধ্যমেরই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। রাষ্ট্র তথা প্রজাতন্ত্রের সুশাসন নিশ্চিত করতে সংবাদমাধ্যম পাহারাদারের ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক ও জনগুরুত্বপূর্ণ সর্বোপরি সুশাসন যেমন সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে ঠিক তেননি সংবাদমাধ্যম সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে রাষ্ট্রকে উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে। এদিক থেকে সংবাদমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ (ঋড়ঁৎঃয ঊংঃধঃব) বলা হয় । রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদপত্রকে সর্বপ্রথম নির্দেশ করেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টারিয়ান এডমন্ড বার্ক। তিনি ১৭৮৭ সালে হাইজ অব কমন্সের সংসদীয় বিতর্ক পর্বে ঋড়ঁৎঃয ঊংঃধঃব প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন।
বিগত দিনগুলির অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে- সমাজের নানা অসংগতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত না হলে তার প্রতিকার করার জন্য রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ এগিয়ে আসে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হবার পরে প্রশাসনের নজরে আসে। এখানে সহযোগী একটি পত্রিকায় সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা বেনজির আহমেদের কার্যকলাপের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পরে শাসন বিভাগের টনক নড়েছিল এবং সেটা দেশের টক অব দ্যা কান্ট্রিতে পরিণত হয়েছিল। অতএব বুঝাই যাচ্ছে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।
আমাদেরকে দেখতে হবে গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন কি না। বাংলাদেশে সাংবাদিকরা নানান সীমাবদ্ধতা নিয়ে কাজ করে থাকেন। দেশে বিরাটসংখ্যক প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও অনলাইন মিডিয়া কার্যকর রয়েছে বর্তমানে। এই সমস্ত মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকগণ কি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন? স্বাধীন সাংবাদিকতায় যে বিষয়গুলো বেশি বাধা হিসেবে কাজ করে তা হচ্ছে- অধিকাংশ গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকগণ তাদের প্রতিদিনের কাজের পারিশ্রমিক সঠিকভাবে পান না। মানুষ কোনো একটা পেশা অবলম্বন করে সেই পেশাকে কেন্দ্র করেই উপার্জনের মাধ্যমে সংসার চালান। গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা যদি জীবিকা নির্বাহের মতো প্রয়োজনীয় আয় করতে না পারেন তাহলে তাদের মধ্যে পেশাগত দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত মফস্বলের সাংবাদিকগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নামমাত্র একটা পারিশ্রমিক পান। অনেক গণমাধ্যম শুধুমাত্র নামমাত্র নিয়োগ দিয়ে একটি পরিচয়পত্র দিয়ে থাকে। পারিশ্রমিক হিসেবে তেমন কিছুই পান না এই সাংবাদিকরা।
সঠিকভাবে কোনো কাজের পারিশ্রমিক না পেলে তার কাছ থেকে সততার সাথে কাজ পাওয়া কঠিনই যে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাধীন সাংবাদিকতার আরেকটি অন্তরায় হচ্ছে- আমাদের দেশে সাংবাদিকতায় যারা যোগ দেন তাদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষাগত কোনো যোগ্যতা থাকে না বললেই চলে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাংবাদিকতায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ থাকলেও পেশাগত কাজের জন্য কোনো ডিপ্লোমা কোর্স করার সুযোগ নেই। এ কারণে যারা সাংবাদিক হতে চান অন্তত রুট লেভেলের সাংবাদিক যারা হতে চান তাদের সাংবাদিকতা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক পড়াশোনাটাই নাই। প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার স্পোর্টস রিপোর্টগুলো একটু লক্ষ করে দেখলেই বোঝা যাবে তাদের রিপোর্টের মান এবং বাচনভঙ্গি কতটা অদক্ষ। স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আরেকটি অন্তরায় হচ্ছে দলবাজি করা। অনেক আগে থেকে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এই বিভক্তির কারণে সাংবাদিকদের মাঝে ঐক্যও গড়ে ওঠেনি। এক গ্রুপ বিপদে পড়লে অন্য গ্রুপ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া তো দূরে থাক বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা আত্মতৃপ্তিতে ভোগে থাকে। এ কারণে বাংলাদেশের সকল সাংবাদিকের জন্য একটি অভিন্ন একক প্ল্যাটফর্ম থাকা দরকার।
স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য সংবাদ মাধ্যমগুলোর নিরপেক্ষ মনোভাব থাকা খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি। দেখা গেছে পত্রিকাগুলো এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলো কোনো না কোনো দলের প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন করে থাকে। অথচ এটা করা উচিত নয়। কোনো একটি বিশেষ অনুষ্ঠান কভার করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের ঊর্ধ্বতন সম্পাদকগণকে খেয়াল রাখতে হবে এই বিষয়টি যে- যাকে রিপোর্টার হিসেবে ঐ অনুষ্ঠানে পাঠানো হচ্ছে তিনি যেন বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে আগে থেকেই ধারণা নিয়ে যান। নইলে সেই অনুষ্ঠানের সঠিক চিত্র সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার তুলে আনতে পারবেন না। অতীতে দেখা গেছে- সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কেউ রাষ্ট্রীয় সফর শেষে দেশে ফিরে আসার পর যখন তিনি সংশ্লিষ্ট দেশটির সফর নিয়ে প্রেস ব্রিফিং করেন সেখানে প্রায়শই উপস্থিত অনেক সাংবাদিকের প্রশ্নের ধরনে বুঝা যায় যে- সংবাদসম্মেলনকৃত অনুষ্ঠানটির বিষয়ে তার কোনো ধারণাই নেই।
অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও লক্ষণীয় যে আমাদের অনেক সাংবাদিকই বিষয়ভিত্তিক দায়িত্বটি সঠিকভাবে পালন করেন না। উলটো তারা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলে সফরকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো গরম মন্তব্য আদায় করার চেষ্টা করেন। ফলে পরের দিন প্রিন্ট মিডিয়াতে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ঐ নির্দিষ্ট সফরের মূল আলোচনাটাই থাকে অনুপস্থিত। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি তোষামোদির মাধ্যমে সঠিক প্রশ্ন না করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রিয়ভাজন হওয়ার চেষ্টা করে থাকে অনেক সাংবাদিক। তোষামোদ যে স্বাধীন সাংবাদিকতা বিকাশের একটা অন্তরায় হিসেবে পরিগণিত- এটা সবাইকে মনে রাখতে হবে। স্বাধীন সাংবাদিকতা একটি গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম ভিত্তি, যেখানে মানুষের বাক্স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। তবে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে বাংলাদেশে, সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের বাধা ও চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। এই লেখায় আমি স্বাধীন সাংবাদিকতার পথে প্রধান অন্তরায়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই।
রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও চাপ: গণমাধ্যম সবসময়ই রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে। বিভিন্ন সময়ে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধা দেয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র সাংবাদিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করে নির্দিষ্ট মতাদর্শ প্রচারের জন্য। সরকারের সমালোচনা করা সংবাদপত্রগুলোকে ‘দেশবিরোধী’ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এছাড়াও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে সাংবাদিকদের উপর মানহানি মামলা করা, গ্রেফতার, এমনকি কারাবরণ করতে বাধ্য করার ঘটনাও ঘটে। যেমন, বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-এর মাধ্যমে সাংবাদিকদের মতপ্রকাশের অধিকার সংকোচিত করার অভিযোগ রয়েছে।
অর্থনৈতিক চাপ ও মালিকপক্ষের প্রভাব: সাংবাদিকদের উপর সবচেয়ে বড়ো চাপ বা প্রভাব হলো অর্থনৈতিক। অনেক সংবাদমাধ্যমের মালিকপক্ষ রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকে। তারা সাংবাদিকদের উপর প্রভাব খাটিয়ে তাদের নিজেদের স্বার্থে সংবাদ প্রচার করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কোনো সংবাদ পরিবেশন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া, সাংবাদিকদের মজুরি কম হওয়া ও তাদের পেশাগত নিরাপত্তার অভাবও তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধা দেয়। এর ফলে সংবাদমাধ্যম অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতাদের চাহিদা অনুযায়ী সংবাদ প্রকাশ করতে বাধ্য হয়।
সহিংসতা ও হয়রানি: বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকরা প্রায়শই সহিংসতা, হুমকি এবং শারীরিক আক্রমণের শিকার হন। বিশেষ করে তদন্তমূলক/অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের অনেক ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়। বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই সাংবাদিকরা শুধুমাত্র সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণনাশের হুমকি, শারীরিক নির্যাতন, এমনকি নির্মম হত্যাকা-ের শিকারও হন। আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংগঠনগুলোর তথ্যমতে, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এমন সহিংসতা প্রায়ই বিচারবহির্ভূত থেকে যায়, যা অপরাধীদের আরো উৎসাহিত করে।
আইনগত সীমাবদ্ধতা: সাংবাদিকতার জন্য আইনি সুরক্ষা কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অনেক দেশেই এমন কিছু আইন প্রয়োগ করা হয় যা স্বাধীন সাংবাদিকতাকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন, বাংলাদেশের ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এমন একটি আইন যা অনলাইন এবং অফলাইন উভয় মাধ্যমেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে হুমকির মুখে ফেলে। এই আইনের আওতায় ‘রাষ্ট্রবিরোধী’, ‘অপপ্রচার’ বা ‘জনশৃঙ্খলা ভঙ্গের’ অভিযোগে যেকোনো সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হতে পারে। এমন আইনগুলো সাংবাদিকদের নিজেদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমিত করে দেয়, কারণ তারা সব সময় আইনি ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। যে কারণে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না এবং কাজ শুরু করলেও নানানভাবে নিগৃহীত হন।
প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ ও সাইবার আক্রমণ: বর্তমানের আধুনিক ডিজিটাল যুগে সাংবাদিকরা ক্রমশ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে তাদের কাজের প্রচার করছেন, যা তাদের জন্য নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ বয়ে নিয়ে এসেছে। সাইবার আক্রমণ, হ্যাকিং, তথ্যচুরি ইত্যাদি সাংবাদিকদের কাজকে ব্যাহত করছে। পাশাপাশি, অনেক সময় বিভিন্ন সরকার ও প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকদের অনলাইন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তথ্য ফাঁস বা হ্যাকিংয়ের মাধ্যমেও সাংবাদিকদের কাজের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হয়, যা তাদের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পথে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
সেন্সরশিপ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ: অনেক সময় সরকার বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরাসরি সেন্সরশিপ প্রয়োগ করে, অর্থাৎ তারা নির্দিষ্ট সংবাদ বা তথ্য প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তবে শুধু বাইরের সেন্সরশিপই নয়, সাংবাদিকরাও প্রায়শই আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সেল্ফ-সেন্সরশিপ প্রয়োগ করেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, নিজেকে ও পরিবারকে বিপদমুক্ত রাখতে এবং কাজের নিরাপত্তা বজায় রাখতে সাংবাদিকরা নিজেরাই অনেক তথ্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকেন। এই ধরনের সেন্সরশিপ সাংবাদিকতার মান এবং নিরপেক্ষতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের চাপ: আজকের যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সাংবাদিকতা ও মতপ্রকাশের একটি বড়ো প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। যদিও এটি তথ্য ছড়ানোর একটি শক্তিশালী মাধ্যম, কিন্তু এর ফলে ভুয়া খবর বা মিথ্যা তথ্যেরও প্রচার বাড়ছে। সাংবাদিকরা প্রায়ই সামাজিকমাধ্যমের বুলিং, ট্রলিং, অপমান এবং মানসিক হয়রানির শিকার হন। ভুয়া তথ্য ছড়ানোর ফলে সাংবাদিকদের বিশ্বাসযোগ্যতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তারা সামাজিকমাধ্যমের এই চাপের কারণে প্রায়ই নিজেদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধাগ্রস্ত বোধ করেন।
জনসাধারণের আস্থা সংকট: সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করা। আজকের তথ্য-প্রযুক্তির যুগে ভুয়া খবর বা প্রোপাগান্ডা খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অনেকেই প্রকৃত সাংবাদিকতা এবং ভুয়া সংবাদ বিভ্রান্তিতে পড়েন। বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে অনেক সংবাদমাধ্যম পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ প্রকাশ করে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতি আস্থা কমিয়ে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে সাংবাদিকরা অনেক সময় নিজেদের কাজের যথার্থতা প্রমাণে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।
সাংবাদিকতার পেশাগত দক্ষতার অভাব: বর্তমানে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব একটি বড়ো সমস্যা। অনেক সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরা যথাযথ প্রশিক্ষণ ছাড়াই কাজ শুরু করেন, যার ফলে তারা সংবাদ সংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরির সময় যথাযথ মান বজায় রাখতে পারেন না। দক্ষতার অভাবে অনেক সময় সাংবাদিকরা ঘটনার সঠিক বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হন এবং তাদের প্রতিবেদন পক্ষপাতদুষ্ট বা ভুল তথ্যযুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে সংবাদমাধ্যমের প্রতি আস্থা হ্রাস পায় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
সাংবাদিকদের নিরাপত্তার অভাব- সাংবাদিকরা কাজের সময় প্রায়শই শারীরিক ও মানসিক ঝুঁকির সম্মুখীন হন। অনেক দেশে সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তার জন্য সঠিক আইন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মাদক ব্যবসা, মানবপাচার বা রাজনৈতিক দুর্নীতি নিয়ে কাজ করার সময় সাংবাদিকদের উপর হুমকি ও হামলার ঝুঁকি হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তারা আইনি সহায়তা বা নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে পারেন না, যা তাদের পেশাগত কাজকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে।
স্বাধীন সাংবাদিকতা গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হলেও, এটি এখন বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনি ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জগুলো সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে বড়ো অন্তরায় সৃষ্টি করছে। সাংবাদিকদের জন্য একটি নিরাপদ ও স্বাধীন পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে তারা নিরপেক্ষভাবে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার করতে পারেন। স্বাধীন সাংবাদিকতার সুরক্ষার জন্য আইনি কাঠামো আরও শক্তিশালী করা এবং সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।
লেখক: কলামিস্ট ও সাবেক কলেজ শিক্ষক