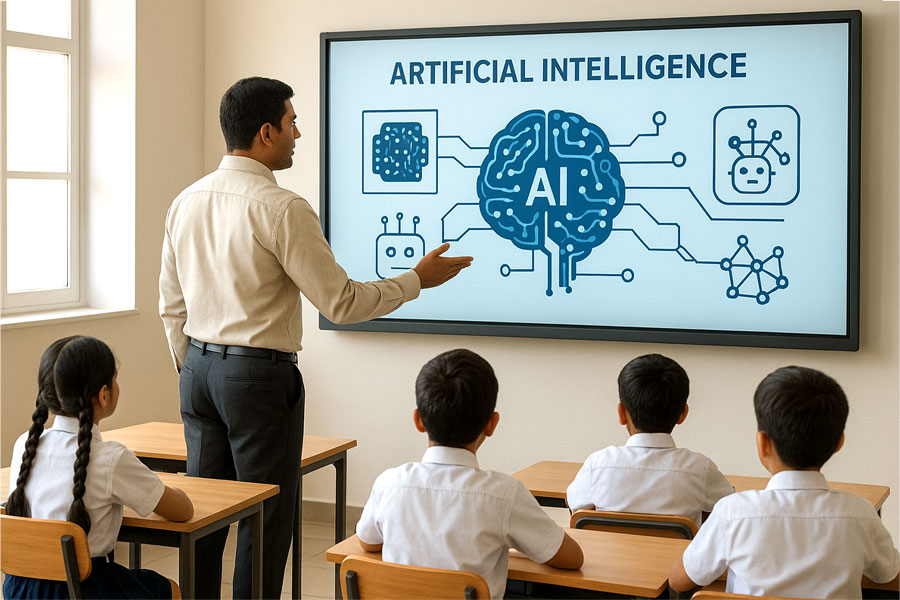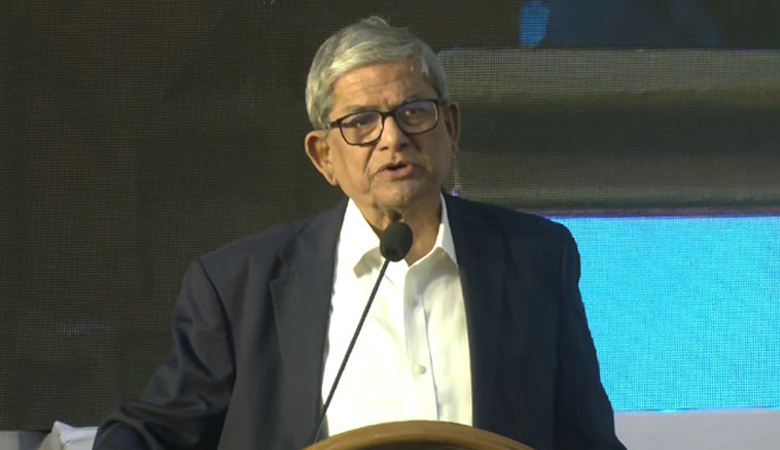বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সেই ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাত ধরে বাংলাদেশে এসেছে স্টারলিংক ইন্টারনেট সেবা। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ইলন মাস্কের সঙ্গে ভিডিওকলে আলোচনা করেন প্রধান উপদেষ্টা। বাংলাদেশে স্টারলিংক ইন্টারনেট সেবা চালুর বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করেন তারা। ইতোমধ্যে স্টারলিংককে বাংলাদেশে ব্যবসার অনুমতি দিয়েছে সরকার।
স্যাটেলাইটনির্ভর ইন্টারনেট সেবায় আইনানুগ আড়িপাতার সুযোগ রেখে নতুন একটি নির্দেশিকা জারি করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। নতুন নির্দেশিকা বা গাইডলাইনের নাম ‘রেগুলেটরি অ্যান্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইনস ফর নন-জিওস্টেশনারি অরবিট (এনজিএসও) স্যাটেলাইট সার্ভিসেস অপারেটর ইন বাংলাদেশ’। আসলে স্টারলিংক হলো একটি সিস্টেম। মোট ৪২ হাজার লো আর্থ অরবিট বা এলইও স্যাটেলাইট দিয়ে একটি ইন্টারনেট কাভারেজ তৈরি করতে যাচ্ছে ইলন মাস্কের কোম্পানি স্পেসএক্স। ইলন রিভ মাস্ক হলেন একজন প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি খাতে সফল উদ্যোক্তা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। যত বেশি পরিমাণ স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হবে, স্টারলিংকের ইন্টারনেট সেবা তত উন্নতমানের হবে।
ইন্টারনেটের গতি পরীক্ষা ও বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান ‘ওকলা’র গত জানুয়ারির হিসাবে, বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেটের গড় ডাউনলোড গতি ৪০ এমবিপিএসের কিছু কম। আপলোডের গতি ১৩ এমবিপিএসের মতো। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ডাউনলোড গতি প্রায় ৫১ এমবিপিএস। আপলোডের ক্ষেত্রে তা প্রায় ৪৯ এমবিপিএস। অবশ্য বাসাবাড়িতে সাধারণ গ্রাহকরা গতি পান আরও কম। গ্রামে অনেক জায়গায় ইন্টারনেট সংযুক্ত হওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। প্রশ্ন হচ্ছে, স্টারলিংক থেকে বাংলাদেশ কীভাবে লাভবান হবে। তা হলো-
দূরবর্তী ও দুর্গম অঞ্চলে ইন্টারনেট সুবিধা: বাংলাদেশের অনেক গ্রামীণ ও পার্বত্য অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড বা ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা নেই। স্টারলিংকের স্যাটেলাইট-ভিত্তিক ইন্টারনেট এসব অঞ্চলে সহজেই উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে দিতে পারে। এতে ডিজিটাল বিভাজন কমে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি হবে।
ডিজিটাল ইকোনমি ও ই-গভর্ন্যান্সের উন্নয়ন: নির্ভযোগ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই-কমার্স, অনলাইন ব্যাংকিং এবং রেমিট্যান্স সেবার প্রসার ঘটবে। সরকারি সেবা যেমন ই-গভর্ন্যান্স, টেলিমেডিসিন এবং অনলাইন শিক্ষা কার্যকরভাবে চালু করা সম্ভব হবে।
জরুরি যোগাযোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে প্রচলিত ইন্টারনেট ও টেলিকম নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্টারলিংকের স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক জরুরি যোগাযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ কার্যক্রমে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব হবে।
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন: প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল, কলেজ এবং মেডিকেল সেন্টারে উচ্চগতির ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন ক্লাস, ভিডিও কনফারেন্সিং এবং টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা যাবে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সঙ্গে ভার্চুয়াল কনসাল্টেশন করে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি পাবে।
ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের উন্নতি: উচ্চগতির ইন্টারনেটের মাধ্যমে রিমোট ওয়ার্ক, ফ্রিল্যান্সিং (আপওয়ার্ক, ফাইভার) এবং আউটসোর্সিং সেক্টর আরও শক্তিশালী হবে। টেক স্টার্টআপগুলো গ্লোবাল মার্কেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে।
প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা খাতে সুবিধা: স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের মাধ্যমে সীমান্ত ও সমুদ্রপৃষ্ঠের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা উন্নত করা যাবে। ড্রোন এবং স্মার্ট সিকিউরিটি সিস্টেমে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।
প্রতিযোগিতা ও সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট: স্টারলিংকের প্রবর্তন হলে স্থানীয় ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে; যা ইন্টারনেটের দাম কমাতে ও গতি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।
অন্যদিকে স্টারলিংক ব্যবহারে বাংলাদেশের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। তা হলো-
ডিভাইসের মূল্য: স্টারলিংক কিট (অ্যান্টেনা+রাউটার) এর দাম প্রায় ৫০০-৭০০ ডলার। বাংলাদেশি বিনিময় হারে তা প্রায় ৬০ থেকে ৮৪ হাজার টাকা। যা স্থানীয় আইএসপি যেমন বিটিসিএল, গ্রামীণ, বাংলালিংকের চেয়ে অনেক বেশি। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য ব্যয়বহুল। স্টারলিংকের ওয়েবসাইটে বলা আছে, বাসাবাড়িতে তাদের সেবা নিতে কিছু সরঞ্জাম কিনতে হবে। সেখানে থাকে একটি রিসিভার বা অ্যান্টেনা, কিকস্ট্যান্ড, রাউটার, তার ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা বা পাওয়ার সাপ্লাই। এটাকে স্টারলিংক কিট বলা হয়, যার মূল্য ৩৪৯ থেকে ৫৯৯ ডলার পর্যন্ত (৪৩ থেকে ৭৪ হাজার টাকা)। আবাসিক গ্রাহকদের জন্য স্টারলিংকের মাসিক সর্বনিম্ন ফি ১২০ ডলার (প্রায় ১৫ হাজার টাকা)। তবে করপোরেট গ্রাহকদের জন্য স্টারলিংক কিটের দাম ও মাসিক ফি দ্বিগুণের বেশি। তবে দেশ ভেদে দামে ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে মাসিক সংযোগ ফি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
আবহাওয়ার প্রভাব: ভারী বৃষ্টি বা মেঘলা আবহাওয়ায় সিগন্যাল বিঘ্নিত হতে পারে।
লাইসেন্সিং ও আইনি জটিলতা: বেসরকারিভাবে ব্যবহার করলে জরিমানা বা ডিভাইস বাজেয়াপ্তের ঝুঁকি আছে।
ডেটা ক্যাপ: কিছু প্ল্যানে উচ্চগতির পর ডেটা থ্রটলিং (স্পিড কমানো) হতে পারে, যা ভারী ইউজার (স্ট্রিমিং, ডাউনলোড) এর জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে।
স্থানীয় আইএসপির সঙ্গে প্রতিযোগিতা: শহরাঞ্চলে ফাইবার বা ৪এ নেটওয়ার্কের তুলনায় স্টারলিংকের দাম ও সেবা কম প্রতিযোগিতামূলক মনে হতে পারে।
পরিবেশগত উদ্বেগ: স্যাটেলাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি মহাকাশে ডেব্রিস (স্পেস জান্ক) এবং আলো দূষণের ঝুঁকি বাড়ায়। স্টারলিংক বাংলাদেশের জন্য একটি গেম-চেঞ্জার হতে পারে। বিশেষ করে যেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দুর্বল। তবে উচ্চ খরচ, লাইসেন্সিং ইস্যু এবং আবহাওয়ার সংবেদনশীলতা এর ব্যবহার সীমিত করতে পারে। সরকার যদি সহজ শর্তে লাইসেন্স দেয় এবং স্থানীয় অংশীদারত্বের মাধ্যমে খরচ কমানো হয়, তাহলে এটি ডিজিটাল বিভাজন কমাতে অবশ্যই সাহায্য করবে।