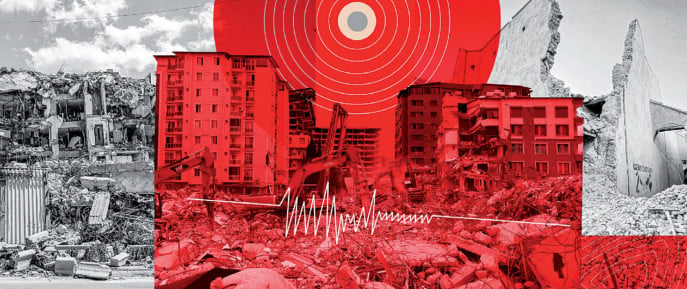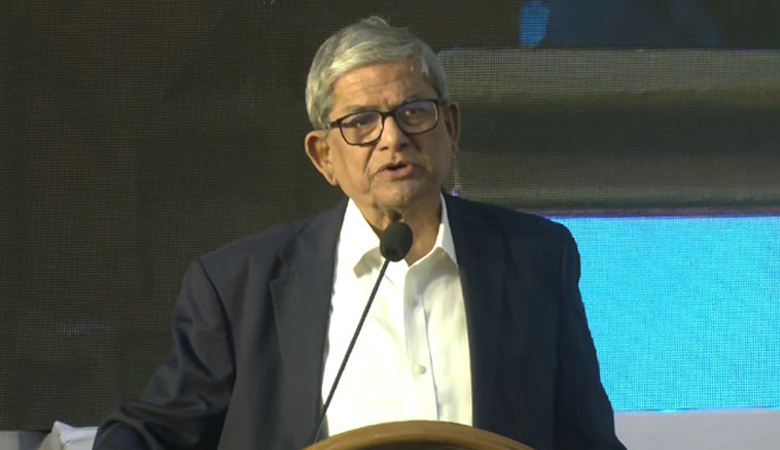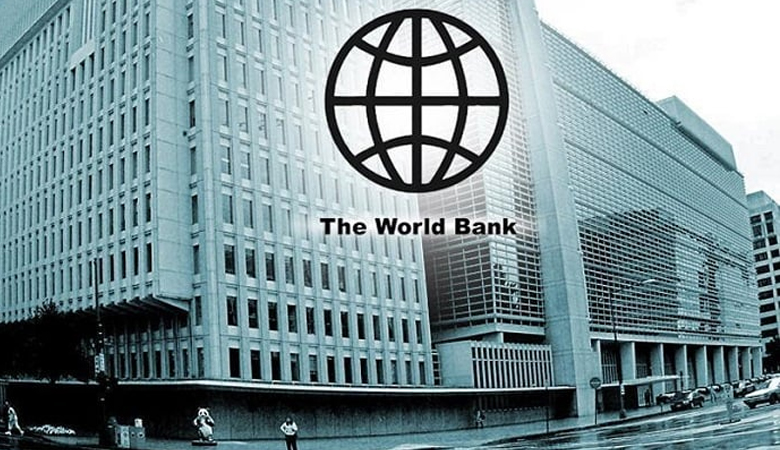কাওসার আহ্মেদ : বাঙালি জাতীয়তাবাদ যদি বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র পত্তনের ভিত্তিমূল হয় তবে বাংলা ভাষাকে বলতে হবে তার সঞ্জীবনী ধারা। কারণ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বলা আছে, ‘প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।’ তবে বাস্তবতা হলো রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন এখনও সুদূরপরাহত বিষয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্র-কাঠামো, আইন ব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষা ও প্রাত্যহিক দাফতরিক কাজকর্মে এখনও বাংলা তথা প্রমিত বাংলার প্রচলন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। অথচ মাঝে মধ্যেই আবার বাংলাকে জাতিসংঘের দাফতরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি ওঠে।
এ প্রসঙ্গে সরকারের তরফে সর্বশেষ যা জানা গেছে তা হলো, বাংলাকে জাতিসংঘের দাফতরিক ভাষা হিসেবে প্রচলন করতে হলে প্রতিবছর ৬০০ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় সোয়া ৫ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। বিপুল খরচের প্রসঙ্গ দিলেও যেখানে দেশের রাষ্ট্র-কাঠামোর সর্বস্তরে এখনও প্রমিত বাংলা ভাষা প্রচলন করা সম্ভব হয়নি, সেখানে জাতিসংঘে বাংলা প্রচলনের চিন্তা শুধু অযৌক্তিকই নয়; বরং অবাস্তবও বটে। তদুপরি জাতিসংঘের দাফতরিক ভাষা হিসেবে বাংলা প্রচলন করার জন্য যে অর্থ ব্যয় করতে হবে তার চেয়ে অনেক কম অর্থ বিনিয়োগ করে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রমিত বাংলা প্রচলন করা সম্ভব এবং এর দরুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জন করা যাবে বহুগুণ বেশি। দেশের সর্বস্তরে প্রমিত বাংলা প্রচলন হবে বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এ বিষয়ে যেসব পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করা যেতে পারে তা নিয়ে এই নিবন্ধ।
শিল্প-সাহিত্য একটি ভাষার সৌকর্য হলেও সঙ্গত কারণেই দৈনন্দিন ব্যবহারের দ্বারাই কোনও ভাষা বহমানতা ও পুষ্টি লাভ করে থাকে। অনুমান করা যায়, দেশে প্রতিদিন যে পরিমাণ লিখিত ভাষা উৎপন্ন হয় তার সর্ববৃহৎ অংশ আসে রাষ্ট্রের দফতর, সংস্থা ও আদালতের কার্যক্রম থেকে। তাই এসব প্রতিষ্ঠানে প্রমিত বাংলা ব্যবহার নিশ্চিত করা সবার আগে প্রয়োজন। উল্লেখ্য, আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের প্রধানতম মাধ্যম হিসেবে বাংলা এখন মোটামুটি জায়গা করে নিলেও দেশের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পীঠস্থান অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে বাংলার সার্বিক প্রচলন এখনও সম্ভব হয়নি।
ঔপনিবেশিক আইনের প্রাধান্য সংবলিত আমাদের বিচার বিভাগে ইংরেজির গুরুত্ব এখনও অপরিসীম। সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বাংলা পাঠের প্রাধান্য থাকলেও দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের রায় ও কার্যবিবরণী ইংরেজি ভাষাতেই লেখা হয়। দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিষয় সম্পর্কিত প্রধান প্রধান আইনসমূহ প্রণীত হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজি ভাষায়। তাই সার্বিকভাবে বিচার বিভাগে বাংলা ভাষা প্রচলন করার কাজটি ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইন ও উচ্চ আদালতের গুরুত্বপূর্ণ রায়সমূহ বাংলায় ভাষান্তর করার মাধ্যমে শুরু করা যেতে পারে। বিশেষ করে জনগুরুত্বপূর্ণ রায়গুলো বাংলায় অনুবাদের জন্য সুপ্রিম কোর্টে একটি অনুবাদ শাখা স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য এই প্রক্রিয়ায় একটি বড় বাধা হবে বাংলা আইনি পরিভাষার অভাব, যা বিগত কয়েক দশকে বাংলা ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ লক্ষ করলে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়। এ সমস্যা উত্তরণে সরকার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করে বাংলা আইনি পরিভাষা সৃষ্টির মাধ্যমে ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইন ও রায়সমূহ ভাষান্তরের কাজ সহজ ও ত্বরান্বিত করতে পারে। একইসঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ, দফতর ও সংস্থায় বাংলা ভাষার ওপর দক্ষ মানবসম্পদ নিয়োগ করা প্রয়োজন, যাতে সরকারি নথিপত্র ও দলিলসমূহে প্রমিত বাংলা ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এর ফলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বাংলা বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর অর্জনকারীদের সরকারি কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বাংলা ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।
আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি করতে চাইলেও জাতিসংঘের দাফতরিক ভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতির আগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার অধিকতর প্রচলনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। দুঃখজনক হলেও সত্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। এক্ষেত্রে একটি উপায় হতে পারে, বিদেশি রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক চুক্তি, সমঝোতা স্মারক, প্রস্তাব, বার্তা, চিঠিপত্র, বিবৃতি, বক্তব্য, নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতির যথাসম্ভব বাংলা পাঠ প্রস্তুত করা এবং সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে উপরোক্ত দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদির প্রামাণিক পাঠের ভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি লাভের জন্য চেষ্টা করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সম্প্রতি চীনের সঙ্গে কোভিড টিকা ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তির প্রামাণিক পাঠের ভাষা ছিল ইংরেজি এবং মান্দারিন। যেহেতু এটা ছিল চীন এবং বাংলাদেশের মধ্যকার চুক্তি, তাই এখানে ইংরেজি ও মান্দারিনের পাশাপাশি বাংলাকেও চুক্তির প্রামাণিক পাঠের ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হতো। এজন্য প্রয়োজন সরকারের দূরদৃষ্টি, সদিচ্ছা এবং পৃষ্ঠপোষকতা।
জাতিসংঘে ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, স্প্যানিশ ও মান্দারিন ভাষা ১৯৪৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি দাফতরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। একই বছর ২৪ জুন শুধু ইংরেজি ও ফরাসি ভাষাকে নিরাপত্তা পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কিত ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রুশ এবং স্প্যানিশকে নিরাপত্তা পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার জন্য ২২ জানুয়ারি ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কিত ভাষা হিসেবে মান্দারিন গৃহীত হয় ১৯৭৪ সালে। অন্যদিকে আরবি ভাষা জাতিসংঘের ষষ্ঠ দাফতরিক ভাষা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয় ১৯৭৩ সালে এবং তা নিরাপত্তা পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কিত ভাষা হিসেবে গৃহীত হয় ১৯৮২ সালে। জাতিসংঘের দাফতরিক ভাষা হিসেবে গৃহীত হওয়ার জন্য কোনও ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় ওই ভাষার ভূ-রাজনৈতিক উপযোগিতা, অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ওই ভাষার প্রভাব ও অবদানের মাত্রা। বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি দক্ষিণ এশিয়ার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং বহির্বিশ্বে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই বাস্তবতার নিরিখে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে জাতিসংঘ অথবা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার দাফতরিক ভাষা হিসেবে বাংলা প্রচলনের পরিবর্তে যদি সেই অর্থের কিয়দংশ বিনিয়োগ করে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রমিত বাংলার প্রচলন করা হয়, তাহলে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার অবস্থান সুদৃঢ় হবে এবং এর ফলশ্রুতিতে বাংলা ভাষার বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করা সহজ হবে।
সবশেষে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার যে বিপুল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসতে পারে সে সম্পর্কে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। যেমন, বাংলা ভাষায় আইন প্রণয়ন করা হলে তা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হবে। দাফতরিক ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে প্রমিত বাংলার ব্যবহার অনাকাঙ্ক্ষিত মতবিরোধ হ্রাস করার ক্ষেত্রে বহুলাংশে ভূমিকা রাখতে পারে।
লক্ষ করা যায়, ব্যক্তিজীবনে ভুল বোঝাবুঝি বা বিরোধের অন্যতম কারণ হতে পারে ভাষাগত দক্ষতার অভাব। আমাদের দেশে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক মামলা-মোকদ্দমার অন্যতম কারণ সরকারি নথিপত্র বা দলিল-দস্তাবেজের ভাষাগত দুর্বলতা। এসব বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রতিবছর রাষ্ট্র ও জনগণের বিপুল পরিমাণ সময় ও সম্পদ ব্যয় করতে হয়। তাই প্রমিত বাংলার ব্যবহার কর্মক্ষেত্রে গতি সঞ্চারে সহায়ক এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকা-ের জন্য ইতিবাচক বলে বিবেচিত হতে পারে। এর ফলে ব্যক্তির সাংস্কৃতিক মান ও ব্যক্তিত্বের অধিকতর বিকাশ ঘটা সম্ভব হবে। সর্বোপরি রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার আঞ্চলিকতামুক্ত সর্বজনীন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারাকে পুষ্ট করে রাষ্ট্রের সংহতি আরও মজবুত করবে।
আমাদের দেশে প্রমিত ভাষার ব্যবহার প্রসারের সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণের সম্পর্ক নিয়ে খুব বেশি গবেষণা হয়নি। ভাষাকে বলা হয় পাবলিক গুড, অর্থাৎ এর কল্যাণ অনিঃশেষ। তাই ভাষার উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হলে তার সুফলও হবে অপরিমেয়।
লেখক: আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।
সর্বস্তরে প্রমিত বাংলার প্রচলনই হবে আন্তর্জাতিকীকরণে প্রথম পদক্ষেপ
ট্যাগস :
জনপ্রিয় সংবাদ