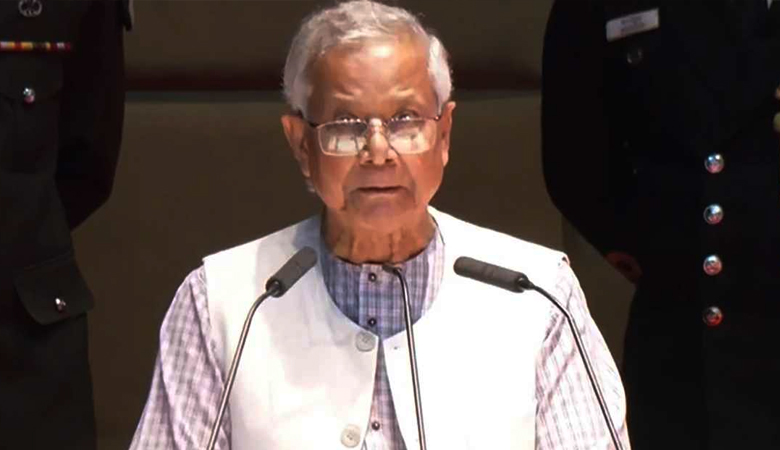ফকির ইলিয়াস : এটা কে না জানে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিপ্লব বিশ্বে মানবিক ও শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক পরিবর্তন সাধন করেছে। মানুষ জেনেছে কীভাবে বিবর্তন সাধন করতে হয়। কীভাবে আলোর কাছাকাছি যেতে হয়। ভাষা ও সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবন ও সমাজ গঠনের অন্যতম একটি শক্তি। মানুষ যখন ঘরে ফিরে তখন কথা বলে একেরারেই ঘরোয়া ভাষায়। ‘কথ্যভাষা’ দিয়ে সাহিত্য হয় কী না, তা নিয়েও আলোচনা করা যায়। হতে পারে তর্ক-বিতর্ক। বিভিন্ন দেশে কথ্যভাষায় বিস্তর সাহিত্য হচ্ছে। নাটক হচ্ছে। ছায়াছবি হচ্ছে। একটা বিষয় আমি বলে নিতে চাই, যারা এর পাঠক কিংবা শ্রোতা- এরা কিন্তু একটি বড়ো গোষ্ঠী। তারা এসব প্রকাশিত বই কিনেন। মুভি দেখেন। তাই এর একটা বাজার আছে। ‘বাজার’ কথাটি এজন্য বললাম- ভাষার সাথে অর্থনীতির একটা সম্পর্ক আছে। বিদেশে ‘আমি এই এই ভাষায় কথা বলি’- ক্ষমতাটি কিন্তু একটা ‘এক্সট্রা পাওয়ার’।
মানুষ জন্ম নিয়েই ধ্বনি শোনে। এই ধ্বনি থেকে পরিচিত হয় শব্দের সাথে। তারপরে আসে অক্ষরের সাথে বোঝাপড়া। এই অক্ষরই ভাষার স্তম্ভ। অক্ষরের পরিচয় দিয়ে ভাষাকে চিহ্নিত করা যায়। আর সংস্কৃতি লালন করে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত সভ্যতা, সাহিত্য, লোকাচারের ধারাবাহিকতা। দিয়ে যায় শিকড়ের সন্ধান। ভাষা তাই সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভাষা সংস্কৃতিকে ধারণ করে। আর সংস্কৃতি নির্মাণ করে সমাজ।
বাঙালি জাতির সংস্কৃতির মেরুদণ্ডে আঘাত এসেছে বার বার। উর্দুকে জাতীয় ভাষা বলে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন জিন্নাহ। পারেননি। এখন ২০২৪ সাল। বাংলা ভাষাকে বাঙালির কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। কিন্তু চেষ্টা যে চলছে না- তা কিন্তু নয়। আমাদের শিশুদের পাঠ্যবইয়ে ভুল, মনগড়া, অসত্য তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে যে ভুল পথে চালাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, এটা কারা করছে? কেন করছে?
আমরা দেখি, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসকগোষ্ঠী সংস্কৃতিকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে নানা কৌশলে চাপিয়ে দিয়ে গণমানুষের সৃজন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ফলে সংস্কৃতি আপন শক্তিতে বিকাশ লাভ করতে পারে না। এভাবে অজ্ঞ-অনক্ষর জনগণ হয়ে পড়ে ভীত ও বাস্তবতাবিমুখ। গণমানুষ কেবল আর্থিকভাবেই দরিদ্র হয় না, মানসিকভাবেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। তাই তাদের মনে ও মগজে বাসা বাঁধে ভাববাদী ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার। তারা হয়ে পড়ে একান্তভাবে ভাগ্য নির্ভর। এসবের হাত থেকে মুক্তির জন্য দরকার তাদের বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী ও যুক্তিবাদী করে তোলা। কিন্তু সমাজকে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে কোনো সফল সাংস্কৃতিক আন্দোলন আশা করা যায় না। সমাজ বিকাশের স্বার্থে তাই অনক্ষরতা-অশিক্ষা দূরীকরণের কার্যক্রমসহ পাঠচক্র গঠন ও পাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, তা হতে পারে সংস্কৃতির লক্ষ্যে পৌঁছানোর শক্তিশালী উপায়।
বিশ্বের সব দেশে, সব কালে সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসকশ্রেণি সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমানুষের ওপর শাসন-শোষণ-অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়। সমাজ শৃঙ্খলার নামে, আইনের নামে, এমনকি ধর্মের নামে, গণমানুষের চেতনাকে দমিত ও ভোঁতা করে রাখে। এ কাজে রাষ্ট্রের শান্ত্রী-সেপাই, আইন-আদালতকে ব্যবহার করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। অথচ এরাই আবার গণমানুষের নেতা সেজে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের বাণী শোনায়, কিন্তু কোনো ভাগ্যোন্নয়ন ঘটে না, ঘটা সম্ভবও নয়, বরং তারা ধনে ও মনে হয়ে পড়ে আরো নিঃস্ব। প্রকৃত সত্য এই যে, লড়াই-সংগ্রাম ছাড়া কারো ভাগ্যবদল হয় না। তাই গণমানুষের অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তাদেরই করতে হয়। বিষয়টি রাজনৈতিক সংগ্রামের। সে সংগ্রামে জয়ী হতে হলে গণমানুষের চেতনার জাগরণ ও উৎকর্ষসাধন প্রয়োজন। মানসিক উৎকর্ষসাধন করে সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সংস্কৃতির কাজ। মানুষের চিন্তা-চেতনার জগতে ও তার মানসগঠনে পরিবর্তন আনতে এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্য গড়ে তুলতে পারে কেবল সংস্কৃতি। তাই গণমানুষের মুক্তি সংগ্রামে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম অবিচ্ছেদ্য নয় কেবল, সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্ভব নয়। প্রকৃত পক্ষে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম থেকেই রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্ম। আবার রাজনৈতিক সংগ্রামের সাফল্যকে ধরে রাখার বাহনও সংস্কৃতি। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত বাংলার স্বদেশি আন্দোলন থেকে সাতচল্লিশ পরবর্তী বিভক্ত বাংলার ভাষা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান সবই ছিল গণমানুষের শক্তি।
মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নিয়ামক ছিল শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ডাক। সংস্কৃতির উজ্জীবনী ধারায় বাংলার গণমানুষ আপ্লুত ও জাগ্রত হয়েছিল সেই সময়ে। সংস্কৃতি যে গণমানুষের মুক্তি সংগ্রামে কত বড়ো হাতিয়ার, অতীতের নানামাত্রিক আন্দোলন সংগ্রাম থেকে তা যেমন প্রমাণিত হয়েছে; বর্তমানে ও আগামী দিনের আন্দোলন সংগ্রামেও সে প্রমাণ রাখতে সক্ষম। সংস্কৃতির কাজ, অতীত আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শৈল্পিক কৌশলে জনগণের কাছে তুলে ধরা। মানুষের মাঝে নতুন চেতনা, নতুন আশা ও নতুন স্বপ্ন সৃষ্টি করা। মানুষের ভেতরে সুপ্ত থাকা বিবেকবান, সংবেদনশীল মানুষটিকে জাগিয়ে তোলা, জাগিয়ে রাখা, নিরন্তর প্রেরণা শক্তি জুগিয়ে বিকশিত করে এগিয়ে নেওয়া।
বাঙালি জাতি এগোতে চাইছে। কিন্তু এগোবার পথটি কী? ভাবলে আমরা যে চিত্রটি প্রথমেই দেখি, তা হচ্ছে একটি অগ্রসরমান প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। তা নির্মাণে নিরলস অধ্যবসায়। একটি প্রজন্ম শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াতে দুটি শক্তির প্রয়োজন পড়ে বেশি। প্রথমটি হচ্ছে সৎভাবে সমাজের অবকাঠামো নির্মাণ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে সমকালের সঙ্গে সংগতি রেখে কর্মপরিধির ব্যাপ্তি ঘটানো। কাজ করতে হলে একটি যোগ্য কর্মীবাহিনী প্রয়োজন, যারা তাদের মেধা ও মনন দিয়ে কাজ করবে নিরন্তর।
জ্ঞানার্জনে ভাষা একটি ফ্যাক্টর তো বটেই। কারণ মানুষ না জানলে সেই তথ্য, তত্ত্ব ও সত্যগুলোকে নিজের জীবনে, সমাজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারে না। আর সেজন্য প্রয়োজন পড়াশোনা। পড়াশোনা করতে শিক্ষার প্রয়োজন। প্রয়োজন সেই ভাষাটিও রপ্ত করা। বাংলাদেশের নিরক্ষর মানুষরা প্রয়োজনীয় অক্ষরজ্ঞান পেলে নিজেদের জীবনমান যেমন বদলাতে পারবেন, তেমনি পারবেন সমাজের চিত্রও বদলে দিতে। একজন শিক্ষিত মা-ই পারেন একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিতে। আমরা সে কথা সবাই জানি ও মানি। আমরা এটাও জানি, একটি জাতি শিক্ষিত হলে সেই রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন ঘটে। মানুষ যখন তার অধিকার বিষয়ে সচেতন হয় তখন সে অনেক দাবিও আদায় করতে পারে। অথবা নিজেই চেষ্টা করে ফেরাতে পারে নিজের ভাগ্য। কিন্তু একটি প্রজন্মকে সঠিকভাবে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে কি? কিংবা তাদের সঠিক তথ্য জানিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে কি? এমন অনেক কথাই আসছে।
বাংলাদেশে দুটি শিক্ষা পদ্ধতি বিদ্যমান। একটি স্কুল শিক্ষা আর অন্যটি মাদ্রাসা শিক্ষা। বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডও রয়েছে। এই যে দুটি পদ্ধতি, তা কি পরস্পর বিরোধী নয়? এ নিয়ে অনেক কথাই বলা যেতে পারে। শিক্ষা বিষয়ে আমাদের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা একটু পড়া যাক। ‘(ক) রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজননীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।’
এখানে আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর বলতে আমরা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রাইমারি শিক্ষাব্যবস্থাকে বুঝতে পারি। সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এটা স্পষ্ট যে, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা হবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত, অবৈতনিক, বাধ্যতামুলক এবং দেশের সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই পদ্ধতির। না- তা খুব একটা পালিত হচ্ছে না। বাংলাদেশে প্রাইভেট স্কুল-কলেজগুলোতে এখন ইংরেজি ভাষার আধিপত্য। এর কারণ হচ্ছে, ইংরেজি ভাষা না শিখতে পারলে বিদেশে ভালো চাকুরি করা যাবে না। এমনকি দেশে ভালো এনজিও-তেও কাজ পাওয়া যাবে না!
ভাষার যত রকম প্রয়োজনীয়তার সংজ্ঞা আমরা তুলি না কেন, প্রধান বিষয় হচ্ছে একটি জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার গুরুত্ব। মানুষ সুশিক্ষিত হলেই তার জ্ঞান খুলবে, সে উদার হবে, সে সৎ কাজগুলো করবে। এটাই নিয়ম। পাশ্চাত্যে আমরা উচ্চশিক্ষিতের যে হার দেখি, এ জনশক্তি সে রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনায় একটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।
মানুষ নিজ ভাষায় তার অর্জন ও সাফল্যকে অন্যের জন্য বিলিয়ে দিতে পারে। আমি মনে করি, একজন শিক্ষিত কৃষক ক্ষুদ্র আকারে তার অধিক ফলন অভিজ্ঞতার বিষয়টি হাতে লিখে, কম্পোজ করিয়ে অন্যদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন। বিষয়টি ক্ষুদ্র হলেও এর প্রধান দিকটি হচ্ছে, একজন শিক্ষিত কৃষকই তা পারবেন। আর সেজন্যই শিক্ষার বিষয়টি আগে আসছে। শিক্ষিত হলেই মনের প্রখরতা বাড়ে। আর শিক্ষা গ্রহণ করা যায় জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।
আগেই বলেছি, পরিশুদ্ধ ভাষা ও সাহিত্য একটি প্রজন্মকে আলোর পথে এগিয়ে নেয়। কিন্তু বেদনার বিষয় হচ্ছে, এই বাংলাদেশে এখনও কিছু মানুষ আছে যারা- মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা যেমন, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বিংবা সংবিধানের অনেক বিধানও তারা স্বীকার করে না। বিজয়, স্বাধীনতা, শহিদ দিবসে দল বেঁধে ফুল দেওয়া, প্রভাতফেরি, কুচকাওয়াজ ও মাঠে যাওয়া, জাতীয়সংগীত গাওয়াসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চেতনামুলক কর্মসূচি-আয়োজনকে তারা ইসলামবিরোধী মনে করে। বাংলদেশের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের ধারণা একমুখী, অনেকটা এই অঞ্চলে ইসলাম বিকাশের সাথে সম্পর্কিত। ভাষা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের ধারণা খণ্ডিত। তারা সুযোগ পেলেই তাই ধর্মের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা দখলের কথা বলতেও কসুর করে না। আরও শঙ্কার কথা হচ্ছে, এই ভূতের আছর এখন প্রাথমিক শিক্ষাস্তরেও পড়তে শুরু করেছে। সম্প্রতি সাপ্লাইকৃত সরকারি বইয়ে যে ভুল দেখা গেছে তা নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়ায় কথা হছে প্রতিদিন। নতুন পাঠ্যপুস্তকে ভুলের জন্য শিক্ষাখাত সংশ্লিষ্ট সরকারের মন্ত্রণালয়ের কেউ দায়িত্ব নিতে চাইছে না। তারা একে অন্যের উপর দোষ চাপাচ্ছেন।
একটি কথা মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার বিষয়টিই এখন আর প্রধান নয়। কারণ চারপাশের বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে যত বেশি ভাষা রপ্ত করতে পারবে তার জন্য তত বেশি খুলে যাবে বিশ্ব দরজা। একথা আজকের প্রজন্ম জেনে যাচ্ছে প্রতি পদে পদে। দেশের আধুনিক বিদ্যানিকেতন এবং এর প্রসারতা সেই প্রমাণ করছে। আজ যা বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে ভাষার চেতনা। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, আদর্শের উৎস সন্ধান করে সত্যের পক্ষে প্রজন্মের মনন বিনির্মাণ।
এখনও এই দেশে উর্দু ভাষায় গুরুত্ব দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা চলে। হাদিস-সুন্নাহর দোহাই দেওয়া হয়, ভাষার বিষয়ে। বলা হয়, ঐ ভাষায় হাদিসগুলো লিখিত।
বাংলা তর্জমায় কেন তা পড়ানো হয় না। উর্দু তো ইংরেজির মতো এত দরকারি নয়। তারপরও এত বেশি উর্দু প্রীতি কেন? মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাদী শক্তির এ বিষয়টি সিরিয়াসলি ভাবা দরকার। যারা বিত্তবান, তারা নিজ নিজ এলাকায় মেধাবী প্রজন্মকে সাহায্যের মাধ্যমে হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারণ মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে অপশক্তি যতটা তাদের অনুসারীদের সাহায্য করছে, যুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তি তা করছে না। কেন করছে না? আমাদের গাফিলতি কোথায়? এ কারণগুলো সবাইকে খুঁজে দেখতে হবে। সরকার ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণমানুষের ঐক্যই পারে একুশের চেতনা, ভাষার চেতনা ধরে রাখতে।
আমি সব সময়ই রূপান্তরে বিশ্বাস করি। রূপান্তরই হচ্ছে ফিরে আসা, অনূদিত হওয়া কিংবা বিবর্তিত হওয়া। বিবর্তন না হলে নতুনের উন্মেষ ঘটে না। তুলনামূলক আলোচনা ছাড়া জানা যায় না বিশ্বের ভাষার নান্দনিক বিবর্তন কীভাবে ঘটছে। লক্ষ করেছি, একুশের বইমেলায় বেশকিছু দুর্লভ প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য যেমন- চর্যাপদ, সিলেটি নাগরী, আদিবাসী শ্লোক নিয়ে বেশ কাজ হয়েছে। এগুলো আশার বিষয়। এসব উৎস সন্ধানই প্রজন্মকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষকে ভাষার কাছে ফিরতে হয়। শিকড়ের কাছে ফিরতে হয়। ফিরতে হয় নিজের প্রয়োজনে। হ্যাঁ, সেই সাথে বিশ্বের অন্যান্য হারিয়ে যেতে বসা ভাষাভাষি মানুষগুলোকেও সম্মান করতে শিখতে হবে। এটা আমিও লিখে রাখতে চাই, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে, আমাদের প্রজন্ম- আমার প্রজন্ম একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়েই এগোতে চেয়েছিলাম।
আমি কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণে অতীতে ফিরে যাই। সবেমাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছি। কলেজ শেষ করে শহরের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে আড্ডা দিই। সিলেটের ‘লালকুঠি’ সিনেমা হলের দোতলায় ‘তৃষ্ণা রেস্টুরেন্ট’ আমাদের আড্ডাস্থল। বিশিষ্ট শিল্পী বিদিত লাল দাস (সম্প্রতি একুশে পদকপ্রাপ্ত)-এর অন্যতম কর্ণধার। সেখানেই আড্ডা দিয়ে কথা শুনি মহাজনদের। শাহ আব্দুল করিম, গীতিকার সিদ্দিকুর রহমান, গীতিকার ও শিল্পী সৈয়দ মোফাজ্জিল আলীসহ অনেকেই আসেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসেন গীতিকার গিয়াস উদ্দিন আহমদ। আমি তখন দু’চারটে বাউল গান লিখতে শুরু করেছি। একদিন সাহস করে গিয়াস ভাই’কে বলেই ফেলি- গিয়াস ভাই আমিও তো কয়েকটি গান লিখলাম। কিন্তু কেউ আমার গানগুলোতো গায় না। গাইতে চায় না। হেসে উঠেন গিয়াস ভাই। বলেন- ‘আরে ধুর, আমি গান লিখি ২৫ বছর যাবৎ আমাকেই কেউ পাত্তা দেয় না’। কথা শুরু করেন বিদিত লাল দাস। বলেন- ‘লেগে থাকো হে! এই মাঠে লেগে থাকতে হয়!’
আমাদের মনে আছে, ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায়’- এই প্রখ্যাত গানটির গীতিকার গিয়াস উদ্দিন আহমদকে লাইম লাইটে নিয়ে এসেছিলেন হুমায়ুন আহমেদ। না- গিয়াস উদ্দিন আহমদ তাঁর জীবদ্দশায় তেমন কোনো স্বীকৃতি পাননি। তিনি অনেকটা হতাশা নিয়েই ছেড়ে গেছেন আমাদের। এভাবে অনেকে যান। এরা সমাজকর্তৃক, রাষ্ট্র কর্তৃক মূল্যায়িত হন না। কেন হন না? বিদিত লাল দাশ একুশে পেয়েছেন ২০২৩ সালে মৃত্যুর অনেক বছর পর!
বিশ্ব বদলাচ্ছে। পরিবর্তিত বিশ্বে অনেককিছুই ঘটে যাচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। গীতিকবি বব ডিলান নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তার গীতিকবিতার জন্য। তাকে খ্যাতি দেওয়া হয়েছে- ‘গানের কবি’। সুইডিশ অ্যাকাডেমি বলছিল, ‘আমেরিকার সংগীত ঐতিহ্যে নতুন কাব্যিক মূর্চ্ছনা সৃষ্টির’ জন্য রক, ফোক, ফোক-রক, আরবান ফোকের এই কিংবদন্তিকে নোবেল পুরস্কারের জন্য বেছে নিয়েছে তারা।
ডিলান তথাকথিত সাহিত্যিক নন। তবে এখন তার নাম উচ্চারিত হচ্ছে টমাস মান, রুডইয়ার্ড কিপলিং, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, বার্ট্রান্ড রাসেলদের সঙ্গে। নোবেলের ১১২ বছরের ইতিহাসে এ পুরস্কারজয়ী প্রথম সংগীতশিল্পী ও গীতিকার তিনি। গার্ডিয়ান লিখেছিল, এর আগে বহুবার নোবেলের মনোনয়নের তালিকায় নাম এলেও সাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানজনক এ পুরস্কারের ঘোষণায় ডিলানের নাম বিস্ময় হয়েই এসেছে। পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ সম্মেলনে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমির স্থায়ী সচিব সারা দানিউস বলেছিলেন, তাদের এবারের নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা হবে না বলেই তিনি আশা করছেন। ডিলানকে তিনি বর্ণনা করেন ইংরেজি বাচনরীতির ‘এক মহান কবি’ হিসেবে, নোবেল পুরস্কার যার ‘প্রাপ্য’। তিনি বলেন- ‘৫৪ বছর ধরে চলছে তার এই অভিযাত্রা, প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে চলেছেন, সৃষ্টি করছেন নতুন পরিচয়।’ ডিলানের ‘দ্য টাইমস দে আর আ-চেইঞ্জিং’ গানটিকে দানিউস তুলনা করেছেন গ্রিক কবি হোমার আর শ্যাফোর সঙ্গে। আমরা যদি ৫০০০ বছর পিছনে ফিরে যাই, আমরা হোমার আর স্যাফোকে পাব। তাদের গীতিকবিতা লেখাই হতো গেয়ে শোনানোর জন্য। বব ডিলান একই কাজ করেছেন।’
না- বাংলাদেশে গীতিকবি বিভাগে কোনো ‘বাংলা একাডেমি পুরস্কার’ নাই। অথচ বাংলা একাডেমি একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। তারা বাংলাদেশের লোকগীতিকে কোনো সময়ই ‘পুরস্কারের যোগ্য’ মনে করেননি কিংবা করছেন না। লোক বিভাগে একাডেমি পুরস্কার পান গবেষকরা। যাদের গান নিয়ে গবেষণা হয়- সেই গীতিকবিরা থাকেন অচ্ছ্যুত! কী বেদনা!
বাংলাদেশে অনেক বড়ো বড়ো লোককবি, গীতিকবি আছেন। এদেরই একজন কুটি মনসুরের নাম উল্লেখ করা যায়। কুটি মনসুরের মূল নাম মো. মনসুর আলী খান হলেও তিনভাই দুই বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো হওয়ায় আদর করে মায়ের ডাকা নাম ‘কুটি মনসুর’ নামেই তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। ১৯২৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলার লোহারটেক গ্রামে জন্ম নেয় কুটি মনসুর।
তিনি ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তরের অধীনে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্তে তার স্বরচিত ৩০০ গান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাউল শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের কণ্ঠশিল্পী অডিশন বোর্ডের সম্মানিত বিচারক হিসেবে দীর্ঘদিন তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমিতে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মাননীয় অধ্যক্ষ হিসেবে এবং আনসার ভিডিপিতে ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সংগীত প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
৫২’র ভাষা আন্দোলন, ৬৬’র ছয় দফা, ৬৯’র গণ-অভ্যত্থান, ৭১’র মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও দেশভিত্তিক প্রচুর গান ও কবিতা রচনার পাশাপাশি তিনি প্রায় ৫০টি বিষয়ে এ পর্যন্ত ৮ হাজার গান রচনা ও ৪ হাজার ৫০০ গানের সুরারোপ করেছেন। তার রচিত ও সুরারোপিত আড়াই শত গান ঢাকা রেকর্ড ও ইপসা রেকর্ড নামের দুটি গ্রামোফোন কোম্পনি থেকে লং প্লে ডিস্ক রেকর্ডে প্রকাশ হয়েছে। এসব গানের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে- ন্যায্যকথা বলতে গিয়া শেখ মুজিবর জেলে যায়, বাঙ্গালিরা দোষী কোন যায়গায়, শিয়াল কয় খাটাশ ভাইরে, যৌবন জোয়ার একবার আসেরে। তিনি তার মৃত্যুর আগে কী বলে গেছেন তা শুনবেন প্রিয় পাঠক? গভীর কষ্ট ও ক্ষোভ থেকে তিনি বলেছেন- ‘বেঁচে থাকতে যেহেতু কোনো মূল্যায়ন হলো না, তাই আমি মারা যাবার পর কোনো মরোণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হলে তোমরা তা গ্রহণ করো না’। এই হলো বাংলাদেশ। এই হলো বাংলাদেশের সংস্কৃতি। আচ্ছা জানতে চাই- সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কি জানে না দেশের কোন গুণীকে কদর করতে হবে?
সংস্কৃতির একটা নিজস্ব শক্তি আছে। কী সেই শক্তি তা আমরা ৫২, ৬৯, ৭০, ৭১-এ দেখেছি। দেখেছি ৯০-এও। তাহলে আমরা আমাদের অতীত ভুলে যাচ্ছি কেন। সৈয়দ আবুল মকসুদ একুশে পদক পাননি। কেন পাননি- এর কারণ অজ্ঞাত! তিনি পেতে পারতেন। কারণ তিনি তো আজীবন ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেছেন। তাঁর লেখা- ‘জঙ্গিবাদ ছাড়াও সমাজের আরও শত্রু আছে’ শিরোনামের একটি নিবন্ধে তিনি লিখেছেন- “আমাদের সমাজে বহু মেধাবী মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে খুব বড় কর্মীও দেখেছি। বড় বিজ্ঞানী পেয়েছি। শিক্ষাবিদ পেয়েছি। পীর-ফকিরও প্রচুর দেখেছি। আধুনিক কালে আমরা বড় বড় নেতার উদ্দীপক বক্তব্য শুনেছি। কবি-সাহিত্যিকদের মূল্যবান লেখা পড়েছি; কিন্তু একমাত্র লালন শাহ ছাড়া আর কোনো সাধকের সহজ-সরল অমিয় বাণী আমাদের কানে যায়নি।
সাধককে সব ত্যাগ করতে হয়। সংসারের চাওয়া-পাওয়া, মায়া-মমতা-বন্ধনের মোহ ত্যাগ করে সামগ্রিকভাবে সব মানুষের কল্যাণে একটি প্রেমময়, ন্যায়বিচারভিত্তিক ও যুক্তিবাদী সমাজ বিনির্মাণে যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন, তিনিই তো সাধক বা কবির ভাষায় ‘পাগল’। ওই জাতীয় পাগলেরাই মহান পথপ্রদর্শক ও নৈতিক শিক্ষক। তেমন শিক্ষক আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আমরা পাইনি।
দেশমাতৃকার প্রতি সন্তানের কী কর্তব্য, সমাজের প্রতি নাগরিকের কী দায়িত্ব, কোনটা কাজ, কোনটা কর্তব্য আর কোনটা ত্যাগ তা আমরা অনুধাবন করতে পারিনি। তাই দেশের জন্য কিছু করে তার বিনিময়ে নানা কিছু চাই। একজন অসুস্থ এক ভিখারিকে কোলে করে রাস্তা পার করে দিল। ওপারে গিয়ে সন্তুষ্ট ভিখারি যদি তার হাতে পাঁচটি টাকা গুঁজে দেয় এবং সে ওই টাকা গ্রহণ করে, তাহলে কোলে করে রাস্তা পার করার ত্যাগটা থাকল না। দেশকে কিছু দিয়ে বিনিময়ে কিছু নিতে নেই।”
সৈয়দ আবুল মকসুদ জাতির পিতাকে সম্মান করতেন শ্রদ্ধার সাথে। তিনি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেছেন- ‘অনেকেই বলেন বঙ্গবন্ধু মহান নেতা কিন্তু প্রশাসক হিসেবে তিনি ততটা সাফল্যের পরিচয় দেননি। আমি মনে করি, এটা একটা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি। স্বাধীনতার পরে যে তিন-চার বছর তিনি দেশ শাসন করেছেন, আমরা খুব কাছে থেকে দেখেছি যে তিনি ফাইলওয়ার্কও অত্যন্ত নিপুণভাবেই করতেন। শুধু যে স্থানীয় প্রশাসনিক কাজ তা না, এতগুলো দেশের স্বীকৃতি তিনি আদায় করেন। সেটা তার কূটনৈতিক দক্ষতা ছাড়া সম্ভব হতো না। তার যে কূটনৈতিক সাফল্য, সেটা তুলনাহীন।’
তিনি আরও বলেছিলেন, ‘নানা রকম প্রতিবন্ধকতা, পাকিস্তানের নানা রকমের শত্রুতা, এসবকে মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর স্বীকৃতি আদায় করেছেন। কাজেই তাঁর যে জীবন ও কর্ম সেগুলো আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া দরকার। সেগুলো থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম জাতির নেতার কাছ থেকে আদর্শ যদি গ্রহণ করতে না পারে তাহলে অগ্রসর হওয়া কঠিন।’
বাংলাদেশে একটি বড়ো রকমের সাংস্কৃতিক বিপ্লব দরকার। আর এজন্য যারা অগ্রণী, তাদের মূল্যায়ন দরকার। যে দেশে লাখ লাখ ঋণখেলাপি হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে দিব্যি বেঁচে যায়- এই দেশ তাদের জন্য স্বাধীন হয়নি। ৩০ লাখ শহিদ এদের জন্য প্রাণ দেননি। তাহলে এরা রাষ্ট্রীয় মদত পাচ্ছে কীভাবে? এদের পেছনে কারা? কেন আজ সরকারি দলের একটি সদস্য পদের জন্য খুনোখুনি হয়? কেন ‘কাউন্সিলর’ পদ বিক্রি হয়ে যায় বড়ো টাকার বিনিময়ে?
আমরা দেখি, এই বাংলাদেশে তারাই বেশি নিগৃহীত, যারা বাঙালি চেতনার কান্ডার এখনও ধরে রেখেছেন। প্রজন্মকে এদের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। ভোগবাদী নয়, ত্যাগের মহিমায় আলোকিত হতে না পারলে একটি সমাজ এগোতে পারে না কোনোদিনই। কথাগুলো প্রজন্মকে ভাবতে হবে। কারণ মুক্তির পথ একটিই- সমাজে সৎ ও মানবিক হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো।
লেখক: কবি ও সাংবাদিক