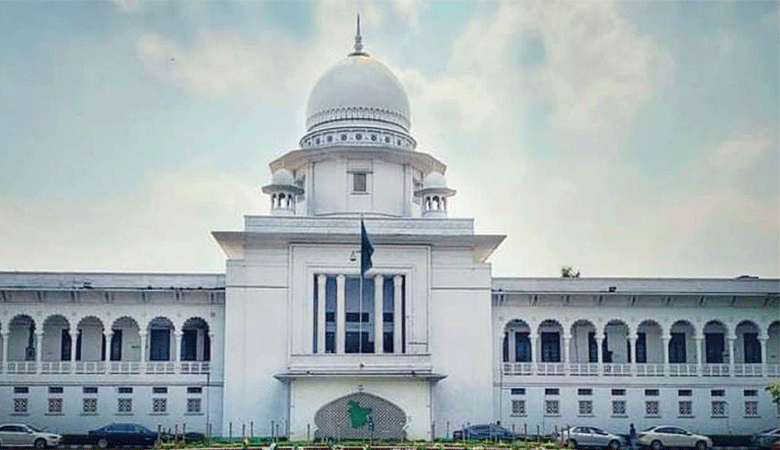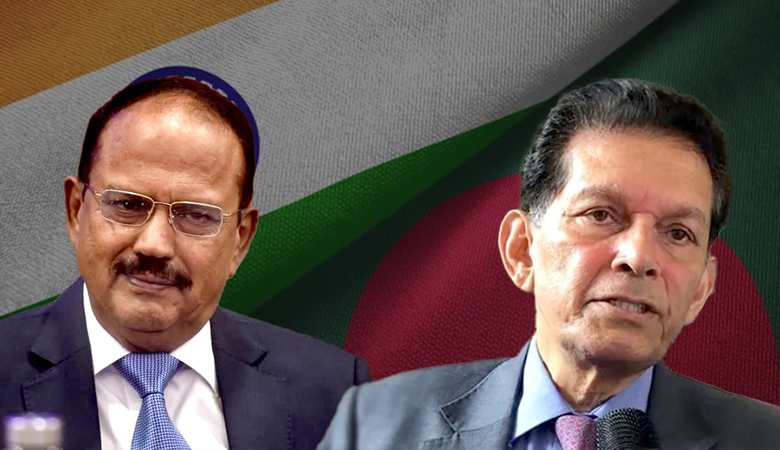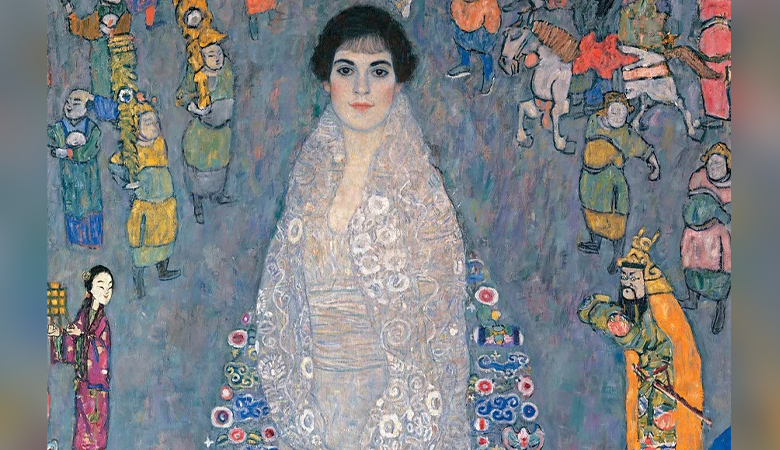বিশেষ সংবাদদাতা : অর্থনীতিতে কাঙ্খিত গতি আনতে দরকার বিনিয়োগ। মানুষের আয় বাড়াতে কর্মসংস্থানের জন্যও দরকার বিনিয়োগ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্টি নেই বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থাগুলোর মধ্যে। চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের গতিও শ্লথ। কাটছাঁট করা হয়েছে বরাদ্দ। এতেও মানুষের আয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। সম্প্রতি সরকার দেশে একটি বিনিয়োগ সম্মেলন করেছে। এতে অনেক বিদেশি বিনিয়োগকারী ও ব্র্যান্ড অংশ নেয়। ওই সম্মেলনে আশা প্রকাশ করা হয় যে বাংলাদেশ ২০৩৫ সালে সিঙ্গাপুর বা থাইল্যান্ড হবে। তবে দ্য গ্লোবাল ইকোনমির তথ্যভাণ্ডার থেকে দেখা যায় যে ‘রিটার্ন অন ইকুইটি’ বা ব্যবসায় মূলধন অনুপাতে লাভের অংশের হিসাবে বৈশ্বিক তালিকায় ১৩৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৩তম।
২১ বছরের গড় হিসাবে এটি ১৩.৮৫ শতাংশ। কিন্তু ‘রিটার্ন অন অ্যাসেট’ তালিকায় বাংলাদেশ নেমে পড়ে ৯৬তম স্থানে, যেখানে রিটার্ন ০.৯৬ শতাংশ। এটি ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানেরও চেয়ে কম। অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশে যখন বিদেশি উদ্যোক্তাদের সামনে বিনিয়োগ সম্মেলন চলছিল, তখন বাটা, কোকা-কোলাসহ বিভিন্ন বিদেশি ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর হচ্ছিল মব সংস্কৃতির কারণে। এই বার্তাও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বে। এর আগে বিশ্বখ্যাত সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক প্রেসিডেন্ট মীর নাসির হোসেন বলেন, ‘বিনিয়োগে বাংলাদেশে প্রচুর সম্ভাবনা আছে। বড় বাজার, প্রচুর লোকের দেশ। তবে এখানে গ্যাসের সংকট রয়েছে। এটা নিশ্চিত করতে হবে।
অনেক পুরনো কারখানা গ্যাস পাচ্ছে না। আর নতুন সম্প্রসারণেও গ্যাস লাগবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পের প্রসার দরকার। এখন মার্কিন শুল্কনীতির পরিবর্তনের কারণে চীনের বেশ কিছু ব্যবসা ও শিল্প এখানে আসার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে তার জন্য ব্যবস্থাপনাটা ঠিক করে দিতে হবে। অবকাঠামো, কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হবে।’ তিনি গ্যাসের দাম বাড়ানোর ফলে নতুন যাঁরা বিনিয়োগ করবেন, তাঁদের ৩৩ শতাংশ বেশি দামে গ্যাস কিনতে হবে জানিয়ে বলেন, ‘এটা নতুনদের উৎসাহিত করবে না। কারণ একই শিল্প যদি কম দামে পায়, আবার নতুন উদ্যোক্তাকে আরো বেশিতে কিনতে হয় তাহলে তার প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে যাবে। ’ বাংলাদেশ ব্যাংক কয়েক দিন আগে বিনিয়োগের সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায়, ২০২৪ সালে দেশে মোট নেট এফডিআই এসেছে ১.২৭ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১৩.২৫ শতাংশ কম। ২০২৩ সালে এই অঙ্ক ছিল ১.৪৬ বিলিয়ন ডলার। এর আগে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) বিদেশি বিনিয়োগ আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে কমে চার ভাগের প্রায় এক ভাগে নেমেছিল। এ সময়ে বিদেশি বিনিয়োগ আগের বছরের চেয়ে ৭১ শতাংশের মতো কমে গিয়েছিল।
ওই ছয় মাসে মাত্র ২১ কোটি ৩০ লাখ ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ আসে। গত অর্থবছরের একই সময়ে পরিমাণ ছিল ৭৪ কোটি ৪০ লাখ ডলার। এদিকে দীর্ঘমেয়াদি মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থানের সংকট এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক ধীরগতির প্রভাবে বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য আরও বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে বিশ্বব্যাংক। (বুধবার) ২৩ এপ্রিল প্রকাশিত সংস্থাটির সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘চলতি ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২৫ সালে দেশের জাতীয় দারিদ্র্যের হার ২২ দশমিক ৯ শতাংশে পৌঁছাতে পারে, যা ২০২২ সালে ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ।’ বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, ‘অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর হার অর্থাৎ যাদের দৈনিক আয় দুই ডলার ১৫ সেন্টের নিচে, তা দ্বিগুণ হয়ে ৯ দশমিক ৩ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। এতে অতিরিক্ত ৩০ লাখ মানুষ অতিদারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।’ বিশ্বব্যাংক বলছে, ‘উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের কারণে নিম্নআয়ের পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মতো মৌলিক খাতে।’ তবে আশার আলো হিসেবে বিশ্বব্যাংক পূর্বাভাস দিয়েছে, ‘২০২৬ সাল থেকে দেশের দারিদ্র্যের হার আবারও হ্রাস পেতে শুরু করতে পারে যদি অর্থনীতির গতি পুনরুদ্ধার হয় এবং স্থিতিশীল নীতিমালা গ্রহণ করা হয়।’ বিশ্লেষকরা বলছেন, দারিদ্র্য রোধে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদার করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। অন্যথায়, দেশের অর্জিত উন্নয়ন অগ্রগতি স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিশ্বব্যাংকের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘খাদ্য মূল্যস্ফীতির দীর্ঘস্থায়ী চাপ এবং প্রকৃত মজুরি না বাড়ায় দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে।’
বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘২০২৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে দেশের প্রায় ৪ শতাংশ শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। স্বল্পদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি কমেছে ২ শতাংশ এবং উচ্চদক্ষদের মজুরি হ্রাস পেয়েছে ০.৫ শতাংশ। এমনকি টানা ৪০ মাস ধরে প্রকৃত মজুরি ধারাবাহিকভাবে কমছে। ফলে প্রতি পাঁচটি পরিবারের মধ্যে তিনটি তাদের সঞ্চয় ভেঙে দৈনন্দিন খরচ চালাতে বাধ্য হচ্ছে।’ বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ‘২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি কমে ৩ দশমিক ৩ শতাংশে দাঁড়াতে পারে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৫ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেকটাই কম। প্রবৃদ্ধি হ্রাসের কারণ হিসেবে বিনিয়োগে স্থবিরতা, উচ্চ সুদহার, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং নীতিগত দুর্বলতাকে দায়ী করা হয়েছে।’ প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, ‘চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় ২৪.১ শতাংশ এবং মূলধনী পণ্যের আমদানি ১২ শতাংশ কমেছে।
এছাড়া ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি মাত্র ৭ দশমিক ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে গত তিন দশকে যা সর্বনিম্ন।’ বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ‘চলতি অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতির হার ১০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় বেশি। খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য, আমদানি ব্যয় এবং সরবরাহ ঘাটতির কারণে এই চাপ অব্যাহত থাকবে। তবে কঠোর মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের ফলে দীর্ঘমেয়াদে মূল্যস্ফীতির গতি কমতে পারে।’ ‘এদিকে দেশের শ্রমবাজার এখনও অনানুষ্ঠানিক ও স্বল্প উৎপাদনশীল খাত নির্ভর। বিপুল সংখ্যক মানুষ স্বনিযুক্ত ও অনিরাপদ পেশায় নিযুক্ত থাকায় আয় বৈষম্য বাড়ছে।’ তবে ‘অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাপ থাকলেও রেমিট্যান্স ও তৈরি পোশাক খাতে রফতানি কিছুটা স্থিতি এনে দিয়েছে। চলতি হিসাবে ঘাটতি ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে।’ বিশ্বব্যাংক মনে করে, ‘মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুনরারোপিত পাল্টা শুল্কনীতির ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের রফতানি ১.৭ শতাংশ এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ০.৫ শতাংশ পয়েন্ট কমতে পারে। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে না বলেও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।’
বিশ্বব্যাংকের মতে, ‘বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত এখনও অস্বাভাবিকভাবে কম মাত্র ৭ দশমিক ৪ শতাংশ। এই হারে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন।’ তারা মনে করে, ‘রাজস্ব আহরণ বাড়ানো না গেলে মানব উন্নয়ন ও অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ হ্রাস পাবে।’ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ‘চলতি অর্থবছরে জিডিপির অনুপাতে সরকারের ঋণের পরিমাণ ৩৭ দশমিক ৮ শতাংশে উন্নীত হবে— যা আগের বছরের তুলনায় ১ শতাংশ পয়েন্ট বেশি। একইসঙ্গে বিদেশি ঋণের অনুপাতও বেড়ে ১৪ দশমিক ১৬ শতাংশে পৌঁছাবে।’
বিশ্বব্যাংক বলেছে, ‘প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়ন করা গেলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৯ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ব্যাংক ও রাজস্ব খাত সংস্কারে বিলম্ব এবং নীতির অস্থিরতা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।’ সংস্থাটির সর্বশেষ ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট’ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য সংকটের প্রেক্ষাপটে অর্থনীতি চাপে পড়তে পারে।’ সংস্থাটি বলেছে, ‘অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারে উদ্যোগ নিলেও পুলিশের কার্যকারিতা, নীতির ধারাবাহিকতা এবং নির্বাচনের সময় নিয়ে রাজনৈতিক মতানৈক্য অর্থনীতির স্থিতিশীলতায় বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।’ এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংক তাদের সুপারিশে আর্থিক শৃঙ্খলা, রাজস্ব আহরণে দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যাংকিং খাতে সংস্কার এবং ব্যবসা সহজ করার ওপর জোর দিয়েছে। বিশ্বব্যাংক মনে করে, ‘সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সাহসী সংস্কার দরকার। এর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আর্থিক খাত পুর্নগঠন, রাজস্ব আদায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য সহজ করা।’ বিশ্বব্যাংক আশাবাদ ব্যক্ত করেছে, ‘প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়ন হলে মধ্য মেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে এবং প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি উভয়ই নিয়ন্ত্রণে আসবে। তবে বৈশ্বিক বাণিজ্য অনিশ্চয়তা রফতানিনির্ভর অর্থনীতিকে চাপে রাখবে’, বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
ব্যাংক খাতের টেকসই পুনর্গঠনে ১০ সুপারিশ
এদিকে নানাবিধ চ্যালেঞ্জে জর্জরিত বাংলাদেশের ব্যাংক খাতকে স্থিতিশীল ও টেকসই করতে ১০ দফা সুপারিশ করেছে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটির মতে, দীর্ঘদিনের কাঠামোগত দুর্বলতা, সুশাসনের অভাব ও রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে ব্যাংক খাত এখন গুরুতর ঝুঁকির মুখে রয়েছে। এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে দ্রুত সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে আন্তর্জাতিক এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিবেদনে বলা হয় বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত বর্তমানে উচ্চ খেলাপি ঋণ, মূলধন ঘাটতি, পরিচালন অদক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রভাবে ঋণ বিতরণসহ একাধিক সমস্যায় জর্জরিত। এ অবস্থায় ব্যাংক খাতের দুর্বলতা দূর করতে সুসংগঠিত ও কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০২৪ সালের জুনের শেষে দেশের ব্যাংক খাতের মোট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ২১ হাজার ২০০ কোটি মার্কিন ডলার, যা দেশের আর্থিক খাতের ৮৮ শতাংশ এবং মোট জিডিপির প্রায় ৫০ শতাংশ। এর মধ্যে ৭০ শতাংশ রয়েছে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের, ২৫ শতাংশ রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের এবং ৪ শতাংশ বিদেশি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে।
বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে ঋণের নামে অর্থ আত্মসাৎ, পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাংক অনুমোদন দেওয়ার মতো ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে চলমান। ২০২৩ সালে ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন করে এক পরিবারের সদস্যদের পর্ষদে থাকার মেয়াদ ১২ বছরে উন্নীত করায় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির তথ্য উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে আটটি ব্যাংকের পরিচালকদের মধ্যে পারস্পরিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৭০ কোটি মার্কিন ডলার, যা প্রমাণ করে ব্যাংক খাতে কীভাবে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম ইনস্টিটিউশনালাইজড হয়ে উঠেছে।
বিশ্বব্যাংক সতর্ক করে বলেছে, ব্যাংক খাতের অস্থিরতা কেবল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করে না, বরং বিনিয়োগকারীদের আস্থা হ্রাস করে এবং জিডিপির প্রায় ৭ শতাংশ পর্যন্ত বার্ষিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭০ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত বিশ্বের ১৫১টি ব্যাংকিং সংকট বিশ্লেষণ করে এমনটাই উঠে এসেছে। সংস্থাটি মনে করে, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত করে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে এই উদ্যোগকে কার্যকর করতে হলে বিশ্বব্যাংকের সুপারিশ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও কার্যকর নীতিনির্ধারণ প্রয়োজন। বিশ্বব্যাংক জোর দিয়ে বলেছে, ব্যাংকিং খাতের সংকট মোকাবিলায় যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে, অর্থনৈতিক ক্ষতির মাত্রা ততই হ্রাস করা সম্ভব হবে।