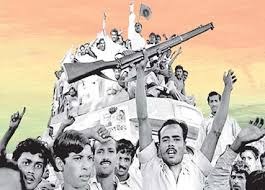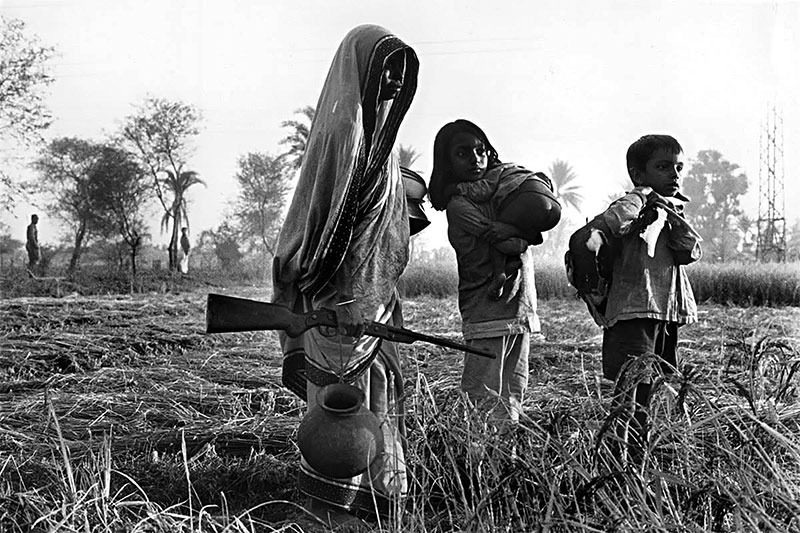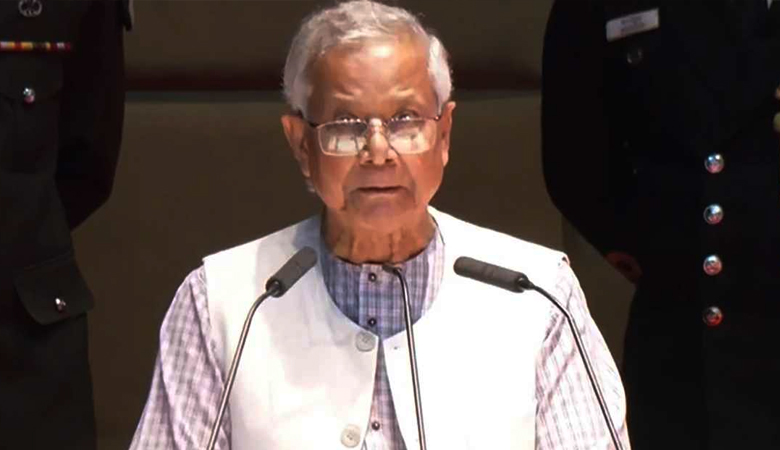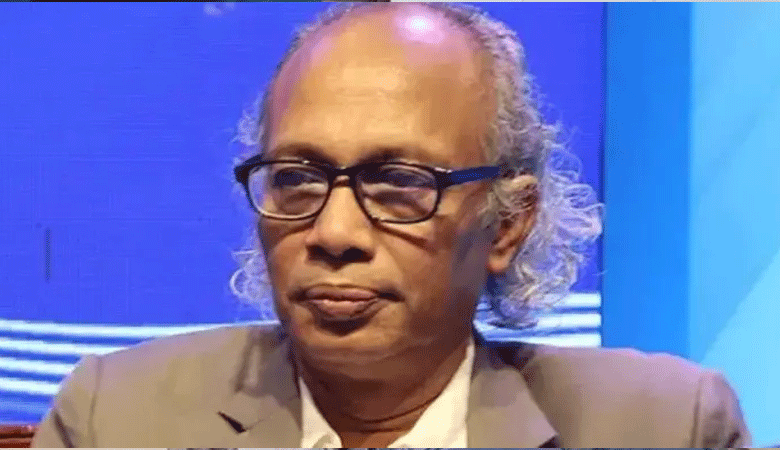- সুস্মিতা সরকার শুভ্রা
স্বাধীনতার ৫৩ বছর পেরিয়ে এলেও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও মুখস্থনির্ভরতা, পরীক্ষাকেন্দ্রিকতা এবং বাস্তবতাবিমুখ পাঠ্যক্রমের ফাঁদ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। অথচ বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন দক্ষতাভিত্তিক, চিন্তাশীল ও সৃজনশীল শিক্ষা।
১৯৭৪ সালের প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের চলমান বিতর্কিত শিক্ষাক্রম সংস্কার পর্যন্ত নানা চেষ্টা সত্ত্বেও কাঠামোগত দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।
স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে প্রথম শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য ছিল সবার জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করা। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর, সর্বস্তর থেকে শিক্ষা সংস্কারের দাবি উঠে আসে। এর পেছনে অবশ্য কারণ ছিল ইংরেজ শাসন আমল ও পাকিস্তান আমলের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা বাংলাদেশের জনগণের মানোন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই, বাংলাদেশের জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করতে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের দিকে জোর দেওয়া হয়। যদিও এই শিক্ষানীতি জোর দিয়েছিল দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নতির দিকে। যা বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে মুখস্থনির্ভরতা থেকে মুক্তি দিত। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে, শিক্ষানীতি সংসদ কর্তৃক পাসই হতে পারেনি। এর ফলে, মুখস্থবিদ্যার বেড়াজাল থেকে জাতি বের হতে পারেনি।
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা মুখস্থনির্ভর হওয়ার
পেছনে একটি বড় কারণ হচ্ছে পরীক্ষার কাঠামো।
প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার্থীরা
বিশ্লেষণ কম করে এবং মুখস্থ বেশি করে।
আর পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করাই থাকে শিক্ষার্থীদের মূল লক্ষ্য।
ওই সময়ের (১৯৭৫-১৯৯৯) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতি প্রথমদিকে পাঠ্যবই নির্ভর হলে ও পরবর্তীতে গাইড বই নির্ভর হয়ে পড়ে। এমনকি কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট শিক্ষকগণও গাইড বইয়ের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং পূর্ববর্তী বোর্ড প্রশ্নের ওপর বিশেষ জোর দেন। ৯০-এর দশকের শেষের দিকে ‘কমন পড়া’ নামক এক ধরনের ট্রেন্ড শুরু হয়ে যায়। পরীক্ষার্থীরা কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্ন মুখস্থ করত এবং তারা অনেকেই প্রত্যাশামাফিক ফলও পেত। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, গণিত পরীক্ষাও শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করেই দিত। যেখানে কিছু প্রশ্ন মুখস্থ করেই ভালো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে সৃজনশীল ও দক্ষতাভিত্তিক জ্ঞানচর্চার প্রতি চাহিদা কম থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু কী!
২০০৩ সালে আবারও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারে নতুন করে শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। এসময় একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের কথা বলা হয় যেন ইংরেজি, জেনারেল ও মাদ্রাসা মিডিয়ামের ব্যবধান কমিয়ে একধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা যায়। কিন্তু এটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ প্রতিটা কারিকুলামই ভিন্ন। তৎকালীন শিক্ষা কমিশন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার ও পাঠ্যক্রম সংস্কারের সুপারিশ করলেও সংসদে এই শিক্ষানীতিটিও পাস হয়নি।
এই বাস্তবতায় গুরুতর একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে চলে আসে-স্বাধীনতার ৩২ বছর পরও কেন দেশে কোনো শিক্ষানীতি পাস হয়নি! শুধু শিক্ষা কমিশনই বারবার গঠিত হয়, কিন্তু নীতি বাস্তবায়িত হয় না। কিছু পরিবর্তন হয়নি, তা নয়। তবে, ছিল না কোনো একক নীতি। এর পেছনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দায়ী আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, শাসনব্যবস্থার অস্থিরতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। একটি সরকার যখন শিক্ষানীতির খসড়া করে, পরবর্তী সরকার তা রাজনৈতিক কারণে উপেক্ষা বা বাতিল করে। তাছাড়া, যেখানে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, সেখানে শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারে না রাখাটা যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ। বরং, পরীক্ষা পদ্ধতির কাঠামো, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, গাইড বই নির্ভর ও সাজেশনভিত্তিক পড়াশোনা, কোচিং সংস্কৃতি, ভালো ফলাফলের জন্য সামাজিক ও পারিবারিক চাপ শিক্ষার্থীদের মুখস্থবিদ্যার প্রতি ধাবিত করে। এটি একটি বড় কারণ, যার জন্য আমরা আজও বৈশ্বিক দৌড়ে বারবার পিছয়ে পড়ছি।
বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিই ছিল স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে গৃহীত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি। ওই সময় সবার জন্য শিক্ষার পরিবর্তে সবার জন্য গুণগত শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হয়। মুখস্থনির্ভর পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়। তবে বাস্তবায়ন কতটুকু হবে, সেটা নিয়ে ছিল ধোঁয়াশা। সৃজনশীল পরীক্ষা কাঠামো শিক্ষকদের কাছে ততটা পরিচিত ছিল না। সেজন্য প্রয়োজন ছিল পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ। সেটা যথেষ্ট পরিসরে না পাওয়ার ফলে, সৃজনশীল পরীক্ষা কাঠামোও মুখস্থনির্ভর হয়ে পড়ে। তাছাড়া, ওইসময়, বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রতিও বেশ জোর দেওয়া হয়। তবে আবারও পিছিয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। এছাড়াও রয়েছে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা। তবে এটিই মুখ্য কারণ কী! কথায় আছে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। যেখানে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো শিক্ষাব্যবস্থার ওপর জোর দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের দেশে শিক্ষার গুরুত্ব এখনও গৌণ।
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা মুখস্থনির্ভর হওয়ার পেছনে একটি বড় কারণ হচ্ছে পরীক্ষার কাঠামো। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ কম করে এবং মুখস্থ বেশি করে। আর পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করাই থাকে শিক্ষার্থীদের মূল লক্ষ্য। কারণ ভালো ফলাফল করলে ভালো চাকরি পাবে। আর বাইরের দেশে পড়তে যাওয়ার জন্যও ভালো সিজিপিএ প্রয়োজন। এজন্য জানার ও শেখার আগ্রহের তুলনায়, ভালো নম্বর পাওয়ার প্রতি ঝোঁক বেশি। যা সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করছে এবং মুখস্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থাকে তরান্বিত করছে।
পাশাপাশি, আমাদের চাকরির পরীক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় অংশ মুখস্থনির্ভর। যদি বিসিএস পরীক্ষার দিকে লক্ষ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রিলিমিনারি ও রিটেন বেশিরভাগই মুখস্থনির্ভর। ব্যাংক, সরকারি সংস্থা ও বিভিন্ন কমিশনের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ও লিখিত পরীক্ষাগুলোর কন্টেন্টও বেশিরভাগই মুখস্থধর্মী-বিশ্লেষণধর্মী বা সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন কম। এজন্য দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা বিভাগীয় পড়াশোনার থেকে চাকরির পড়া বেশি পড়ে। আর তা শুরু করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষ থেকেই। তাহলে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানার্জন কীভাবে হবে!
যদিও বেসরকারি ব্যাংকগুলো বিশ্লেষণধর্মী বা সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন এখন পরীক্ষার মধ্যে রাখছে। মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও দক্ষতা যাচাইয়ের চেষ্টা করছে। কিন্তু সেটা কি আদৌ পর্যাপ্ত? অনেক চাকরিদাতাই অভিযোগ করছেন, তারা দক্ষ প্রার্থী পাচ্ছেন না। এটা খুবই হতাশাজনক! প্রায় ১৬/১৭ বছর পড়াশোনা করার পর যদি নিজেকে দক্ষ করে তোলা না যায়, তাহলে সেটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ করে। আর এভাবে চলতে থাকলে, বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলানো কি আদৌ সম্ভব!
বহির্বিশ্বের কথা বাদই দিলোাম! আমরা নিজেরাই কি আদৌ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখতে পারছি? যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো, তারা অনেকেই নিজেদের সন্তানদের বিদেশে পড়াচ্ছেন। চিকিৎসাক্ষেত্রেও আমরা বিদেশি ডিগ্রিকে বেশি মূল্যায়ন করি। একজন একাডেমিশিয়ান বা গবেষকের ক্ষেত্রেও আমরা খোঁজ নেই-তার ইউরোপ বা আমেরিকা থেকে পিএইচডি আছে কিনা। অথচ আমাদের দেশেও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা নিজেরা আমাদের দেশের ডিগ্রিধারীদের মূল্যায়ন কতটুকু করি? যখন আমরা নিজেরাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখতে পারি না, তখন বহির্বিশ্ব কেন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেবে?
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখতে পারছি না কেন? এর প্রধান কারণ, মুখস্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা এবং নম্বরের প্রতি শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ঝোঁক। এখানে শেখার থেকে নম্বর পাওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরো একটি বড় সমস্যা হলো, চাকরির সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ কমে গেছে। আজকাল দেখা যায়, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে অনেকেই ব্যাংকে চাকরি করছেন।
এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে দক্ষ ব্যক্তির যথাযথ মূল্যায়ন হবে কীভাবে? অনেক চাকরিপ্রার্থী অভিযোগ করেন, তারা যোগ্য হয়েও চাকরি পাচ্ছেন না, তাই বাধ্য হয়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। এটাও একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, চাকরির শূন্যপদের তুলনায় প্রার্থীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। এছাড়া মেধা পাচারের প্রবণতাও বাড়ছে। অনেক দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষার্থীই বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন এবং সেখানেই ভালো কাজ করছেন। ওই দেশের হয়ে অবদান রাখছেন। কিন্তু এতে করে আমাদের দেশের অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। এভাবে আর কতদিন চলবে? কীভাবে আমরা এই পরিস্থিতি থেকে বের হবো?
চাকরির বাজারে দক্ষতার সঙ্গে মেলাতে না পারা, যোগ্যদের অবমূল্যায়ন, আর গবেষণায় বিনিয়োগের ঘাটতির কারণে আমরা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় প্রতিনিয়ত পিছিয়ে পড়ছি। প্রযুক্তি কিংবা উদ্ভাবনের কোনোদিকেই আমরা অগ্রসর হতে পারছি না। নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে নতুন করে কোনো শিল্প গড়ে তুলতে পারছি না, কারণ দক্ষ জনশক্তির অভাব দিন দিন প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন খাতে অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে। সরকার নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে, কিন্তু বাস্তবায়ন হচ্ছে না।
২০২৫ সালে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের কথা বলা হচ্ছে, পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু আবার পরিবর্তন হচ্ছে, তবে পরিবর্তন কতটা সৃজনশীল ও প্রযুক্তিনির্ভর হবে তা নিয়ে এখনো সন্দেহ রয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো, বারবার শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলেই কি সমাধান আসবে? সব পড়াশোনা কেন ডিগ্রির ওপর নির্ভর করবে? সবাইকে কেন স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে? দক্ষতা কি কেবল সনদে মাপা যায়? যেখানে বিশ্ব এই ধ্যানধারণা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে, সেখানে আমরা এখনো পুরোনো ব্যবস্থায় আটকে আছি। আমাদের এখনই কারিগরি ও বাস্তবমুখী দক্ষতা বাড়াতে সচেতন হতে হবে, অটোপাস ও মুখস্থনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং শিক্ষাকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। তবেই আমরা উন্নতির পথে এগোতে পারব এবং বৈশ্বিক দৌড়ে আর পিছিয়ে পড়ব না।
লেখক: গবেষক, কলামিস্ট