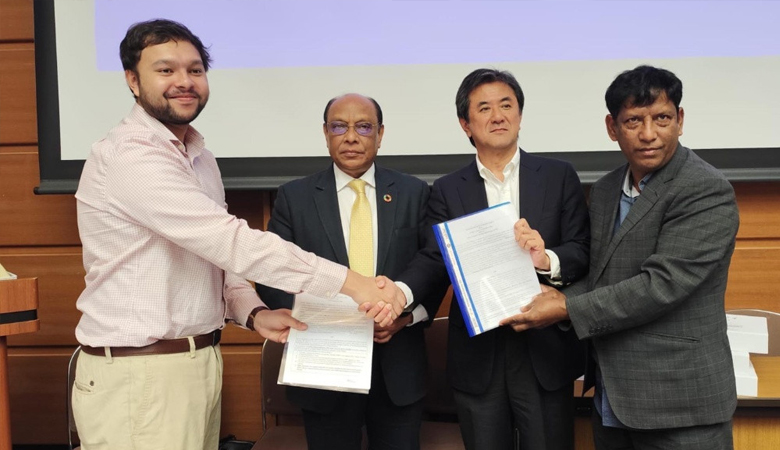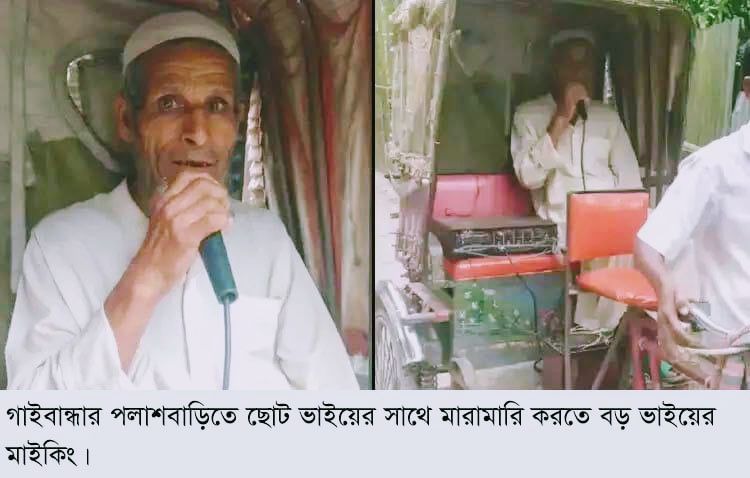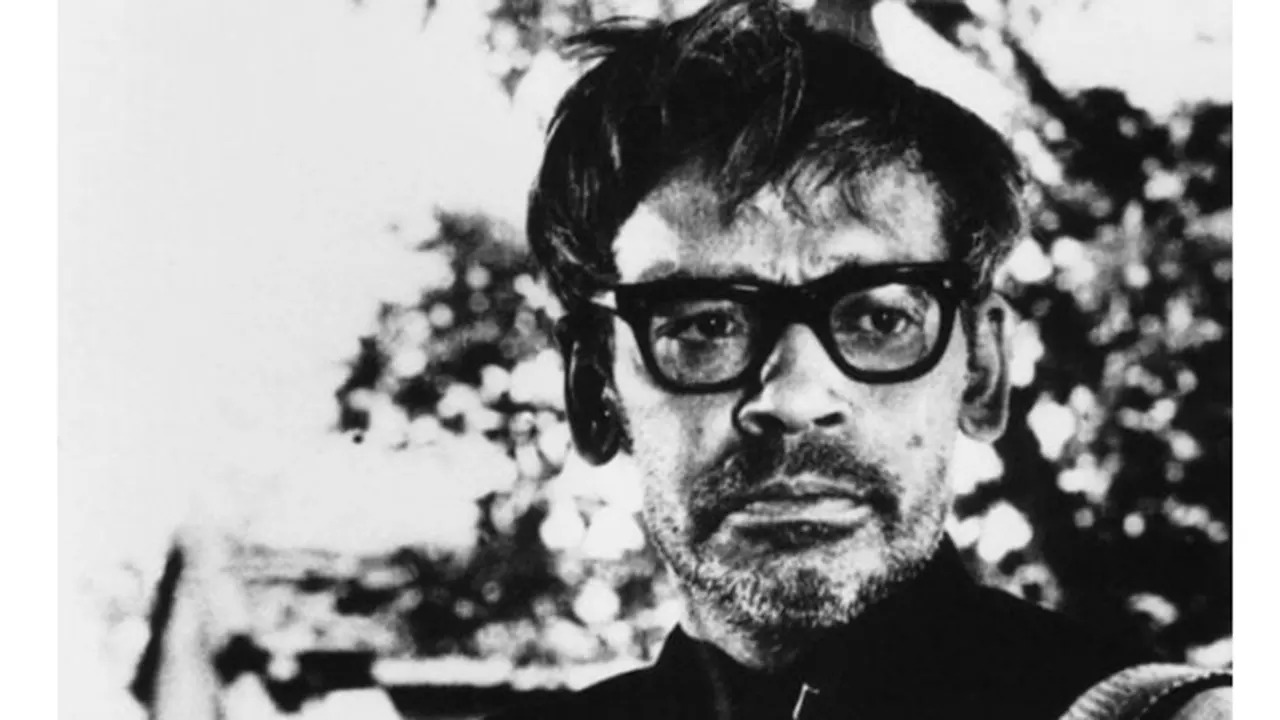দেবব্রত চক্রবর্তী বিষ্ণু : সব কিছুর শেষ আছে কিন্তু মানুষের অধিকারের শেষ নেই— এই সত্যটুকু শাসক কিংবা রাষ্ট্র পরিচালকরা ভুলে যান! স্বাধীনতা-উত্তর প্রতিটি রাজনৈতিক সরকারের শাসনামলেই জনঅধিকার কম-বেশি শাসকদের পদদলিত হয়েছে। কোনো কোনো অরাজনৈতিক সরকারের শাসনামলও এর বাইরে নয়। অসংখ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের দ্বিচারিতা-হীনস্বার্থবাদিতা-স্বেচ্ছাচারিতা-লুণ্ঠনসহ অজস্র নেতিবাচক কর্মকাণ্ডই তো দেশের সাধারণ মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে।
বলা হয়, রাজনীতি হলো জনকল্যাণের অপর নাম। রাজনীতিবিহীন যে কোনো সমাজ বদ্ধ জলাশয়ের মতো। রাজনীতির এত ব্যাপকার্থতার প্রভাব দেশে দেশে ভিন্ন, যদিও তা কাম্য নয়। কারণ রাজনীতির ইতিবাচক প্রভাব সমভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে এটাই তো কাঙ্ক্ষিত।
ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাজনীতিকদের একাংশ অনাচার-দূরাচার-কদাচারের চারণভূমি বানিয়েছেন এ দেশটাকে। যারা স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা-জনঅধিকারের কথা বলেন তারাও যেন পেছনের অধ্যায় ভুলে না যান। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার টানা ১৫ বছরে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংসের পাশাপাশি লুটেরাদের লুটপাটের গোপন লাইসেন্স দেওয়া এবং জনস্বার্থবিরোধী আরও অনেক কিছু করার পথ মসৃণ করেছিল। এটা যেমন সত্য, তেমনি এর আগের রাজনৈতিক সরকারগুলোর শাসনামলেও অনেক ক্ষেত্রেই জনবৈরী সিদ্ধান্ত কিংবা কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়েছে এবং দুৰ্ভাগ্যজনকভাবে নির্বাচনের নামে তামাশা হয়েছে। বিনাবিচারে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। কদাচারের ক্ষেত্র তো তৈরি হয়েছে ধারাবাহিকভাবে।
ইতিহাসের পাতা ছিঁড়ে ফেললেই কি ইতিহাস মুছে যায়? বিচারহীনতার অপসংস্কৃতি তৈরি হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। মানবতাবিরোধী কিংবা জীবনবৈরী যেসব ঘটনা এখনও ঘটে চলেছে, তাতে জনমনে প্রশ্নের সারি দীর্ঘ হচ্ছে। জননিরাপত্তা নিয়ে তো রয়েছে কঠিন প্রশ্ন। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষের বঞ্চনার মর্মন্তুদ ইতিহাসও নতুন নয়। তাদের ক্ষতের ওপর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে বারে বারে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যেসব জীবনবৈরী ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটেছে ওই সবই অনভিপ্রেত। গণতন্ত্রের জন্য সাম্য যে অপরিহার্য শর্ত এ কথা যেমন লেনিন বলেছেন, তেমনটা আব্রাহাম লিংকনও বলেছেন, আরও স্পষ্ট করে, আরও জোর দিয়ে বলেছেন লিংকন।
সর্বজনের রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের জনগুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়টি বাংলাদেশের বাস্তবতায় নিছক রাজনৈতিক বাকোয়াজ ছাড়া যে আর কিছু যে নয় এর নজির আছে অনেক। এই বাস্তবতায় সঙ্গতই প্রশ্ন দাঁড়ায়, অধিকারের সমতল ভূমি নিশ্চিত করা কি এত সহজ? এ নিয়ে যত আওয়াজ এ যাবৎ আমরা শুনেছি এর ন্যূনতম কিছু কি বাস্তবায়নের আয়োজন কখনও দৃশ্যমান হয়েছে? ৫৩ বছরের রক্তস্নাত বাংলাদেশে বাড়ি, চিহ্ন, প্রতীক ভেঙে নেতিবাচক অনেক কিছু করেই রাগ তো কম দেখানো হয়নি। মনে রাখা প্রয়োজন, এভাবে ফ্যাসিবাদের যবনিকাপাত ঘটে না বরং ফ্যাসিবাদের পুনঃজন্ম কিংবা পুনরুৎপাদনই হতে থাকে এবং রাজনীতির গায়ে কালিমা লেপন হয়।
দুর্ভাগ্যক্রমে স্ববিরোধিতা যে দেশের রাজনীতির অঙ্গভূষণ হয়ে গেছে, ওই দেশে শুভ কিছুর প্রত্যাশা দূরাশার নামান্তর। অধিকার ও জীবনবৈরী কোনো অভিঘাতই মেনে নেওয়া যে কোনো মানবিক মানুষের পক্ষে দুরূহ। বিচারহীনতার অপসংস্কৃতির নজিরও আমারা কম দেখিনি। এখন প্রশ্নও দাঁড়ায়, সর্বজনের রাষ্ট্র গড়ার যে প্রত্যয় ছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার তা কি রাজনীতিকদের অনিচ্ছার কারণেই হারিয়ে যায়নি? অথচ এ দেশের রাজনীতির অর্জন তো কম নয়। কেন ঘটল এই অর্জনের বিসর্জন? আজকের প্রেক্ষাপটে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর সন্ধান জরুরি নয় কি?
রাষ্ট্র কেন আজও সর্বজনের হয়নি তা অন্তহীন প্রশ্ন হয়ে থাকতে পারে না। রাষ্ট্র ও সমাজের বিকাশে স্বচ্ছ রাজনীতি ও রাজনীতিকদের দায়বদ্ধতার কোনো বিকল্প নেই। এ দুই ক্ষেত্রেই ব্যাপক ঘাটতি জিইয়ে রেখে রাজনীতির নানা মেরুকরণ হয়েছে। অপকৌশলে রাজনীতিকরা রাজনীতিকে শ্রীহীন করেছেন। এই অভিযোগ ঢালাও না হলেও অনেকাংশেই তো সত্য। নীতিনির্ধারক অনেকেরই উচ্চারণসর্বস্ব অঙ্গীকার-প্রত্যয় এই প্রশ্নও দাঁড় করিয়েছে, এই কি জনকল্যাণের রাজনীতি? স্বাধীনতার পর সঙ্গত কারণেই আশা জেগেছিল, রাজনীতি সঠিক পথে হাঁটবে। কিন্তু ওই আশা বারবার হোঁচট খেয়েছে। এ কারণেই রাষ্ট্র সর্বজনের হয়নি আজও। এই তমসা কাটানোর দায় রাজনীতিকদের ওপর ছিল। কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন তো করেনইনি বরং রাজনীতিকে আমলাতন্ত্রের বৃত্তবন্দী করার পথটাও সুগম করেন।
আমলাতন্ত্রকে চেনা যায় না, এ যেন দৃশ্যের বাইরে অদৃশ্য শক্তি— যে শক্তির প্রভাব আমাদের রাষ্ট্রে অনেক বেশি। আমরা প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাই। কিন্তু এর জন্য তো সবার আগে জরুরি গণতান্ত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতি। দুঃখজনক হলেও সত্য, রাজনীতিকরা কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় তা অনুশীলন করতে পারেননি। ইতিহাস সাক্ষী, আমলাতন্ত্র নষ্ট করতে পারঙ্গম। আমাদের অবস্থাটা যেন এমন— বাইরে বন্দনা অন্তরে হনন। আমাদের অতীত ইতিহাসে মীরজাফর ছিলেন। ছিলেন উমিচাঁদ এবং জগৎশেঠও। দেশের স্বার্থ তারা বিক্রি করে দিয়েছিলেন বিদেশিদের কাছে। কিন্তু সিরাজ-উদ-দৌলাও ছিলেন। তার সম্পর্কে যত কথাই শোনা যাক না কেন, তিনি যে খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিলেন এ নিয়ে তো বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। ক্ষমতার দণ্ড হাতে নিয়ে তিনি বিদেশিদের হাতে দেশ তুলে দেয়ার চেষ্টা করেননি। গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগসহ আমাদের রাজানীতিকদের আরও অনেকের বিরুদ্ধেই দেশের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের বহু গুরুতর অভিযোগ আছে।
টাকার লোভ, ক্ষমতার লোভ অনেককেই ভয়ঙ্করভাবে কদাচারী করে তুলেছে এবং এর নজির কম নেই। সরকার এসেছে, সরকার গেছে এসব কদাচারের কোনো প্রতিবিধান হয়নি। কেন হয়নি, এও যেন এক অন্তহীন প্রশ্ন। আবারও বলি, আমরা দেখেছি প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক মেরুকরণের পেছনে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থের সমীকরণ হয়েছে। এমন গুরুতর ব্যাধি যে দেশের রাজনীতির অনুষঙ্গ হয়ে গেছে ওই দেশে সর্বজনের অধিকার নিশ্চিত করা কি এত সহজ? আমাদের রাজনীতিকদের অনেকের দেশপ্রেম নিয়ে নানা কথা আছে এবং সেসব কথা যে অমূলক নয় এও, অনস্বীকার্য।
মনে রাখা জরুরি, জনগণের মুক্তির অনিবার্য শর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকতা। এর অর্থ হলো, গণতান্ত্রিক সরকারে জনগণের অংশগ্রহণ, জনগণের দ্বারা ও জনগণের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত সরকার। রেমন্ড গারফিল্ড গেটেল, অধ্যাপক গেটেল নামে সমধিক পরিচিত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, “যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগে অংশ নেওয়ার অধিকারী তাই গণতন্ত্র।” কিন্তু আমাদের দেশে দুৰ্ভাগ্যজনকভাবে এরও ব্যত্যয় ঘটেছে বার বার। রাষ্ট্র সর্বজনের হওয়ার ক্ষেত্রে এও অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর দায় কি রাজনীতিকরা এড়াতে পারেন?
রাষ্ট্রের মালিক জনগণ এটা আমাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি। জনগণ কি প্রকৃতার্থে রাষ্ট্রের মালিক হতে পেরেছে? রাষ্ট্র হোক হোক সবার— এই প্রত্যাশা এখনও জারি আছে, জারি থাকবেও। বহুমুখী সংস্কারের যে কার্যক্রম বর্তমানে চলছে এই সংস্কারের দাবি সমস্বরে না হলেও ক্ষীণকণ্ঠে এর আগেও উঠেছে। কিন্তু তা হালে পানি পায়নি। সংস্কার এক-দুই দিনের বিষয় নয়— সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। সবার আগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার দরকার। রাজনীতি যদি পরিশুদ্ধ হয়, রাজনীতি যদি সঠিক পথে হাঁটে তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভালো হলে সার্বিক অবস্থা এমনিতেই ভালো হবে। সর্বজনের রাষ্ট্র গড়ার পথও মসৃণ হবে।
জাতীয় ইস্যুতে রাজনৈতিক ঐক্যের কথাও বহুবার আলোচনায় এসেছে কিন্তু আকাঙ্ক্ষার তো ঐক্য আছে বলে কখনও মনে হয়নি। ঐক্যর ভিত্তি তো সবার আগে হবে আকাঙ্ক্ষা-ব্যবস্থা ও কর্ম। শাসকশ্রেণি বারবার আলাদা হয়ে যায় শাসিতশ্রেণি থেকে। অতীতে আমলাতন্ত্রের শক্তির বিষয়টি বহুবারই কদর্যভাবে দৃশ্যমান হয়েছে এবং এই শক্তির ওপরই নির্ভর করেছে সরকারের জীবন-মরণ। বৈষম্য নিরসনের একদফা দাবির সড়ক যদিও এখন অনেক চওড়া কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফল কবে নিশ্চিত হবে এও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। বৈষম্য আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করছে। একে রোখা জরুরি যত দ্রুত সম্ভব এবং এ জন্য রাজনৈতিক দৃঢ়তা-অঙ্গীকার জরুরি। সর্বজনের রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে এর বিকল্প কিছু আছে কি!
লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট