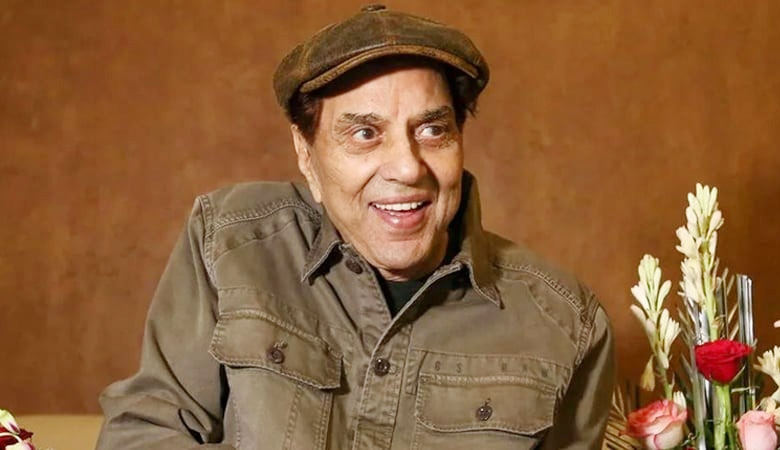আমীন আল রশীদ : অর্থবছরের মাঝামাঝি প্রায় একশো পণ্যের ওপর মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা ফোরামে সরকার সমালোচনার মুখে পড়ায় কিছুটা পিছু হটেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআর। রেস্তোরাঁসহ কিছু পণ্য ও সেবায় ভ্যাট আগের মতোই বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে। গত ১৬ জানুয়ারি অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, সাধারণ মানুষের ওপড় প্রভাব ফেলে এমন কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এবং ওষুধ ও রেস্তোরাঁর মতো খাতে সম্প্রতি বৃদ্ধি করা ভ্যাটের হার পর্যালোচনা করছে সরকার। তিনি বলেন, ‘সরকার ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার(আইএসপি), ফোন, আমদানি করা বিদেশি জুসের মতো কিছু পণ্যের ওপর ভ্যাট বৃদ্ধি করেছে যা খুব বেশি লোক কেনে না এবং এগুলোর তেমন প্রভাব পড়ে না। তা সত্ত্বেও সরকার কিছু পণ্যের ওপর ভ্যাট না বাড়ানোর বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করছে।
প্রশ্ন হলো, বছরের এই সময়ে এসে কেন সরকারকে ভ্যাট বাড়ানোর মতো একটি অজনপ্রিয় উদ্যোগ নিতে হলো যখন এমনিতেই দেশের মানুষ নানামুখী আর্থিক চাপে রয়েছে; যখন অনেক শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে প্রচুর মানুষ বেকার হয়েছেন; যখন অনেক প্রতিষ্ঠানে খরচ কমানোর জন্য কর্মী ছাঁটাই করা হচ্ছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠানে হয় বেতন বন্ধ হয়ে গেছে না হয় বেতন অনিয়মিত হয়ে গেছে? গত এক দশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির মধ্যেই যেখানে কাঙ্ক্ষিত হারে কর্মসংস্থান হয়নি; যখন দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছাড়িয়েছে দুই অংকের ঘর-এমন পরিস্থিতিতে ওষুধ, এলপি গ্যাস, মোবাইলে ফোনের সিম কার্ডের মতো প্রয়োজনীয় পণ্যসহ শতাধিক পণ্য ও সেবায় আমদানি, উৎপাদন, সরবরাহ পর্যায়ে শুল্ক ও কর বাড়ানোর সিদ্ধান্তটি সরকার নিলো, তা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন আছে।
ভ্যাটের ইতিহাস: ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর (মূসক) হচ্ছে একটি পরোক্ষ কর। সহজ ভাষায়, কোনো ক্রেতা যখন কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় করেন, তার মূল্যের অতিরিক্ত যে কর তিনি দিয়ে থাকেন, সেটটিই হচ্ছে ভ্যাট বা মূসক। এই মূসক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার দায়িত্ব বিক্রেতার।
বাংলাদেশে ভ্যাট বা মূসক প্রথম চালু হয় ১৯৯১ সালের পয়লা জুলাই। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরামর্শে এটি চালু করা হয়। এর আগে বাংলাদেশে বিক্রয় কর চালু ছিল। ভ্যাট ব্যবস্থা চালুর মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়া সহজ, স্বচ্ছ ও কার্যকর করা। ভ্যাট আইন ১৯৯১-এর আওতায় প্রথমে কিছু নির্দিষ্ট খাতের ওপর কর আরোপ করা হয় এবং পরবর্তীতে এর পরিধি বাড়ানো হয়।
ভ্যাটের সুবিধা: ১. ভ্যাট একটি বহুমুখী কর ব্যবস্থা, যা দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
২. ভ্যাট পদ্ধতিতে প্রতিটি স্তরে কর আদায় হয়, ফলে এর কার্যকারিতা বেশি এবং কর ফাঁকির সুযোগ কম।
৩. সঠিক রেকর্ড ও হিসাব রক্ষার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা সহজ।
৪. ভ্যাট অনেক দেশে প্রচলিত, তাই এটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থাকে মানানসই করে তোলে।
ভ্যাটের অসুবিধা: ১. ভ্যাট একটি পরোক্ষ কর, যা পণ্য ও সেবার দামে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটি ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাইকে সমানভাবে প্রভাবিত করে। ফলে নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর বেশি চাপ পড়ে।
২. ভ্যাট সংক্রান্ত নীতিমালা ও কার্যক্রম অনেক সময় জটিল, যা ছোট ও মাঝারি ব্যবসার জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।
৩. ভ্যাট নিবন্ধন, রিটার্ন দাখিল এবং কর সংগ্রহ প্রক্রিয়া ব্যবসার জন্য অনেক সময় সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল হতে পারে।
৪. সঠিক তদারকি না থাকলে ভ্যাট ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বাড়ে।
সাম্প্রতিক বিতর্ক: গত ২ জানুয়ারি ‘মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫’ এবং ‘দ্য এক্সাইজ অ্যান্ড সল্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫’ নামে এ দুটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। তার আগে পয়লা জানুয়ারি অন্তর্র্বতী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে মূল্য সংযোজন কর-ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক বাড়াতে এনবিআরের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। অধ্যাদেশ জারির পরপরই এটা কার্যকর হয়ে গেছে।
শুরুতে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ দাবি করেছিলেন, ভ্যাট বাড়লেও তাতে ভোক্তার অসুবিধা হবে না। কারণ তাকে বাড়তি মূল্য গুণতে হবে না। এনবিআরের বিজ্ঞপ্তিতেও দাবি করা হয়েছিল যে, ভ্যাট বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত মূল্যস্ফীতিতে প্রভাব ফেলবে না। যদি তা-ই হয় তাহলে সমালোচনার মুখে কেন অর্থ উপদেষ্টা পরে বললেন যে, কিছু পণ্যের ভ্যাট আগের মতোই থাকবে বা এনবিআরও কেন সমালোচনার মুখে সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটলো? তাছাড়া ভ্যাট বাড়ানো হলে ভোক্তার ওপর তার প্রভাব পড়বে না বা ভোক্তাকে বাড়তি মূল্য দিতে হবে না-এটি কতখানি যৌক্তিক, সে প্রশ্ন তোলাই থাকলো।
বলা হচ্ছে সরকার আর্থিক পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে বলে ভ্যাট বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। অথচ একই সময়ে সরকারি কর্মচারীদের মহার্য্য ভাতার ঘোষণা দিয়েছে। তার মানে সরকারি কর্মচারীদের হাতে রাখা তথা তাদের তোষণ করার এই নীতি থেকে নির্দলীয় সরকারও মুক্ত হতে পারেনি! যে প্রশাসন ও পুলিশের লোকের ওপর সাধারণ মানুষের রাগ ক্ষোভ সবচেয়ে বেশি; জুলাই অভ্যুত্থানে যাদের ব্যাপারে আন্দোলনকারীদের তীব্র অভিযোগ ছিল-অর্থনৈতিক সংকটের ভেতরেও তাদের জন্য মহার্ঘ ভাতা ঘোষণাটি স্পষ্টতই সরকারের স্ববিরোধী আচরণ।
যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন: গত ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে নানা কারণেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বেসামাল। সম্প্রতি শীতকালীন সবজির সরবরাহ ভালো হওয়ায় সবজির দাম সাধারণের ক্রয়সীমার নাগালে এলেও গত আগস্টে অন্তর্র্বতী সরকারের দায়িত্ব নেয়ার পরে দুই তিন মাস পর্যন্ত সবজির দামও ছিল আকাশচুম্বি। পেঁয়াজের দাম তো বটেই। সয়াবিন তেলের দামও সম্প্রতি বেড়েছে। মাছ-মাংসের দাম অনেক বেশি না বাড়লেও যেহেতু মানুষের আয় বাড়েনি বরং অনেকের আয় কমে গেছে, এমনকি অনেকের উপার্জন বন্ধও হয়ে গেছে; তারওপর টিসিবির ট্রাক সেল কার্যক্রম বন্ধ-সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষ মনে করেছে নতুন করে আরোপিত এই কর তাদের ওপর নতুন আরেকটি বোঝা চাপাবে। কেননা ভ্যাট বৃদ্ধির কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। তাতে গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্তরা বেশি চাপে পড়বে। ব্যবসায়ীদের দাবি, ভ্যাট বাড়ানোর ফলে তাদের উৎপাদন খরচ এবং পণ্যের বাজার মূল্য বেড়ে যাবে-যা তাদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে ক্ষতি করবে।
রাজস্ব আদায়ের সহজ পথ: বস্তুত রাজস্ব আদায় বাড়াতে সরকার সবচেয়ে সহজ পথটি বেছে নিয়েছে। অথচ গণমাধ্যমের খবর বলছে, ১৮ কোটি লোকের দেশে এখনও ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষদের ৮৭ শতাংশ কোনো ধরনের আয়কর দেন না। দেশের মাত্র ১৮ লাখ মানুষ কর দেন। তাদের মধ্যে ১০ লাখ সরকারি চাকরিজীবী এবং বাকিরা অন্যান্য চাকরিতে নিয়োজিত। ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্তদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা ৯ থেকে ১০ লাখ। অথচ এই সংখ্যাটি হওয়ার কথা প্রায় ৮০ লাখ। সুতরাং করযোগ্য আয় থাকার পরেও এত কম লোকের আয়কর দেয়াটা শুধু বিস্ময়করই নয় বরং লজ্জারও। এটি স্পষ্টতই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অদক্ষতা। কেননা, যে দেশে শত কোটি টাকার মালিক পাড়ায় মহল্লায়-সেই দেশে এত কম লোকের আয়কর দেয়াটা স্বাভাবিক কথা নয়। তার আয়মানে সরকার যে খাত থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় করতে পারতো সেখানেই তার ব্যর্থতা সবচেয়ে বেশি। বেশি বলে সে রাজস্ব ঘাটতি মেটানোর জন্য সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত পয়সায় কেনা পণ্যের ওপর ভ্যাট বাড়ায়।
করণীয় কী? ১. করের পরিধি বাড়ানো: ভ্যাটের পরিধি বাড়ানোর পরিবর্তে আয়কর আদায়ে মনোযোগ দেয়া দরকার। করযোগ্য লোকদের করের জালে নিয়ে আসা দরকার। কর ফাঁকির সকল পথ বন্ধ করা দরকার। কর প্রদান পদ্ধতি সহজ ও জনবান্ধব করে করের ব্যাপারে মানুষকে আগ্রহী করে তোলা দরকার।
২. প্রগতিশীল কর কাঠামো: নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর চাপ কমিয়ে ধনী ও করপোরেট প্রতিষ্ঠান থেকে বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করা প্রয়োজন।
৩. ডিজিটালাইজেশন: ভ্যাট প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজ করে কর সংগ্রহ সহজ ও স্বচ্ছ করা দরকার।
৪. সুবিধা দেওয়া: ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ভ্যাট ছাড় বা হ্রাসকৃত হার প্রবর্তন করা।
৫. সচেতনতা বৃদ্ধি: ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের মধ্যে ভ্যাট বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালানো দরকার।
পরিশেষে: সম্প্রতি অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য রাজধানীতে একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, অন্তর্র্বতী সরকার প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সেক্টরের সংস্কারে বেশি গুরুত্ব দিলেও অর্থনৈতিক সংস্কারে সেভাবে মনোযোগ নেই। অন্তর্র্বতী সরকারের একজন ঘনিষ্ঠ অর্থনীতিবিদও প্রকাশ্যে এই যে মন্তব্যটি করলেন, তার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে অর্থনৈতিক সংস্কার বা ভেঙেপড়া অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে যে ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল, সরকার তা নিচ্ছে না। কেন নিচ্ছে না বা নিতে পারছে না-সেটি বিরাট প্রশ্ন। অথচ গত বছরের ৮ আগস্ট এই সরকার দায়িত্ব নেয়ার পরে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দটি হচ্ছে ‘সংস্কার’।
অর্থনীতি যদি ঠিক না থাকে; সাধারণ মানুষের জীবন যদি কঠিন থেকে কঠিনতর হয়; ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তারা যদি ভরসা না পান, যদি তারা ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে থাকেন, তাহলে সেই সংস্কারটি হবে কী করে বা সেই সংস্কারের ফল কে ভোগ করবে?
আগের সরকারের আমলে যেমন বলা হতো আগে উন্নয়ন তারপর গণতন্ত্র-তার একটি অর্থনৈতিক দিক ছিল। কিন্তু এখন যদি বলা হয় আগে বিচার তারপরে সংস্কার, সেক্ষেত্রে অর্থনীতি আরও বেশি খাদের কিনারে চলে যাবে। জুলাই অভ্যুত্থানে যাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ রয়েছে, তাদের বিচার হতে হবে। কিন্তু সেই সাথে এটিও নিশ্চিত করতে হবে যে, বিচার ও সংস্কারের নামে দেশের মানুষ, বিশেষ করে স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষের জীবন যেন আগের চেয়ে খারাপ না হয়। যদি সেটি হয় তাহলে বিচারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠবে, তেমনি সংস্কারের ব্যাপারেও মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। মনে রাখতে হবে, এই সরকারের ব্যাপারে মানুষ নিরাশ হয়ে গেলে দেশ আরেকটি বড় সংকটে পড়ে যাবে-যা কারোরেই কাম্য নয়।
লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট