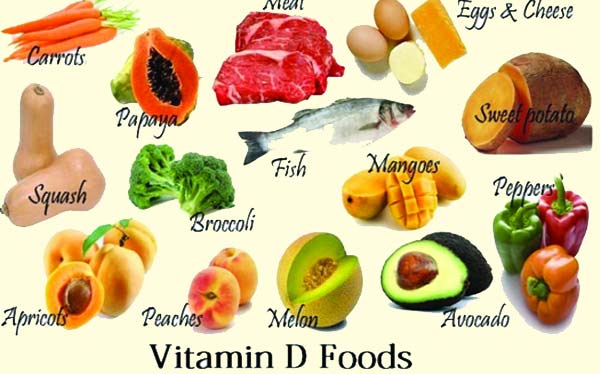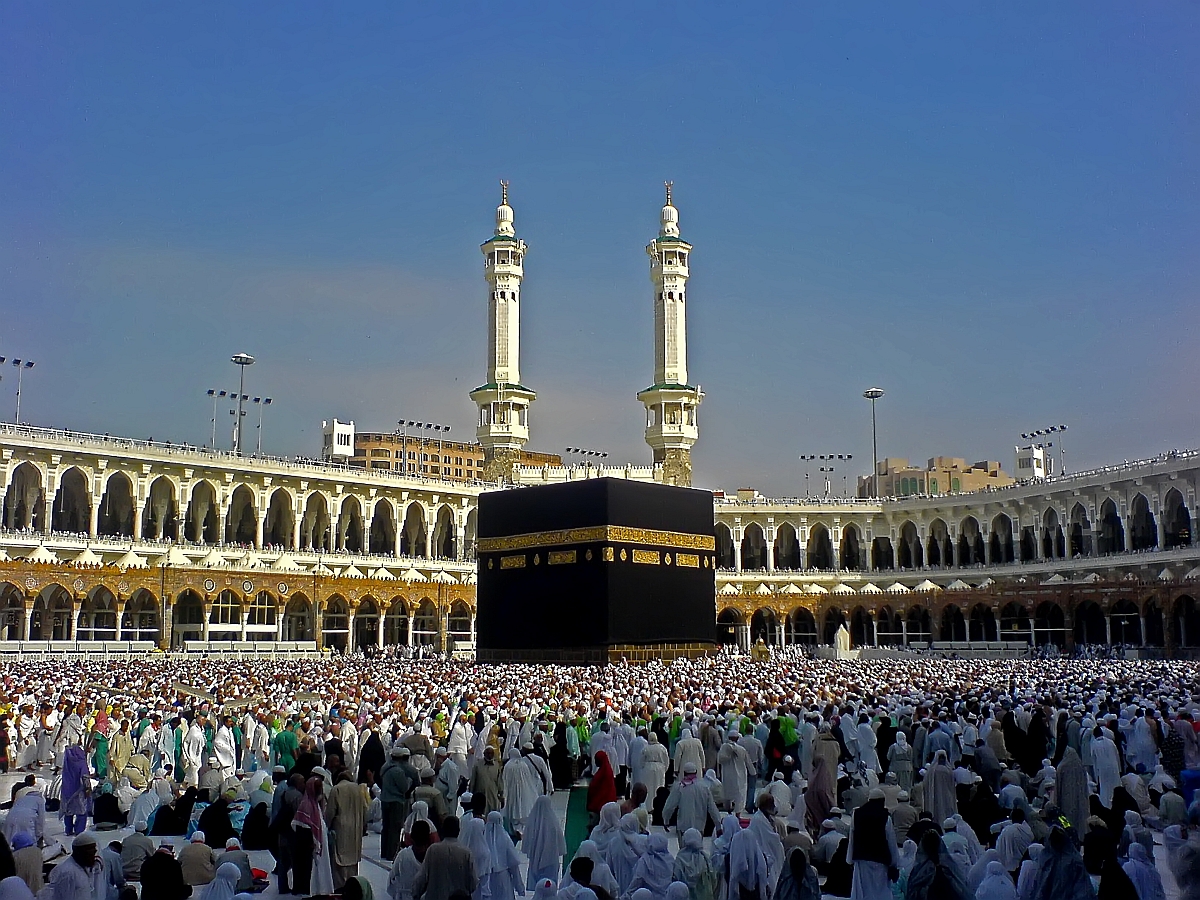- খালিদুর রহমান
কাজী কাদের নেওয়াজের ‘শিক্ষাগুরুর মর্যাদা’ কবিতায় দিল্লির বাদশাহ আলমগীরের সামনে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবনত রাজার সেই চিরন্তন প্রতিচ্ছবি আমাদের শিখিয়েছিল, শিক্ষকই রাজাধিরাজের ঊর্ধ্বে। কিন্তু আজ যেন সেই কাব্যিক সংবিধান উল্টে গেছে। শেখ হাসিনা হোন কিংবা মুহাম্মদ ইউনূস, যারাই ক্ষমতায় থাকুন না কেন, যখন শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য অধিকার নিয়ে রাস্তায় নামেন, তখন তাদের বলা হয় ‘বাধাদানকারী’। যারা প্রজন্ম গড়েন, তারাই আজ অবহেলিত বেতনভোগী মাত্র। রাষ্ট্রের বিলাসে অর্থের অভাব হয় না, কিন্তু শিক্ষকের প্রাপ্য সম্মান আর সামান্য ভাতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যেন সে রাজকোষ নিঃশেষ হয়ে যায়।
বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য স্তম্ভ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা আবারও রাজপথে নেমেছেন ন্যায্য দাবি বাস্তবায়নের আহ্বান জানাতে। এমপিওভুক্ত (গড়হঃযষু চধু ঙৎফবৎ) শিক্ষকরা বছরের পর বছর সীমিত আর্থিক সুবিধার মধ্যে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয় তাদের বাধ্য করেছে নিজেদের ন্যায্য দাবি তুলে ধরতে। বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির আবেদন এখন তাদের টিকে থাকার আর্তি হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই দাবি জানাতে গিয়ে লাঠিপেটার শিকার হয়েছেন শিক্ষকরা। তাদের যৌক্তিক আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করতে ব্যবহার করা হয়েছে জলকামান।
তাদের এই আন্দোলন কেবল টাকার জন্য নয়, বরং এটি বঞ্চনা, অবহেলা আর অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘশ্বাস। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু রাষ্ট্রের নীতিগত মনোযোগ ও সহানুভূতি তাদের প্রতি আজও সীমিত পর্যায়েই রয়ে গেছে।
তাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার নির্মম পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাদের প্রতিদিনের ক্ষুণ্নিবৃত্তির লড়াইয়ে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ২৬ হাজার ৪৪৭টি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩ লাখ ৮০ হাজার শিক্ষক এবং ১ লাখ ৭৭ হাজার কর্মচারী কর্মরত আছেন। অর্থাৎ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এক বিশাল অংশ সরাসরি এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভরশীল।
এই শিক্ষকরা সরকারের কাছ থেকে মূল বেতন ও কিছু সীমিত ভাতা পান। বর্তমানে বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক যোগদানকারী একজন সহকারী শিক্ষক এমপিও প্রকল্পের আওতায় মাসে ১২,৫০০ টাকা বেতন পান, যার ১০ শতাংশ অবসরভাতার জন্য কর্তন করা হয়। তারা মাসে মাত্র ১,০০০ টাকা বাড়িভাড়া, ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং উৎসব ভাতা হিসেবে মূল বেতনের ৫০ শতাংশ পান। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয় বাড়িভাড়া ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ১,৫০০ টাকা করার পরিপত্র জারি করেছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, এটি কি বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
ঢাকা কিংবা বিভাগীয় শহরে এখন একটি ছোট পরিবারের জন্য একটি সাধারণ ফ্ল্যাট ভাড়া দিতে হয় ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। অথচ একজন শিক্ষক যার মাসিক বেতন ১২,৫০০ থেকে ৪৪,০০০ টাকার মধ্যে, এবং তার বাড়িভাড়া ভাতা মাত্র ১,৫০০ টাকা। চিকিৎসা ভাতার ক্ষেত্রেও একই কষ্টকর অবস্থা। আজকাল ৫০০ টাকা দিয়ে কোনো হাসপাতালের সাধারণ চিকিৎসাও সম্ভব নয়।
উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তুলনা দূরে থাক, পাশের দেশগুলোতেও শিক্ষকরা তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো অবস্থায় আছেন। ভারতে একই ধরণের প্রাথমিক যোগদানকারী একজন সহকারী শিক্ষক মাসে অন্তত ২০,০০০ রুপি, পাকিস্তানে ৪০,০০০ রুপি এবং শ্রীলঙ্কায় ৩৫,০০০ রুপি বেতন পান। এই তুলনাই বলে দেয় আমরা শিক্ষকদের কোথায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি।
শিক্ষক সংগঠনগুলো সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে অনেকদিন ধরে। গত কয়েক মাস হল ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করছে দারা। শুরুতে মানববন্ধন ও প্রতীকী অনশন দিয়ে শুরু হলেও পরে তা রূপ নেয় অনির্দিষ্টকালের অবস্থান কর্মসূচিতে।
গত ১২ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা অবস্থান কর্মসূচি শুরু করলে পুলিশের লাঠিচার্জ, জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেডের ঘটনা ঘটে। এর আগে ১৩ অগাস্ট একই দাবিতে ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট’ প্রেস ক্লাবের সামনেই বিক্ষোভ সমাবেশ করেছিল।
তাদের দাবি তিনটি—
১. বাড়িভাড়া ভাতা মূল বেতনের ২০ শতাংশ নির্ধারণ করা,
২. চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি করা,
৩. সর্বজনীন বদলি ব্যবস্থা চালু করা।
কিন্তু এই দাবিতে সাড়া মেলেনি, বরং তাদের সামনে দাঁড়িয়েছে দমননীতি। প্রশ্ন জাগে, শিক্ষক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি এতটাই ঠান্ডা হয়ে গেছে?
বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত। ভোক্তা মূল্যসূচক অনুযায়ী ২০২৪ সালে মুদ্রাস্ফীতি প্রায় ৯ শতাংশে পৌঁছেছে। বাসাভাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও চিকিৎসা খরচ বেড়েছে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত।
অন্যদিকে সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বারবার সমন্বয় করা হলেও এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা থেকে গেছেন একই জায়গায়। সর্বশেষ ২০১৫ সালে তাদের বেতনভাতা কাঠামো হালনাগাদ হয়েছিল, তারপর আর কোনো পরিবর্তন হয়নি।
একজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক যেখানে বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা সুবিধা পান, সেখানে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই বৈষম্য শুধু অর্থনৈতিক নয়, এটি সামাজিক মর্যাদাকেও ক্ষতবিক্ষত করে।
শিক্ষক সমাজের আর্থিক অনিশ্চয়তা সরাসরি শিক্ষার মানকে প্রভাবিত করছে। শিক্ষক যখন নিজ পরিবারের নিত্যপ্রয়োজন মেটাতে হিমশিম খান, তখন তার পক্ষে মনোযোগী হয়ে পাঠদান করা কঠিন হয়ে পড়ে।
ফলস্বরূপ অনেক শিক্ষক বাধ্য হচ্ছেন প্রাইভেট টিউশন বা কোচিং করাতে। এতে বিদ্যালয়ের মূল পাঠদান দুর্বল হয়ে পড়ে, আর শিক্ষার্থীরা হারায় মনোযোগ। পবিত্র পেশা আজ জীবিকার তাগিদে পরিণত হয়েছে এক সংগ্রামে।
শিক্ষক সমাজের আলোকবর্তিকা। কিন্তু যখন সেই আলো নিজেই নিভে যেতে বসে, তখন অন্ধকার গ্রাস করে পুরো সমাজকে। আজকের শিক্ষার্থীরা দেখছে তাদের শিক্ষক মর্যাদা পেলেও নিরাপত্তা পান না, সম্মান পেলেও নিশ্চিন্ত জীবন পান না। এই দৃশ্য তরুণ প্রজন্মের মনে শিক্ষাদান পেশার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করছে।
বাংলাদেশে অনেক মেধাবী স্নাতক শিক্ষকতা পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, কারণ তারা জানেন এই পথে অর্থনৈতিক স্থিতি নেই। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা, মানবসম্পদ ও জাতির ভবিষ্যৎ।
সরকার মাঝে মাঝে শিক্ষকদের দাবি স্বীকার করলেও বাস্তবায়নের ধীরগতি হতাশাজনক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, বাজেটের সংকট ও প্রশাসনিক জটিলতা—সব মিলিয়ে সমস্যার সমাধান বিলম্বিত হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও নীতিনির্ধারণের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়।
জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির মাত্র ২ শতাংশেরও কম, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম। ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী এটি হওয়া উচিত জিডিপির অন্তত ৪ থেকে ৬ শতাংশ বা জাতীয় বাজেটের ১৫-২০ শতাংশ।
এই প্রেক্ষাপটে বেসরকারি শিক্ষকদের আর্থিক উন্নয়নকে ‘অতিরিক্ত ব্যয়’ হিসেবে না দেখে ‘বিনিয়োগ’ হিসেবে দেখা উচিত। কারণ, শিক্ষকদের মানোন্নয়ন মানেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানোন্নয়ন।
সম্ভাব্য সমাধানের দিকনির্দেশনাগুলো হতে পারে-
১. বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা:
বর্তমান বাজারদরের ভিত্তিতে বাড়িভাড়া ভাতা কমপক্ষে মূল বেতনের ২০–২৫ শতাংশ হওয়া প্রয়োজন।
২. নিয়মিত পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রবর্তন:
প্রতি তিন বছরে একবার শিক্ষক ভাতা কাঠামোর পুনর্মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে, যাতে মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে।
৩. শিক্ষা বাজেটে বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য আলাদা বরাদ্দ:
সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের শিক্ষকদের মধ্যে ন্যায্য ভারসাম্য রক্ষায় পৃথক তহবিল গঠন করা প্রয়োজন।
৪. জাতীয়করণের রূপরেখা তৈরি:
ধাপে ধাপে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সরকারি কাঠামোর আওতায় আনার রোডম্যাপ তৈরি করলে শিক্ষক সমাজে আস্থা ফিরে আসবে।
মোটকথা, শিক্ষক কোনো বিলাসবহুল সুবিধা দাবি করছেন না। তারা কেবল তাদের ন্যায্য অধিকার চাইছেন—একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার। দেশের ভবিষ্যৎ গঠনের ভার তাদের কাঁধে, অথচ তাদের নিজস্ব জীবন টিকিয়ে রাখাই যখন চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়, তখন শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা অপ্রাসঙ্গিক নয়।
রাষ্ট্র যদি সত্যিই ‘মানুষ গড়ার কারিগরদের’ সম্মান জানাতে চায়, তাহলে এখনই সময় তাদের দাবির যৌক্তিক সমাধান দেওয়ার। নতুবা শিক্ষার মূল ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে, যার প্রভাব পড়বে জাতির অগ্রগতির প্রতিটি স্তরে।
লেখক: কলামিস্ট
সানা/আপ্র/১৪/১০/২০২৫