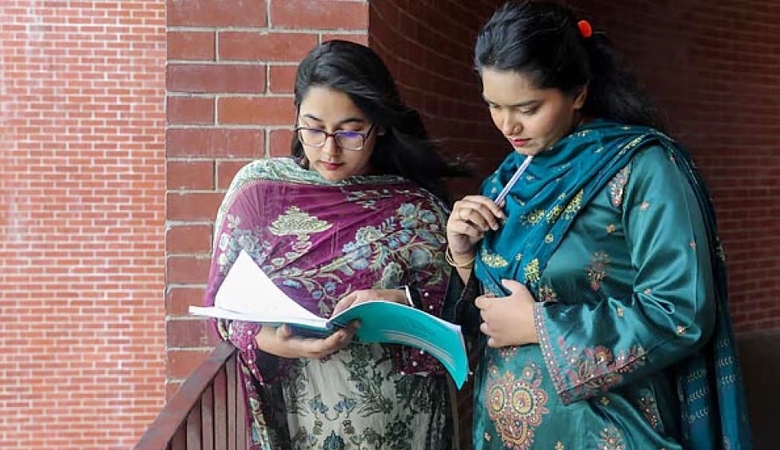রাজু আলাউদ্দিন : একাত্তর জার্নালের টকশোর আলোচনা নিয়ে প্রতিক্রিয়ার ফলে কৌতূহলবশত ড. এইচ এম জাকিরসহ সাতজনের গবেষণাপত্রটি পড়ার সুযোগ হলো। এনিয়ে বিতর্ক না হলে হয়তো কখনোই পড়া হতো না। এটি প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত ঘধঃঁৎব পত্রিকার অঙ্গীভূত উন্মুক্ত তথ্য জার্নাল (ড়ঢ়বহ ংড়ঁৎপব লড়ঁৎহধষ) হিসেবে পরিচিত ঝপরবহঃরভরপ জবঢ়ড়ৎঃং-এ। বিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্য খোঁজখবর জানা পাঠকের কাছে সায়েন্টিফিক আমেরিকান, নেচার এবং সায়েন্স-এই তিনটি পত্রিকা অপরিচিত হওয়ার কথা নয়। আমি এক সময় উৎসাহ নিয়ে এই তিনটি পত্রিকা কেবল পড়িইনি, বাংলাবাজার পত্রিকার বিজ্ঞানবিষয়ক বিভাগটি আমার তত্ত্বাবধানে থাকার কারণে সেখান থেকে বহু লেখা অনুবাদ করে ছাপিয়েছি এই পত্রিকাগুলো থেকে। নিজেও কখনো কখনো সেগুলোর কোনো লেখা অনুবাদ করেছি। যারা বিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষক, তাদের কাছে শুনেছি, তিনটি পত্রিকাই বিশ্বসেরা বিজ্ঞান সাময়িকীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ও আলোচিত। নিশ্চয়ই আরও কিছু পত্রিকাও আছে। আমাদের পত্রিকাজগতের অনেক কর্মীও নিশ্চয়ই এই পত্রিকাগুলোর সাথে পরিচিত। সুতরাং, নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে এগুলোর কোনো একটিতে গবেষণা প্রকাশিত হওয়া মানে সত্যি খুব বিরাট ব্যাপার, খুবই সম্মানের।
ড. জাকিরদের গবেষণাটি সরাসরি ‘নেচার’ পত্রিকায় প্রকাশিত না হলেও, তারই অঙ্গীভূত ঝপরবহঃরভরপ জবঢ়ড়ৎঃং-এ প্রকাশিত হওয়ায় গবেষণাপত্রটির মহিমা একবিন্দুও কমে যায় না। আমি সত্যিই গর্বিত বোধ করি যে, আমাদের মতো বিজ্ঞান ও গবেষণার আকালের দেশে একদল গবেষকের লেখা ওরকম একটি উঁচুমানের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই দেশে যখন মানবদেহে আরবি অক্ষর ও কালাম আবিষ্কারের মতো বিজ্ঞানের নামে অবৈজ্ঞানিক গবেষণা (গবেষণাটিও অন্য কোনো বিদেশি অখ্যাদ্য এক জার্নাল থেকে চুরি করা) করা হয়, সেখানে এরকম একটি গবেষণা প্রকাশের কারণে গৌরববোধ করা এবং গবেষকদেরকে সাধুবাদ জানানো উচিত ছিল আমাদের। কিন্তু আমার করেছি ঠিক উল্টো, যেমনটা করে থাকে ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো তাদের বিজ্ঞানবিমুখতার কারণে। মৌলবাদীদেরকে চিনতে অসুবিধা হয় না এবং বুঝতেও অসুবিধা হয় না কেন তারা সেটা করে। তারা তাদের কাজে স্পষ্ট। তারা প্রগতিশীলতার আল্লাখেল্লা পরে নেই। কিন্তু যারা তা পরে আছে এবং মৌলবাদীদের মতোই অভিন্ন আচরণ করছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে, তখন কিন্তু সত্যিই সেটা ভয়ের বিষয়।
আপনি যাদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক ভাবছেন তারা তা নয়। এই অর্থে, মিথিলা ফারজানার সঞ্চালনায় একাত্তরের জার্নালের টকশোটি আমাদেরকে কেবল হতাশই করেনি, পাশাপাশি বহু ভীতিকর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। এক, একাত্তর টিভিতে এই অনুষ্ঠানটি কীভাবে হতে পারল যেখানে এই গবেষণাকে তিরস্কৃত করা হয়েছে? একাত্তরের চেতনা থেকেই যদি এই টিভির জন্ম হয়ে থাকে তাহলে তাদের এই কাজটি কি ওই চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে? দুই, বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে এভাবে তিরস্কৃত ও অবমূল্যায়ন করা মানে এ ধরনের কাজকে নিরুৎসাহিত করা। ডিজিটাল এই সরকার কি তাদের এই বিজ্ঞানবিদ্বেষী মনোভাবের সাথে একমত? তিন, তাদের এই আচরণ মূলত ধর্মীয় সেই সব মৌলবাদীদেরকে উৎসাহিত করবে এবং বৈধতা দেবে যারা হামেশাই বিজ্ঞানবিরোধী বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি এক ভিডিওতে দেখলাম মুফতি কাজী ইব্রাহিম বলছেন, “আইস্টাইন একটা চোর , নিউটন একটা চোর, গ্যালিলিও তো আরও বড় চোর।” মানবজাতির সর্বকালের সেরা তিন বিজ্ঞানী সম্পর্কে এই অসম্মানজনক উক্তি– এটাই এখন আমাদের সংস্কৃতির অংশ। কিন্তু বিষয়টি কেবল সাংস্কৃতিক আদর্শের জায়গাতেই সীমাবদ্ধ নয়, আরও কতগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে দেয়।
গণমাধ্যমের কতগুলো নীতিমালা আছে যা আপনি মান্য করার মাধ্যমে এই পেশার মর্যাদা ও সম্মানকে সমুন্নত রাখবেন। সংবাদপত্র, নিউজ পোর্টাল এবং ভিজুয়াল মিডিয়া- এই তিনটি গণমাধ্যমের গুরুত্ব জনমনে অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, ভিজুয়াল মিডিয়া আমাদের মতো স্বল্পশিক্ষিত বা বৃহত্তর শিক্ষাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দেশে স্বাভাবিক কারণেই অপেক্ষাকৃত বেশি প্রভাববিস্তারী। একজন নিরক্ষর মানুষ পড়তে না জানলেও দেখার জন্য তার কোনো অক্ষরজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মনে এই মাধ্যমটির অভিঘাত অনেক বেশি। আর বেশি বলেই যেকোনো সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সতর্কতা বেশি দাবি করবে।
কিন্তু, দুঃখজনক হলো, যে মাধ্যমটির সতর্কতা বেশি বলে কাম্য, ওই মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি অসতর্কতার নজির আমরা লক্ষ্য করেছি গত কয়েক বছরে। বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে শুধুই টিআরপি বাড়ানোর প্রলোভনে পড়ে সংবাদটির যথার্থতা, বস্তুনিষ্ঠতার তোয়াক্কা না করে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা করতে গিয়ে তারা একবারও ভেবে দেখছেন না কত মানুষ এই সংবাদটি দেখে সঙ্গে সঙ্গে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। কিংবা যদি সেই সংবাদটি ভাইরাল-চরিত্রের হয় বা ধরা যাক ধর্মীয় বা সাম্প্রাদায়িক সংঘাত বিষয়ের কোনো সংবাদ হয়, তাহলে তা কী ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে সেটি তিনি সাংবাদিকসুলভ সংবেদনশীলতা দিয়ে ভেবে দেখছেন না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, সংবাদ পরিবেশনের শক্তির কারণে ওয়াটারগেট কেলেংকারিতে রাষ্ট্রের প্রবল পরাক্রমশীল প্রেসিডেন্টের পতন ঘটতে পারে। আবার ভিন্ন ধরনের একটি সংবাদ পরিবেশনের কারণে হাজার হাজার মানুষ সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে প্রাণ হারাতে পারে। তার মানে, অন্য যেকোনো সংবেদনশীল পেশার মতোই সাংবাদিকতা দাবি করে সর্বোচ্চ সতর্কতা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমরা এই পেশায় ওই সংবেদশীলতার প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হচ্ছি।
এত কিছু বলার কারণ একাত্তর জার্নালের সর্বসাম্প্রতিক টকশো। প্রথম কথা হলো, যে গবেষককে অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে আনা হয়েছিল, তার সাথে দুর্ব্যবহার। দ্বিতীয়ত, যাদেরকে এই বিষয়ে আলোচক হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছিল, তারা কেউ-ই, এমনকি সঞ্চালক মিথিলা ফারজানাও ওই গবেষণাপত্রটি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা না নিয়েই কথা বলছিলেন। আমি বলছি না, কোনো দার্শনিকের সাক্ষাৎকার নিতে হলে আপনাকে দার্শনিক হতে হবে। কিন্তু তার সম্পর্কে কথা বলার জন্য বা প্রশ্ন করার জন্য ন্যূনতম ধারণাটি আপনার থাকতেই হবে। তা নাহলে আপনি তাকে প্রশ্ন করবেন কীভাবে?
ঘটনা হলো, অনুষ্ঠানটি দেখার পরে মনেই হয়নি যে তারা এই গবেষকের বা গবেষক দলের লেখাটি পড়েছেন। এমনকি, এই লেখাটি যে একটি মর্যাদাপূর্ণ গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্পর্কেও তাদের কোনো ধারণা ছিল না। তারা বারবার জিজ্ঞেস করেছেন, এটি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি লেখাটির শুরুতেই যে পত্রিকাগুলোর নাম উল্লেখ করেছি, সেগুলো নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোনো পত্রিকা নয়, যদিও সেগুলোর সম্পাদকীয় পরিষদের সাথে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গবেষকরাই, এমনকি নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ও গবেষকরা সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এই বিষয়ে আলোচকদের বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকার কারণে তারা প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে গবেষণাটি। তারা ধরেই নিয়েছেন বাংলাদেশে বেশিরভাগ জার্নালই, বিশেষ করে বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল, যেহেতু কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই প্রকাশিত হয়, সুতরাং এই গবেষকের অনুসন্ধানটিও সেরকমই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোনো জার্নালেই প্রকাশিত হওয়ার কথা। অর্থাৎ, কুয়োর ব্যাঙয়ের মতো এই বিশ্বকে দেখার এক ভান তারা অনুষ্ঠানটিতে তুলে ধরেছিলেন। বাংলাদেশের বাস্তবতা দিয়েই তারা পরিমাপ করছিলেন গোটা বিশ্বকে। তারা একবারও ভাবেননি এই বিষয়ে আলোচনা করার আগে এই সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নেয়া উচিত ছিল।
যেহেতু তারা বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, এমনকি পত্রিকাগুলো সম্পর্কেও তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, সেক্ষেত্রে এমন বিষয়ে যুক্ত না হওয়াই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। টিভি কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল সাংবাদিকতার নীতির সুষ্ঠু ধারা অনুসরণ করে একই বিষয়ের দুজন গবেষককে আলোচনায় যুক্ত করা। গবেষক দলের অনুসন্ধানে যদি কোনো ত্রুটি বা বিচ্যুতি থেকে থাকে, সেটা তারা যতটা সহজে ও দক্ষতার সাথে চিহ্নিত করতে পারবেন, আমাদের মতো সাধারণ পাঠকদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের দুঃসাহস ও জ্ঞানের দম্ভ এতটাই ছিল যে উক্ত বিষয়ে পুরোপুরি অজ্ঞ দুজনকে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত করেছেন। আর সঞ্চালক হিসেবে যিনি যুক্ত ছিলেন, তিনি ছিলেন সেই অজ্ঞতার চূড়ামণি।
এই ধরনের টকশোগুলো সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদের সেই অলঙ্ঘ্য উক্তি হয়তো আপনার মনে পড়বে যিনি বলেছিলেন, “বাঙলাদেশের প্রধান মূর্খদের চেনার সহজ উপায় টেলিভিশনে কোনো আলোচনা-অনুষ্ঠান দেখা। ওই মূর্খম-লীতে উপস্থাপকটি হচ্ছেন মূর্খশিরোমণি।” দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বহু আগে কথিত হুমায়ুন আজাদের কথাটিকেই সত্য করে তুলছিলেন নানান ধরনের প্রশ্ন করে যার সাথে কোনোই যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না গবেষণার। একই ধরনের প্রশ্নবাণে গবেষককে জর্জরিত করে যাচ্ছিলেন মাসুদা ভাট্টি ও মিথিলা ফারজানা। তাদের মাথাতে একবারের জন্যেও এই প্রশ্ন আসেনি যে অনুষ্ঠানটি বহু মানুষের গোচরে আসবে। কী ভাববে তাদের এই উপস্থিতি সম্পর্কে? আর শুধু মূর্খের মতো প্রশ্নেই এর শেষ ছিল না, যুক্ত হয়েছিল আরও ভয়াবহ কিছু উপাদান। গবেষককে যদিও তার অনুসন্ধানের সারাৎসার জানাবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, কিন্তু আদতে পুরো অনুষ্ঠানটিই ছিল গবেষকের অনুসন্ধানকে অস্বীকার এবং তাকে অপরাধী হিসেবে প্রতিপন্ন করা।
কীভাবে? আপনারা আমার কথায় অন্ধের মতো বিশ্বাস করুন-এই দাবি আমি করব না, আমি চাই আপনারা অনুষ্ঠানের ভিডিওটি দেখুন এবং আপনারদের নিজেদের বিচারবোধ দিয়ে বিষয়টি অবলোকন করুন। এখানে সঞ্চালক প্রথম দিকে মোটামুটি পক্ষপাতহীনভাবে গবেষক সম্পর্কে বললেও, অল্পসময়ের মধ্যেই উন্মোচিত হয়ে যায় তাদের উদ্দেশ্য। অনেকটা পূর্বপরিকল্পিতভাবেই জানতে চাইছিলেন এই গবেষণার নেতিবাচক দিকটি সম্পর্কে।
গবেষক শুরু থেকেই বলার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন যে এই গবেষণার উদ্দেশ্য নেতিবাচক বা ইতিবাচক দিকটি প্রতিপন্ন করা তার উদ্দেশ্য নয়, মূলত গবেষণার স্বাভাবিক পদ্ধতি হিসেবে শুধুই নির্ণয় করা কী কী উপাদান তারা খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আলোচকবৃন্দ ও সঞ্চালক যেহেতু বদ্ধপরিকর ছিলেন এর নেতিবাচক দিকটিকে ফলাও করার ব্যাপারে, তাই ত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়ে প্রায় জোর করে তার মুখ থেকে এই গবেষণার ক্ষতিকর দিকটি উদ্ধারের জন্য মরিয়া ও মারমুখী হয়ে উঠেছেন। কেন তারা এতটা বেপরোয়াভাবে এই ব্যাপারে উগ্র ও ঝগড়াটে হয়ে উঠেছিলেন? কারণ, অন্য এক সাংবাদিকের পরিবেশিত সংবাদের শিরোনাম: ‘বেগুন ক্যানসারের কারণ’। তাদের কাছে পুরো গবেষণা বলতে আসলে ওই শিরোনামটুকুই ছিল। আর তারা দীর্ঘ সময়ব্যাপী ওই শিরোনামটিকেই পুঁজি করে বিজ্ঞ গবেষককে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গবেষণাটির কোথাও এমনটা সরাসরি বলা হয়নি যে বেগুন ক্যানসারের কারণ। তারা গবেষণার শর্ত অনুসারে শুধু বিভিন্ন উপাদানের অনুপাতগুলো উল্লেখ করেছেন। গবেষণার আন্তর্জাতিক মান হিসেবে তারা শুধু উল্লেখ করেছেন এই কথা যে:
ঈধষপঁষধঃরড়হ ড়ভ পধৎপরহড়মবহরপ যবধষঃয ৎরংশ
ঞযব রহপৎবসবহঃধষ ষরভবঃরসব পধহপবৎ ৎরংশ (ওখঈজ) ধিং পধষপঁষধঃবফ ঃড় ফবঃবৎসরহব ঃযব ৎরংশ ড়ভ পধৎপরহড়মবহরপ যবধষঃয বভভবপঃং ভৎড়স ঃৎধপব সবঃধষ বীঢ়ড়ংঁৎব নু ংড়রষ ফবৎসধষ ধফংড়ৎঢ়ঃরড়হ ধহফ ড়ৎধষ পড়হংঁসঢ়ঃরড়হ ড়ভ নৎরহলধষ ভৎঁরঃং. ঞযব ভড়ষষড়রিহম বয়ঁধঃরড়হং, ধং ফবভরহবফ নু ঃযব টঝঊচঅ২৩, বিৎব ঁংবফ ঃড় পড়সঢ়ঁঃব ওখঈজ াধষঁবং ভড়ৎ াধৎরড়ঁং ঃৎধপব বষবসবহঃং.
কথা হচ্ছে, এই বক্তব্যে গবেষকরা এটা বলতে চাচ্ছেন না যে বেগুন খেলেই ক্যানসার হবে। জীবৎকালে ক্যানসারের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির একটা হিসেব তারা তুলে ধরেছেন তাদের গবেষণার ফল থেকে। কিন্তু সাংবাদিক সেই ঝুঁকিটাকেই গবেষকদের এক ‘নিশ্চিত’ বক্তব্য হিসেবে উপস্থাপন করেছেন তার প্রতিবেদনে। আর আলোচক ও সঞ্চালক শুধু সেই শিরোনামটিকে পুঁজি করেই অত্যন্ত হিংস্র, অশালীন ও আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ঝাপিয়ে পড়েছেন গবেষকের উপরে। তাকে, সেই মধ্যযুগীয় বর্বর ইনকুজিশনের ধর্মান্ধ ক্যাথলিক পুরুতদের মতো অকথ্য প্রশ্নবাণে এমনভাবে বিদ্ধ করছিলেন যা থেকে পরিত্রাণের উপায় প্রায় ছিল না। কেননা তার চতুর্দিকে ছিল, মিথিলা ফারজানা, মাসুদা ভাট্টি, উদিসা ইসলাম ও একাত্তর টেলিভিশন নামক চারটি শ্যাওলাচ্ছন্ন কুপম-ুকতার দেয়াল। তারা তাকে উপর্যুপরি হুমকি দিচ্ছিল তার গবেষণাটিকে ফৌজদারি অপরাধমূলক ধারা হিসেবে বিবেচনা করা যায় বলে। গোটা অনুষ্ঠানটিকে তারা অজ্ঞতার এক এজলাসে রূপান্তরিত করেছিলেন হুমকি আর ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে।
একটা গণমাধ্যম যখন গৌরবকে অপরাধ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায়, তখন গণমাধ্যমের চরিত্রকেই তা কলংকিত করে। গবেষকের সাথে সামান্যতম ভদ্রতা ও শিষ্টতা দেখাননি তারা, উল্টো তার জ্ঞান নিয়ে মাসুদা ভাট্টি উপহাস করেছেন বেগুনের পরিবর্তে ঝিংগা নিয়ে কেন গবেষণা করেননি বলে। নীতি-পুলিশের মতো তার ওপর চালিয়েছেন অজ্ঞতার অকথ্য নিপীড়ন। যদিও বলা হয়ে থাকে প্রশ্ন করার মধ্যেই সৌন্দর্য, কিন্তু সেই সৌন্দর্যকে বিকৃত করা হয়েছে তাদের অপজ্ঞান চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে।
বেগুন নিয়ে গবেষণাটিতে যদি সত্যি সত্যি ক্যানসারের উপাদান চিহ্নিত হয়ে থাকে, তাতে করে গবেষককে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করার কী কারণ থাকতে পারে? আমাদের কোনো খাদ্যদ্রব্যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদান পাওয়া গেলে সেটার জন্য গবেষকরা দায়ী হবেন কেন? আর সেই উপাদান সম্পর্কে অবহিত করা মানে তো তিনি আসলে আমাদের জন্য বরং কল্যাণকর এক কাজ করেছেন বলে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তার গবেষণার সূত্র ধরে এই ক্ষতিকর উপাদান যাতে খাদ্যে প্রবেশ না করে সেই উপায় বের করার কথা আমাদের ভাবা উচিত। কিন্তু সঞ্চালক ও আলোচকরা গবেষককেই অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য ছিলেন বদ্ধপরিকর। তাই বেগুন চাষিদের ক্ষতিপূরণের ভয়ও দেখিয়েছেন তারা। তাদের আলোচনায় এই কথাও উঠে এসেছে, কেন তারা গবেষণাটি আগে সরকারের লোকজনকে অভিহিত করেনি। কি হাস্যকর ও অজ্ঞতায় মোড়ানো এইসব প্রশ্ন।
গবেষণার নীতিমালা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা থাকলে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও এই ধরনের প্রশ্ন করে না। কিন্তু তারা করেছেন, কারণ তারা নিজেদেরকে অসাধারণ সবজান্তা শমসের বলে মনে করেছেন। যে বিষয়ে তারা আলোচনা করছিলেন ওই বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান তো দূরের কথা, সংশ্লিষ্ট বিষয়েও ছিল তাদের অজ্ঞতার প্রকাশ। যেমন মিথিলা ফারজানা বলছিলেন, “গবেষণায় বেগুনে ক্যানসারের কোষ (নতুন আবিষ্কার বটে) পাওয়া গেছে বলে সংবাদ বেরিয়েছে। মাসুদা ভাট্টিও জ্ঞানে পিছিয়ে ছিলেন না, তাই তিনি মিথিলার জ্ঞানকে পূর্ণতা দেয়ার জন্য বললেন, “বেগুনে ক্যানসারের জীবাণু (তাই নাকি? ক্যানসারের জীবাণু আছে তাহলে!) পাওয়া গেছে গবেষণায় এমনটাই পত্রিকায় বের হয়েছে।”
গবেষক ভদ্রতাবশত তাদের অজ্ঞতার প্রতি বিন্দুমাত্র কটূক্তি না করে বরং শান্তভাবে বারাবার বলতে চেষ্টা করেছেন যে, “আপনার বক্তব্যের শুরুটাই সঠিক নহে। যেভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে মেসেজ কিন্তু সেটা নয়। ‘বেগুনে ক্যানসারের কোষ বা জীবাণু’ আছে এধরনের কথা বলার কোনো সুযোগই নাই, আমাদের গবেষণার বিষয়ও তা ছিল না। এমনকি বেগুন খেলে ক্যানসার হবে এমনটাও আমরা আমাদের গবেষণার কোথাও বলিনি। আমরা গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বলেছি- গবেষণার জন্য আমাদের সংগৃহীত স্যাম্পল বেগুনে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিমাত্রায় মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর তিনটি ভারি ধাতুর [খবধফ (সিসা), ঈধফসরঁস (ক্যাডমিয়াম), হরপশবষ (নিকেল)] উপস্থিতি পাওয়া গেছে এবং এই ধাতুগুলো ক্যানসারের জন্য দায়ী হতে পারে।” এত স্বচ্ছভাবে বলার পরও তারা গবেষকের ভাষা নাকি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। সঞ্চালক তাই সহজ বাংলায় বুঝাবার জন্য বক্তাকে অনুরোধ করেন। দৃশ্যত অনুরোধ করলেও গবেষক তার বক্তব্য শেষ করার আগেই উপর্যুপরি বাধা দিয়ে গেছেন তিনজনই। পুরো অনুষ্ঠানটিকেই মনে হয়েছে পরিকল্পিতভাবে সম্মানিত এই গবেষককে হেনস্তার লক্ষ্যে সাজানো। একাত্তর জার্নালে এরকম অনুষ্ঠান এটাই প্রথম নয়, এরকম নজির আরও আছে। তারা গণমাধ্যমের শক্তিকে নীতিবর্জিত উপায়ে নির্দিষ্ট কারো কারো ওপর প্রয়োগ করেছে এর আগেও।
বহু আগে পড়া জার্মান মহান লেখক গ্যোটের একটি স্বল্পপরিচিত নাটক গোৎস ফন বের্লিকহিঙ্গেন (এস্খঃু াড়হ ইবৎষরপযরহমবহ)-এর একটি চরিত্রের সেই উক্তিটি মনে পড়ছিল যেখানে তিনি বলেছিলেন, “প্রতারণার যুগ আসছে। অপদার্থরা করবে প্রভুত্ব বিস্তার আর কাপুরুষদের হাতে বন্দি হবেন বীরগণ।”
আজকের দিনে বাংলাদেশে জন্মালে তিনি নিশ্চিতভাবেই এই উক্তিটিকে ভবিষ্যৎবাচক না রেখে চলমান বর্তমান কালে রূপান্তরিত করতেন।
অজ্ঞরা এখন বিশেষজ্ঞ। মূর্খরা এখন জ্ঞানী। অজ্ঞ ও মূর্খ হওয়া দোষের নয়, দোষের হচ্ছে বিজ্ঞ হওয়ার ভান করা।
লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট
মিডিয়ার মাস্তানি, অজ্ঞতা ও কয়েকটি বেগুন
ট্যাগস :
মিডিয়ার মাস্তানি
জনপ্রিয় সংবাদ