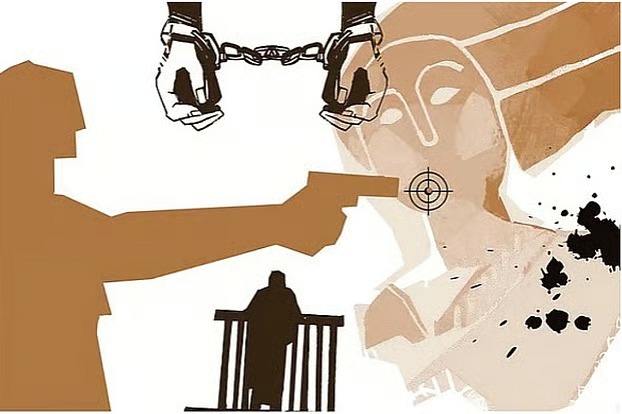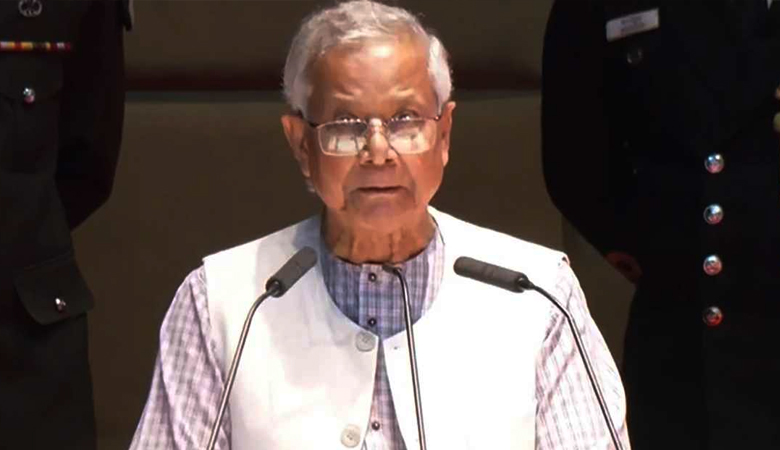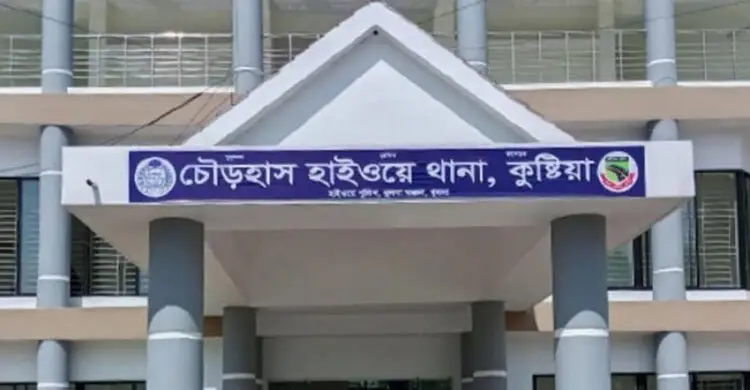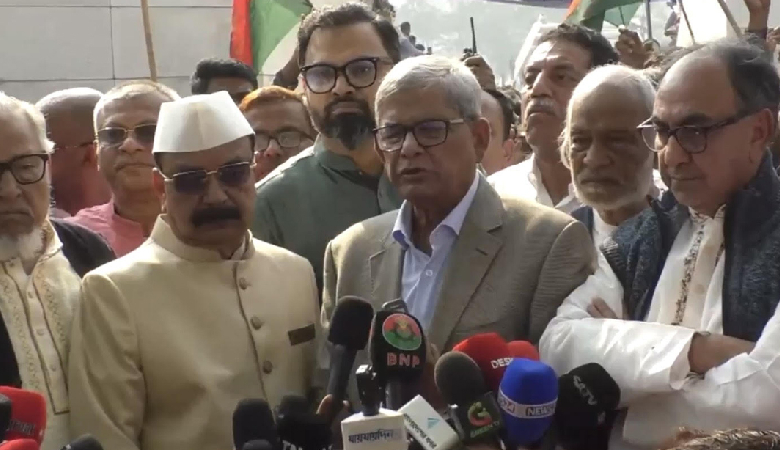চিররঞ্জন সরকার
উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা গোটা জাতিকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। সরকারের করণীয়, বিমানবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকাসহ নানা বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এসব আলোচনা অনিবার্য ও প্রাসঙ্গিক। তবে এই হৃদয়বিদারক ঘটনার পর সংবাদমাধ্যম যেভাবে ঘটনাটি উপস্থাপন করেছে, তা ঘিরে সমাজের সচেতন মহলে জন্ম নিয়েছে এক ধরনের অস্বস্তি ও ক্ষোভ—যা উপেক্ষা করা যায় না।
সংবাদমাধ্যমের মূল দায়িত্ব তথ্য পরিবেশন, সত্য অনুসন্ধান ও জনসচেতনতা তৈরি। কিন্তু যখন তা অতিরঞ্জিত আবেগ বা শোককে পণ্যে রূপান্তরের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন প্রশ্ন উঠবেই—এই সাংবাদিকতা দায়বদ্ধ, নাকি বেদনাকে বাজারে তোলার এক ধরনের প্রতিযোগিতা? সংবাদমাধ্যম যখন সমাজের বিভিন্ন স্তরকে জবাবদিহির আওতায় আনে, তখন নিজেদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিও কি সেই একই মানদণ্ডে যাচাইযোগ্য নয়?
দুর্ঘটনার পর পরই বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘটনার হৃদয়বিদারক দিকগুলো ঘন ঘন দেখানো হতে থাকে। বেদনা বাণিজ্যের সাংবাদিকতা করতে গিয়ে অনেক সময় সংবাদ উপস্থাপনায় সংবেদনশীলতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা পর্যন্ত উপেক্ষা করা হয়। নিহত বা আহতদের স্বজনদের অনুমতি ছাড়াই তাদের শোকাহত মুহূর্ত, কান্না, অসহায়তা—সব কিছু ক্যামেরায় ধারণ করে প্রচার করা হয়। শিশুদের পোশাক, বই, এমনকি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেহাংশের ছবি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। আহতদের চিকিৎসা পরিস্থিতির চেয়ে বরং রাজনীতিবিদদের আগমন বা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি সংবাদমাধ্যমের কেন্দ্রে চলে আসে।
প্রতিটি সংবাদমাধ্যম তখন প্রতিযোগিতায় নামে কে কতটা ‘নাটকীয়’ বা ‘মানবিক’ চিত্র তুলে ধরতে পারে। ক্যামেরা ঘুরে যায় শোকাহত পরিবারের মুখের দিকে, যন্ত্রণাবিদ্ধ চোখ, কান্নার ধ্বনি, এমনকি জ্ঞান হারানো মুহূর্তও প্রচারিত হয় সরাসরি সম্প্রচারে। অ্যাম্বুলেন্সে করে আহতদের বহনের দৃশ্য কিংবা পুড়ে যাওয়া জিনিসপত্র—সবই হয়ে ওঠে ‘দর্শকপ্রিয়’ কনটেন্ট।
এই প্রবণতা আসলে একটি গভীর সমস্যা নির্দেশ করে—মাইলস্টোন দুর্ঘটনা আমাদের আবার মনে করিয়ে দিয়েছে অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমের মূল উদ্দেশ্য তথ্য পরিবেশন নয়, বরং মানুষের বেদনা ও শোককে ‘আকর্ষণীয় দৃশ্য’ হিসেবে উপস্থাপন করা। এই ধারা এক ধরনের বেদনাবিলাসী সাংবাদিকতা, যেখানে কষ্ট আর করুণাকে উপস্থাপন করা হয় মনোযোগ পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে।
এই ধরনের প্রবণতা নতুন কিছু নয়; সংবাদমাধ্যমের ইতিহাসে ট্র্যাজেডিকে কেবল সংবাদ হিসেবে নয়, বরং কৌতূহল, আবেগ ও দর্শনের উপাদান হিসেবে উপস্থাপনের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট ইয়েটস এই প্রবণতাকে চিহ্নিত করেছেন ‘অন্যের দুর্ভাগ্য থেকে আহরিত অনুভূতিজনিত তৃপ্তি’ হিসেবে। প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যুর ঘটনায় সংবাদমাধ্যমের মাত্রাতিরিক্ত কভারেজ প্রসঙ্গে তিনি ‘শোক-ভোগবাদিতা’ শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন—যেখানে ব্যক্তিগত শোক এক প্রকার সামাজিক বিনোদনে পরিণত হয়। এধরনের প্রতিবেদন ব্যক্তিগত বেদনার মধ্য দিয়ে সমষ্টিগত উত্তেজনা সঞ্চার করে; যা দর্শকের কাছে এক ধরনের ‘বদলি আবেগের’ অভিজ্ঞতা তৈরি করে।
এই পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসি দার্শনিক গায় ডিবর্ডের বিশ্লেষণও প্রাসঙ্গিক। তার ‘দ্য সোসাইটি অফ দ্য স্পেকট্যাকল’ বইয়ে ডিবর্ড যুক্তি দেন, আধুনিক সমাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মানবিক সম্পর্ক ক্রমে দৃশ্য-আধিপত্যে পরিণত হচ্ছে অর্থাৎ যা এক সময় জীবন যাপনের অন্তর্গত ছিল, এখন তা হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবলই উপস্থাপনের বস্তু। এই ‘স্পেকট্যাকল সমাজে’ ট্র্যাজেডি, শোক বা সহমর্মিতা বাস্তব মানবিক অনুভূতি হিসেবে নয়, বরং নির্দিষ্ট ভঙ্গিমায় ক্যামেরাবন্দি ফ্রেমে দেখানোর বিষয় হয়ে উঠেছে—যার গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হয় তার ভিজ্যুয়াল প্রভাব ও শেয়ারযোগ্যতার ওপর।
সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসঙ্গে এসে এই প্রবণতা আরও জটিল ও ব্যাপক রূপ নেয়। বিমান দুর্ঘটনার মতো মর্মান্তিক ঘটনার পরপরই পোড়া দেহাবশেষ, শিশুদের বই-খাতা বা ইউনিফর্মের ছবি ভাইরাল হয়ে পড়ে। অনেক ব্যবহারকারী এই ছবি ও স্ট্যাটাস পোস্ট করেন যেন একধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রকাশ ঘটাতে- ‘আমি দেখেছি’, ‘আমি কেঁদেছি’, কিংবা ‘আমি সংবেদনশীল’। কিন্তু এই ‘ডিজিটাল শোকপ্রকাশ’ অনেক সময়ই সহমর্মিতার চেয়ে আত্মপ্রদর্শনের রূপ নেয়; যেখানে আবেগ নয়, বরং দৃশ্যমান অংশগ্রহণই মুখ্য হয়ে ওঠে। এটি এক প্রকার ‘ডিজিটাল পারফরমেটিভ গ্রিফ’; যার উদ্দেশ্য বেদনায় অংশগ্রহণ নয়, বরং শোকের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিংয়ের অংশ করে তোলা।
এই ধরনের আচরণকে সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক ক্যারল সার্লার। তিনি উল্লেখ করেন, এই নতুন প্রজন্মের ‘বেদনাবিলাসিতা’কে অনেক সময় ‘উৎসর্গ’ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু বাস্তবে এটি হয়ে দাঁড়ায় এক ধরনের অশালীন আত্মপ্রকাশ—যেখানে দুঃখের অভিজ্ঞতা নয়, বরং তার প্রদর্শনই মুখ্য হয়ে ওঠে। তার ভাষায়- এটি হলো ‘সবচেয়ে খারাপ কিছুর মধ্য থেকে সবচেয়ে জঘন্য উপস্থাপন।’
এই বাস্তবতায় আমরা এক গভীর নৈতিক ও পেশাগত প্রশ্নের মুখোমুখি হই- সংবাদমাধ্যমের কাজ কেবল তথ্য পরিবেশন, নাকি তা সমাজে সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা ও নৈতিক বোধ গঠনের একটি দায়িত্বশীল কাঠামোও বটে? আধুনিক সাংবাদিকতায় যখন বেদনা ও ট্র্যাজেডিকে কনটেন্ট হিসেবে পণ্যায়ন করা হয়, তখন সে দুঃখবোধ একটি মানবিক অভিজ্ঞতা হিসেবে আর থাকে না; বরং তা পরিণত হয় দর্শনীয় এক চিত্রনাট্যে; যা শোকের অন্তর্নিহিত মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে। এই প্রবণতা কেবল সংবাদ উপস্থাপনকে নয়, বরং পাঠকের উপলব্ধি ও আবেগ অনুধাবনের ধরণকেও প্রভাবিত করে।
শোক একটি অন্তর্জগতের অভিজ্ঞতা- গভীর, নিঃশব্দ ও সংবেদনশীল। তা কখনোই ক্যামেরার সামনে উপস্থাপনযোগ্য নাটক নয়। সাংবাদিকতার দায়িত্ব হওয়া উচিত সেই শোককে সম্মান করা, তার প্রেক্ষাপট বুঝে নেওয়া এবং তার ভেতর থেকে সমাজ, রাষ্ট্র বা ব্যক্তিজীবনের অন্তর্নিহিত বার্তা বিশ্লেষণ করে তোলা। কিন্তু যখন মিডিয়া ট্র্যাজেডিকে ‘ভিউস’ বা ‘এনগেজমেন্ট’-এর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে, তখন তা এক ধরনের ‘বেদনাবিলাস’-এ রূপ নেয়; যেখানে সহানুভূতির পরিবর্তে তা হয়ে ওঠে শোকের বাণিজ্যিকীকরণ।
এ বাস্তবতায় আমরা নিজেরাই গড়ে তুলছি এক প্রক্সি-আবেগের সমাজ- যেখানে অন্যের দুঃখে কান্না করা নয়, বরং সেই দুঃখের ‘ভিজ্যুয়ালাইজেশন’ দেখে নিজেকে সংবেদনশীল মনে করাটাই হয়ে উঠছে নতুন সামাজিক প্যাটার্ন। প্রশ্ন তাই থেকে যায়- আমরা কি এখন শোককে দেখছি একটি প্রকাশযোগ্য উপাদান হিসেবে—অভিনবতা ও ভিজ্যুয়াল ড্রামার খোরাক হিসেবে, নাকি এটিকে দেখছি এক সংযম, সহানুভূতি ও সম্মানের অনুশীলন হিসেবে?
সাংবাদিকতা যদি সত্যিই সমাজের দর্পণ হয়, তাহলে তা হতে হবে এক সংবেদনশীল, মানবিক ও নৈতিক দর্পণ; যেখানে সংবাদপাঠ শুধু তথ্যের চর্চা নয়, ন্যায়ের অনুধাবন এবং মানুষের প্রতি সহমর্মিতার বহিঃপ্রকাশ। বেদনাবিলাসী সাংবাদিকতা শুধু সাংবাদিকদের দায়িত্বহীনতা নয়; বরং এটি পাঠক, দর্শক এবং সামগ্রিক সমাজেরও একধরনের নৈতিক বিচ্যুতি। যখন পাঠক রেটিং বাড়ানোর সংবাদ খুঁজে বেড়ায় কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় কারো ব্যক্তিগত বেদনার ভিডিও শেয়ার করে আবেগের প্রতিক্রিয়া জানায়, তখন এই দায়িত্বজ্ঞানহীন সংস্কৃতি আরও গভীরভাবে প্রোথিত হয়। তাই দায়ভার এককভাবে সাংবাদিকদের ওপর চাপানো যথাযথ নয়।
মানবিক ও সম্মাননির্ভর সাংবাদিকতা গঠনের জন্য প্রয়োজন বহুমাত্রিক প্রচেষ্টা- প্রথমত, সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিগত সংস্কার, যেখানে ট্র্যাজেডি কভারেজের জন্য একটি নৈতিক গাইডলাইন অনুসরণ বাধ্যতামূলক হবে; দ্বিতীয়ত, সাংবাদিকদের সংবেদনশীলতা ও মানবিক চেতনার ওপর প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত মানোন্নয়ন; এবং সর্বোপরি, পাঠক ও দর্শকের দিক থেকেও দায়িত্ববান ও সমালোচনাশীল চেতনার চর্চা— যেখানে আবেগ নয়, মূল্যবোধই হয়ে উঠবে সংবাদ গ্রহণের মানদণ্ড।
সর্বোপরি একটি গণতান্ত্রিক, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ নির্মাণে সাংবাদিকতা শুধু তথ্যের বাহক নয়; বরং নৈতিক পথনির্দেশক হিসেবেও কাজ করতে পারে। তবে তার জন্য প্রয়োজন সত্য, সম্মান ও সংবেদনশীলতার প্রতি অবিচল দায়বদ্ধতা। আর এ দায় শুধুই সাংবাদিকদের নয়—সমাজের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের।
লেখক: কলামিস্ট
(মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব)
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ