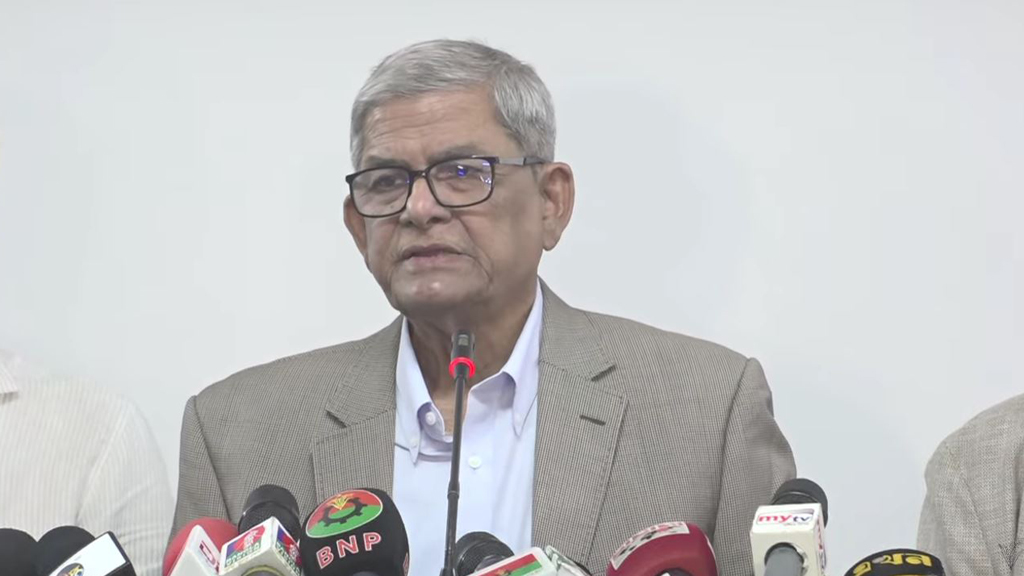মুনতাসির মামুন : মাইক্রোপ্লাস্টিকের আলোচনা সাধারণ মানুষের কাছে ঠিক কতটুকু গুরুত্ব পায় সেটি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এর প্রধান কারণ, জানার অপ্রতুলতা। আবার জানার জন্য- ঠিক কী জানতে হবে সেটাও জরুরী। স্ববিরোধী কথার মতো শোনালেও বাস্তবতা আসলেই এমন।
আমরা জেনেছি ৫ মিলিমিটারের থেকে ছোট যে কোনও প্লাস্টিকে তৈরি কিছুই মাইক্রোপ্লাস্টিক। প্লাস্টিক যেহেতু অপচনশীল এবং আমাদের তৈরি এক ধরনের যৌগ কিংবা মৌল, তাই এর আকার যত ছোটই হোক, এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণাগুলো প্লাস্টিকের সকল গুণাগুণ বহন করে। প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়না এমন কোনও পণ্য এখনকার দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আর এ থেকে মাইক্রোপ্লাস্টিক উৎপাদিত হয়। পত্রপত্রিকায় নিয়মিতভাবেই গত কয়েকবছরে সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে- ‘ঢাকা আজ পৃথিবীর দূষিততম স্থানগুলোর মধ্যে একটি’। হররোজ একই শিরোনাম দেখতে দেখতে আমরা হয়তো অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। মানসিকভাবে অভ্যস্ত হওয়ার মানে কিন্তু এই নয় যে, দূষণজনিত ভয়াবহতা কমে যাচ্ছে বা এ থেকে রক্ষা পাচ্ছি।
ঢাকার কোথায় কী হয়- যে এত দূষিত হয়ে যাচ্ছে? শুধুই যে কলকারখানার জন্যই দূষণ হয়ে থাকে এই চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ঢাকার (শুধু উদাহরণ হিসেবে) দূষণের জন্য অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে যানবাহন। এ আবার নতুন কি তথ্য! এতো আমাদের জানাই। কিন্ত আমরা কেবল গাড়ির কালো ধোঁয়াকে দায়ী করি এই দূষণের জন্য দায়ী। এটা ভুল নয়। তবে এটাই একমাত্র কারণ বা মূল কারণ নয়।
তাহলে আর কোন কোন উৎস আছে? মাইক্রোপ্লাস্টিকের উৎসগুলোর মধ্যে যেগুলো সব থেকে বেশি দায়ী- সিন্থেটিক টেক্সটাইল (সিন্থেটিকে কাপড়) ৩৫ শতাংশ, টায়ার (গাড়ি বা যেকোন যানে চাকায় যা ব্যবহার করা হয়) ২৮ শতাংশ, সিটি ডাস্ট (নগরের ধুলো। নানাবিধ কারণে এই ধুলোর তৈরি হতে পারে) ২৪ শতাংশ, রোড মার্কিং (রাস্তার উপর যে রং এর দাগ দেয়া হয়) ৭ শতাংশ, মেরিন কোটিং (জলযানের গায়ে যে ধরনের রং ব্যবহার করা হয়) ৪ শতাংশ, পারসোনাল কেয়ার প্রোডাক্ট (প্রসাধনী) ২ শতাংশ, আর বাকিটুকু অন্যান্য।
এই সংখ্যাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, আমরা যে বস্ত্র পরি তা থেকে পরিবেশ সবচেয়ে বেশি দূষিত হতে পারে (এ নিয়ে বিষদে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। দূষণের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশীদার গাড়ির টায়ার। এ নিবন্ধটিতে টায়ার থেকে দূষণ নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমেই একটা গাড়ির টায়ারে কী কী উপাদান থাকে তা জেনে নিই। টায়ার বললেই আমাদের বুঝি- রাবারের মতো প্রাকৃতিক (অরগানিক) উপাদানে তৈরি। এ থেকে আবার দূষণ কী করে হয়!
ব্রিজস্টোন টায়ার কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, বর্তমানের একটা টায়ার তৈরিতে প্রাকৃতিক রাবার, সিন্থেটিক রাবার, কার্বন ব্লাক, সিলিকা, তেল, এন্টি-অক্সিডেন্ট, সালফার, রাবার আর সালফারকে একত্রীকরণের জন্য ভলকানাইজেশন এক্সেলেরেটর এবং সর্বোপরি পলিয়েস্টার, রেয়ন কিংবা স্টিল ব্যবহার করা হয়। শুধু রাবার থেকে যে টায়ার এখন তৈরি হয় না, তার কারণ বিশ্বব্যাপী এর চাহিদা বৃদ্ধি। বাহনের ঝাঁকি কমানোর জন্য প্রথম দিকে চাকায় চামড়া ব্যবহার হলেও ১৮০০ সালের দিকে চার চাকার গাড়ি উদ্ভাবনের পরপর দৃশ্যপট বদলে যায়। চাকায় বাতাসে ভরা টিউবের ওপর টায়ার চাপানো শুরু হয়। শুরু দিকে এই টায়ার প্রাকৃতিক রাবার থেকেই তৈরি হতো। দিনে দিনে গাড়ির সংখ্যার সাথে তাল মেলাতে রাবার বাগান করার জন্য অনেক বন কেটে উজাড়ও করা হয়ে। [১]
বিংশ শতব্দীর গোড়ার দিকে গাড়ি আরও বেশি জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য হয়ে পড়ে। ফলে চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে রাবার থেকে টায়ার তৈরি কঠিন হয়ে পরে।
১৯০৯ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রিন্টজ হল্ফম্যান বেয়ার কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রথম সিন্থেটিক রাবার তৈরি করেন। এক বছরের মধ্যে সিন্থেটিক রাবার টায়ার তৈরিতে ব্যবহার হতে শুরু করে। ১৯৩১ সালে আমেরিকার ডুপন কোম্পানি সিন্থেটিক রাবার প্রস্তুত করার জন্য শিল্প কারখানা তৈরি করে। সেই থেকে শুরু। সময় আর উদ্ভাবনের কারণে কিছুটা পরিবর্তন আসলেও, আজও টায়ার প্রায় একইভাবে তৈরি হয়। এখনকার একটি টায়ারে ১৯ ভাগ প্রাকৃতিক রাবার, ২৪ ভাগ সিন্থেটিক রাবার (যা একটি প্লাস্টিক যৌগ) বাদ বাকিগুলো অন্যান্য যৌগ, মৌলের সংমিশ্রণ থাকে। বর্তমানের উৎপাদন ধরে রাখার জন্য যে পরিমাণ রাবার গাছের চাষবাস হয়, তা প্রাকৃতিক বন ধ্বংসের অন্যতম কারণ। সিন্থেটিক রাবার তৈরির অন্যতম উপাদান হলো জীবাষ্ম জ্বালানি। একটা ছোট গাড়ির (সেডান কার) টায়ার তৈরিতে প্রায় সাড়ে ২৬ লিটার আর বড় গাড়ির টায়ার তৈরিতে তেলের প্রয়োজন হয় ৮৩ দশমিক ৩ লিটার। [২]
যেকোনও বস্তু ব্যবহার করলে তো বটেই, অব্যবহৃত রেখে দিলেও পানি-বায়ু-সূর্য তাপে এর আকার, ওজন বা ভর ক্ষয় হয়, এটি নতুন করে জানার কিছু নয়। গাড়ির টায়ারও ব্যতিক্রম নয়। স্থলভাগে চলাচল করে এমন প্রায় সব ধরনের যানের চাকায় টায়ার থাকে। রাস্তায় গড়িয়ে চলার সময় টায়ারের সাথে ভূ-পৃষ্ঠের যে ঘর্ষণ হয় তা থেকে মূলত তিনভাবে মাইক্রোপ্লাস্টিক তৈরি হয়। সেগুলো হলো- টায়ার ওয়ার পার্টিক্যাল, ব্রেক ওয়ার পার্টিক্যাল এবং রোড ওয়ার পার্টিক্যাল।
বর্তমান সময়ে সামুদ্রিক, জলজ এবং স্থলজ পরিবেশের মাইক্রোপ্লাস্টিকজনিত দূষণ বহুল আলোচিত। কিন্তু মাইক্রোপ্লাস্টিকজনিত বায়ুম-লীয় দূষণ আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। রাস্তার গাড়ি বা যানবাহন থেকে উপরিল্লেখিত তিনভাবে মাইক্রোপ্লাস্টিক তৈরি হয়। মাইক্রোপ্লাস্টিক যেহেতু আকারে ক্ষুদ্র এবং হালকা হয়, তাই বায়ু দ্বারা এর পরিবহন হওয়াটাও স্বাভাবিক। [৩]।
জটিল গবেষণা বা আলোচনায় না গিয়ে সোজাসাপ্টাভাবে বলা যায়, প্রতিদিন ব্যবহারের ফলে গাড়ির টায়ারের যে ক্ষয় হয়, সেটি প্রকৃতিতে কোথাও না কোথাও জমা হতে থাকে। প্রতিদিনের ঘটনা হলেও এই দূষণ নিয়ে আমরা এখনও ভাবি কিনা- সে প্রশ্ন রাখাই যায়! এই ভাবনা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালকদেরও থাকা উচিত। প্রায় সব ধরনের দূষণ নিয়ে আলোচনা এবং তা প্রতিরোধের প্রবণতা ও প্রচার আমরা লক্ষ্য করি। তবে ট্রান্সপোর্ট ও যানবাহনের টায়ারজনিত দূষণটা ঠিক কোন মাত্রায় বা তার পরিমাপ করা হচ্ছে কিনা- সেটা নিয়ে কোনও আলোচনাই আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে অন্তত দেখিনি। তবে বাংলাদেশ তো বটেই সারা দুনিয়াতে এ দূষণ একেবারেই লাগামছাড়া এবং এ নিয়ে আলোচনা অনেক কম। গাড়ির টায়ার অবিরাম ঘোরে এবং বাতাসের তাড়নায় এর থেকে উৎপন্ন মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলো বায়ুবাহিত হয়ে পরে। বাতাসের গতি এবং বহন করার সক্ষমতাভেদে বায়ুবাহিত এই মাইক্রোপ্লাস্টিক দীর্ঘক্ষণ বায়ুতেই থাকে। আর এখান থেকে তা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানবদেহে, জলাভূমির উপরিভাগে, মাটিতে এবং গাছপালার গায়ে জড়িয়ে থাকতে পারে। বাতাসের ধুলা (ডাস্ট) বলে যাকে আমরা সহজেই মেনে নিতে শিখে গেছি, এই ধুলার সবটাই যে কেবল মাটি থেকে আগত, তা নয়। [৪]
২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট নিবন্ধিত মোটরযানের সংখ্যা ৪৪ লাখ ৭১ হাজার ৬২৫টি। [৫]
এরমধ্যে সব ধরনের যন্ত্রচালিত যানবাহন আছে। কিন্তু রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা, সাইকেলের পরিসংখ্যান কতো[- সেটা অনুমান করা ছাড়া কোন উপায় নেই। যেমন ঢাকা শহরে মাত্র ২৮ হাজার রিকশা নিবন্ধিত। কিন্তু ধারণা করা হয়, প্রায় ১০ লাখের মতো রিকশা কেবল ঢাকাতেই আছে, যার কোনও নিবন্ধন নাই। [৬]
যানবাহনের আসল সংখ্যাটা কত হতে পারে- সেটির সঠিক উত্তর আমাদের আসলে ধারণা করেই নিতে হবে। যানবাহনের পরিসংখ্যান থেকেই টায়ারের পরিসংখ্যান নিয়ে একটি সম্ভাব্য হিসেব কষে নেওয়া যায়। এর পাশাপাশি টায়ারের ক্ষয়ে যাওয়া থেকে দূষণের মাত্রার একটি পরিমাণ সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়।
সবকিছুর মান যাচাই-বাছাই কিংবা তদারকির প্রচেষ্টা রয়েছে। তবে বায়ুদূষণ রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ ঠিক কী বা কোনটা এবং সেটা নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারকদের বিষদ পরিকল্পনা কী- তা একেবারেই স্পষ্ট নয়।
দুই দশক আগে ঢাকায় বেবিট্যাক্সি উঠিয়ে দেওয়ার পেছনে একটা বড় কারণ দেখানো হয়েছিল ‘সীসাযুক্ত কালো ধোঁয়া’। গাড়ির ফিটনেসের জন্যও এর বাধ্যবাধকতা আছে। ফিটনেসের ক্ষেত্রে একটি গাড়ির গ্রিনহাউজ গ্যাস ইমিশন, এক্সজস্ট ইমিশন তথা কম্বারশন জনিত দূষণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। [৪] কিন্তু ঘর্ষণজনিত দূষণের ব্যাপারে দৃষ্টিপাতের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে দুনিয়াজুড়েই।
একটি মাঝারি মাপের গাড়ির টায়ার ব্যবহার যোগ্যতা হারানোর আগে গড়ে প্রায় ১ দশমিক ১৩ কেজি মাইক্রোপ্লাস্টিক ক্ষয় করে। আর সে হিসেবে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই বছরে প্রায় ১৮ লাখ টন মাইক্রোপ্লাস্টিক নিঃসরণ হয় যানবাহন থেকে, যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। [৭]
এ পরিসংখ্যান যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যা, বাংলাদেশ তথা অন্যান্য দেশের জন্যেও একই হবার কথা। দূষণের তারতম্য হবে মোটরযানের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে। যারা কখনই কোনও প্রকার যানবাহন ব্যবহার করেন না, তাদেরও অবদান আছে মাইক্রোপ্লাস্টিক তৈরিতে। জুতার তলা ক্ষয়ে যায়। এটা নিত্য ব্যাপার। কিন্তু আমরা কখনও ভেবে দেখেছি তলা বা সোল ক্ষয়ে গিয়ে কোথায় হারিয়ে যায়? এও এক ধরনের মাইক্রোপ্লাস্টিক, কেননা বেশিরভাগ জুতার তলা বা সোল প্লাস্টিক জাতীয়। কেউ কেউ বলতে পারেন, টায়ার তো রিসাইকেল হয়। এটা সত্যি, পুরাতন টায়ার রিসাইকেল হয়। যা অবশ্যই ভালো দিক। কিন্তু একটা টায়ার তার ব্যবহার যোগ্যতা হারাবার পূর্বে যে পরিমাণ দূষণ ঘটায় তা নিয়ে আমাদের ভাবার সময় হয়তো অনেক আগেই হয়েছে। রাস্তাঘাটের উন্নয়নে গণপরিবহনের সংখ্যা কমে প্রাইভেট গাড়ির দিকে ঝুঁকছেন অনেকে। এটা উন্নত দেশগুলোতে কয়েক যুগ আগে থেকে শুরু। এখন বাংলাদেশেও দেখা যাচ্ছে। একটি গাড়িতে যতো বেশি পরিমাণ মানুষ যাতায়াত করতে পারবেন, সেটা সামগ্রিকভাবে সব ধরনের দূষণ কমাতে সাহায্য করবে। আমরা কী করতে পারি- অবশ্যই তা আমাদের জানাতে হবে। প্রশাসন থেকে শুরু করে এই বিষয়ে যাদের জ্ঞান আছে তাদের এগিয়ে আসা উচিত। উন্নত বিশ্বে টায়ারজনিত দূষণ রোধে চাকায় হাওয়ার পরিমাণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সঠিক পরিমাণের হাওয়া টায়ারের কর্মক্ষমতাকে যেমন বাড়ায়, তেমনি এর ক্ষয়ও রোধ করে। পাবলিক ট্রান্সপোর্টে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যত বেশি মানুষ গণপরিবহনের ওপর নির্ভর করবে, ততো বেশি দূষণের মাত্রা কমে আসবে। সবশেষে, টায়ার থেকে যে মাইক্রোপ্লাস্টিক ঝরে বা পরিবেশের দূষণ হয়, তা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। বায়ুদূষণের তালিকায় আমাদের কোনও নগরীর নাম শীর্ষে থাকলে আগে নিজেদের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে সেই দূষণে কতোটা ভূমিকা রাখছি- সেটা পরিমাপ করাটাও জরুরী বৈকি!
তথ্যসূত্র: [১] যঃঃঢ়ং://িি.িড়িৎষফরিষফষরভব.ড়ৎম/ঢ়ৎড়লবপঃং/ঃৎধহংভড়ৎসরহম-ঃযব-মষড়নধষ-ৎঁননবৎ-সধৎশবঃ
[২] যঃঃঢ়ং://িি.িহধঃরড়হধষমবড়মৎধঢ়যরপ.পড়স/বহারৎড়হসবহঃ/ধৎঃরপষব/ঃরৎবং-ঁহংববহ-ঢ়ষধংঃরপ-ঢ়ড়ষষঁঃবৎ
[৩] যঃঃঢ়ং://িি.িহধঃঁৎব.পড়স/ধৎঃরপষবং/ং৪১৪৬৭-০২০-১৭২০১-৯
[৪] যঃঃঢ়ং://িি.িৎবংবধৎপযমধঃব.হবঃ/ঢ়ঁনষরপধঃরড়হ/৩২৬০৬৩১০১থঞরৎবথঅনৎধংরড়হথধংথধথগধলড়ৎথঝড়ঁৎপবথড়ভথগরপৎড়ঢ়ষধংঃরপংথরহথঃযবথঊহারৎড়হসবহঃ
[৫] যঃঃঢ়ং://নৎঃধ.ঢ়ড়ৎঃধষ.মড়া.নফ/ংরঃবং/ফবভধঁষঃ/ভরষবং/ভরষবং/নৎঃধ.ঢ়ড়ৎঃধষ.মড়া.নফ/ঢ়ধমব/৬ফ৮৪৯পপনথ০৯ধধথ৪ভনবথধবভ২থ৩ফ২৫৪ধ২ধ০পফ১/২০২০-০৭-০২-২৩-২১-ভনধ১বনধধ৩প৬ধ৭২৯৯ভবফ০ফ৫প২ধন৮ভ৩২ভধ.ঢ়ফভ
[৬] যঃঃঢ়ং://িি.িঃনংহবংি.হবঃ/নধহমষধফবংয/ড়হষু-য়ৎ-পড়ফবফ-ৎরপশংযধংি-ৎঁহ-ফযধশধ-সধুড়ৎ-ধঃরয়-৪৭০৯০২
[৭] যঃঃঢ়ং://িি.িহধঃরড়হধষমবড়মৎধঢ়যরপ.পড়স/বহারৎড়হসবহঃ/ধৎঃরপষব/ঃরৎবং-ঁহংববহ-ঢ়ষধংঃরপ-ঢ়ড়ষষঁঃবৎ