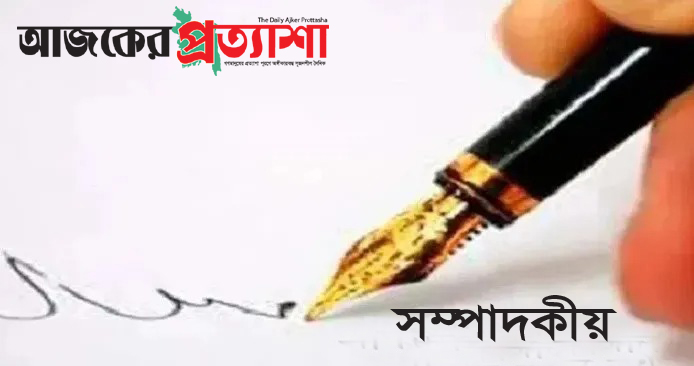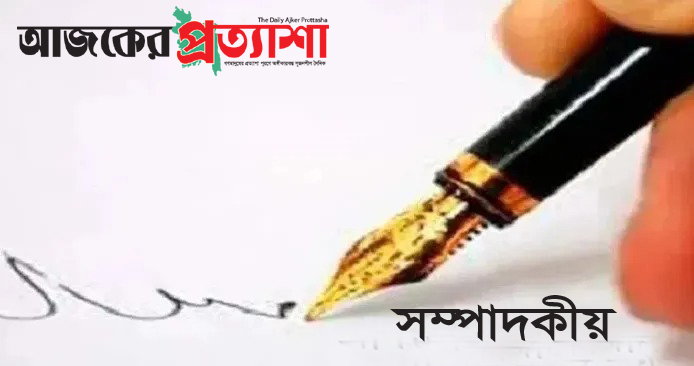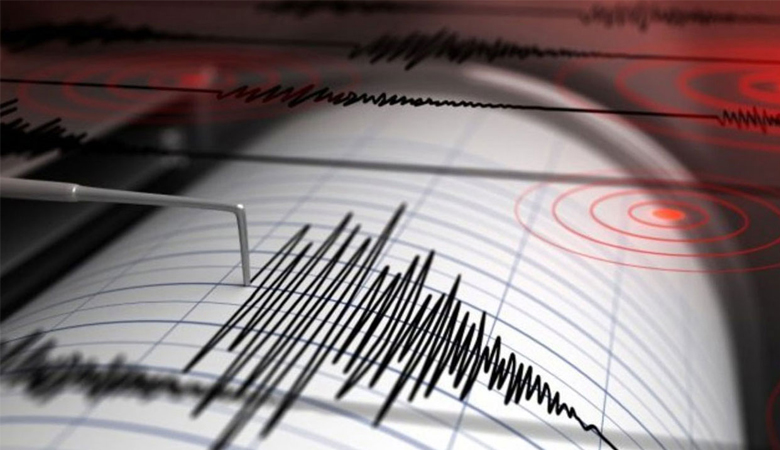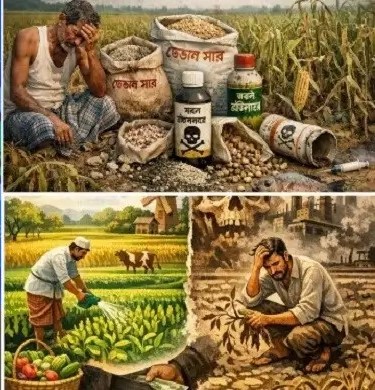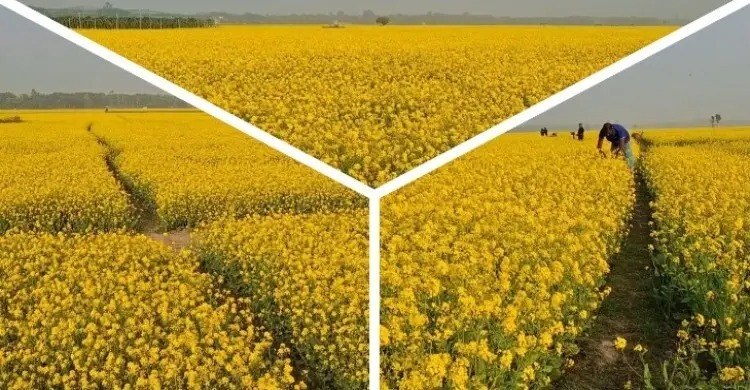প্রভাষ আমিন : সবাই বলছেন, ২০২৩ সালটি খুব খারাপ যাবে। বলছেন বলে নয়, এটাই বাস্তবতা। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে নয় মাস ধরে। যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণও নেই। করোনায় ধুঁকতে থাকা বিশ্ব অর্থনীতি যখন ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই করছিল, তখনই যুদ্ধ এসে সেই লড়াই আরও কঠিন করে দেয়।
বিশ্ব অর্থনীতি ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। যত দিন যাবে যুদ্ধের প্রভাবে অর্থনীতি আরও মন্থর হবে। এই প্রবণতা গোটা বিশ্বের। আর বাংলাদেশ মোটেই বিশ্বের বাইরে নয়। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতি যে দারুণ মোমেন্টাম পেয়েছিল, তা স্থবিরতার দিকে এগোচ্ছে। তাই ২০২৩ সালটি খারাপ যাবে, এটি আর নিছক শঙ্কা নয়, নিষ্ঠুর বাস্তবতা। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান অর্থনীতির দেশের জন্য এই বাস্তবতা সামাল দেওয়া সত্যি কঠিন।
আমার খালি শঙ্কা, এখন অর্থনীতির যে অবস্থা, তাতেই সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস। ২০২৩ সালে আরও খারাপ হলে মানুষ টিকবে কীভাবে? অর্থনীতি আর কতটা খারাপ হবে?
অর্থনীতি যে খারাপের দিকে যাচ্ছে, সেটা অনুমিতই ছিল। সরকারও সেটা জানতো। তাই আগে থেকেই তারা নানান পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু পদক্ষেপ নিয়ে তো আর অর্থনীতির ধস ঠেকানো যাবে না। বড় জোর ক্ষতি কীভাবে পোষানো সম্ভব, তার চেষ্টা করা যাবে। দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে হঠাৎ করেই প্রবল ভাটার টান। ৪৮ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ কমতে কমতে এখন ৩৪ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে। নেট রিজার্ভ এখন ২৮ বিলিয়ন ডলার।
রিজার্ভের মূল দুই উৎস রপ্তানি আর রেমিট্যান্সেও ভাটার টান। তাই রাতারাতি রিজার্ভ বেড়ে যাবে, তেমন সম্ভাবনাও নেই। রিজার্ভের পতন ঠেকানোর আপাতত একটাই উপায় আমদানি ব্যয় কমানো। রিজার্ভের মূল দুই উৎস রপ্তানি আর রেমিট্যান্সেও ভাটার টান। তাই রাতারাতি রিজার্ভ বেড়ে যাবে, তেমন সম্ভাবনাও নেই। রিজার্ভের পতন ঠেকানোর আপাতত একটাই উপায় আমদানি ব্যয় কমানো। সরকার সেই চেষ্টাও করছে। তাই এলসির ব্যাপারে সরকার একটু রক্ষণশীল আচরণ করছে। কিন্তু সমস্যা হলো আমদানিতে রাশ টানলে উৎপাদনেও তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আমাদের অর্থনীতির মূল সমস্যাও এটাই। আমাদের মাথা ঢাকলে পা উদোম হয়ে যায়, পা ঢাকলে মাথা। তবে অপ্রয়োজনীয় বিলাস সামগ্রী আমদানির ব্যাপারে আমাদের সত্যি কঠোর হতে হবে। যত চাহিদাই থাকুক, কিছু জিনিসের আমদানি একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। বিদেশি পানি ছাড়া যাদের তৃষ্ণা মেটে না, তাদের তৃষ্ণা মেটানোর দায়িত্ব জাতি নেবে না।
রিজার্ভ কমে যাওয়া, ডলারের বাজারে অস্থিরতা, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, সাথে গুজব-সব মিলে অর্থনীতির ওপর যে প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়েছে; তাতে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকাই দায়। জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছুঁয়েছে আগেই।
করোনার সময়ই চাকরি হারিয়ে, ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অনেক সচ্ছল মানুষও দরিদ্র হয়ে গেছেন, গ্রামে ফিরে গেছেন। চলমান সঙ্কট তাদের একদম প্রান্তে ঠেলে নিয়েছে। ব্যয় বাড়লেও মানুষের আয় বাড়েনি। বরং মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিলে আয় কমে গেছে। ব্যাংকে টাকা রাখলে টাকা বাড়ে তো নাই, উল্টো কমে যায়। এই অবস্থায় মানুষের পেটে টান পড়েছে। মানুষ না খেয়ে আছে, এমন অবস্থা এখনো তৈরি হয়নি, আশা করি কখনো হবেও না। কিন্তু না খেয়ে থাকা আর পুষ্টিকর খাবার এক বিষয় নয়। আমাদের অর্থনীতি যে জায়গায় পৌঁছেছিল, তাতে দুই বেলা দুই মুঠো খাওয়া নয়, পুষ্টিকর খাওয়া নিয়ে ভাবনা-চিন্তা চলছিল। কিন্তু এখন আবার কোনোমতে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার দিকেই যেতে হচ্ছে আমাদের।
মধ্যবিত্তের পাত থেকেও ডিম-দুধ সরে যাচ্ছে। মাংস এখন মাসিক খাবার। ফল এখন বিলাসিতা। মানুষ এখন সঞ্চয় ভেঙে খাচ্ছে। কিন্তু সঞ্চয় ভেঙে কয়দিন চলবে? কেউ তো জানে না সঙ্কটের শেষ কোথায়, কবে? সঙ্কট সামাল দেওয়ার জন্যই সরকার আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল-আইএমএফ’এর কাছে ঋণ চায়। এখানে সরকারের দূরদর্শিতার প্রমাণ মেলে। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান গর্তে পড়ার পর আইএমএফ’এর কাছে ঋণ চেয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ বিপদ আঁচ করেই ঋণ চেয়েছে। তবে আইএমএফ চাইলেই যেকোনো দেশকে ঋণ দেয় না। আইএমএফ’এর ঋণ পেতেও যোগ্যতা ও সক্ষমতা লাগে। আইএমএফ’এর একটি প্রতিনিধিদল ১৫ দিনের সফরে সংশ্লিষ্টদের সাথে দফায় দফায় বৈঠক করে বাংলাদেশকে সাড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত জানায়। মোট ৭ কিস্তিতে বাংলাদেশ এই ঋণ পাবে, যার প্রথমটি আসবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে।
আইএমএফ’এর সাড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণে বাংলাদেশের সব সমস্যা মিটে যাবে, ব্যাপারটি এমন নয়। তবে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে আইএমএফ’এর সম্মতিই স্বস্তির নিঃশ্বাস আনতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে। আসলে আইএমএফ’এর সিদ্ধান্তের একটা বড় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে দেশে এবং বিদেশে। বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হয়ে যাচ্ছে, এমন আশঙ্কায় যারা উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তাদের মুখও বন্ধ হয়ে যাবে। আইএমএফ’এর এই ঋণ মঞ্জুরির ঘোষণা বাংলাদেশের জন্য আরও অনেক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকাসহ অন্য উন্নয়ন সহযোগীরাও এখন বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে বা ঋণ দিতে দ্বিতীয়বার ভাববে না। আইএমএফ’এর ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা মানেই, সেটি একটি দেশের মানদ- ঠিক করে দেওয়া। অন্য উন্নয়ন সহযোগীদের আর নতুন করে যাচাই করতে হবে না। করোনার সময়ই চাকরি হারিয়ে, ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অনেক সচ্ছল মানুষও দরিদ্র হয়ে গেছেন, গ্রামে ফিরে গেছেন। চলমান সঙ্কট তাদের একদম প্রান্তে ঠেলে নিয়েছে। ব্যয় বাড়লেও মানুষের আয় বাড়েনি।
তবে আইএমএফ ঋণ দেওয়ার আগে কিছু শর্ত দেয়। অবশ্য কেউ বলেন শর্ত, কেউ বলেন সুপারিশ, কেউ বলেন পরামর্শ। যাই হোক, আইএমএফ’এর ঋণ পেতে কিছু শর্ত মানতেই হয়। আমার কাছে কিন্তু ঋণের চেয়ে শর্তগুলো বেশি আকর্ষণীয়, মনে হয়েছে। আইএমএফ’এর অধিকাংশ শর্তের সঙ্গে কেউই দ্বিমত পোষণ করবেন না। বরং বহুদিন ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ ও সুশীল সমাজ এই কথাগুলো বলে আসছিল। আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা আনা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ঋণ খেলাপি সংস্কৃতি বন্ধ করা, ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত বাড়ানো, রাজস্ব খাতে সংস্কার আনা, ভর্তুকি কমানো ইত্যাদি কোনো শর্তের সাথেই কেউ দ্বিমত করবেন না। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের অর্থনীতির সক্ষমতার ঘাটতি। আগেই যেমন বলেছি, পা ঢাকতে গেলে মাথা উদোম হয়ে যায়। আইএমএফ’এর শর্ত মেনে ভর্তুকি কমাতে গেলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গরিব মানুষের ওপর প্রবল চাপ পড়বে। এই দুঃসময়ে সেই চাপ নেওয়ার মত সক্ষমতা মানুষের আছে কিনা সেটাও ভেবে দেখা দরকার। আবার শর্ত না মানলে আইএমএফ ঋণ দেবে না। মানুষের যখন নুন আনতে পান্তা ফুরায় দশা তখন সরকার আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। আপাতত পাইকারি হারে বাড়লেও শিগগিরই খুচরা পর্যায়েও বাড়বে নিশ্চয়ই। ধরেই নেওয়া যায়, আইএমএফ’এর শর্ত মানতেই বাড়ানো হলো বিদ্যুতের দাম। শর্ত না মানলে আইএমএফ ঋণ দেবে না, আর শর্ত মেনে ভর্তুকি কমালে সাধারণ মানুষের ওপর চাপ পড়বে। বিদ্যুৎ এমন একটি কৌশলগত পণ্য, যার দাম বাড়লে তার প্রভাব পড়বে সর্বত্র। সরকার বলছে, আপাতত গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়বে না। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম যে বাড়বে, তার প্রভাব তো সাধারণ মানুষকেই পোহাতে হবে। ৩৮ দিন আগেও একবার পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন বিদ্যুতের সঙ্কট ছিল চরমে। আর আইএমএফ’এর শর্তও ছিল না। তাই তখন সরকার পিছিয়ে আসে। কিন্তু এবার আর পেছানোর উপায় নেই। পেছানোর উপায় না থাকলে সরকার দাম বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সাধারণ মানুষ পিছিয়ে কোথায় যাবে?
লেখক : বার্তা প্রধান, এটিএন নিউজ
মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা
ট্যাগস :
জনপ্রিয় সংবাদ