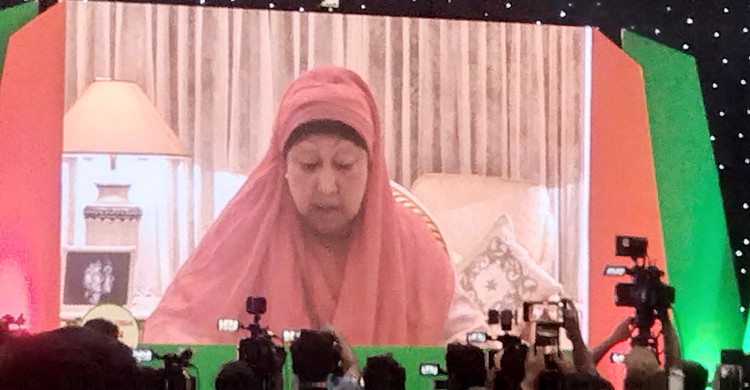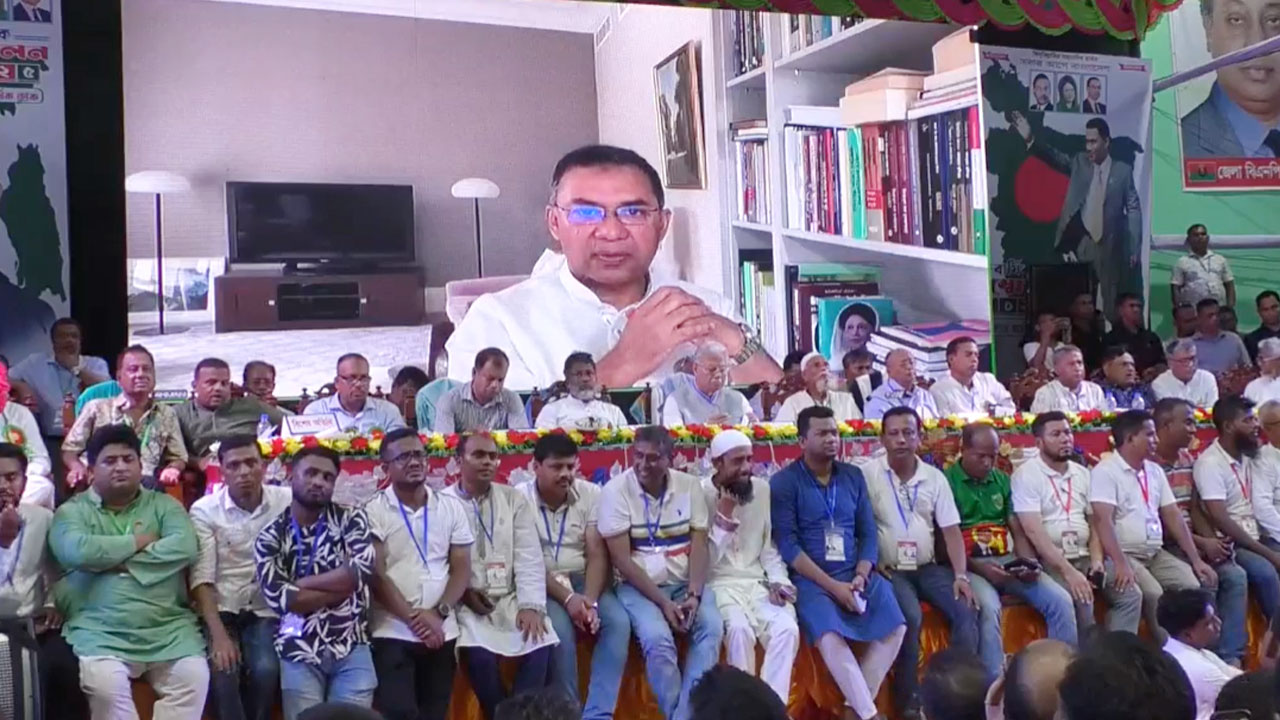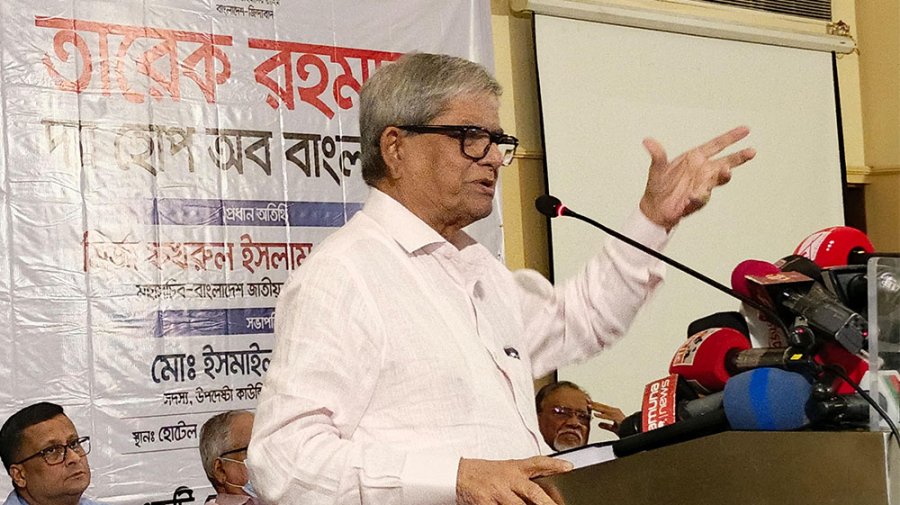শিশির ভট্টাচার্য্য : মানুষের জীবন ‘চিহ্নময়’। চিহ্ন চার প্রকার: প্রতিমা, প্রতীক, সংকেত এবং সূচক। ‘মানচিত্র’ একটি দেশের ‘প্রতিমা’, ‘হৃদয়’ ভালোবাসার প্রতীক, ‘কলম-বই’ ইত্যাদি শব্দ হচ্ছে বস্তুগুলোর সঙ্কেত এবং ‘ধোঁয়া’ হচ্ছে আগুনের সূচক। বস্তুর সঙ্গে চিহ্নের অনেকটাই মিল থাকলে ‘প্রতিমা’, মিল কম থাকলে ‘প্রতীক’, কোনো মিল না থাকলে ‘সংকেত’। ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা-অগণিত, বিচিত্র চিহ্নের সমাহার।
স্বীকার করি বা না করি, ‘বাঁকা চাঁদ’ ইসলামের প্রতীক এবং ‘ত্রিশূল’ বা ‘স্বস্তিকা’ হিন্দুধর্মের প্রতীক। ‘শাপলা’ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতীক, ‘কাস্তে-হাঁতুড়ি’ সাম্যবাদের প্রতীক, ‘ষড়শির তারা’ ইহুদি জাতির ‘প্রতীক’, ‘ঈগল’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতীক, ‘ম্যাপল পাতা’ কানাডা রাষ্ট্রের প্রতীক। প্রতিমাপূজা করুক বা না করুক, প্রতিটি জাতি ‘প্রতীকপূজা’ করে, কম আর বেশি। মসজিদের চূড়ায় বাঁকা চাঁদ দেখে প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলমানের মন শ্রদ্ধায় নত হয় না কি? শ্রদ্ধাকালীন কয়েকটি প্রশংসাসূচক কথা বলতে বলতে হাত দিয়ে এক-দুইটা ফুল ছুঁড়ে দিলেই ‘শ্রদ্ধা রূপান্তরিত হয়ে যায় ‘পূজা’য়।
চিহ্নগুলোর মধ্যে টিকে থাকার প্রতিযোগিতা চলে। জাতিতে-জাতিতে কিংবা একই জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতা-দ্বন্দ্বের স্মারক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই চিহ্নগুলো, যুদ্ধের ময়দানে বিবদমান গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন পতাকার মতো। প্রতিযোগিতায় হেরে গেলে একেকটি চিহ্ন মরে যায়। চিহ্ন মরে গেলে মরে যায় জাতি। মৃত্যুকে বিলম্বিত করে অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যেই প্রতিযোগী বা আক্রমণকারীর সঙ্গে মানুষ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে লিপ্ত হয়।
যেকোনো যুদ্ধের মতো প্রতীকের যুদ্ধেও প্রতিযোগী পক্ষগুলো জানে, তারা কী চায়। উভয় পক্ষেরই পরাজিত হবার ভয় আছে এই যুদ্ধে, যে কারণে কোনো পক্ষই ছাড় দিতে চাইছে না। মঙ্গল শোভাযাত্রায় পেঁচার মুখোশ নিয়ে আপত্তি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার জাফরউল্লাহর টেপা পুতুল চিনতে না পারাৃ একটি বিশেষ গোষ্ঠী হেরে যাবার ভয়ের উপসর্গ মাত্র। এই যুদ্ধে একটি পক্ষের অস্ত্রাগার হচ্ছে ‘ইসলাম ধর্ম’ (কিংবা এর বিশেষ ব্যাখ্যা) এবং তাদের বিরোধীদের অস্ত্রাগার হচ্ছে আবহমান ‘বাঙালি সংস্কৃতি’।
গত কয়েক শ বছর ধরে বাংলাদেশে এই দুটি পক্ষের লড়াই চলমান। ১৯৭১ সালে ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা-ধর্ষণ করেও একটি পক্ষ এই লড়াইয়ে জিততে পারেনি। তবে কোনো জয়ই চিরস্থায়ী নয়। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকে বিজয়ী দল আবারও হেরে বসে আছে নিজের দোষে। কিন্তু তারা যে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, তার প্রমাণ সামাজিক গণমাধ্যম, ওয়াজ মাহফিল, প্রতি শুক্রবারে মসজিদে-মসজিদে খুৎবায় সমালোচনা, এমনকি বোমাহামলা করেও বাংলাদেশে বর্ষবরণের উৎসবটিকে থামানো যায়নি।
দুই সংস্কৃতি কিংবা সংস্কৃতি ও ধর্মের এই লড়াই অভিনব কোনো ঘটনা নয়, অনুরূপ লড়াই চলছে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে, ভিন্ন রূপে, ভিন্ন প্রতিবেশে। এইসব লড়াই বা রাজনীতির প্রকৃত না বুঝে নববর্ষ কিংবা মঙ্গল শোভাযাত্রা সম্পর্কে ঢালাও মন্তব্য করতে গেলে সমূহ ভুল হবার ঝুঁকি থাকবে।
দেশে দেশে, যুগে যুগে, নববর্ষের উৎসবগুলো একেকটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। ইরানি-কুর্দি-পশতুনদের ‘নওরোজ’ আরবি ভাষা-সংস্কৃতির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক-হাতিয়ার। প্রবল চীনা সংস্কৃতির বিপক্ষে নিজেদের আবহমান সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রামে অন্যতম উৎসব-প্রতীক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ‘সঙ্করণ’। একইভাবে পাকিস্তান আমলে ছায়ানটের নববর্ষ বরণ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের দিক থেকে পাকিস্তানের অপশাসনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিবাদের প্রতীক। বাংলাদেশ আমলে নববর্ষ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা অন্ধকারবাদীদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের প্রতিবাদের প্রতীক।
জাতিতে জাতিতে যেমন টিকে থাকার প্রতিযোগিতা চলে, প্রতিযোগিতা চলে একাধিক সন তথা নববর্ষ উৎসবের মধ্যেও। একটি উৎসব চায় কোনোমতে টিকে থাকতে, অন্যটি চায় যেন তেন প্রকারে চেপে বসতে। বলা বাহুল্য, দুই নববর্ষের মধ্যে নয়, লড়াইটা চলে দুই বিবদমান জনগোষ্ঠী কিংবা তাদের সংস্কৃতির মধ্যে। মূলত প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের আত্মরক্ষার লড়াই এটা। বর্তমান পৃথিবীতে বেশ কয়েকটি সন বা অব্দ পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত: খ্রিস্টিয় বা গ্রেগরিয়ান সন, নওরোজ, আকবরের ফসলি সন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্করণ, হিজরি সন এবং চীনা সন।
আকবরের ফসলাব্দ তারিখ-ই-এলাহি বা বঙ্গাব্দ শুরু হয় মধ্য এপ্রিলে। ইরান-আফগানিস্তানে নওরোজ এবং ভারতের শকাব্দের সূচনা হয় মার্চের মাঝামাঝি। ভারত থেকে শুরু করে বাংলাদেশ-মায়ানমার-থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া-লাওস পর্যন্ত এপ্রিলের মাঝামাঝি সঙ্করণ বা নববর্ষ উৎসব পালিত হয়। চীনা নববর্ষ শুরু হয় মধ্য জানুয়ারিতে। গ্রেগরিয়ান যেকোনো মাসেই হিজরি সন শুরু হতে পারে।
নওরোজ এবং শকাব্দের সঙ্গে আকবর প্রবর্তিত ফসলাব্দের প্রতিযোগিতা চলছে দক্ষিণ এশিয়ায় গত শ পাঁচেক বছর ধরে। উত্তর ভারতে শকাব্দ আকবরের ফসলাব্দ তারিখ-ই-এলাহির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিতে গেছে, কিন্তু পিছিয়ে আছে সে গ্রেগরিয়ান অব্দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। তবে ফসলাব্দ যে একেবারে হেরে যায়নি তার প্রমাণ, পাকিস্তানের কোনো কোনো অঞ্চলে আশির দশকেও এপ্রিলের মাঝামাঝি নববর্ষ পালিত হতো, বাংলাদেশের মতোই।
মধ্য এপ্রিলে শুরু হওয়া একটি সন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হাজার বছর আগে থেকেই ছিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে আসা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বাঙালির অন্যতম পূর্বপুরুষ। তাদের হাত দিয়ে সনটি বাংলায় এসেছে কিংবা হয়তো বাংলা কিংবা ভারত থেকে এশিয়ায় ছড়িয়েছে। যেহেতু এসব অঞ্চলে আকবরের সাম্রাজ্য ছিল না কখনোই, সেহেতু মধ্য-এপ্রিলে শুরু হওয়া ফসলি সনের প্রকৃত প্রবক্তা আকবর হতেই পারেন না, তিনি এই সনটির সঙ্গে বিশেষ তারিখ (১৪২৯) যোগ করেছিলেন মাত্র।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্করণকে চীনা নববর্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হচ্ছে। এর প্রমাণ, ‘দাই’ জাতি চীন থেকে থাইল্যান্ডে এসে ‘থাই’ হবার আগে পর্যন্ত জানুয়ারিতেই চীনা নববর্ষ পালন করত। মূল চীনে দাই জাতি এখনও চীনা নববর্ষ পালন করে। থাইল্যান্ডের কোথাও কোথাও এখনও জানুয়ারিতে চীনা নববর্ষ পালিত হয়। থাইরা পরবর্তীকালে অনুধাবন করে যে মধ্য এপ্রিলে নববর্ষ শুরু করা থাইল্যান্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ।
আরব দেশে ইসলামপূর্ব যুগে সৌরবর্ষ চালু ছিল। ইসলাম-পরবর্তী যুগে চান্দ্র হিজরি সন চালু হয়। ‘অবৈজ্ঞানিক ও ত্রুটিপূর্ণ’ মনে করায়, হিজরি সন কমপক্ষে দুইবার বাদ দেওয়া হয়েছে মুসলিম শাসনামলেই, একবার আন্দালুসিয়ায় এবং আরেকবার ভারতবর্ষে, আকবরের আমলে। ইরানেও হিজরি সন নওরোজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। সুলতানি আমলে চালু থাকা হিজরি সনকে বাতিল করেই আকবলের ফসলি সন বা বঙ্গাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
বাঙালি জাতিয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে টিকে থাকলেও সন হিসেবে বঙ্গাব্দ বাংলা অঞ্চলে মৃতপ্রায়। বেশির ভাগ বাঙালি জানেই না বর্তমানে কোন বঙ্গাব্দ চলছে। ১৫ এপ্রিল থেকে পরের বছরের মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত বেশির ভাগ বাঙালি বাংলা সনের কোনো খবরই রাখে না। বঙ্গাব্দকে যদি শিক্ষাবর্ষ ও করবর্ষ ঘোষণা করা হতো (করা উচিত, কারণ বঙ্গাব্দ বাংলাদেশের ঋতুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ!) তবে নিত্যদিনে ব্যবহার্য ও অপরিহার্য হয়ে বঙ্গাব্দ বাঙালির জীবন ও মননের অংশ হয়ে উঠত। হাজার বছর আগে মৃত হিব্রু ভাষাকে ইজরায়েল রাষ্ট্র যদি পুনরুজ্জীবিত করতে পেরে থাকে, নিজের ঐতিহ্যের অন্যতম প্রতীক বঙ্গাব্দকে নিত্যজীবনের অংশ করে তোলা বাঙালির পক্ষে এমন কি কঠিন?
পৃথিবীর বাকি সবগুলো সনকে হারিয়ে আপাতত প্রথম অবস্থানে রয়েছে গ্রেগরিয়ান সন বা খ্রিস্টাব্দ। হিজরি এবং খ্রিস্টাব্দ– এই দুই সনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে নওরোজ ও বঙ্গাব্দকে। খ্রিস্টাব্দ এবং চীনা সন– এই দুইয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্করণ। তুরস্ক ও ইরানের কুর্দি জনগোষ্ঠী, আফগানিস্তান-পাকিস্তানের পশতুনদের মধ্যে নওরোজ এখনও টিকে আছে।
নতুন ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া হলে পুরনো সংস্কৃতি, পুরনো ভাষা সাধারণত হারিয়ে যায়। কিন্তু এখানেও প্রতিযোগিতার ব্যাপার আছে, জাতিতে জাতিতে মানসিক গঠনেও তফাৎ থাকে। মাগরিব অঞ্চলে আরবির সঙ্গে যুদ্ধে স্থানীয় ভাষাগুলো অনেকটাই হেরে গেছে। অনেক মনোকষ্ট নিয়ে বের্বেরভাষীরা নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি কোনোমতো টিকিয়ে রেখেছে। পক্ষান্তরে ধর্মের লড়াইয়ে হেরে গিয়েও পারসিক ভাষা ও সংস্কৃতি সগৌরবে টিকে আছে ইরানে। তুরস্কে আরবি ভাষা ও লিপি হেরে গেছে, কিন্তু তুরস্কের নিজস্ব কোনো নববর্ষ নেই।
জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে মানসিকতায় তফাৎ আছে। হিন্দুরা সংস্কৃতে মন্ত্র পড়ে। কিন্তু ইউরোপের মানুষ সেই মধ্যযুগেই অবোধ্য ল্যাটিন ভাষায় প্রার্থনা করতে রাজি হয়নি। পাকিস্তানের মুসলমানের ওপর উর্দুভাষা, আরবি লিপি সহজেই চাপিয়ে দেওয়া গিয়েছে, কিন্তু পূর্ব ভারতে বাঙালিরা এই অপচেষ্টা সফল হতে দেয়নি। কোনো কোনো জাতির আত্মসম্মানবোধ এতটাই প্রবল যে নিজের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় সে জানবাজি লাগিয়ে দেয়, কারণ সে জানে, প্রতীকের পরাজয় মানে তার নিজেরও পরাজয়। সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে ধর্ম পালন করে মৃত্যুর পর ‘স্বর্গে’ যাবার কথায় বিশ্বাস সে করে। কিন্তু মৃত্যুর আগে মাটির পৃথিবীটাকে অসংস্কৃত এবং আবাস-অযোগ্য নরক হতে দিতে তারা একেবারেই রাজি নয়।
লেখক : অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।