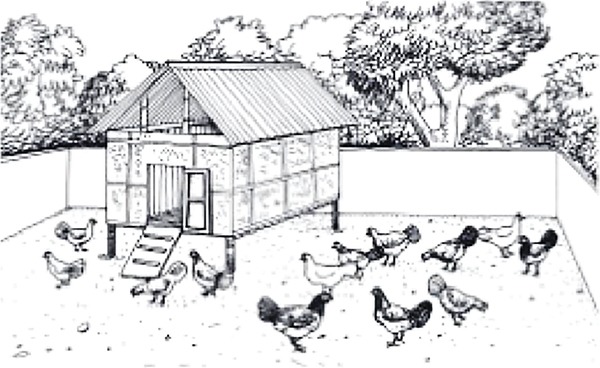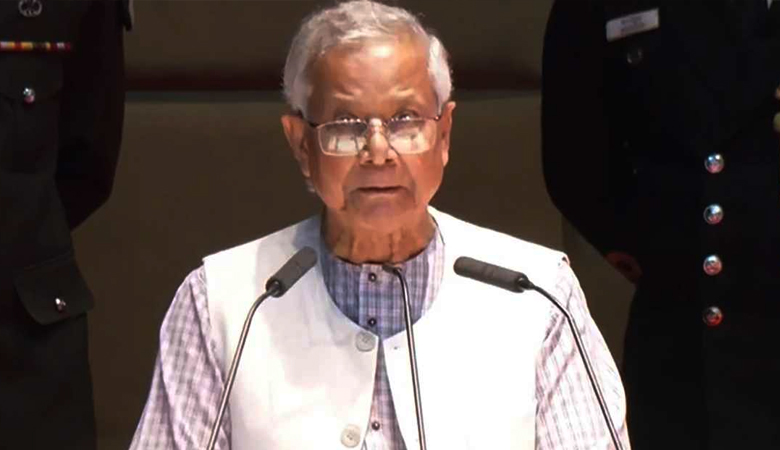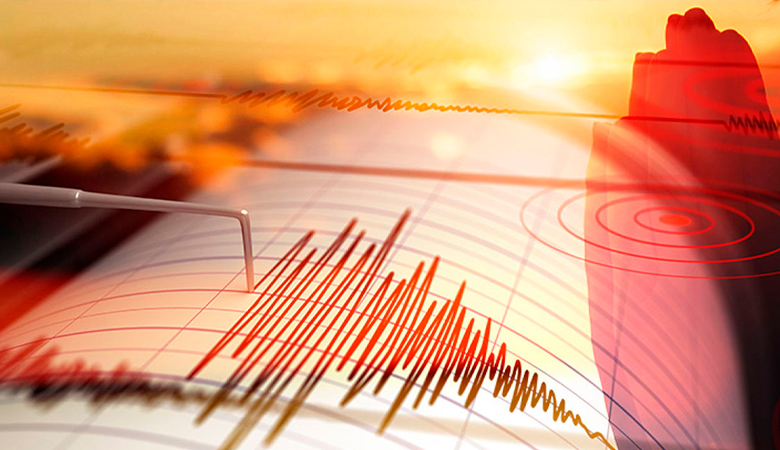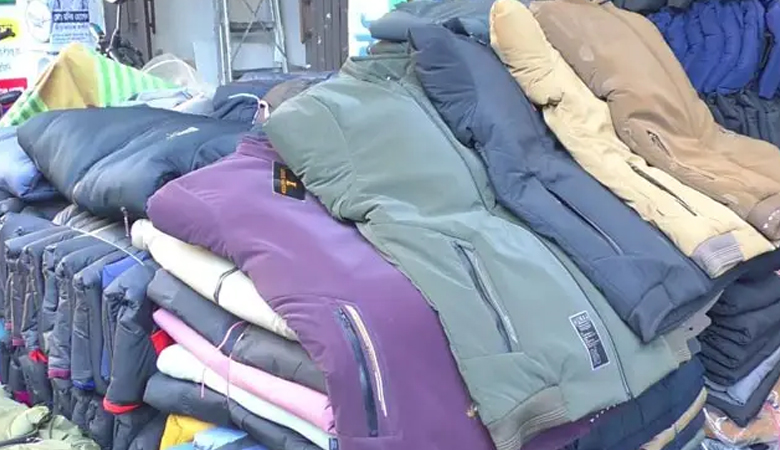প্রশান্ত কুমার শীল
হাজার হাজার বছর আগে হিন্দু বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ‘প্রাপ্তেষু ষোড়শ বর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ’। অর্থাৎ ১৬ বছর বয়স হলেই পিতার উচিত সন্তানের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করা। শাস্ত্রকারদের এই দৃষ্টিভঙ্গি এটাই বোঝায় যে, ষোড়শী বয়সসীমায় মানুষ চিন্তাচেতনায় পরিপক্বতার এক নতুন ধাপে প্রবেশ করে। যদিও এই মতের বিজ্ঞানভিত্তিক কোনও সমীক্ষা নেই, তবুও এই মতের ভিত্তি ছিল তৎকালীন সমাজে কিশোরদের আচরণ ও দায়িত্ব গ্রহণের প্রবণতা।
বর্তমান আধুনিক বিশ্বে দীর্ঘ গবেষণা ও আলোচনার ভিত্তিতে অধিকাংশ দেশেই ১৮ বছর বয়সকে সাবালকত্বের সীমা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর ফলে নাগরিকরা ভোটাধিকারসহ একাধিক আইনগত অধিকার অর্জন করে এই বয়সসীমায়। তবে এই বয়স নির্ধারণের পেছনে রয়েছে বৈজ্ঞানিক যুক্তি, সামাজিক বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। তবু প্রশ্ন থেকেই যায়, এই ১৮ বছর বয়স কি আজও প্রাসঙ্গিক বর্তমান বাস্তবতায়? তবে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতায় কবি উল্লেখ করেছেন- ১৮ বছর হলো ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, দুঃসাহসিকতা, পদাঘাতে পাথর বাধা ভাঙার স্বপ্ন কিংবা রক্তদানের পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে তরুণদের ঝাঁপিয়ে পড়ার বয়স। আসলেই কি ১৮ বছর এমনই?
১৬ বছর বয়সে মানুষ কতটা পরিপক্ব? এই নিয়ে রয়েছে বেশ বিতর্ক কিংবা খোঁড়া যুক্তি। তবে আধুনিক সময়ে ১৬ বছর বয়সি কিশোররা শুধুই স্কুলের পাঠে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় থাকে, চাকরির চেষ্টা করে, কখনো কখনো পারিবারিক দায়িত্ব বহন করে এবং নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়; এমনকি বিভিন্ন দেশে যেমন- অস্ট্রিয়া, ব্রাজিল ও স্কটল্যান্ডে ১৬ বছর বয়স থেকেই ভোটাধিকার দেওয়ার ইতিহাস রয়েছে।
সম্প্রতি ব্রিটেনও ঘোষণা দিয়েছে, পরবর্তী নির্বাচনে ১৬ বছর বয়সীদের ভোটাধিকার দেওয়া হবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার যুক্তি দিয়েছেন- ‘যে নাগরিক আয় করে, কর দেয়; তার দেশের সিদ্ধান্তে মতামত জানানোর অধিকারও থাকা উচিত।’ এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে আসে- বাংলাদেশ কি এই পদক্ষেপ অনুসরণ করতে প্রস্তুত?
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ১৬ বছর বয়সি ভোটারদের যত সমস্যা: বাংলাদেশ একটি জনবহুল উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। এখানে তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি একটি বিশাল জনগোষ্ঠী রয়েছে, যারা এখনো মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় যুক্ত। এদের মধ্যে অনেকেই প্রগাঢ় রাজনৈতিক সচেতনতা, সামাজিক অনুভূতি এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতায় পারদর্শী। কিন্তু এখানেই কিছু মৌলিক প্রশ্ন সামনে চলে আসে; যা নিয়ে এখন খোলামেলা আলোচনা করা দরকার।
১. পরিপক্বতার প্রশ্ন: ১৬ বছর বয়স তরুণ-তরুণীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিবর্তনের সময়। এই সময় তারা বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় দেখা দেয় নানা অস্থিরতা। বাংলাদেশের মতো দেশে রাজনীতির জটিল বাস্তবতা বোঝার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ, পরিপক্বতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন। প্রশ্ন ওঠে, এই বয়সী ভোটাররা আদৌ কি দেশের জন্য সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে কিনা? নাকি নিজস্ব বিবেক বিসর্জন দিয়ে মরীচিকার পিছনে ভোঁ-দৌড় দিবে?
২. রাজনৈতিক অপব্যবহারের ঝুঁকি: বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় দলীয় সমর্থনের নামে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার করে রাজনৈতিক দলগুলো। এই সময় তারা নানা ধরনের উদ্দেশ্য হাসিল করে খুব সুকৌশলে। মূলত রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ব্যবহার করে দলের ক্যাডার বা লাঠিয়াল বাহিনীর ভূমিকায়। তাই তো এই ১৬ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক দলে টানার প্রবণতা আরও বাড়বে সামনের নির্বাচনে; যা তাদের শিক্ষাজীবন, মানসিক স্বাস্থ্য এবং স্বাভাবিক বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে পড়াশোনা করা। এসব বাদ দিয়ে তারা যদি একেবারে রাজনৈতিক জাঁতাকলে পড়ে, তাহলে দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে পড়বে। অটো পাসের মতো অনার্য দাবি তারা চাওয়া শুরু করবে। এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় নেমে আসবে চরম নৈরাজ্য।
৩. পরিচয় ও নথিপত্র জটিলতা: যদি আগামী বছর জুনের আগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে এত কম সময়ের মধ্যে ভোটার তালিকা, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও বায়োমেট্রিক যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা পোহাতে হবে আমাদের নির্বাচন কমিশনকে। প্রশ্ন থেকে যায় এত কম সময়ের মধ্যে তারা কি সব প্রস্তুত করতে পারবে? এর উপর এবারের নতুন সংযোজন প্রবাসীদের ভোটদানে সংযুক্ত করা। আবার ১৬ বছর বয়সিদের সম্পৃক্ত করা; যা প্রশাসনিকভাবে জটিল ও ব্যয়বহুল হবে। বলে রাখা ভালো, এখনো অনেকেই জন্মসনদের অসঙ্গতি, ঠিকানার অস্থায়িত্ব ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে ভোগান্তিতে আছে। তার ওপরে এই নতুন নিয়ম চালু হলে হয়তো আরও অনেক বেশি জটিলতা সৃষ্টি হবে।
৪. শিক্ষাগত বাধা ও প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা: এই বয়সে অতি আবেগে অনেক ছাত্রছাত্রী রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিসরে যুক্ত হতে চায়। তাই তাদের অতি সহজেই রাজনৈতিক দলগুলো প্রভাবিত করে। যার ফলে এসবে জড়িয়ে পড়ে তাদের পড়াশোনায় চূড়ান্ত ক্ষতি হবে। যা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিক আচরণে প্রভাব ফেলবে। আমাদের বুঝা উচিত কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিরা এই রাজনীতিকে পেশা বা খেলা হিসেবে দেখে। আবার ভোট কেনাবেচার মতো দুর্নীতিতে এই বয়সীরা সহজে শিকার হতে পারে। তাই এই প্রভাব সহজে মুক্ত করতে প্রয়োজন রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষক, পরিবার বা মিডিয়ার প্রত্যক্ষ ভূমিকা।
৫. জুলাই চেতনা ও তরুণদের রাজনৈতিক অভিলাষ: ছাত্রছাত্রীরা গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটা স্বৈরাচারী সরকারের পতন করেছে। যা তাদের অবস্থানকে ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় করে রাখবে। বাস্তবতা হলো সব তরুণ যে রাজনীতি করবে- এমনটা যেন না হয়। বিভিন্ন শ্রেণি পেশায় তাদের যুক্ত হওয়া উচিত। শুধু রাজনীতির আবর্তে শুধু ঘুরতে না থেকে তাদের বিভিন্ন সেক্টরে যাওয়া উচিত। শুধু রাজনীতি তাদের যেন একমাত্র ব্রত না হয়। এর ফলে দেশ অনেকটা পিছিয়ে যাবে।
নাবালকত্ব বনাম গণতান্ত্রিক অধিকার- দ্বৈততা কেন? একদিকে ১৬ বছর বয়সে যদি কেউ অপরাধ করে, তাহলে তাকে ‘নাবালক’ হিসেবে গণ্য করে আইনি সুবিধা দেওয়া হয়। আবার সেই একই বয়সে যদি কেউ আয় করে, কর দেয়, তাহলে তার ওপর রাষ্ট্রের একগুচ্ছ দায়িত্ব চাপানো হয়। তাহলে ১৬ বছর বয়সীরা যখন কাজ করতে, আয় করতে, কর দিতে সক্ষম- তাদের গণতান্ত্রিক মত প্রকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা কি যৌক্তিক? এই দ্বৈততার পরিপ্রেক্ষিতে আইন ও বাস্তবতার মধ্যে একটি সমন্বয়ের দরকার রয়েছে। যদি কোনও বয়সে কেউ রাষ্ট্রীয় দায়ভার বহন করতে পারে, তাহলে মতপ্রকাশ বা অংশগ্রহণের অধিকার থেকেও তাদের বাদ দেওয়া অন্যায্য।
সম্ভাব্য প্রভাব- ভবিষ্যতের নির্বাচন: বাংলাদেশে যদি ভোটের বয়সসীমা ১৮ থেকে কমিয়ে ১৬ করা হয়, তাহলে নির্বাচনি মাঠে যেসব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে; তা হলো ১. ভোটার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। ২. তরুণভিত্তিক ইস্যুগুলো নির্বাচনি মেনিফেস্টোতে প্রাধান্য পাবে। ৩. প্রযুক্তিনির্ভর, স্মার্ট প্রচারণার গুরুত্ব বাড়বে। ৪. রাজনৈতিক দলগুলোয় তরুণ কর্মীবাহিনীর প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।
অন্যদিকে বিপরীত চিত্রও থাকতে পারে। অদক্ষ বা অপ্রস্তুত তরুণ ভোটাররা ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে; যার প্রভাব জাতীয় নেতৃত্বে পড়বে। রাষ্ট্র তখন কার্যকর ভূমিকায় নাও থাকতে পারে। ১৬ বছর বয়স মানেই যে পূর্ণ পরিপক্বতা, তা নয়। এটা এক রকম বুদ্ধিবৃত্তিক উন্মেষের সূচনার বয়স। এই বয়সে নাগরিকরা যেমন কিছু অধিকারভোগী, তেমনি অনেক দায়িত্ববানও। কাজেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ১৬ বছরে ভোটাধিকার দেওয়ার আগে প্রয়োজন ব্যাপক গবেষণা, পাইলট প্রকল্প, সচেতনতামূলক প্রচার এবং স্কুল পর্যায়ে নাগরিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। প্রয়োজনে আইন স্থবির নয়, সময়োপযোগী পরিবর্তন অপরিহার্য। তবে তা হঠাৎ করে নয়—পরিকল্পিত, পর্যবেক্ষণভিত্তিক এবং সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনার নিরিখে বিবেচনায় রাখা উচিত । সেক্ষেত্রে হয়তো একদিন আমরা বলতে পারবো ষোড়শ বর্ষেই ভোটের অধিকার। আর তা হবে যুক্তি ও বাস্তব সিদ্ধান্তের নিরিখে ।
লেখক: গণমাধ্যম শিক্ষক ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক
(মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব)
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ