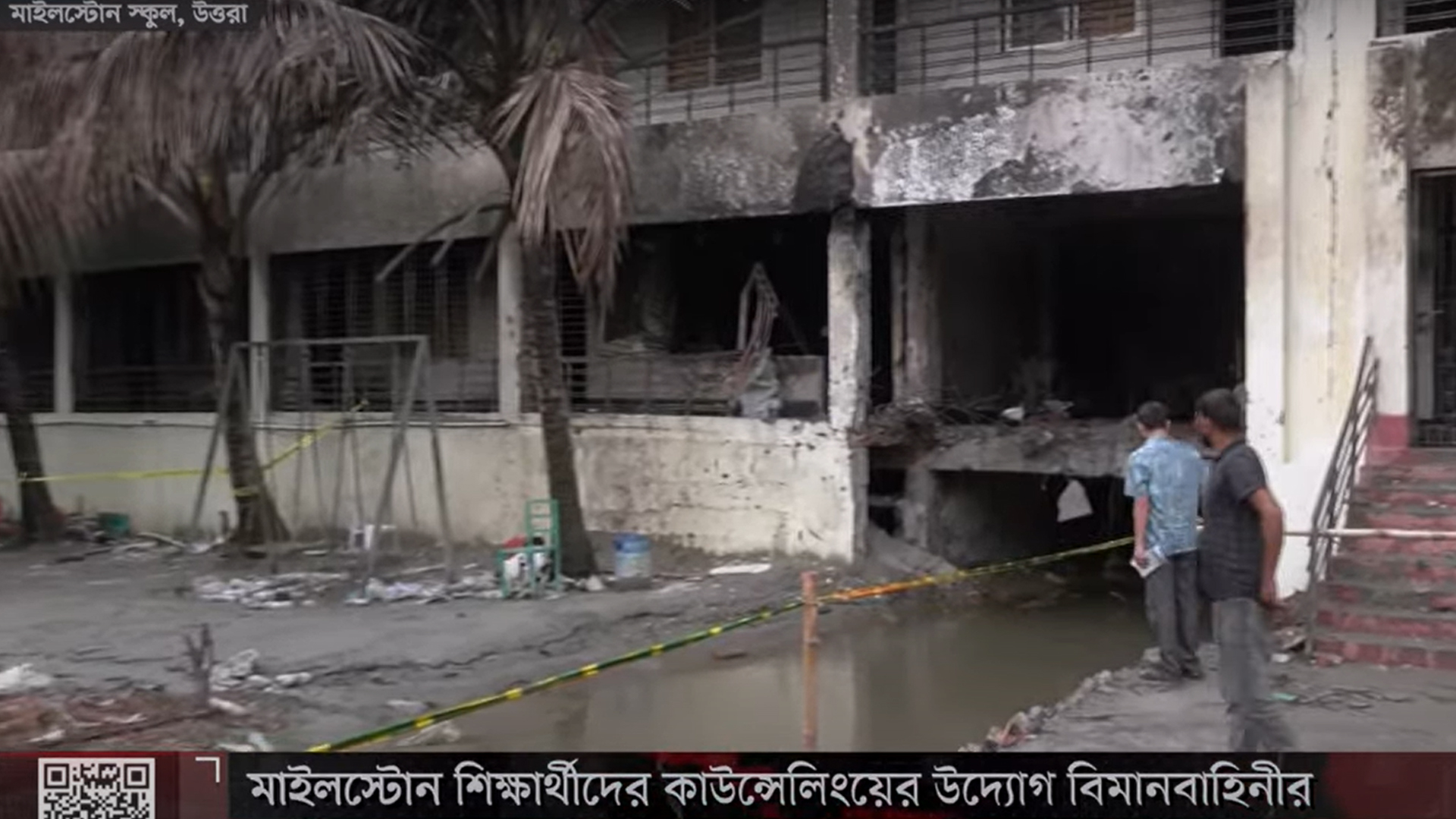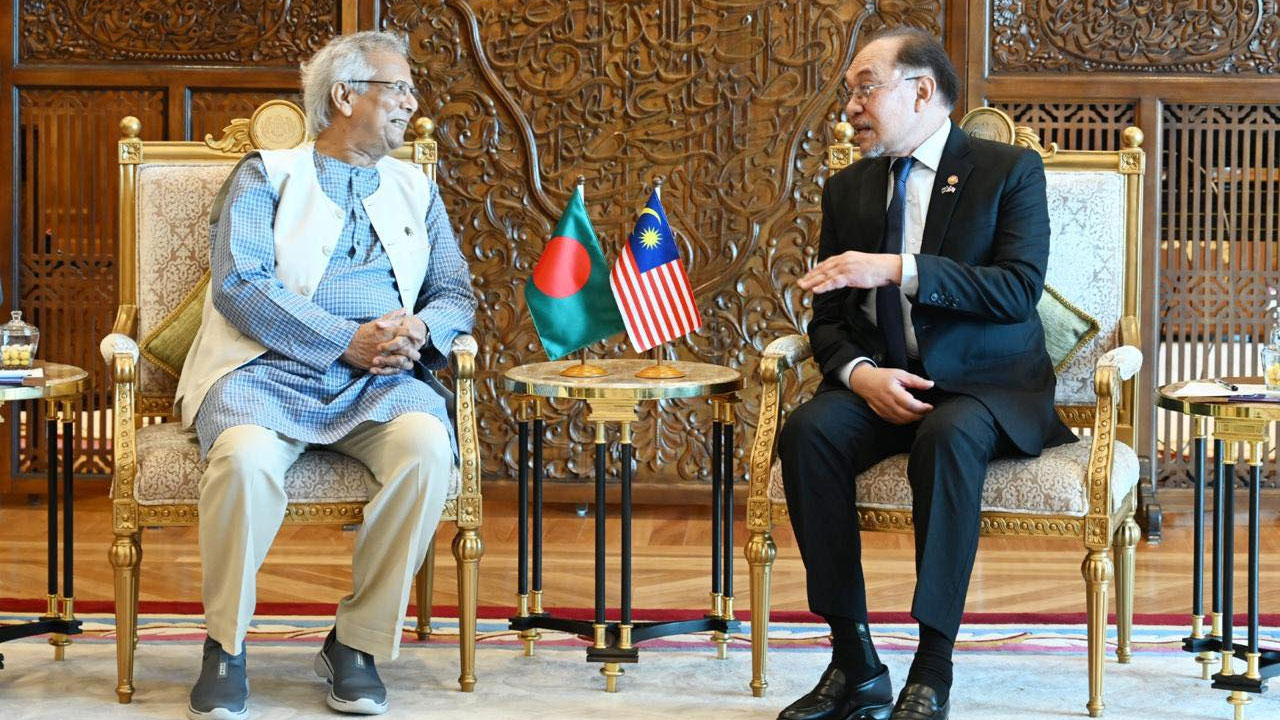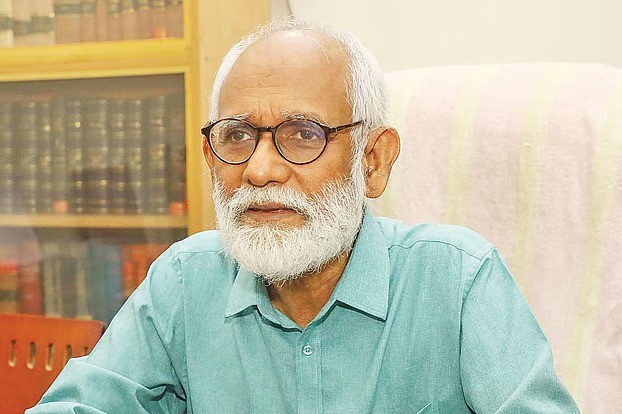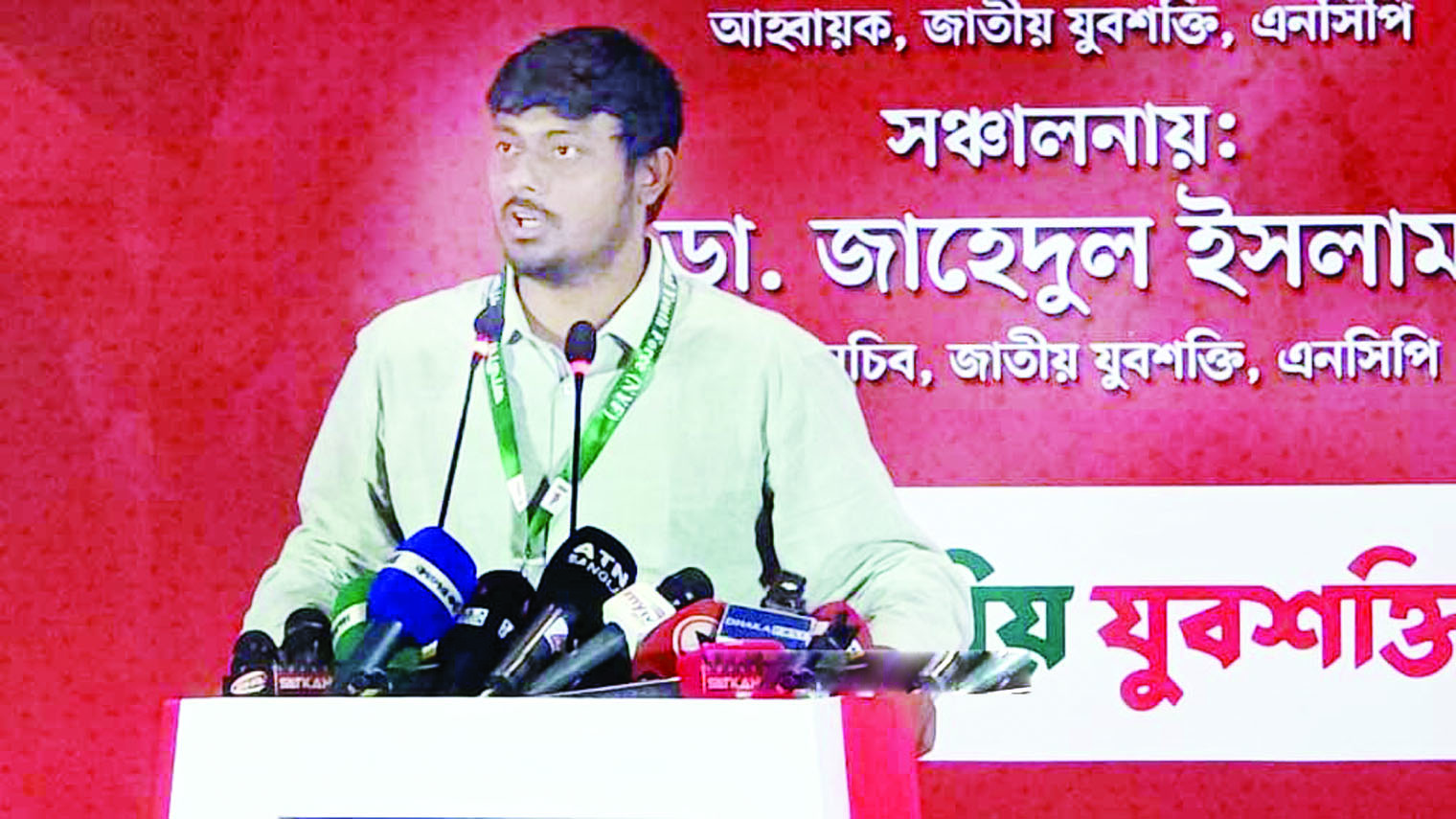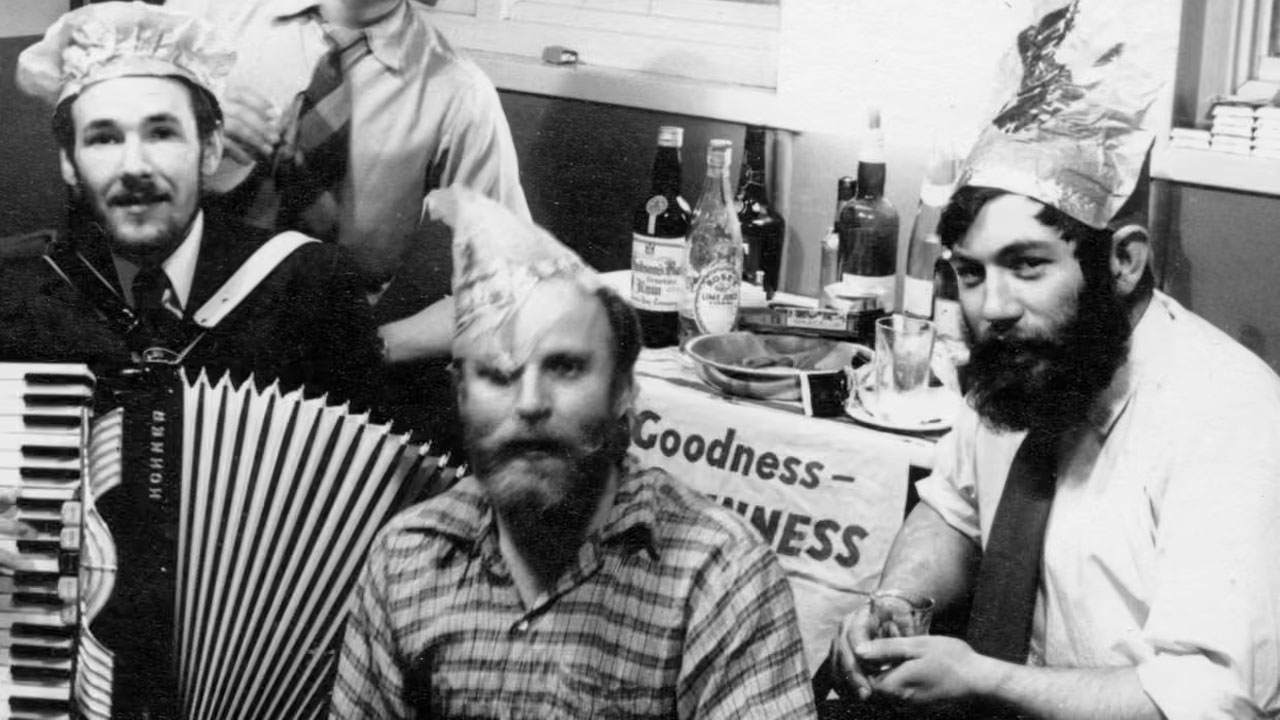আমীন আল রশীদ : শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে রাতের আঁধারে চুপিচুপি কিংবা পুলিশি পাহারায় উপাচার্যের ক্যাম্পাস ত্যাগের একাধিক ঘটনা এই দেশে ঘটেছে। এবার ঘটলো তার উল্টো। ছাত্রদের একটি অংশের নির্যাতনের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে অনশন কর্মসূচি পালন করেছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা তার প্রতিষ্ঠানের কিছু শিক্ষার্থীর হাতেই লাঞ্ছিত হয়েছেন—যারা ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ। সুতরাং আমাদের দেশে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক যে কোন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে কী হাল—সেটি বোঝার জন্য এইসব আপাতবিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোই যথেষ্ট।
সাম্প্রতিক কয়েকটি সংবাদ শিরোনামে চোখ বুলানো যাক:
১. চমেক ছাত্রলীগের ‘নির্যাতনের’ শিকার দুই ছাত্র আইসিইউতে; প্রথম আলো, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩।
২. ছাত্রলীগের নিপীড়নের প্রতিবাদে রাবি অধ্যাপকের অনশন; দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩।
৩. ‘ভাই কি এই ক্যাম্পাসের’ প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয় ছিনতাই; ডেইলি স্টার বাংলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩।
৪. ছিনতাইয়ের ঘটনায় ঢাবি ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার; কালবেলা, ১৯ জানুয়ারি ২০২৩।
৫. কাভার্ড ভ্যান আটকে ‘ছিনতাই’, দুই ছাত্রলীগ কর্মীসহ ৩ শিক্ষার্থী গ্রেপ্তার; প্রথম আলো, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩।
৬. দম্পতিকে মারধর করে চেইন ছিনতাইয়ের অভিযোগ, ঢাবি ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার; সমকাল, ১৯ জানুয়ারি ২০২৩।
৭. বইমেলায় পুলিশ পরিচয়ে চাঁদাবাজি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের ২ নেতা গ্রেপ্তার; বিডিনিউজ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩।
প্রথম শিরোনামের স্থল চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ। সাম্প্রতিক এই ঘটনাটি সারা দেশে আলোড়ন তুলেছে। প্রশ্ন উঠেছে, যারা সহপাঠীদের নির্যাতন করে আইসিইউতে পাঠিয়ে দেন, ডাক্তার হওয়ার পরে তারা রোগীদের সঙ্গে কী আচরণ করবেন? রোগীদের সেবা দেবেন নাকি আইসিইউতে পাঠাবেন? কী শেখানো হয় এই মেডিকেলে কলেজে? সমস্যাটা কার? শিক্ষক, অভিভাবক না রাজনীতির?
দ্বিতীয় শিরোনামটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের। খবরে বলা হয়, দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের নৈরাজ্য ও নিপীড়নের প্রতিবাদে এবং দোষীদের বিচারের মুখোমুখি করার দাবিতে প্রতীকী অনশন করেছেন অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন খাঁন। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও দখলমুক্ত ক্যাম্পাসের দাবি জানান।
প্রশ্ন হলো, কীরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হলে একজন অধ্যাপককে তার সন্তানতুল্য ছাত্রদের বিচারের দাবিতে অনশন করতে হয়? ছাত্রদের সঙ্গে কি তার কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে? নাকি এখন ওই শিক্ষকের রাজনৈতিক পরিচয় খুঁজে তার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দল বা ছাত্র সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের অভিযোগ আনা হবে? তাকে কি সরকারবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে?
অস্বীকার করা যাবে না যে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও দলীয় রঙে রঞ্জিত বা দলীয় পরিচয়ে বিভক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞান বিকাশ ও গবেষণার বাইরে গিয়ে যে দলীয় ক্ষমতা চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হলো, সেখানে শিক্ষকদের এই দলীয় লেজুড়বৃত্তিও কম দায়ী নয়। আবার এও ঠিক যে, রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র-শিক্ষকদের এভাবে দলীয় কর্মীতে পরিণত করে নিজেদের ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সহজ করতে চায়। তার মানে সমস্যার শেকড় অনেক গভীরে। ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী পরিচয়ে মাস্তানি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও বিরোধী মতের অনুসারীদের পিটিয়ে আইসিইউতে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনার পেছনে এই দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতিই যে প্রধানত দায়ী, সেটি অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই।
৬ নম্বর শিরোনামের ঘটনাটি ৪ ফেব্রুয়ারির। এক বিবাহিত দম্পতি তাদের নাজিমউদ্দিন রোডের বাসা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মামার বাড়িতে বেড়াতে যান। তারা ঢাবির শহীদ মিনার চত্বরে পৌঁছালে ঢাবি ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ১০ থেকে ১২ জনের একটি দল তাদের বাধা দেয়, নির্দয়ভাবে মারধর করে, ২২ হাজার টাকা ও এটিএম কার্ড ছিনতাই করে চলে যায়।
এই ছিনতাইয়ের ঘটনায় ভুক্তভোগীর মামা ঢাবির মাস্টারদা সূর্য সেন হলের প্রিন্সিপাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মো. আব্দুল মোতালেব গণমাধ্যমকে আক্ষেপের সুরে বলেন, ‘আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঢাবির শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করি। অথচ, সেই শিক্ষার্থীরা আমার গায়ে হাত তুলতে একটুও দ্বিধা করলো না! ওরা কবে থেকে এমন ঠা-া মাথায় অপরাধী হয়ে গেল?’
দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পরে যেখানে ভর্তি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকেন লাখ লাখ শিক্ষার্থী। কিন্তু সেখানে ভর্তি হওয়ার পরে তাদের একটি অংশ কী করে ছিনতাইকারী হয়ে ওঠে? কেন তাদের কারণে কিছুদিন পরপরই এই বিশ্ববিদ্যালয়টি খারাপ খবরের শিরোনাম হয়? কেন তাদের ছিনতাই করতে হয়। টাকার জন্য?
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে কি অনেক টাকা লাগে যে পরিবার সেই টাকা দিতে পারছে না বলে তাদের ছিনতাই করতে হচ্ছে? যদি তাই হতো তাহলে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ছিনতাইয়ে জড়িত হতো। তা যেহেতু হচ্ছে না, তার মানে অভাবের কারণে তারা ছিনতাই করছে না। তারা ছিনতাই করছে টাকার লোভে; তারা ছিনতাই করছে নেশার পয়সা জোগাড় করতে; তারা ছিনতাই করছে ছাত্র অবস্থাতেই বিলাসী জীবনের সুখলাভ করতে; তারা ছিনতাই করছে ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করতে; তারা ছিনতাই করতে পারছে কারণ তারা কোনও না কোনোভাবে ক্ষমতার বৃত্তে অবস্থান করছে এবং তাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, তারা ধরা পড়বে না; ধরা পড়লেও রাজনৈতিক বড়ভাইরা তাদের প্রশ্রয় দেবে। তাদের মনে জন্মেছে যে রাজনৈতিক ক্ষমতাই শেষ কথা।
প্রশ্ন হলো, কোন প্রক্রিয়ায় বা কীভাবে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিনতাইকারী হয়ে ওঠে? ক্লাসরুমে শিক্ষকরা তাদের কী পড়ান? নিশ্চয়ই সেখানে ছিনতাইয়ের কলাকৌশল শেখানো হয় না। তাহলে ছিনতাইয়ের এই ‘জ্ঞান’ তারা কোথায় পায়?
গণমাধ্যমের খবর বলছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, দোয়েল চত্বর, ভিসি চত্বর, কলা ভবন, ফুলার রোড ও পলাশী এলাকায় একটি সংঘবদ্ধ চক্র সক্রিয়। তারা নিজেদেরকে ঢাবির শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা পরিচয় দেয়। এই সমস্যা দীর্ঘদিনের হলেও দায়মুক্তির সংস্কৃতির কারণে তারা আরও বেপরোয়া।
আবার ছাত্রলীগ কর্মীরা অপরাধমূলক কাজ করে শিরোনাম হলে নেতারা বলেন, ‘সংগঠন ব্যক্তির দায়ভার নেবে না’। অথচ খুব কম ক্ষেত্রেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিষয়টা এরকম হয়ে গেছে যে, যতক্ষণ না কারো বিরুদ্ধে কোনও অপরাধমূলক কাজের খবর আসছে, ততক্ষণ তিনি দলের আদর্শিক কর্মী। কিন্তু অপরাধের অভিযোগ এলেই অনুপ্রবেশকারী!
তবে সাংগঠনিক এই ব্যবস্থা গ্রহণ বা দলীয় রাজনীতির অপরাধমূলক প্রবণতার বাইরে গিয়েও বিশ্বিবদ্যালয়ের পরিবেশ তথা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কী- সেই প্রশ্নও অনেক দিন ধরে নানা ফোরামে আছে। যেমন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কতটি আসলেই বিশ্ববিদ্যালয়, আর কতটি কলেজের উন্নত সংস্করণ, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে নতুন জ্ঞান তৈরি ও মুক্তচিন্তা বিকাশের জায়গা। চিন্তা করতে শেখা ও প্রশ্ন করার সাহস জোগানোর প্লাটফর্ম হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। এটি নেতৃত্ব তৈরির কারখানা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কী ধরনের নেতৃত্ব তৈরি করছে? নেতৃত্ব মানে মাস্তানি করা? এমন নেতৃত্ব যে তার বিরুদ্ধে স্বয়ং একজন অধ্যাপককে অনশন করতে হয়?
সমস্যা হলো, এখন সবাই পরীক্ষার্থী। শিক্ষার্থী নন। স্কুলে কলেজে তারা জিপিএ ফাইভযোদ্ধা আর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিসিএসযোদ্ধা। অর্থাৎ যেকোনও উপায়ে পরীক্ষায় পাস এবং সরকারি চাকরিই ‘এইম ইন লাইফ’। সুতরাং শিক্ষকদের কেউ যদি এখন তার শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের ভেতরে মানবিক বোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেন, সেই শিক্ষককে পিটুনি খেয়ে ক্যাম্পাস ছাড়তে হবে কি না—সেটিই বড় প্রশ্ন।
এই সমস্যা থেকে বেরোনোর একমাত্র উপায় রাজনৈতিক সদিচ্ছা। রাজনৈতিক দলগুলো যদি তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যবহার করা বন্ধ না করে, তাহলে নতুন জ্ঞান সৃজন, মুক্তচিন্তার বিকাশ, চিন্তা করার শক্তি ও প্রশ্ন করার সাহস জোগানোর বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বিশ্বের যাবতীয় বিদ্যা এসে লয়প্রাপ্ত হবে- যেখান থেকে প্রতি বছর লাখ লাখ পরীক্ষার্থী পাস করে বের হবে, কিন্তু কোনও শিক্ষার্থী বের হবে না। দেশে সার্টিফিকেটধারী লোকের সংখ্যা বাড়বে, কিন্তু মানুষ বাড়বে না।
লেখক: কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এডিটর, নেক্সাস টেলিভিশন।