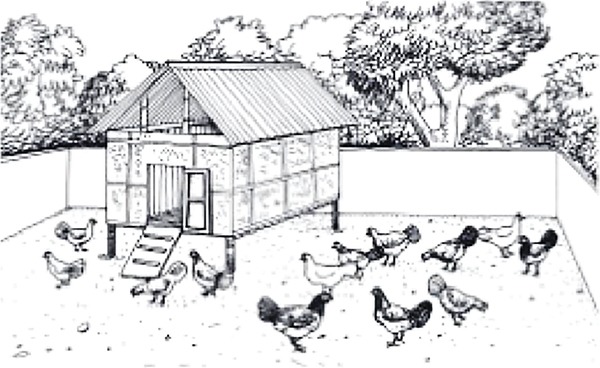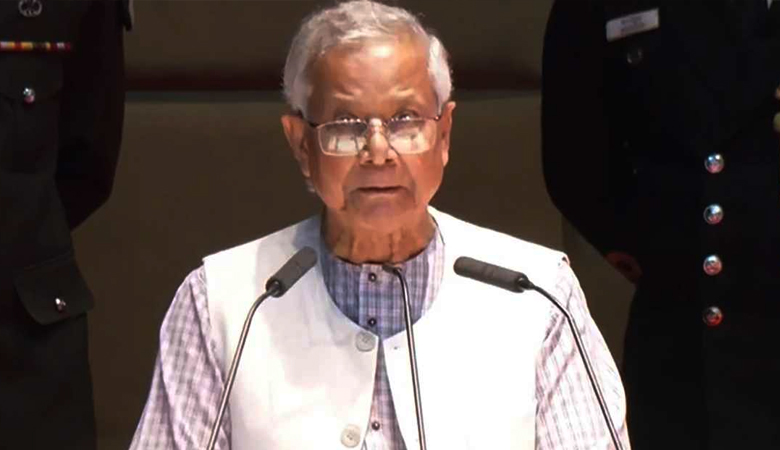- হাসান মামুন
রাজধানীর একটি শ্মশানে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও কলাম লেখক বিভুরঞ্জন সরকারের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে শনিবার সন্ধ্যায়। অনেকের মধ্যে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। পেশাগত কারণেই মূলত তার জীবনের একটি অধ্যায় খুব কাছ থেকে দেখা। অজস্র স্মৃতি ঘিরে আছে এ নিবন্ধ লেখার সময়। তবে এখানে কোনো স্মৃতিচারণ করব না।
এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, তিনি স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছেন। গণমাধ্যমে পাঠানো সর্বশেষ লেখায় যা বলে গেছেন, সেটাকে তার ‘সুইসাইড নোট’ বলেই গণ্য করা হচ্ছে। এতে ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সংকটে পর্যুদস্ত হওয়ার কথা অকুণ্ঠিতভাবে সামনে এনেছেন তিনি। গণমাধ্যমে দীর্ঘ নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে এর গভীর সংকটের দিকেও সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। এ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা এখানেও হতে পারে।
বিভুরঞ্জন সরকারের মতো বহু সাংবাদিক (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, রেডিও, অনলাইন মিলিয়ে) নানান সংকট মোকাবিলা করেই এ খাতে কর্মরত। গণমাধ্যম মালিকদেরও আরেক ধরনের সংকট মোকাবিলা করতে হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে। গণমাধ্যমের প্রধান অংশীজন পাঠক, দর্শক, শ্রোতাদের দিক থেকে আবার অভিযোগ রয়েছে এ দুই পক্ষের বিরুদ্ধে। তাদের আস্থার জায়গায় ধস নেমেছে বলেও মনে হয়। এ ক্ষেত্রে বিগত সরকারের দীর্ঘ শাসনামলের অভিজ্ঞতাটি বিশেষভাবে আলোচিত। গণমাধ্যম মালিক তো বটেই; কর্মরত সাংবাদিকদের একাংশও এখন জনতার কাঠগড়ায়।
অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে যেসব ক্ষেত্রে সংস্কার আনতে কমিশন গঠিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে গণমাধ্যম। কমিশনটির সুপারিশ এখন সরকারের হাতে। দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য কিছু সুপারিশ নিয়ে সরকার কাজ করছে বলেও জানা যায়। এর মধ্যে রয়েছে সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত। সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা নিরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন হার যৌক্তিকীকরণের বিষয়ও রয়েছে বলে জানা যায়।
ইলেকট্রনিকসহ অন্যান্য মিডিয়ার দাবিগুলোও গভীরভাবে বিবেচ্য। বস্তুত এ খাতে ঘটে চলেছে দ্রুত রূপান্তর। প্রিন্ট মিডিয়ার আগেকার আধিপত্য আর নেই। হালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও হয়ে উঠেছে প্রভাবশালী। নতুন নতুন মাধ্যমের দ্রুত বিকাশ প্রচলিত সংবাদমাধ্যমকে নতুন চ্যালেঞ্জে ফেলছে। গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রিন্ট মিডিয়া এখনও এক নম্বরে থাকলেও তার আয়ে ভাগ বসাচ্ছে নতুন মাধ্যমগুলো। বিজ্ঞাপনের বাজার সংকুচিত হয়ে এলে তো সংকটের চিত্রও বদলে যায়।
গণঅভ্যুত্থানের পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শ্লথ হয়ে পড়ায় বিজ্ঞাপনের বাজার সংকুচিত হয়ে পড়েছে বৈকি। এর প্রভাব পড়েছে সব ধরনের গণমাধ্যমে। নতুন নিয়োগ কম। সংবাদকর্মী ছাঁটাই বরং বেড়েছে। কর্মরতদেরও অনেকে ঠিকমতো বেতন পাচ্ছেন না। এ অবস্থায় গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন স্বভাবতই জোর দিয়েছে এর ‘বিজনেস মডেলে’। গণমাধ্যমকে নতুন ধারায় পরিচালনার জন্য একগুচ্ছ সুপারিশ দিয়েছেন তারা, যেগুলো নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হচ্ছে কম।
এ বিষয়ে বিভুরঞ্জন সরকার কী ভাবতেন, জানি না। হালে তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, এমনকি ফোনালাপও কম হতো। এর জন্য গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিও দায়ী। ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের মধ্যেও আমাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য কম ছিল না। বেশি দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ হলে বাদানুবাদ থেকে সম্পর্কের অবনতির শংকা ছিল। তবে তার লেখাপত্র পড়েছি। বুঝতে চেষ্টা করেছি বহুদর্শী এ সাংবাদিকের অবস্থান। আরো অনেকের মতো তার মনোভাবেও বড় কোনো পরিবর্তন দেখতে পাইনি। তবে আমার ধারণা, গণমাধ্যম সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই একমত হতাম– তিনি বেঁচে থাকলে।
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রিন্ট মিডিয়াতেই কাজ করেছেন বিভুরঞ্জন সরকার। তার সঙ্গে একটি দৈনিক এবং অন্য একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমি কাজ করেছি। দেখেছি তার কর্মনিষ্ঠা। গণমাধ্যমের চলতে থাকা সমস্যাগুলো নিয়ে সময়ে সময়ে কম আলোচনাও আমরা করিনি। বহুল আলোচিত তার শেষ লেখাটিতে এর সামান্যই এসেছে। স্বেচ্ছামৃত্যু বরণের আগ মুহূর্তে তৈরি লেখায় সুচিন্তিতভাবে তিনি মতামত প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেও মনে হয় না।
গত বছরের ১৫ মে ‘আজকের পত্রিকা’য় (তার সর্বশেষ কর্মস্থল) মুদ্রিত নিবন্ধে বিভুরঞ্জন সরকার কী লিখেছিলেন, সেটি বরং গুরুত্বপূর্ণ। পুরো নিবন্ধটি অনলাইনে মিলবে। তার মনোভাব বোঝাতে এখানে একটি প্যারাই কেবল উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন, “অনেকে হয়তো অখুশি হবেন, তারপরও আমি এটা মনে করি যে, বাংলাদেশে মত প্রকাশ ও গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতার পরিবেশ এখন নেই। খুব শিগগির সেটা হবে বলেও আমি মনে করি না। গণমাধ্যমের মালিকানা এবং পরিচালনা যাদের হাতে, তারা কেউ নিজেদের স্বার্থের পরিমণ্ডলের বাইরে হাঁটতে চান না, চাইবেন না।”
গণঅভ্যুত্থানের পর এ পরিস্থিতি বদলেছে বলা যাবে না। তবে এটা নিয়ে খোদ সরকার কাজ করছে, বক্তব্য দিচ্ছে। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সাংবাদিক সুরক্ষা অধ্যাদেশ জারি হবে বলেই আশা। রাজনৈতিক দলগুলোকে এসব বিষয়ে আপত্তি জানাতে দেখা যাচ্ছে না, এটাও গুরুত্ববহ। গণমাধ্যমের মালিকানায় নতুনত্ব আনার বিষয়েও সুস্পষ্ট সুপারিশ রয়েছে সংস্কার কমিশনের। এক পরিবার বা মালিকের হাতে একাধিক গণমাধ্যম নয়, এমন সুপারিশের পাশাপাশি সংবাদকর্মীদের ন্যূনতম বেতন সমপর্যায়ের সরকারি চাকরির সমান করার প্রস্তাবও রয়েছে। প্রচলিত ওয়েজ বোর্ড প্রথা নিয়ে কিছু না বলায় অবশ্য গুরুতর আপত্তি রয়েছে সংবাদপত্রে কর্মরতদের। এটাও ঠিক, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের কর্মীসহ সবার কথা ভেবেই সুপারিশ দিয়েছে।
বিভুরঞ্জন সরকার সম্মানজনক বেতন পাচ্ছেন না বলে গভীর আক্ষেপ করে গেছেন তার সর্বশেষ লেখায়। উপরোল্লিখিত নিবন্ধে একই বিষয়ে তিনি জোর দিয়েছিলেন সব সংবাদকর্মীর পক্ষ থেকে। চাকরির অনিশ্চয়তা এবং কাজ হারানোর সময় খালি হাতে ঘরে ফেরার অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করেছেন। গণমাধ্যমে বেতন বৈষম্যও নির্মম বাস্তবতা। বেতন বকেয়া থাকার ঘটনাও নিয়মিত, যদিও সংবাদকর্মীরা অন্যান্য খাতের কর্মীদের বকেয়া বেতন দাবিতে আন্দোলনের খবর পরিবেশন করে যাচ্ছেন গভীর মমতায়।
দৃঢ় আর্থিক ভিত্তিসম্পন্ন গণমাধ্যম এদেশে একেবারে নেই, তা অবশ্য নয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের অনেকে সামাজিকভাবে মর্যাদাসম্পন্ন জীবন কাটাচ্ছেন, এটাও বলতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত বিভুরঞ্জন সরকার তেমন প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ পাননি। তাহলে তার সবকিছু হয়তো অন্যরকম হতো। তবে সব সাংবাদিকেরই অধিকার রয়েছে স্বাভাবিক বেতন-ভাতা ও কর্মপরিবেশ লাভের। হামলা, হুমকি ও হয়রানিমুক্ত হয়ে দায়িত্ব পালনের অধিকারও তাদের রয়েছে। রাষ্ট্রকেই সেটা নিশ্চিত করতে হবে। গণমাধ্যমের কাজে কেউ অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হবে না, সেটা দেখাও জরুরি। এজন্য প্রচলিত প্রেস কাউন্সিলের বদলে একটি স্থায়ী গণমাধ্যম কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে, যা সব ধরনের গণমাধ্যমেই স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।
বিভুরঞ্জন সরকার নিশ্চয়ই জানতেন, এর আগেও ১৯৮৪ সালে একটি গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের মাধ্যমে খাতটিকে সুশৃঙ্খল করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। সেটা কেন ব্যর্থ হয়, সে আলোচনা তার বেদনাদায়ক জীবনাবসানের পর যারা বেঁচে আছি– তারা করতে পারি। ওই সময়ের পর, বিশেষত নব্বইয়ে গণতন্ত্রে উত্তরণের পর গণমাধ্যমে কিন্তু বিনিয়োগ অনেক বেড়েছে। প্রিন্ট মিডিয়ার পর ইলেকট্রনিক মিডিয়ারও প্রসার ঘটেছে দ্রুত। কিন্তু গণমাধ্যম কর্মীদের সার্বিক জীবনমান উন্নত হয়নি; তার নিরাপত্তাও বাড়েনি। সাংবাদিকতার মান কতটা উন্নত হয়েছে– এমনকি প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের পর, সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ।
মালিকপক্ষও গণমাধ্যমের ব্যয়ভার নিয়ে তাদের অসন্তোষের কথাটাই বেশি বলেন। সরকারের কাছে জোরালোভাবে এ ব্যবসার ব্যয় হ্রাসের দাবি জানান তারা। সাংবাদিকদের মধ্যে অবশ্য সংহতি খুব কম। তাদের ইউনিয়ন রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত। নব্বইয়ের পর দ্বিদলীয় রাজনৈতিক বিভাজনে তাদের বিভক্তি বাড়াতেও গণমাধ্যমে সংকট বেশি ঘনীভূত হয়েছে। এ পথ ধরেই বিগত সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে সাংবাদিকদের একাংশ হয়েছে ভীষণ বিতর্কিত। তাদের কেউ কেউ এখন কারাগারে। তবে দুর্নীতিমূলক যোগাযোগে লাভবান হয়েছেন কম সাংবাদিকই। কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত সিংহভাগ সাংবাদিক এখনও মানসম্মত বেতন থেকে বঞ্চিত। অনেকেকেই দ্বিতীয় উৎস থেকে আয় করে চলতে হচ্ছে।
বিভুরঞ্জন সরকার সরকারি প্লটসহ অন্যান্য সরকারপ্রদত্ত সহায়তা চেয়েও পাননি বলে খুবই আক্ষেপ করে গেছেন তার সর্বশেষ লেখায়। বিশেষ কোটায় নামমাত্র দামে পাঁচ কাঠার একটি প্লট তিনি পেতেই পারতেন। সেটি হস্তান্তর করে সংকট মোচনও হয়তো করতে পারতেন। কিন্তু এভাবে সংকট মোচনের পথ খোলা রাখা নিয়েই তো রয়েছে প্রশ্ন। কোনো ধরনের সরকারই গণমাধ্যমের বন্ধু নয়। ক্ষমতাবান বেসরকারি গোষ্ঠীও সারা বিশ্বেই চায় গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। এ অবস্থায় তাই সংবাদকর্মীদের দূরে রাখা প্রয়োজন সরকারি প্লটসহ সব ধরনের ‘উপহার’ প্রাপ্তি থেকে।
অল্প কিছু সাংবাদিকের জন্য এ ধরনের সুযোগ অব্যাহত রাখার বদলে সবার জন্য মানসম্মত বেতনের ব্যবস্থা, চাকরির নিশ্চয়তা, অবসরকালীন ভাতা বরং জরুরি। মফস্বলের সাংবাদিকরাও কম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের ঝুঁকি বরং বেশি। সেখানে জীবনযাত্রার ব্যয় কম বলে তাদের বেতন-ভাতা কিছুটা কম হতে পারে। সে ক্ষেত্রেও ব্যবধানটি এখনকার মতো প্রকট হতে পারে না। তাদেরকে বিশেষ করে বিজ্ঞাপন সংগ্রহে নিয়োজিত রাখার অপসংস্কৃতি থেকে মুক্তি দেওয়া জরুরি।
যেনতেনভাবে গণমাধ্যম পরিচালনার কোনো প্রয়োজন তো নেই। সিংহভাগ গণমাধ্যম যেনতেনভাবে পরিচালিত হচ্ছে বলেই কিন্তু বেশি সংকট দেখা দিচ্ছে। গণমাধ্যম মালিকদের জন্য ন্যায়সঙ্গত কর-শুল্ক ইত্যাদি নিশ্চিত করে এ ক্ষেত্রে বরং বলা দরকার, স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবসাটি পরিচালনা করুন।
সময় বদলেছে। গণমাধ্যমের ধরনও বদলাবে। পাঠক, দর্শক, শ্রোতার চাহিদাও কি বদলাচ্ছে না? সে অনুযায়ী বিজ্ঞাপনদাতাদের আগ্রহও পরিবর্তিত হচ্ছে। বিপুলসংখ্যক কর্মী নিয়ে পুরনো ধারায় গণমাধ্যম পরিচালনাও এখন বাস্তবতা নয়। আর সাংবাদিকদের হতে হবে শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত ও নিরন্তর মানোন্নয়নে বিশ্বাসী। বিভুরঞ্জন সরকারও এসব নিয়ে ভাবতেন। দক্ষ ও পরিশ্রমী সংবাদকর্মীদের বিশেষ পছন্দ করতেন তিনি।
তার বয়স ৭০ পেরিয়ে গিয়েছিল। এটা অবসর গ্রহণের বয়স বলে মনে করি। তবে এ বয়সেও তিনি ছিলেন কর্মনিষ্ঠ সাংবাদিক। তার লেখার আলাদা একটা ধরন ছিল। বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন একটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকে লিখে। তার জীবন অগৌরবের ছিল না। তা সত্ত্বেও যে ভয়ানক হতাশায় তিনি নিমজ্জিত হয়েছিলেন, তেমন পরিস্থিতি হয়তো এ পেশার আরো অনেকেই মোকাবিলা করছেন। আত্মহননের মতো পথ বেছে না নিয়ে তারা নিশ্চয় লড়বেন হাতে যেটুকু রয়েছে, তা দিয়েই।
গণমাধ্যমও যেন যেনতেনভাবে পরিচালিত হওয়ার সংস্কৃতি থেকে ক্রমে বেরিয়ে আসে। এ ক্ষেত্রে সরকার, মালিক ও সাংবাদিক-সব পক্ষকেই নবতর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে হবে।
লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট