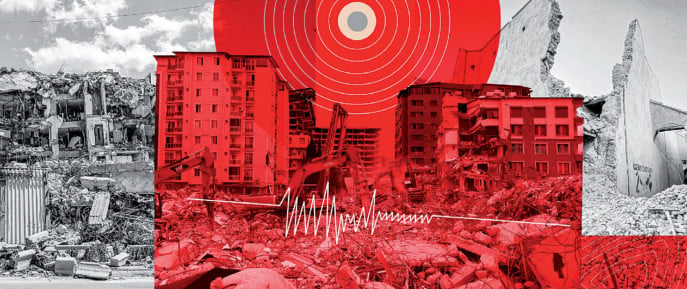সারা সাদবিন
বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে আজও এক গভীর ক্ষত। ইউনিসেফের ২০২৫ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীদের প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ মেয়ে, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে করেছে। শুধু গ্রাম নয়, শহরেও চিত্রটা প্রায় একই। ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ৪৪ শতাংশ মেয়ে বিবাহিত হয়ে যায়। এত প্রচারণা, এত আইন, এত পরিকল্পনা। তবু হার কমছে না। মনে হয়, বাল্যবিয়ে শুধু একটি সামাজিক সমস্যা নয়, এটি এক অদৃশ্য শৃঙ্খল! সেই শৃঙ্খলে আটকে আছে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা আর সামাজিক চাপে ভাঙা মেয়েদের ভবিষ্যৎ। প্রশ্ন জাগে, আমরা কি সত্যিই মেয়েদের মুক্তি দিতে পেরেছি, নাকি শুধু উপরে একটুখানি রঙ লাগিয়েছি?
২০২৫ সালের হিসাব বলে, বাংলাদেশের প্রায় ১৩ মিলিয়ন মেয়ে ১৫ বছর বয়সের আগেই বিয়ে করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ জানিয়েছে, কোভিড-১৯ এর পর এই হার বেড়েছে আরও ৪৪ শতাংশ। শহর আর গ্রামের পার্থক্য খুব সামান্য। গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিটি প্রান্তে এক ধরনের অসহায়তা কাজ করে। কোথাও সামাজিক চোখ, কোথাও অভাব, কোথাও ভয়। এত উদ্যোগ, এত প্রচেষ্টা, এত পোস্টার, তবু সফলতা যেন হাতের মুঠোয় আসে না। সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সব মিলিয়ে মেয়েরা এখনো বন্দি এক নীরব চক্রে।
২০১৭ সালে শিশু বিয়ে নিরোধ আইন পাশ হয়েছিল। কিন্তু সেই আইনের বিশেষ পরিস্থিতি ধারা আজ আইনের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। অনেক পরিবার রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রভাবের আড়ালে সেই ফাঁকটা ব্যবহার করে নেয়। আর আমাদের মানসিকতা? এখনো মেয়েকে বোঝা মনে হয়, তার স্বপ্ন বা শিক্ষার কোনো দাম নেই। ভুল ধর্মীয় ব্যাখ্যা, কিছু নীরব ধর্মীয় নেতার সম্মতি, এই সবই মিলেমিশে সমাজের ভিতর এক অন্ধকার বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখছে। তাই প্রশ্নটা এখন আর পরিসংখ্যানে নয়, মনের ভেতরে।
এত প্রচারণা, এত কথা, এত সভা-সেমিনারের পরও কেন মেয়েরা মুক্তি পায় না? কারণটা অদৃশ্য কিন্তু গভীর। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা, পরিবারের পক্ষপাত, দুর্বল আইন, স্থানীয় দুর্নীতি, আর চারপাশের সামাজিক চাপ- সব মিলে বাল্যবিয়ের শৃঙ্খলকে আরো শক্ত করে ফেলে। যারা এসব উদ্যোগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের জীবনে পরিবর্তন আসে না। তাই এই লেখাটা কোনো প্রতিবেদন নয়, এক প্রশ্ন। আমরা সত্যিই পরিবর্তন চাই, নাকি কেবল বদলে যাওয়ার অভিনয় শিখেছি?
বাল্যবিয়ের মূল কারণ: বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে এখনো এক গভীর উদ্বেগের বিষয়। যত প্রচারণাই চালানো হোক, যত আইনই করা হোক, সমস্যা যেন কমে না। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও ঘন হয়। এই বিয়েগুলো চোখে দেখা যায়, কিন্তু এর শিকড় থাকে মাটির অনেক নিচে।
কারণগুলো সহজ নয়। সমাজের সব রকমের চাপ মিলেই মেয়েদের শৈশব কেড়ে নেয়। কেউ ভাবে মেয়ে বড় হলে দায় বাড়ে। কেউ ভাবে ধর্মের কাজ করছে। কেউ আবার ভাবে সমাজ কী বলবে। এই ভাবনাগুলো এমনভাবে গেঁথে গেছে আমাদের সমাজে যে, মেয়েদের বিয়ে এখন এক ধরনের সহজ সমাধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এই লেখায় আমরা সেই কারণগুলোর ভেতর ঢুকব। চেষ্টা করব বুঝতে, কেন এখনো এত মেয়ের বিয়ের সময় হয় না, অথচ তাদের জীবনের সময় ফুরিয়ে যায়।
দারিদ্র্যতা- একটি অবিরাম চক্র: বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং উপকূলীয় এলাকায়, যেখানে কৃষির উপর নির্ভরশীল জীবন আর কম আয়ের বাস্তবতা ঘিরে থাকে, সেখানে মেয়েশিশুদের অনেক সময় অর্থনৈতিক বোঝা হিসেবে দেখা হয়। যখন মেয়ে একটু বড় হয়, শারীরিকভাবে পরিণত হয়, তখন অনেক পরিবার ভাবে বিয়ে দিলে দায় কিছুটা কমবে। কেউ ভাবে, তাতে যৌতুকের পরিমাণও কমে যাবে, সংসারের চাপটাও হালকা হবে।
বিশ্বব্যাংক ও ইউনিসেফের গবেষণা বলছে, দারিদ্র্যতাই বাল্যবিয়ের অন্যতম বড় কারণ। ২০১৭ সালের ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, দারিদ্র্যতাগ্রস্ত এলাকায়- যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুযোগের অভাব; সেখানে বাল্যবিয়েকে অনেক সময় সহজ সমাধান হিসেবে দেখা হয়। গরিব পরিবারগুলো ভাবে, মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিলে সংসারের ভার কিছুটা কমে যাবে। কিন্তু তারা বোঝে না, এই সিদ্ধান্ত ওই মেয়ের ভবিষ্যতের দরজা বন্ধ করে দেয়। শিক্ষা না থাকলে ওই মেয়ের জীবনের গতি থেমে যায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসে। আর সে দারিদ্র্যের ঘূর্ণি থেকে বের হতে পারে না।
বিশ্বব্যাংকের ২০১৭ সালের হিসাব বলছে, দারিদ্র্যতার কারণেই গ্রামীণ এলাকায় প্রায় অর্ধেক মেয়ের বিয়ে হয় স্কুল শেষ হওয়ার আগেই। ফলে তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে না, আর জীবনের মান নিম্নতর হয়ে পড়ে।
ধর্মীয় ভুল ব্যাখ্যা- বিশ্বাসের অপব্যবহার: বাংলাদেশে অনেক সময় ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা বাল্যবিয়ের অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে। কিছু ধর্মীয় নেতা বা গোষ্ঠী এখনো মনে করে মেয়েকে ছোটবেলায় বিয়ে দেওয়া একটি ধর্মীয় কর্তব্য। এমনকি অনেকে বলে, মেয়েকে বিয়ে দিলে পুণ্য হয়। এই ধরনের ধারণা সমাজে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, মানুষ সেটাকে সত্য ভেবে নেয়। অথচ ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষায় বিয়ের আগে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতির কথা স্পষ্টভাবে বলা আছে। কিন্তু কিছু মানুষ সেই শিক্ষা উপেক্ষা করে, নিজেদের মতো করে ধর্মের ব্যাখ্যা তৈরি করে নেয়।
ইসলামে মেয়ে ও ছেলের জন্য বিয়ের আগে শারীরিক, মানসিক এবং আইনগত প্রস্তুতি অপরিহার্য। তবু কিছু ধর্মীয় নেতা মনে করেন, মেয়েকে দ্রুত বিয়ে দিলেই দায়িত্ব শেষ। এতে তারা বুঝতে পারেন না- এমন সিদ্ধান্ত মেয়ের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা বিপজ্জনক। এই ভুল ব্যাখ্যা শুধু ধর্মীয় শিক্ষা বিকৃত করে না, নারীদের অধিকার ও সমাজে তাদের অবস্থানকেও ক্ষুণ্ন করে।
সামাজিক চাপ ও সংস্কৃতি- পারিবারিক সম্মান রক্ষায় বাল্যবিয়ে: বাংলাদেশের অনেক এলাকায়, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে, সামাজিক চাপ মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। আমাদের সমাজে এখনো প্রচলিত ধারণা, মেয়েকে যত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া হবে, ততই পরিবারের সম্মান বাড়বে। এই ভাবনা মেয়েদের ওপর চাপ তৈরি করে। অনেক পরিবার মনে করে, যদি তারা মেয়ের বিয়ে না দেয়, তাহলে সমাজে পরিবারকে সম্মানহীন মনে করা হবে।
মিডিয়া, প্রথা এবং পারিপার্শ্বিক সামাজিক মানসিকতা মিলে মেয়ের বিয়েকে এক ধরনের সামাজিক দায়িত্বে পরিণত করেছে। অনেক অভিভাবক তাই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেন শুধু নিজেদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য। ইউনিসেফের ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ৪৩ শতাংশ মেয়ে পরিবার ও সমাজের চাপে বাল্যবিয়ের সম্মতি দিতে বাধ্য হয়। এই চাপ মেয়ের শৈশব এবং ভবিষ্যত উভয়কেই প্রভাবিত করে।
অনেক পরিবার বয়সের তুলনায় মেয়ের ‘অবস্থা’ বা সমাজের প্রত্যাশা পূরণের জন্য দ্রুত বিয়ে দেয়। এতে মেয়ের নিজের স্বপ্ন, পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্তের অধিকার কেবল মুছে যায় না বরং সে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় সামাজিক চাপের মুখে।
বাল্যবিয়ের প্রভাব: বাল্যবিয়ের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদী এবং বহুমুখী। এর প্রভাব কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমাজের সার্বিক কাঠামো এবং দেশের অর্থনীতিতে একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং সামাজিক কাঠামোয় এর নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে অনুভূত হয়।
স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব: বাল্যবিয়ের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি ৩ বহুমুখী। এটি শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, পুরো সমাজের কাঠামো এবং দেশের অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক কাঠামোয় এর নেতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।
স্বাস্থ্যের দিক থেকে বাল্যবিয়ে সবচেয়ে ভয়ানক। এটি মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু এবং অবস্টেট্রিক ফিস্টুলা অর্থাৎ প্রসবজনিত যোনি বা মূত্রনালীর সমস্যা; যা প্রসবকালীন জটিলতার কারণে হয় এর মতো সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সি মেয়ে শিশুর প্রসবকালীন মৃত্যু অন্য বয়সিদের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি। কারণ তাদের শরীর জন্মদানের জন্য প্রস্তুত নয়।
১৫ থেকে ১৯ বছরের মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রসবকালীন মৃত্যু দুইগুণ বেশি। এই মৃত্যু শুধু মেয়ের জন্য নয়, পুরো পরিবারে সামাজিক এবং আর্থিক ক্ষতি সৃষ্টি করে।এবং অল্প বয়সে গর্ভবতী হওয়া এবং সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে মেয়েরা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে তাদের সুস্থ্যতা এবং জীবনের মান বিপদের মধ্যে পড়ে।
শিক্ষায় ক্ষতি এবং ভবিষ্যতের সুযোগের অভাব: শিক্ষা বাল্যবিয়ের কারণে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাল্যবিয়ের পর মেয়েদের শিক্ষাজীবন কার্যত থেমে যায়। ২০১৭ সালের অ্যান্সারি গবেষণায় দেখা গেছে, বাল্যবিয়ের কারণে প্রায় ৬৫ শতাংশ মেয়ে তাদের শিক্ষা শেষ করতে পারে না। বিশ্বব্যাংক এবং ইউনিসেফের পরিসংখ্যানও দেখায়, বাল্যবিয়ে মেয়েদের শিক্ষা ও জীবনযাত্রাকে বিপন্ন করে। এর ফলে তারা পরবর্তী জীবনে দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরমূলক অবস্থার মুখোমুখি হয়।
একদিকে তারা সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়, অন্যদিকে পেশাগত জীবনও সীমিত হয়ে যায়। যদি ভবিষ্যতে তারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়, তবে তার পথ অনেকটাই বন্ধ হয়ে যায়।
সামাজিক কাঠামোয় ক্ষতি: বাল্যবিয়ে কেবল ব্যক্তিগত জীবনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, এটি পুরো সমাজের কাঠামোকেও প্রভাবিত করে। সমাজে যেখানে সমতা এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তি গড়ে ওঠার চেষ্টা চলছে, সেখানে বাল্যবিয়ে সেই পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েদের অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার ফলে তাদের জন্য সুযোগের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এটি শুধু সামাজিক অবমাননা সৃষ্টি করে না, বরং মেয়েদের সামাজিক অবস্থান এবং নিজের জীবন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতাকেও বাধাগ্রস্ত করে।
বিশ্বব্যাংকের ২০২০ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ৫৫ শতাংশ বাল্যবধূ জীবনে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। এই পরিস্থিতি তাদের জীবনযাত্রা, আত্মবিশ্বাস এবং সমাজে ভূমিকা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ফেলে।
আইনি পদক্ষেপ এবং সরকারি উদ্যোগ- চ্যালেঞ্জ ও অবস্থা: বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে রোধে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বহু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে পাস হওয়া শিশু বিবাহ নিরোধ আইন ছিল সেই প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে কাউকে বিয়ে দেওয়া বেআইনি। তবু আইন বাস্তবায়ন করা অনেক জায়গায় এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আইনি দুর্বলতা ও স্থানীয় দুর্নীতি; আইনের দুর্বলতা এবং স্থানীয় দুর্নীতি বাল্যবিয়ে রোধে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ২০১৭ সালে শিশু বিবাহ নিরোধ আইন পাশ হলেও, ১৮ বছরের নিচে কাউকে বিয়ে করাকে বেআইনি করা হলেও, অনেক এলাকায় সেই আইন কার্যকর হয় না। কোথাও আইন শিথিলভাবে প্রয়োগ হয়, কোথাও ফাঁকফোকর ব্যবহার করে বাল্যবিয়ে বৈধ করা হয়।
স্থানীয় দুর্নীতি এবং আইনের অপ্রকাশিত শিথিলতা ধনী ও প্রভাবশালী পরিবারগুলোর জন্য সুবিধাজনক হয়ে ওঠে। কিছু এলাকায় জনপ্রতিনিধি বা স্থানীয় কর্মকর্তা নিজেদের সামাজিক সম্পর্ক বা চাপের কারণে বাল্যবিয়ে অনুমোদন দিয়ে দেন। এতে সাধারণ মানুষের আইনের প্রতি আস্থা কমে যায় এবং বাল্যবিয়ের প্রবণতা আরো বাড়ে।
সরকারি উদ্যোগের ত্রুটি: সরকারি উদ্যোগের মধ্যে একাধিক সচেতনতা অভিযান, স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য কর্মসূচি, এবং বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে বিভিন্ন আইনগত প্রচেষ্টা রয়েছে। তবে বাস্তবতায় এই উদ্যোগগুলো যথেষ্ট কার্যকর হয়নি। বিশেষত গ্রামীণ এলাকাগুলোতে এই প্রচারণার প্রভাব সেভাবে পড়ছে না, যেখানে বাল্যবিয়ে এখনও সামাজিক রীতির অংশ হিসেবে ধরে নেয়া হয়।
২০২০ সালে ইউনিসেফের এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে সরকারের নানা পদক্ষেপ থাকার পরও ৫০ শতাংশ বাল্যবিয়ের ঘটনা আইনগতভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। এটি দেখাচ্ছে যে, আইনি কাঠামো থাকার পরও সামাজিক চাহিদা এবং আচরণের সাথে মোকাবিলা করা অনেক কঠিন।
শেষ কথা: বাল্যবিয়ে বাংলাদেশের একটি বহুমুখী ও গভীর সামাজিক সমস্যা, যার শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি কেবল আইনি বা নৈতিক সমস্যা নয়, বরং একটি অব্যক্ত সামাজিক চক্র, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। দারিদ্র্যতা, ধর্মীয় ভুল ব্যাখ্যা এবং সামাজিক চাপের সংমিশ্রণে এই চক্র এমন এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে পরিণত হয়েছে; যা সমাজের প্রতিটি স্তরে গভীর প্রভাব ফেলে।
একদিকে প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং আইনের শিথিল প্রয়োগ বাল্যবিয়েকে প্রশ্রয় দেয়, অন্যদিকে সমাজের অনেকেই এটিকে ঐতিহ্য বা ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে সমস্যা আরো জটিল হয়ে ওঠে।
বাল্যবিয়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্যগত প্রভাব ভয়াবহ। এটি শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, গোটা দেশের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের জন্যও বিপদজনক। প্রতিটি মেয়ে শিশু, যারা শৈশবেই এই প্রথার শিকার হয়, শুধু তার নিজের ভবিষ্যতই নয়, তার পুরো সমাজের সম্ভাবনাকেও বিপন্ন করে।
শিক্ষার সুযোগ হারানো, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব মেয়েদের জীবনকে সংকুচিত করে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তবে এই সমস্যা শুধুই একটি দেশ বা সমাজের বিষয় নয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ও বটে।
আইনি পদক্ষেপ এবং সচেতনতা প্রচারণা থাকলেও, সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ এবং সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন এখনো একটি দীর্ঘ পথ। যতদিন না সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতা এবং পরিবর্তন আসে, ততদিন এই অদৃশ্য শৃঙ্খল ভাঙা সম্ভব হবে না।
এটি এমন একটি সংকট- যেখানে শুধু আইন নয়; সমাজের অব্যক্ত ও দৃঢ় ধারণাগুলোর প্রতিও মোকাবিলা করতে হবে। তাই প্রশ্নটি থেকেই যায় যে, আমরা সত্যিই মেয়ে শিশুর মুক্তির জন্য যথেষ্ট করছি, নাকি শুধু সমস্যা আঁকড়ে ধরে চলছি?
লেখক: শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
(মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব)
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ