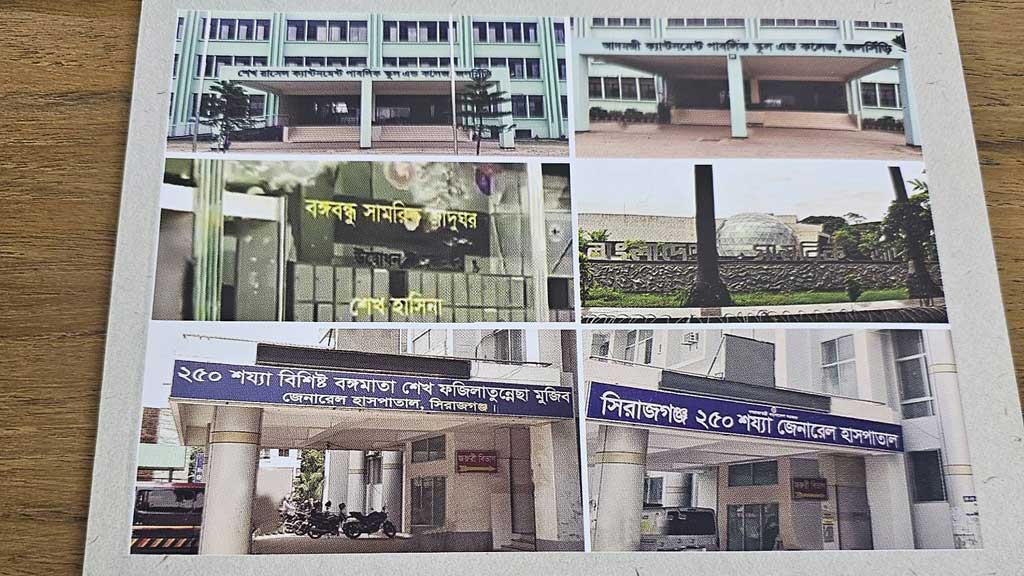-
জগদীশ চন্দ্র সানা
গতকাল ২১ নভেম্বর ২০২৫ সকাল দশটা ৩৮ মিনিটে আকস্মিক আঘাত হানা স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প বাংলাদেশের সব মানুষকে মনে করিয়ে দিয়ে গেলো – আমার হাত থেকে তোমরা কেউ নিরাপদ নও। তাই আগে থেকে সাবধান হয়ে যাও।
এই লেখায় বাংলাদেশে ভূমিকম্পের কারণ, ঝুঁকি, নগর বিকেন্দ্রীকরণ, জরুরি সেবা ও একটি ভূমিকম্প সহনশীল ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তুলে ধরা হলো। উদ্দেশ্য- বাংলাদেশ সরকারসহ প্রতিটি মানুষ যেন ভূমিকম্প বিষয়ে সচেতন হয় এবং নিরাপত্তার কথাটি সকল ক্ষেত্রে বেশি বেশি আলোচনায় আসে| এর ফলে হয়তো ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও একদিন ভূমিকম্প-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
নগর বিকেন্দ্রীকরণ, দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ,
বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং জনসচেতনতা—এই চারটি
স্তম্ভ বাংলাদেশের ভূমিকম্প প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করবে।
একটি বড় ভূমিকম্প যে কোনো সময় হতে পারে—
এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তবে একটি শক্তিশালী,
পরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে
ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব। এখনই সময়
এই প্রস্তুতি আরো শক্তিশালী করার।
বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে একটি হলেও জনসচেতনতা, নগর পরিকল্পনা, অবকাঠামোগত সক্ষমতা এবং জরুরি ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুতি এখনো যথেষ্ট নয়। ভূমিকম্প একটি নীরব, অপ্রত্যাশিত ও তীব্র ক্ষতিকর দুর্যোগ; তাই এর প্রভাব কমাতে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। বিশেষত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট—এই তিনটি শহর উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। পাশাপাশি, নগরের অতি-কেন্দ্রীকরণ, অপরিকল্পিত ভবন নির্মাণ ও দুর্বল জরুরি সেবা দেশের ভূমিকম্প ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে।
ভূমিকম্প কীভাবে ঘটে?
ভূমিকম্প হলো ভূ-পৃষ্ঠের টেকটোনিক প্লেটের বিচ্যুতি, সংঘর্ষ বা সরে যাওয়ার ফলে উৎপন্ন শক্তির আকস্মিক মুক্তি। ভূ-পৃষ্ঠকে ৭টি প্রধান ও কয়েকটি ছোট টেকটোনিক প্লেট ধারণ করে। এসব প্লেটের সীমানায় চাপ সৃষ্টি হলে তা ফাটল বা ফল্টলাইনের মাধ্যমে মুক্ত হয়, আর তখনই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
বাংলাদেশ কেন ঝুঁকিতে?
বাংলাদেশ তিনটি প্রধান টেকটোনিক প্লেট—ইউরেশিয়ান প্লেট, ইন্দো-অস্ট্রেলিয়ান প্লেট এবং বার্মা প্লেট—এর সংযোগস্থলে অবস্থান করছে। এ কারণে দেশটি বহু সক্রিয় ফল্টলাইনের মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে:
* ডাউকি ফল্ট (সিলেটের কাছে)
* চট্টগ্রাম-টেকনাফ ফল্ট
* মধুপুর ফল্ট
* অ্যাসাম স্লাস্ট জোন
এসব অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে শক্তি জমে আছে, যা একটি বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা বাড়ায়। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, বাংলাদেশে ৮ মাত্রার বেশি ভূমিকম্প ঘটার ঝুঁকি রয়েছে, যা শহরাঞ্চলে ভয়াবহ ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।
বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলোর ভূমিকম্প ঝুঁকি
ঢাকা
ঢাকায় জনসংখ্যার অতি-ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৫০,০০০ মানুষ), সংকীর্ণ রাস্তা, অপরিকল্পিত ভবন এবং দুর্বল ভূতাত্ত্বিক গঠন একে সম্ভাব্য “মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির শহর” হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গবেষণা অনুযায়ী, মাত্র ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকায় ৫০,০০০ থেকে ৮০,০০০ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দরনগর হওয়ায় অর্থনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। পাহাড় কেটে বসতি নির্মাণ, সক্রিয় ফল্টলাইন, এবং বন্দর-সংলগ্ন এলাকা একে উচ্চ ঝুঁকির তালিকায় রেখেছে।
সিলেট
সিলেট অঞ্চল ডাউকি ফল্টের খুব কাছে হওয়ায় ভূমিকম্প এখানে ঘন ঘন অনুভূত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ছোট-বড় ভূমিকম্পের বাড়তি হার বিস্তর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।
ভূমিকম্পের বড় ধরনের সম্ভাব্য ক্ষতির চিত্র
প্রাণহানি ও আহত বৃদ্ধি
অপরিকল্পিত ভবন ধসে পড়লে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটতে পারে। ঢাকা শহরের হাসপাতালের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় জরুরি মেডিকেল ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে।
অবকাঠামোগত দুর্বলতা
* সেতু, ফ্লাইওভার, ওভারপাস ক্ষতিগ্রস্ত হলে রাস্তাঘাট অচল হয়ে যাবে
* বিদ্যুৎ, গ্যাস লাইন ফেটে যেতে পারে
* পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যেতে পারে
অর্থনৈতিক বিপর্যয়
বাংলাদেশের প্রধান ব্যবসা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ঢাকাকেন্দ্রিক হওয়ায় একটি বড় ভূমিকম্প জাতীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করতে পারে। ব্যাংক, বীমা, গার্মেন্টস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবকিছু দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের মুখে পড়বে।
কেন নগর বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি?
ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবিলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগুলোর একটি হলো নগর বিকেন্দ্রীকরণ—অর্থাৎ দেশের অর্থনীতি, প্রশাসন, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের চাপ ঢাকা বা কয়েকটি শহরে কেন্দ্রীভূত না রেখে ছড়িয়ে দেওয়া।
বর্তমান কেন্দ্রীকরণের সমস্যা
* ঢাকা দেশের ৪০% অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বহন করে
* সরকারি বেশিরভাগ মন্ত্রণালয় ঢাকায়
* সব বড় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায়
* পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যধিক চাপযুক্ত
একটি ভূমিকম্পে এই পুরো সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশ কার্যত স্থবির হয়ে পড়বে।
বিকেন্দ্রীকরণের সুফল
* নতুন উন্নত শহর গড়ে তোলা সম্ভব
* প্রশাসনিক কাজ বিভাগীয় শহরে ছড়িয়ে যাবে
* ঢাকার জনসংখ্যা কমে যাবে, ঝুঁকি হ্রাস পাবে
* জরুরি সেবা এক শহরে সীমাবদ্ধ থাকবে না
* শিল্প কারখানার বিস্তার বাড়বে
সম্ভাব্য বিকল্প অঞ্চল
* কুমিল্লা
* বরিশাল
* খুলনা
* ময়মনসিংহ
* রাজশাহী
এসব শহরকে উন্নত নগর হিসেবে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা গেলে দেশে ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলা সহজ হবে।
ভূমিকম্প-সহনশীল ব্যবস্থাপনা: কী করা প্রয়োজন
ভূমিকম্প-সহনশীল ভবন নির্মাণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ
* বিল্ডিং কোড অনুযায়ী নির্মাণ
* ভূমিকম্প সহনশীল ডিজাইন
* পুরাতন দুর্বল ভবনের শক্তিশালীকরণ (retrofitting)
* অবৈধ ও অনিরাপদ ভবন ভেঙে ফেলা
শহর পরিকল্পনায় উন্নত ভূতাত্ত্বিক গবেষণা
প্রতিটি শহরের মাটির গঠন, ভূগর্ভস্থ জলস্তর, ফল্টলাইন অনেকটাই ভিন্ন। সেজন্য
* মাটির ধরন
* মাইক্রো-জোনিং ম্যাপ
* ঝুঁকি বিশ্লেষণ
কার্যকর করা জরুরি।
জরুরি সেবা সক্ষমতা বৃদ্ধি
* ফায়ার সার্ভিসের আধুনিক প্রযুক্তি
* উদ্ধারকারী দল প্রশিক্ষণ
* দ্রুত মোতায়েনযোগ্য টিম তৈরি
* হেলিকপ্টার ও ড্রোন ব্যবহারের সক্ষমতা বাড়ানো
জনগণের সচেতনতা
* স্কুল-কলেজে ভূমিকম্প মহড়া
* পরিবারভিত্তিক জরুরি পরিকল্পনা
* সেফ জোন চিহ্নিত করা
* মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি
স্মার্ট সিটি প্রস্তুতি
ভবিষ্যৎ স্মার্ট সিটি পরিকল্পনায়
* ওপেন স্পেস
* প্রশস্ত রাস্তা
* বহুমুখী সেবা কেন্দ্র
* ভূগর্ভস্থ তার ও গ্যাস লাইন সংযুক্ত করলে ভূমিকম্প সহনশীলতা বাড়বে।
বাংলাদেশের সরকারি পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন
বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে কয়েকটি বড় প্রকল্প গ্রহণ করেছে—যেমন বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা (DAP), বাংলাদেশ বিল্ডিং কোড (BNBC 2020), ও আরবান রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম। কিন্তু এর কার্যকারিতা বাড়াতে দরকার:
* কাঠামোগত দুর্বলতা শনাক্ত করে পুনর্বাসন কর্মসূচি
* স্থানীয় সরকারকে আরও ক্ষমতা প্রদান
* ভবন নির্মাণে দুর্নীতি বন্ধ
* বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ
* আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা
প্রযুক্তির ব্যবহার
ভূমিকম্প পূর্বাভাস ব্যবস্থা (যদিও পূর্ণ পূর্বাভাস সম্ভব নয়)
* সেন্সর নেটওয়ার্ক
* রিয়েল-টাইম মনিটরিং
ডিজিটাল ডাটা সংগ্রহ
* GIS
* স্মার্ট বিল্ডিং ডাটাবেজ
* জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা
ভবন স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তি
* Structural Health Monitoring (SHM)
* IoT সেন্সর
ব্যক্তি, পরিবার এবং কমিউনিটির করণীয়
নিজের ঘরকে ভূমিকম্প-সহনশীল করা
* ভারী জিনিস নিচে রাখা
* ফুলদানি/আলনা/আলমারি ভালোভাবে আটকানো
* জরুরি ব্যাগ প্রস্তুত রাখা
o পানি
o প্রাথমিক চিকিৎসা
o খাবার
o টর্চলাইট
o গুরুত্বপূর্ণ কাগজের কপি
ভূমিকম্পের সময় করণীয়
* মাথা ঢেকে টেবিলের নিচে আশ্রয় নেওয়া
* দরজা বা জানালার কাছ থেকে সরে যাওয়া
* লিফট ব্যবহার না করা
ভূমিকম্পের পরে করণীয়
* গ্যাস বা বিদ্যুৎ লাইন পরীক্ষা
* জরুরি নম্বরে যোগাযোগ
* ক্ষতিগ্রস্ত ভবনে প্রবেশ না করা
মূল বার্তা (Key Message)
বাংলাদেশের ভূমিকম্প ঝুঁকি বাস্তব ও ক্রমবর্ধমান। ঘনবসতিপূর্ণ ও অপরিকল্পিত নগরায়ন, দুর্বল ভবন নির্মাণ, এবং অতিরিক্ত চাপ ঢাকা ও অন্যান্য শহরকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই নগর বিকেন্দ্রীকরণ, দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং জনসচেতনতা—এই চারটি স্তম্ভ বাংলাদেশের ভূমিকম্প প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করবে। একটি বড় ভূমিকম্প যে কোনো সময় হতে পারে—এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তবে একটি শক্তিশালী, পরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব। এখনই সময় এই প্রস্তুতি আরো শক্তিশালী করার।
[তথ্যসহ প্রবন্ধটি প্রস্তুতে এআইয়ের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে]।
লেখক: উন্নয়ন বিষয়ক পরামর্শক, সাংবাদিক
এসি/সানা/আপ্র/২২/১১/২০২৫