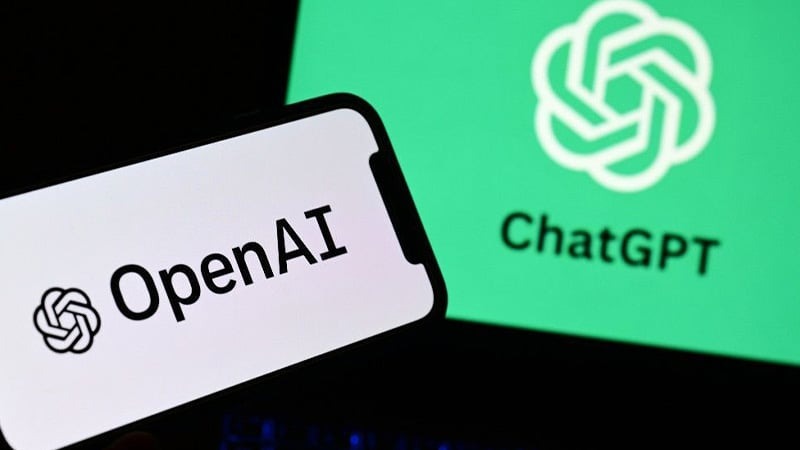আলতাফ রাসেল
জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথে নাটকীয় মোড় এনেছে। কোটা ব্যবস্থা সংস্কারে ছাত্রদের নেতৃত্বে শুরু হওয়া আন্দোলন দ্রুতই গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিয়েছিল; যা শেখ হাসিনার টানা চার মেয়াদের সরকারকে পতনের দিকে নিয়ে যায়। এই ক্ষমতার শূন্যতার মধ্যে মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।
এই সরকারের কাজ ছিল গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নির্বাচনী প্রস্তুতি সম্পন্ন করা। কিন্তু এক বছরেরও বেশি সময় পর ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার আশাভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে- শুধু বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যেও; যারা এক সময় তার উত্থানকে স্বাগত জানিয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন, পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলো শুধু ‘প্যাসিভ’ প্রক্রিয়ায় স্বাগত জানায়নি; বরং ‘অ্যাক্টিটিভ’ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদলের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।
প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মুহাম্মদ ইউনূসের নিয়োগ শুরুতে গণঅভ্যুত্থানের সমর্থক একটি অংশের কাছে আশার আলো হিসেবে এসেছিল। তারা মনে করতেন, তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও ভাবমূর্তি দেশে নতুন যুগের সূচনা করবে। কিন্তু এখন সেই গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের প্রতিশ্রুতি মøান হয়ে গেছে- নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিলম্ব, আওয়ামী লীগের মতো অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দলকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির বদলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে কার্যত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা এবং দেশজুড়ে ধর্মীয় ডানপন্থি গোষ্ঠীর প্রভাব বৃদ্ধিতে মদদ দেওয়ার কারণে।
দেশের আরেক অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি শুরুতে অন্তর্বর্তী সরকারকে কার্যত নিঃশর্ত সমর্থন করলেও মূলত জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিলম্বিত হওয়ার প্রশ্নে দ্রুত সেই নিঃশর্ত সমর্থন তুলে নেয়। বিএনপি নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ শাসনের অবসান চেয়েছে। কিন্তু তার বদলে অনির্দিষ্টকালের জন্য অন্তর্বর্তী শাসনকে সমর্থন করতে পারে না স্বাভাবিক কারণেই।
অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী দৃশ্যত ও কার্যত অন্তর্বর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আর গণঅভ্যুত্থানের ছাত্রনেতাদের একাংশের উদ্যোগে গঠিত রাজনৈতিক দল এনসিপি কিছু মান-অভিমান ও নাটকীয়তা বাদ দিলে এখনও ইউনূস সরকারের মূল নির্ভরতা হয়ে রয়েছে।
যাহোক, অনেক জল ঘোলা করার পর অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিএনপি এই সময়ের মধ্যে নির্বাচন দাবি করেছে এবং সময়সীমা না মানলে সহযোগিতা প্রত্যাহারের হুমকি দিয়ে আসছে। জামায়াতে ইসলামী যথারীতি নির্বাচন আয়োজনের চেয়ে ‘সংস্কার’ সম্পন্ন করার দিকে জোর দিচ্ছে। এনসিপিও যদিও সংস্কার, সনদ, গণভোট প্রভৃতি ইস্যুকে নির্বাচনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে চাইছে, তবুও অন্তর্বর্তী সরকারের মতো তাদের ‘নিয়োগকর্তা’ রাজনৈতিক দলটিরও জনসমর্থন আগের মতো নেই; বরং এনসিপি ও জামায়াতের প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের অতি নির্ভরতা মূলধারার রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে আরো দূরে সরিয়ে দিয়েছে।
প্রশ্ন হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকার প্রশ্নে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর এখনকার ভূমিকা কী? বাংলাদেশ বিষয়ে পশ্চিমা কূটনীতিকদের সাম্প্রতিক তৎপরতা ও বক্তব্য দেখে মনে হয়, তারাও আর আগের অবস্থানে নেই; অন্তত সরকারের দীর্ঘতর মেয়াদ প্রসঙ্গে। মুহাম্মদ ইউনূস যদি ক্ষমতায় থেকে গত দেড় বছরে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও বিস্তৃত জনভিত্তির রাজনৈতিক দল গঠন করে জনসমর্থন অর্জন করতে পারতেন তাহলে পশ্চিমা শক্তিগুলো অন্তত নিজেদের বাজারজাতকৃত গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সম্মান জানিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের দীর্ঘতর মেয়াদকে সমর্থন করে যেতে পারত।
বিশেষায়িত ব্যাংকার থেকে নির্বাচিত রাষ্ট্রনায়কে রূপান্তরে একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তির বিকল্প ছিল না; যা পশ্চিমা কৌশলগত স্বার্থকে গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করত। কিন্তু তার নেতৃত্বাধীন ‘নাগরিক শক্তি’ যেমন ২০০৭ সালে কলি থেকে ফুল না হয়েই ঝরে পড়েছিল; জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর তার সমর্থিত রাজনৈতিক উদ্যোগগুলো একই পরিণতি বরণ করতে পারে। নতুন নতুন প্রচেষ্টার সীমিত অগ্রগতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ভুগে অনেকে যেদিকে বৃষ্টি সেদিকে ছাতা ধরতে পারেন; কিন্তু পশ্চিমা শক্তিগুলোর কাছে আবহাওয়ার যথাযথ খবর ও পূর্বাভাস থাকে।
সত্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা সরকারগুলো এখনো অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু সেটা বাংলাদেশকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের কৌশলগত অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। সেই সমর্থনও ইতোমধ্যে গভীর নীতিগত দ্বন্দ্বের মুখে দাঁড়িয়ে। অবাধ, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবং মানবাধিকারের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নিজেদের ‘ব্র্যান্ড’ তুলে ধরা পশ্চিমা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো কীভাবে দীর্ঘমেয়াদে কোনো অনির্বাচিত সরকারকে সমর্থন করতে পারে- এ প্রশ্ন পশ্চিমা বিশ্বের অন্দরমহলে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।
যদিও পশ্চিমা শক্তিগুলো তাদের ঘোষিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চেয়ে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে অগ্রাধিকার দিয়ে আফগানিস্তান, তবুও ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের অনির্বাচিত সরকারকে সমর্থন দিয়েছে; একই ধরনের নীতিগত দ্বিচারিতা বাংলাদেশে কার্যকর হওয়া কঠিন ভৌগোলিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক অবয়বের কারণেই।
পশ্চিমা গণতন্ত্রের নিজস্ব মূল্যবোধ শুধু নয়; বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কাঠামোকে হুমকির মুখে ফেলে উগ্রবাদকে উস্কানি ও বৈধতা দেওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কেও পশ্চিমা বিশ্বের একরৈখিক অবস্থান কার্যত অসম্ভব। বাংলাদেশ যদি ফ্লোরিডা থেকে মাত্র ৯০ কিলোমিটার দূরের দেশ কিউবা হতো, তাহলে হয়তো হিসাবটা ভিন্ন হতো। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার বাস্তবতায় ভারত ও চীন এখানে নিষ্ক্রিয় থাকবে বা থাকতে পারবে- এমন ধারণা অবাস্তব। ফলে আঞ্চলিক কৌশলপটের প্রতিযোগিতামূলক পুনর্গঠন বাংলাদেশকে বিপজ্জনক অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে।
ওই ঝুঁকির পরবর্তী ধাপ বাংলাদেশের কয়টি ক্রিয়াশীল মূলধারার রাজনৈতিক দল ধারণ করতে পারবে, সে নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী ক্ষমতার শূন্যতা বা ভারসাম্যহীনতা চরমপন্থি গোষ্ঠীগুলো কাজে লাগিয়েছে। পুলিশ স্টেশন থেকে অস্ত্র লুণ্ঠিত হওয়ার আইনশৃঙ্খলাজনিত ঝুঁকি ছাড়াও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও গণহিংসা ইতোমধ্যে জনজীবনে প্রভাব ফেলছে। রোহিঙ্গা সংকট এ জটিলতাকে আরও গভীর করে তুলেছে।
বাংলাদেশের বর্তমান এই অস্থির প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো আজ এক গভীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। তারা কি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে শুধুই ভূরাজনৈতিক কৌশলের পথে হাঁটবে? আর বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী সাধারণ মানুষ কি সেই পথকে গ্রহণ করতে পারবে? প্রশ্নগুলো এখন আর শুধু নীতিগত নয়; বাস্তব রাজনৈতিক ভবিষ্যতের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। পথটি যদিও স্পষ্ট, তা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা অপরিহার্য।
পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অন্তর্বর্তী সরকারকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্ধারিত সময়সীমা মেনে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে এবং সব রাজনৈতিক দলকে অবাধ অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানাতে হবে। পশ্চিমা সমর্থনকে অবশ্যই নির্বাচন ও মানবাধিকারের বাস্তব অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। পশ্চিমা শক্তিকেও তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে হবে। কারণ মানবকল্যাণে কৌশলগত স্বার্থ কখনোই গণতান্ত্রিক নীতির চেয়ে অগ্রাধিকার পেতে পারে না।
এই সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা ভঙ্গুর হলেও বাস্তব। আশার কথা, পশ্চিমা নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এ নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো শুধু আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও জনভোগান্তির নিন্দা জানিয়েই থেমে থাকেনি; তারা এখন সতর্ক করছে, নির্বাচন বিলম্বিত হলে এবং জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা দেখা দিলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ গুরুতরভাবে বিপন্ন হতে পারে।
পশ্চিমা গণতন্ত্রগুলো নিজেদের স্বার্থে যেখানে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে নিজেদের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দাবি করে, আশা করা যায়, তারা বাংলাদেশে একটি অনির্বাচিত সরকারকে দীর্ঘ মেয়াদে সমর্থন করে যাবে না।
অনেকেই বলেন, ওই কৌশলগত স্বার্থ আসলে দীর্ঘমেয়াদি। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জনগণের ইচ্ছা ও স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়া কোনো কৌশলগত স্বার্থই এ অঞ্চলে কখনো দীর্ঘমেয়াদি হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। পশ্চিমা রাষ্ট্রবিজ্ঞানই আমাদের শিখিয়েছে, গণতন্ত্রের বিকল্প হলো আরও উন্নততর গণতন্ত্র।
লেখক: পিএইচডি গবেষক, অর্থনীতি বিভাগ, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য
(মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব)
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ