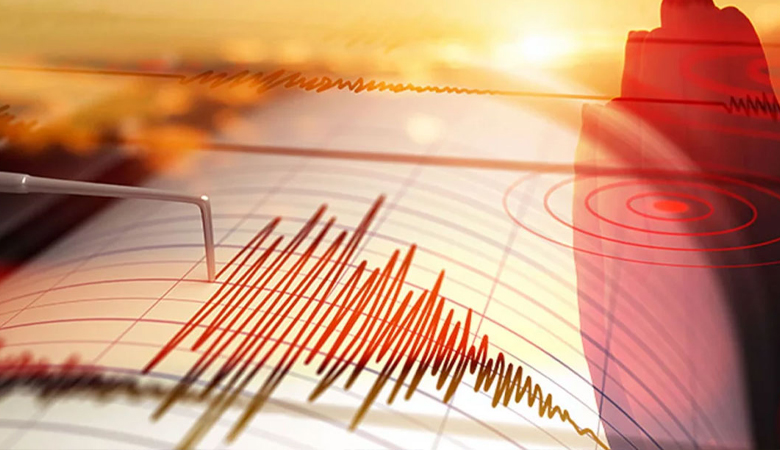আবু তাহের খান
সিইও ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপ থেকে জানা যায়, বই পড়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীর ১০২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে ৯৭তম। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিচে অবস্থানকারী অবশিষ্ট পাঁচ দেশ হচ্ছে ইউএই, সৌদি আরব, পাকিস্তান, ব্রুনেই ও আফগানিস্তান। আর পাঠাভ্যাস তালিকার শীর্ষস্থানীয় পাঁচ দেশ হচ্ছে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও ইতালি। এর বাইরে পাঠাভ্যাসের ক্ষেত্রে ওপরের দিকে থাকা এশীয় দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে তাইওয়ান (১২), সিঙ্গাপুর (১৪), হংকং (১৫), চীন (১৭), ইসরায়েল (২০), থাইল্যান্ড (২১) ও ইরান (২২)।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষ বই পড়তে চায় না কেন? এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে হলে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট জরিপভিত্তিক গবেষণা। কিন্তু সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলা একাডেমি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোনো জরিপ, সমীক্ষা বা গবেষণা পরিচালনার কথা ভেবেছে বলে জানা যায় না। অথচ এ দেশে বই পড়ার অভ্যাস সেই গোড়া থেকেই অত্যন্ত দুর্বল—লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকা একটি দেশের ক্ষেত্রে যা খুবই স্বাভাবিক।
সৈয়দ মুজতবা আলী এখন থেকে ৭৩ বছর আগে হতাশ হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, ‘প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক জোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া’ (বই কেনা, পঞ্চতন্ত্র, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। তো সৈয়দ মুজতবা আলী বই কেনার জন্য যত পীড়াপীড়িই করুন কিংবা নানা ব্যক্তি ও ঘটনার উদাহরণ টেনে ও পরামর্শ দিয়ে তিনি বই পড়ার পক্ষে যত ওকালতিই চালান, এ দেশের মানুষ ওই পথে হাঁটতে নারাজ। আর এ কারণেই উপহার হিসেবে দোকানি বইয়ের প্রস্তাব করলে একই প্রবন্ধের নাসিকা-কুঞ্চিত বাঙালি ধনীর দুলালীকে বলতে শোনা যায়, ‘সেও তো ওর একখানা রয়েছে’। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের জীবনে একটি বই-ই যথেষ্ট!
তো বই পড়া ও কেনার অভ্যাস যে পর্যায়ে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ মুজতবা আলী হতাশা প্রকাশ করেছিলেন, গত সাত দশকের ব্যবধানে সেই পরিস্থিতি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি করুণ ও হতাশাব্যঞ্জক। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার মান এতাই নিচে নেমেছে যে এ মানহীন শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের পক্ষে বই পড়তে আগ্রহী হওয়ার কোনোই কারণ নেই। তদুপরি বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখন ব্যস্ত ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কানাগলিতে।
বই পড়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১০২ দেশের মধ্যে ৯৭তম হলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ দেশের অবস্থান হচ্ছে অষ্টম। অথচ ফেসবুক, টুইটার, লিংকডইন ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের উদ্ভাবক যে যুক্তরাষ্ট্র এবং যে দেশের জনসংখ্যা বাংলাদেশের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি (৩৪ কোটি ৮০ লাখ), সেই দেশ। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের শীর্ষে নেই। অন্য আরও অনেক কিছুর মতোই তারা শীর্ষে রয়েছে বই পড়ার ক্ষেত্রে।
এ ঘটনা ও তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয়, চরিত্রগতভাবেই বাংলাদেশের মানুষ ব্যাপকভাবে অপাঠানুরাগী, জ্ঞানবিমুখ, অলস ও আসক্তিপ্রবণ, যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উপরোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো কিছতা হলেও ভূমিকা রাখতে পারত। কিন্তু সেটি তারা করেনি। তার চেয়ে বরং কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই এ ক্ষেত্রে কিছতা হলেও ভূমিকা রাখতে পেরেছে, যেমন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, বেঙ্গল বই, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ইত্যাদি।
বাংলাদেশের কতসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার আছে, তার হিসাব কি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আছে অথবা এ নিয়ে তারা কি খুব একটা উদ্বিগ্ন? অথচ সর্বজনস্বীকৃত অভিমত হচ্ছে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে না ওঠে, তাহলে জীবনজুড়ে তা আর কখনো গড়ে না ওঠার আশঙ্কাই সর্বাধিক। কিন্তু এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতিনির্ধারক ও সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের মধ্যে তেমন কোনো আগ্রহ ও তৎপরতা আছে বলে মনে হয় না।
অন্যদিকে পুরোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগারসমূহ একসময় ছিল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের উপস্থিতিসমৃদ্ধ পবিত্র পাঠস্থান। কিন্তু সে ঐতিহ্য এখন প্রায় নিঃশেষিত হওয়ার পথে। সেখানে শিক্ষার্থীদের আনাগোনাই যে শুধু কমে গেছে তা-ই নয়, শিক্ষকরাও এখন সেখানে যান খুবই কালেভদ্রে। আর গোটা দশেক ছাড়া বাকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগারের উপস্থিতি অনেকটাই নামসর্বস্ব। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার ও শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দেশের সনদধারী শিক্ষিতদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে না ওঠাই স্বাভাবিক।
সর্বজনীন একটি সত্য এই, যে দেশ বা সমাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানে ব্যর্থ হবে, সে দেশ শুধু পাঠাভ্যাসের ক্ষেত্রেই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা, উদ্ভাবন, এমনকি উন্নত রাষ্ট্র গঠনেও পিছিয়ে পড়তে বাধ্য।
বাংলাদেশ যে দীর্ঘ ৫৫ বছরেও জনগণের কাছে জবাবদিহিপূর্ণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারল না, তার জন্য এই পাঠবিমুখতা অনেকখানি দায়ী।
পাঠ ও অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জ্ঞানী, শিক্ষিত ও মেধাবী মানুষেরা যদি দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলধারায় থাকতেন, তাহলে এ সমাজের চেহারা আজ কোনোভাবেই এতা কদর্য ও রাক্ষুসে আকার ধারণ করতে পারত না। কিছুতেই এখানে প্রধান হয়ে উঠতে পারত না মব, পেশিশক্তি কিংবা কালোটাকার দৌরাত্ম্য। এর বিপরীতে পাঠাভ্যাসের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা শিক্ষিত বিবেকবান সব মানুষ এখানে এমন এক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে পারতেন- যাদের কাছে ন্যায়, সমতা ও মানবিক মূল্যবোধই হতো রাষ্ট্রপরিচালনার মূল ভিত্তি।
বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ নিরক্ষর বা স্বল্প অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হলেও তাদের মধ্যে নতুন কিছু জানার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ ও কৌতূহল রয়েছে। আধুনিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতি কৃষকের আগ্রহ ও তার ভেতরকার সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনার কারণেই সাড়ে পাঁচ দশকের ব্যবধানে বাংলাদেশের খাদ্যোৎপাদন প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ইতোমধ্যে তা ৫০০ লাখ টন ছাড়িয়ে গেছে।
মানহীন শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠা তথাকথিত সনদধারীদের মধ্যে ওই ধরনের আগ্রহ বা কৌতূহল একেবারেই নেই। সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনা তো নেই-ই। এর মূল কারণ হচ্ছে, সৃজনশীলতাবিমুখ মুখস্থনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা এই সনদধারীদের ভেতরকার সুপ্ত প্রতিভা ও সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনাময় চিন্তাভাবনাকে তিলে তিলে বিনষ্ট করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। ফলে মৌলিক চিন্তাভাবনা ও সৃষ্টিশীলতা লোপ পাওয়া ওই সনদধারীদের মধ্যে জ্ঞান আহরণ তথা বই পড়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহই জন্মাচ্ছে না; বরং তাদের পছন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে নিন্দা, পরচর্চা, রটনা, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদিতা ও অনুরূপ অন্যান্য স্থূল বিষয়; যার প্রতিফলন ওই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও দেখা গেছে।
বাংলাদেশের মানুষের পারিবারিক সংস্কৃতিও পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠার পক্ষে নয়। পরিবারের ভেতরে রাজনীতি, কেনাকাটার জন্য বিদেশ ভ্রমণ, বিল গেটস কিংবা ইলন মাস্কের মতো শীর্ষ ধনীদের সম্পদের গতিবিধি, ভিন্ন ভাষার টিভি ধারাবাহিক, নায়ক-নায়িকাদের জীবনযাপন ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়েই আলোচনা হয়। কিন্তু বই সেখানে একেবারেই জায়গা পায় না।
নাগরিক সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের কেউ কেউ মাঝে মধ্যে কনিষ্ঠদের বই পড়তে বলেন বটে। কিন্তু তিনি নিজে কতা পড়েন কিংবা বয়োকনিষ্ঠরা কী পড়বেন, কেন পড়বেন ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই জানান না। অর্থাৎ ‘আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে’ ধারণার চর্চা এ ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপস্থিত। ফলে বই পড়াসংক্রান্ত ওসব দুর্বল পরামর্শ বাস্তবে তেমন কোনো কাজেই আসে না। আর অধিকাংশ সময়জুড়ে মেধাহীন মানুষের দ্বারা পরিচালিত এ রাষ্ট্র বরাবরই গ্রামের মানুষকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মতো আলাদা করে রেখেছে; যেখানে বই পড়ায় যুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগই তাদের জন্য রাখা হয়নি।
মনে করা হচ্ছে, গ্রামীণ মানুষের কাজ শুধু উৎপাদন বা উৎপাদনে সাহায্য করা—বই পড়া তাদের জন্য যেন অনেকটাই নিষিদ্ধ কর্ম। সব মিলিয়ে বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে এই যে রাষ্ট্রই বস্তুত এখানে মানুষকে পাঠবিমুখ করে রেখেছে এবং তাতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হয়েছে জ্ঞান ও শিক্ষাবিদ্বেষী উগ্রপন্থি নিষ্ঠুর লুটেরাদের। তারা সাধারণের শিক্ষা ও পঠন-পাঠনকে তো ভয় পায়ই। তবে তার চেয়ে বেশি ভয় নারীর শিক্ষা ও পাঠাভ্যাসকে। কারণ তারা জানে, নারী শিক্ষিত ও পাঠাভ্যাসী হলে জ্ঞানী মা হিসেবে সন্তানকেও তারা শিক্ষিত এবং পাঠানুরাগী করে তুলবেন; যা রাষ্ট্র ও সমাজের সব কদর্যতা এবং পশ্চাৎমুখী চিন্তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবে।
বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস যদি বৃদ্ধি করতে হয়; তাহলে সর্বাগ্রে এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে- যে ব্যবস্থার আওতায় প্রতিটি মানুষের জন্য খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের মতো বিষয়গুলোর মূল নিয়ামক হবে নারীর অংশগ্রহণযুক্ত মানসম্মত শিক্ষা। বস্তুত এ শিক্ষাই একই সঙ্গে গড়ে তুলবে সমতাপূর্ণ একটি উন্নত রাষ্ট্র ও গভীর পাঠানুরাগী একটি জ্ঞানমনস্ক সমাজ।
লেখক: সাবেক পরিচালক, বিসিক
(মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব)
আজকের প্রত্যাশা/ কেএমএএ