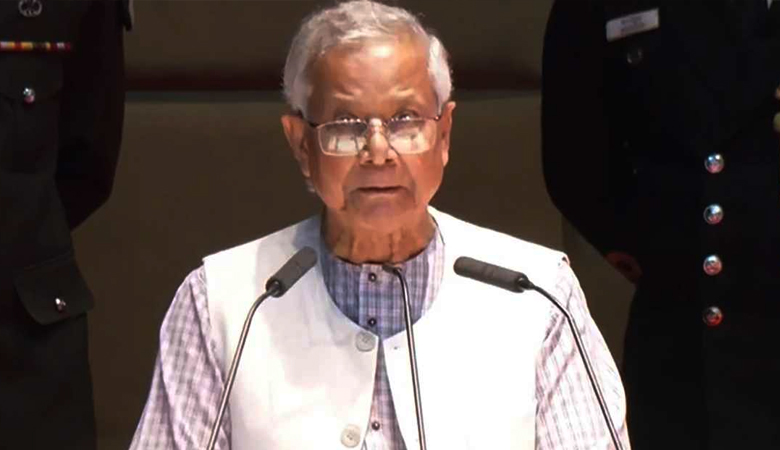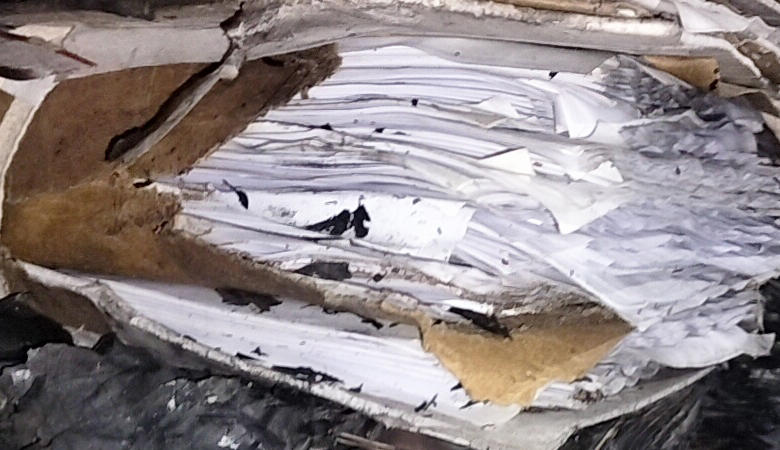স্বাস্থ্য প্রতিদিন : দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনবহুল দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রতি হাজারে স্থূল জন্মহার ১৯ দশমিক ৩ এবং মোট প্রজননহার বা টিএফআর হলো ২ দশমিক ১৫। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হারের পাশাপাশি একটি অংশ সন্তান জন্মদানে ইচ্ছুক হলেও কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে পারছেন না, প্রচলিত ভাষায় যাকে বন্ধ্যত্ব বলা হয়।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কোনো দম্পতি জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি গ্রহণ ছাড়া টানা এক বছর একসঙ্গে বসবাসের পর সন্তান ধারণ করতে সক্ষম না হলে তাকে বন্ধ্যত্ব বলা হয়।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৪৯ মিলিয়ন বা ৪ কোটি ৯০ লাখ দম্পতি বন্ধ্যত্বতে ভোগেন। বন্ধ্যত্বকে দুটি ধরনে ভাগ করা যায়Ñ প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি।
প্রাইমারি বন্ধ্যত্ব হলো যাদের কখনো গর্ভধারণ হয় না এবং সেকেন্ডারি বন্ধ্যত্ব বলতে যাদের আগে অন্তত একবার গর্ভধারণ হয়েছে। কিন্তু পরে আর গর্ভধারণ হচ্ছে নাÑ এ অবস্থাকে বোঝায়।
বন্ধ্যত্ব জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি বৈশ্বিক সমস্যা; যার সামাজিক ও অর্থনৈতিকÑ দুই ধরনের প্রভাবই রয়েছে। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর নীতি ও কাঠামোয় বন্ধ্যত্বের প্রতিকার বরবারই উপেক্ষিত। এসব দেশ যেহেতু অতিরিক্ত জনসংখ্যা সমস্যায় ভুগছে। তাই কিছু মানুষের সন্তান না হওয়াকে জাতীয়ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথচ প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত একটি মানবাধিকার। এ অধিকারের মূলে রয়েছে কোনো ব্যক্তি বা দম্পতি স্বাধীনভাবে কখন তাদের সন্তান জন্ম দেবেন, কতজন সন্তান জন্ম দেবেন, তা নির্ধারণ করতে পারবেন। একই সঙ্গে কোনো ব্যক্তি বা দম্পতির সুবিধা অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার অধিকার থাকবে।
জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠার মতো বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এর মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্য, বিশেষত বন্ধ্যত্ব, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সমস্যা শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
বন্ধ্যত্ব ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। এসডিজির লক্ষ্য ৩-এর অধীন বন্ধ্যত্বের চিকিৎসা সহজলভ্য করার মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যায় এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ বাড়ানো সম্ভব। একইভাবে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৫-এর অধীন নারীদের বিরুদ্ধে বন্ধ্যত্ব নিয়ে সামাজিক বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করার মাধ্যমে লক্ষ্য-১০ অসমতা হ্রাস অর্জনে ভূমিকা রাখা সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশে ঠিক কতসংখ্যক মানুষ বন্ধ্যত্বে ভুগছেন, সে সম্পর্কে তথ্য ও গবেষণা অপ্রতুল।
দেশের স্বাস্থ্যনীতিতে বন্ধ্যত্ব–সংক্রান্ত তথ্যপ্রাপ্তি, বন্ধ্যত্ব নির্ণয় ও বন্ধ্যত্বের চিকিৎসাসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। এ ছাড়া সরকারি হাসপাতালে বন্ধ্যত্ব চিকিৎসা পর্যাপ্ত নয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক বা হরমোনাল চিকিৎসায় বন্ধ্যত্ব ভালো হয়ে যায়।
এ ধরনের চিকিৎসা খুব ব্যয়সাধ্য নয় এবং ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকলে জেলা পর্যায়েই সম্ভব। বাকি ১০ শতাংশের ক্ষেত্রেই কেবল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও চিকিৎসা দরকার হতে পারে।
অ্যাডভান্সিং সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস (অ্যাডসার্চ) বাই আইসিডিডিআরবির রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি ও চাঁদপুরের মতলবের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত ২০ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ২ হাজার ৯৪৮ জন নারীকে নিয়ে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ দম্পতি প্রাইমারি বন্ধ্যত্বে ও ৯ শতাংশ দম্পতি সেকেন্ডারি বন্ধ্যত্বে ভুগছেন।
বন্ধ্যত্বে ভুগছেনÑ এমন ২৩৮ জন দম্পতির মধ্যে ২১৮ জন কোনো না কোনো স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে গিয়েছেন। এর মধ্যে ৯৩ শতাংশ দম্পতি চিকিৎসা ও পরামর্শের জন্য বেসরকারি সেবাকেন্দ্রে গিয়েছেন।
গবেষণাটিতে উঠে এসেছে, দেশের স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রগুলোয় বন্ধ্যত্বের ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারী চিকিৎসক ও টেকনিশিয়ানের অভাব রয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোয় এ সংক্রান্ত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি অপ্রতুল।
দেশে কেবল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বন্ধ্যত্বের জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসাব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে তুলনামূলক স্বল্প খরচে আইভিএফ, ওভারিয়ান প্লাটিলেট রিচ প্লাজমার (পিআরপি) চিকিৎসাব্যবস্থা রয়েছে।
গবেষণাটিতে দেখা গেছে, বন্ধ্যত্বের কারণে একটি দম্পতি পারিবারিক ও সামাজিক নিগ্রহের শিকার হন। এ ছাড়া তাদের দাম্পত্য সম্পর্কেও এর প্রভাব পড়ে। সন্তান ধারণ না হওয়ার পেছনে নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। তবে সন্তান না হওয়া বা ধারণ না করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় কেবল নারীদের দায়ী করতে দেখা যায়। এ কারণে একজন নারী সামাজিক ও মানসিকভাবে নিগ্রহের শিকার হন।
তিনি সংসার ও অন্যান্য কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। সামাজিক অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমে যেতে দ্বিধাবোধ করেন। এমনকি অন্য কোনো দম্পতির সন্তান হওয়ার কথা শুনলেও মনে কষ্ট পান। এভাবে এক সময় সামাজিকভাবেও তিনি নিজেকে গুটিয়ে নেন।
বিদ্যমান সমাজ কাঠামোয় বিয়ের তিন বা চার বছরের মধ্যে সন্তান না হলে, সমস্যা পুরুষের নাকি নারীর, তা নির্ণয় না করেই পুরুষকে আবার বিয়ের জন্য পরিবার থেকে চাপ দেওয়া হয় কিংবা অনেক ক্ষেত্রে বিয়েও করানো হয়।
অনেক সময় নারীদের ‘বাঞ্জা’ বা ‘বাঁজা’ বলে সম্বোধন করা হয়। কোনো শুভকাজে যাওয়ার আগে তাদের মুখ দেখা থেকে বিরত থাকা হয়। এমনকি অলক্ষ্মী বলে কোনো শুভকাজে তাদের নেওয়াও হয় না। পরিবারে তাদের কথার কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না।
গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের থেকে জানা যায়, অন্যান্য রোগের মতো বন্ধ্যত্বের সমস্যার জন্যও অনেক ক্ষেত্রে নারীরা স্থানীয় ফকির, কবিরাজ ও হুজুরের শরণাপন্ন হন।
সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, বিয়ে হলো পৃথিবীর সবচেয়ে আদিম–অকৃত্রিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। যেখানে নারী ও পুরুষ সুন্দর ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় একত্রে বাস করেন। তাদের যৌথ পথচলায় পরিবারে সন্তান আসবেÑ এমনটাই প্রত্যাশা করেন অনেকে। কেউ কেউ আবার সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রজন্ম রেখে যাওয়ার জন্য সন্তান আকাক্সক্ষা অনুভব করেন।
বাংলাদেশে কোনো কোনো দম্পতির কাছে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাও সন্তানের জন্য ব্যাকুলতার একটি কারণ। কেননা এ দেশে বয়স্কদের জন্য সহায়তামূলক কার্যক্রমের অভাব থাকায় পরিণত বয়সে কে তাদের দায়িত্ব নেবে—এমন একটি অনিশ্চয়তা কাজ করে। এসব কারণে সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি দেশের উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের হাসপাতালগুলোয় বন্ধ্যত্ব নিয়ে তথ্য ও সেবা নিশ্চিত করা দরকার। একই সঙ্গে কাঠামোবদ্ধ ও পরিকল্পিত রেফারেল সিস্টেম দরকার। এ সমস্যায় ভুগছেনÑ এ রকম দম্পতিরা প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা করতে পারেন, এমন কারও কাছে যাওয়ার সহজলভ্য ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং যেসব দম্পতির উন্নত সেবা দরকার, তাদের বন্ধ্যত্ব বিশেষজ্ঞদের কাছে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করতে হবে।
দেশের জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। সমাজে যাদের মতামতের গুরুত্ব আছে, যেমন শিক্ষক, চেয়ারম্যান, ধর্মীয় নেতা এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করতে পারেন। সন্তান হচ্ছে নাÑ এমন দম্পতিদের প্রতি পরিবার ও সমাজের সহানুভূতিশীল আচরণ অতি দরকারি।
বন্ধ্যত্ব কোনো অপরাধ কিংবা পাপ নয়। যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা নিলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভবÑ এ সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে অচলায়তন ভেঙে আলোক আসুক। সচেতনতার বীজ ছড়িয়ে পড়ুক চারদিকে।
লেখক: এএসএম রিয়াদ আরিফ, সিনিয়র কনট্যান্ট ডেভলপার; ড. কামরুন নাহার, হেড অব রিসার্চ ও অনুভব চক্রবর্তী কমিউনিকেশনস স্পেশালিস্ট, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য বিভাগ, আইসিডিডিআরবি
ধংস.ধৎরভ@রপফফৎন.ড়ৎম