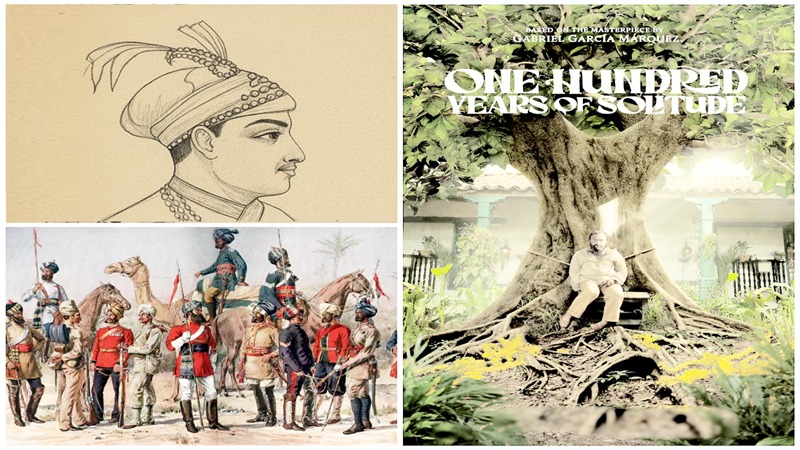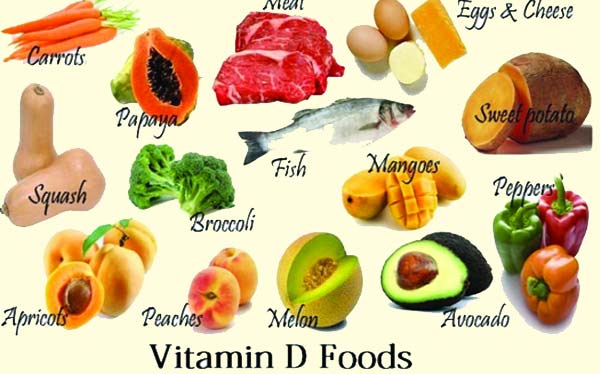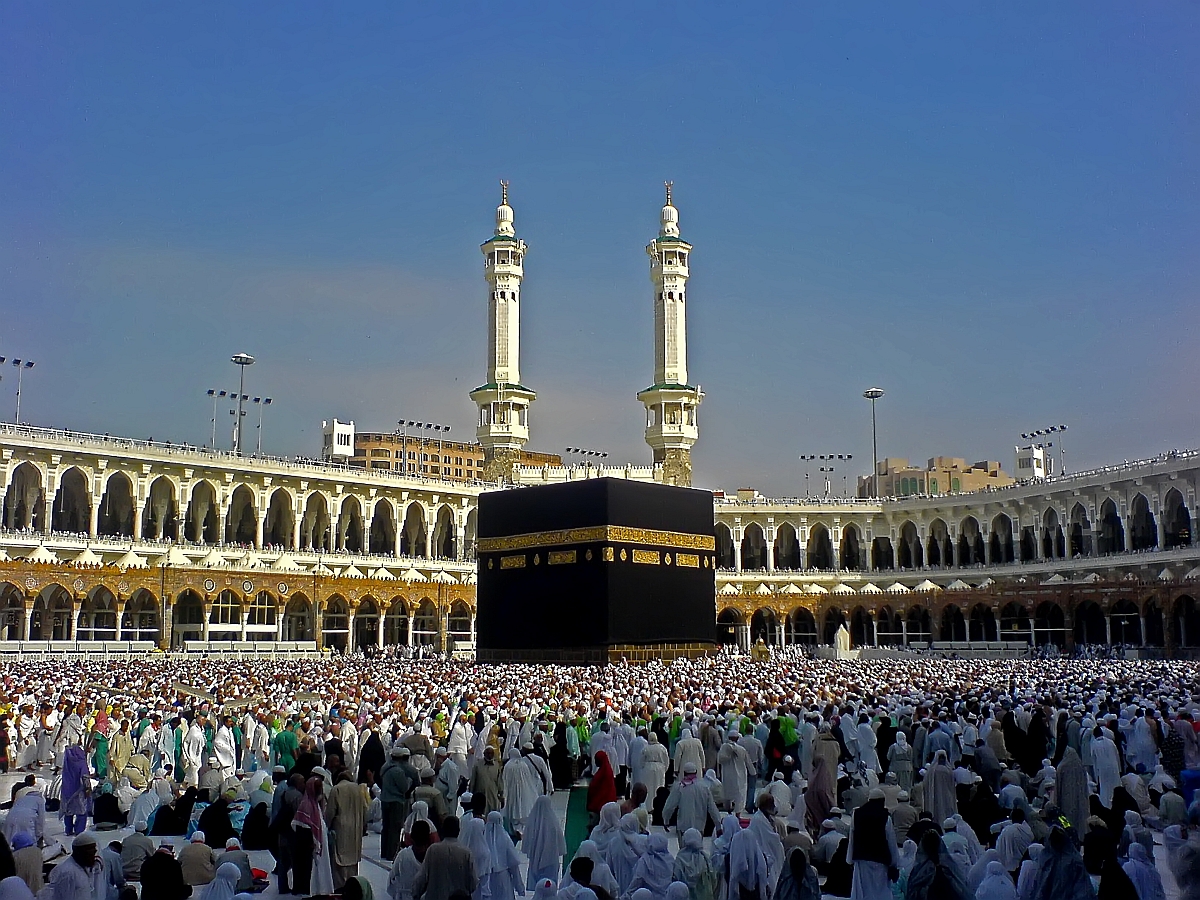মিলু শামস
ঔপনিবেশিক পূর্বসূরিতার ঐতিহাসিক দুর্ভাগ্য এই যে, আজও আমরা নিজেদের ইতিহাস দেখি ঔপনিবেশিক প্রভুর চোখে। অন্তত সতেরোশ’ সাতান্ন থেকে ঊনশিশ’ সাতচল্লিশ পর্যন্ত এ উপমহাদেশে তাদের প্রত্যক্ষ শাসনকাল পর্যন্ত তো অবশ্যই। পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজের কাছে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের প্রচলিত যে ইতিহাস তা ইংরেজ এবং তাদের এদেশীয় সহযোগীদের উদ্দেশ্যমূলক রচনা। একেই আমরা নিজেদের ইতিহাস বলে জেনে এসেছি। আড়াইশ’ বছরের বেশি সময় ধরে তারা সিরাজ-উদ-দৌলাকে দুর্বলচিত্ত অপরিণামদর্শী লম্পট নবাব হিসেবে চিত্রিত করেছে। তার এ দুর্বলতা এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে বিধ্বস্ত বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেখভাল বা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য ইংরেজরা বাধ্য হয়ে রাজ্য দখল করেছিল। নইলে রাজ্য বা ভারত দখলের কোনো ইচ্ছেই তাদের ছিল না! ইতিহাসের এমন পাঠই এতকাল দিয়ে এসেছেন একদল ঐতিহাসিক।
একজন স্বাধীন নবাবকে এক বিদেশি বাণিজ্য কোম্পানি ও তাদের দোসররা নানামুখী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে প্রহসনের যুদ্ধে পরাজিত করে এ দেশ দখল করেছিল। ওই অন্যায় অধিকারকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ইতিহাসকে এভাবে উপস্থাপন করা ঔপনিবেশিক শাসকদের নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য অপরিহার্য হয়। নিজের দেশ ও স্বাধীন নবাবের প্রতি স্থানীয়দের মনে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে বহুমুখী অপপ্রচারের মধ্য দিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই প্রচলিত ইতিহাস পাঠ-সিরাজের প্রতি করুণা যত জাগায়, শ্রদ্ধা জাগায় তার চেয়ে অনেক কম। একজন ‘দুর্বলচিত্ত’ পরাজিত নবাবের করুণ পরিণতি আবেগ তাড়িত করে। কিন্তু এভাবে ভাবায় না যে, সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী ভারতীয় নবাব।
যিনি সব ধরনের টোপ প্রত্যাখ্যান করে নিজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দোদুল্যমানতায় আচ্ছন্ন হননি। এভাবে দেখায় না যে, তিনি ছিলেন আধিপত্য বিস্তারকারী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী প্রথম জাতীয় বীর।
ইতিহাসকে উল্টো করে দেখার এ প্রবণতা শতভাগ ঔপনিবেশিক চাতুরি। বুদ্ধিবৃত্তির দাসত্বমুক্ত কয়েকজন ঐতিহাসিক এই চাতুরীর স্বরূপ উন্মোচন করেছেন সম্প্রতি ইউরোপের বিভিন্ন আর্কাইভস, ব্রিটিশ লাইব্রেরির ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডসে রাখা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নথিপত্র, ‘প্রাইভেট পেপারস’ এবং হল্যান্ডের রাজকীয় আর্কাইভসে সংরক্ষিত ডাচ কোম্পানির দলিল পত্র ঘেঁটে।
বাংলাদেশ বা এ উপমহাদেশের মতো ঔপনিবেশিক নিষ্পেষণের আরেক ভূখণ্ড লাতিন আমেরিকা। স্প্যানিশ ভাষায় সবচেয়ে বেশি পঠিত লেখক মিগুয়েল-দে সের্ভান্তেস এবং গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ।
সময়ের হিসেবে সের্ভান্তেস ও মার্কেজের মধ্যে তিনশ’ বছরের ব্যবধান হলেও ঔপনিবেশিক আধিপত্য ও এর বিরুদ্ধে জনগণের মুক্তি সংগ্রামের আকাক্সক্ষার অন্তর্নিহিত রূপের বিশ্বস্ত দলিল তারা নিজের মতো করে রেখে গেছেন ‘সভ্য’ দুনিয়ার কাছে। ব্যবধানের তিনশ’ বছরে লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তির ইতিহাস রচিত হয়েছে সিমন বলিভারের নেতৃত্বে। স্পেনের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র লাতিন আমেরিকাকে জাগিয়ে সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বলিভার স্পেনের অধীনতা থেকে মুক্ত করেছিলেন বলিভিয়া, পানামা, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু ও ভেনিজুয়েলাকে।
প্রতিষ্ঠিত হয় বেশকিছু জাতীয় প্রজাতন্ত্র। তবে বলিভার ঔপনিবেশিক শাসন থেকে লাতিন আমেরিকাকে রাজনৈতিক মুক্তি দিলেও দীর্ঘদিনের শোষণ-বঞ্চনায় জর্জরিত দেশগুলোর স্বাভাবিক বিকাশ স্তব্ধ হয়ে থাকে আরও প্রায় একশ’ বছর। বিশ শতকে এসে জাতীয় মুক্তির দ্বিতীয় পর্বের যুদ্ধে অবরুদ্ধ লাতিন আমেরিকা, পাবলো নেরুদার ভাষায় ‘বোবা মহাদেশ’টি ভাষা পায় তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কলমে। আর বলিভারের রাজনৈতিক সংগ্রামের রিলে হাতে এগিয়ে চলেন ফিদেল ক্যাস্ট্রো, চে গুয়েভারা, আগাস্তো সান্ডিনোরা।
সের্ভাস্তেসের উত্তরসূরিদের কলমে ভর করে পাহাড়-অরণ্য ঘেরা মিথ আর লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাসের লাতিন আমেরিকা তার সব রহস্যময়তা নিয়ে হাজির হয় এ দেশের পাঠকের দরবারেও। কেমন যেন চেনা মনে হয় তাকে। চেনা শোষণ। আধিপত্যবাদের নিগড়ে বৃত্তাবদ্ধ চেনা জীবন। চেনা সংগ্রাম, চেনা লড়াই। সব কিছু চেনা চেনা। তবে এত চেনার মধ্যেও গভীরতর অচেনা কিছুও নিশ্চয় ছিল। তাই দুবার ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসন থেকে মুক্ত আমাদের এ অঞ্চল থেকে লাতিন আমেরিকা চরিত্রের দিক থেকে আলাদা, অনন্য।
নয়া উদারবাদী অর্থনীতি বা একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের বিশ্বায়নে হাত-পা গুটিয়ে আত্মসমর্পণকে আমাদের মতো দেশগুলো যখন অনিবার্য বাস্তবতা বলে মেনে নিয়েছে তখন সেই তন্ত্রের কেন্দ্রের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশটির নিকটতম প্রতিবেশী লাতিন আমেরিকার অনেক দেশই বারবার প্রতিবাদী হয়েছে ।
নয়া উদারবাদী অর্থনীতি জনকল্যাণমুখী কাজে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমানোর পরামর্শ দিয়ে লাভজনক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তি খাতে ছেড়ে দিয়ে ব্যাপক বেসরকারীকরণের কথা বলে। শিক্ষা চিকিৎসা খাদ্য বাসস্থান ইত্যাদি জনগণের মৌলিক প্রয়োজনীয় খাতগুলোতে ভর্তুকি বন্ধের কথা বলে। বিশ্বায়নের এ চক্রে পড়ে আমাদের মতো দেশগুলোর সাধারণ মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস ওঠে। আর সিমন বলিভার ফিদেল ক্যাস্ট্রোর লাতিন আমেরিকায় প্রাকৃতিক সম্পদ জাতীয়করণের অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় হয়। জনগণের শিক্ষা স্বাস্থ্য আবাসন সমস্যার সমাধানকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব মনে করা হয়।
যেসব কর্পোরেশনের দাপটে মুক্ত দুনিয়া থর থর করে কাঁপে সেসব কোম্পানির স্থানীয় প্রতিনিধিদের পরিষ্কার বলে দেওয়া হয় ও দেশে ব্যবসা করতে হলে তাদের শর্ত মেনেই করতে হবে। নইলে পাততাড়ি গুটিয়ে কোম্পানিরা নিজ নিজ দেশে চলে যেতে পারে।
দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিবাদী ভূমিকার ফ্ল্যাশব্যাকে রয়েছে আধিপত্যবাদী নখড়ের দগদগে ঘা। শোষণের পর শোষণে নিঃস্ব ও একাকী হওয়ার আখ্যান। সের্ভাস্তে যে গল্প বলেছেন তা থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা। লাতিন আমেরিকার স্বকীয়তা ধ্বংস করার অবিরাম প্রচেষ্টা তাকে মানসিকভাবেও পরনির্ভর করতে চায়। একজন দায়িত্বশীল দেশপ্রেমিকের কর্তব্য এই স্বকীয়তা রক্ষা করা।
স্বকীয়তা রক্ষার বৈপ্লবিক দায় থেকেই হয়ত জন্ম নেয় ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিটিউডের মতো উপন্যাস। গণমানুষের সংস্কার বিশ্বাস অবিশ্বাস লৌকিক-অলৌকিকের গল্প শুনিয়ে বিশ্বসাহিত্যে তোলপাড় তুলে লাতিন আমেরিকাকে একটানে মার্কেজ নিয়ে আসেন উজ্জ্বল আলোর আসরে। শুধু নোবেল জয়ী উপন্যাসেই নয়, তার গোটা সাহিত্যকর্মই নিপীড়িত সাধারণ মানুষের জীবন ও সংগ্রাম তাদের হাসিকান্না স্বপ্ন কল্পনার অসামান্য চিত্রায়ন। ঔপনিবেশিক শাসনের কৃত্রিম সমাজের কৃত্রিম ব্যক্তি মার্কেজের মনোযোগ কাড়তে পারেনি।
কৃত্রিম ইতিহাসের আড়ালে চাপাপড়া সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গ আবার স্বপ্ন দেখার শক্তি এবং সাহস নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো; যা গৎবাঁধা চকচকে ইতিহাস লিখিয়েদের মনোযোগের বাইরের বিষয়- মার্কেজ তাকেই লেখার উপজীব্য করেছেন। সব কৃত্রিমতার বাইরে যেখানে বয়ে চলেছে জীবনের সত্যিকারের স্রোত, ওই বহমানতাকে তার নিজস্বতা ও সমগ্রতাসহ তুলে এনেছেন নিজের বিশাল ক্যানভাসে।…
লাতিন আমেরিকার এক স্প্যানিশ বসতির ভাইবোন সম্পর্কের দুই তরুণ-তরুণীর বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং এ বিয়ের পরিণাম হিসেবে অতিপ্রাকৃত এক সংস্কার একশ’ বছর ধরে এই পরিবারের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে আচ্ছন্ন রাখে। সংস্কারটি হলো ভাইবোনের বিয়ের সন্তান লেজ নিয়ে জন্মাবে, এ সংস্কারে তাড়িত হয়ে ওই দম্পতি পরিচিত বসতি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সমাজবিহীন দুর্গম এক এলাকায়।
সেখানে ঘর বাঁধে এবং সন্তানের জন্ম দেয় তারা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম পেরোলেও কোনো সন্তানই লেজ নিয়ে জন্মায় না। তবে লেজবিষয়ক সংস্কারটি তাদের সবার জীবনেই একটি গোপন আতঙ্কের মতো থেকে যায় এবং সংস্কারটি সত্যি হয় পরিবারের শেষ প্রজন্মের শেষ সন্তানের বেলায়। এ সন্তানের জনক-জননীও ভাইবোন সম্পর্কের। লেজ নিয়ে যে শিশু জন্মায় সে আসলে মৃত। মৃত অবস্থায়ই জন্মায় সে এবং তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় তার মা।
উনিশ শতকের শুরু থেকে বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত একশ’ বছর ধরে একটি ঘর ও তা ঘিরে গড়ে ওঠা জনপদের বিকশিত হওয়ার নানান দিক উন্মোচন করতে করতে ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিটিউড এগোতে থাকে। এগোতে থাকেন মার্কেজ। জনমানবহীন দুর্গম এলাকায় ভাইবোনের যে সংসার শুরু হয়েছিল সেখানে এক সময় ঢুকে পড়ে রেললাইন। ঢুকে পড়ে যান্ত্রিক সরঞ্জাম। মার্কিন ধনকুবের, ইতালিয়ান বাদ্যযন্ত্রবিদ, আরব সওদাগর।
দুর্গম এলাকাটি এক সময় জীবনযাপনের জটিলতায় অস্থির ও অশান্ত হয়ে ওঠে। মার্কেজ শুধু একশ’ বছরের নীরবতার গল্প শোনান না। শতকের পর শতক নীরব থাকা, ঘুমিয়ে থাকা মহাদেশটিকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে জাগিয়ে তোলেন। হয়ত সে জন্যই ঘুরে দাঁড়াতে পারে লাতিন আমেরিকা। মার খেতে খেতে সটান দাঁড়িয়ে আবার জানাতে পারে নিজের অস্তিত্বের কথা।
এ জনপদ যেন ঠিক সেভাবে পারে না।
লেখক: কবি ও সাংবাদিক
(মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব)
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ