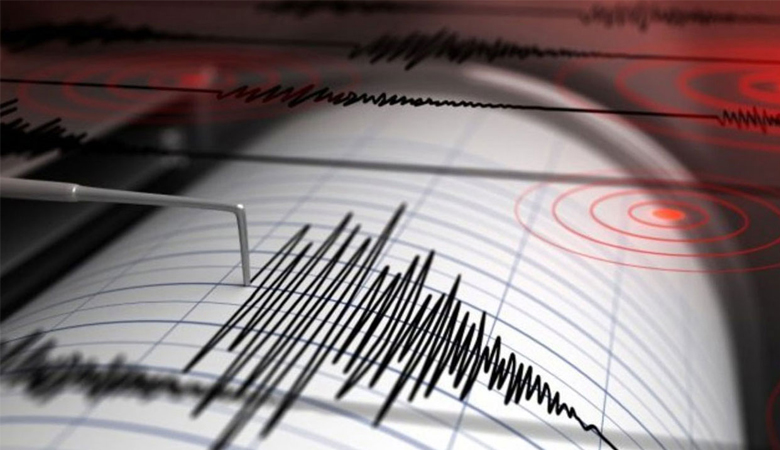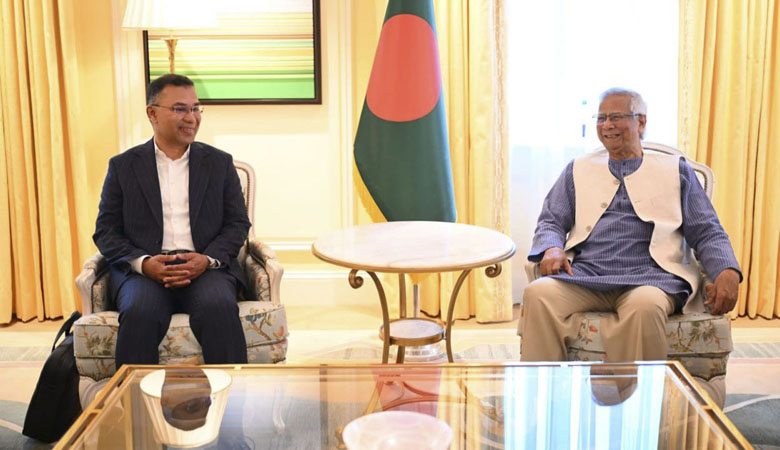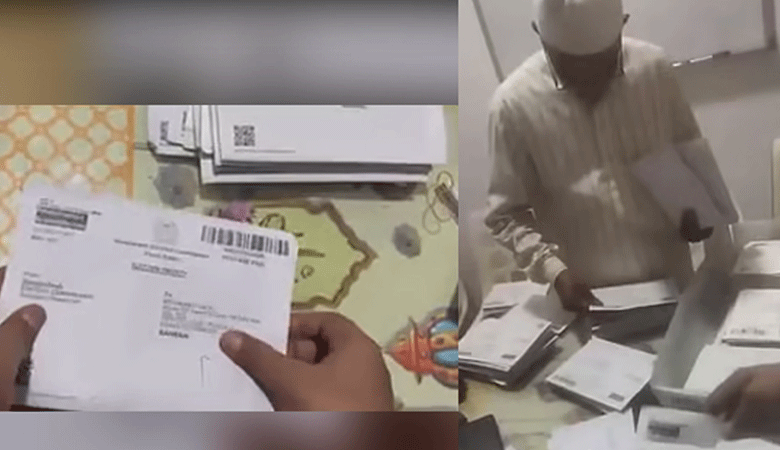সমীরণ বিশ্বাস : ভালো নেই ঢাকার গাছেরা। ধুলা আর বায়ু দূষণের কবলে পড়ে ধুঁকছে তাদের স্বাভাবিক জীবনচক্র! যে গাছের অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকব, আমরা সেই গাছকেই করছি অযতœ আর অবহেলা! বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গাছের যতেœর বিকল্প নেই। কিন্তু সব জেনে বুঝেও উদ্যোগ নেই সংশ্লিষ্ট মহলের। রাজধানী ঢাকার ধুলায় ধুসরিত সড়কদ্বীপের গাছগুলো। ধুলার আস্তর এতটাই পুরু যে, আলো বাতাসের সুযোগ পায় না নতুন কুড়িরাও! মারা যাচ্ছে নতুন ফল দিতে শুরু করা গাছ। একটু পানি ছিটালেই বেরিয়ে আসছে নতুন কুঁড়ি, প্রাণের অস্তিত্ব।
গাছেরা নির্দয় নগরীকে জানায় নিঃশব্দ অভিযোগ! গাছের অক্সিজেন নিয়ে বাঁচে থাকে মানুষ! কিন্তু পাতায় যখন ধুলার আস্তর জমে তখন গাছের পক্ষেও সম্ভব হয় না অক্সিজেন তৈরি করা। এতে ঢাকার বাতাস হয়ে উঠছে আরও বিষাক্ত। রাজধানীর ধুলাবালি দেখে নিজের মনে হয় আমরা একটা ভুল নগরীতে বসবাস করছি। আমাদের নাগরিকের উচিত গাছের প্রতি সচেতন হওয়া। সড়কে খুরাখুরি, সড়কের পাশে অরক্ষিত অবস্থায় ইট, বালি, সিমেন্ট সহ নির্মাণসামগ্রী গাড়ির চাকার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে, উড়ে উড়ে জমে গাছের পাতায়। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা যায়; ঢাকায় গাছের পাতায় প্রতিদিন ধুলাজমে ৪৩৬ মেট্রিক টন।
ঢাকা শহরের অক্সিজেনের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে এটা কিন্তু লক্ষণীয় এর কারণে শিশুদের এবং বয়স্কদের শ্বাসকষ্টজনিত রোগ দিন দিন বেড়ে চলছে। দ্য স্টেট অব গ্লোবাল এয়ার ২০২৩ এর তথ্য অনুযায়ী শুধু বায়ু দূষণজনিত রোগে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের প্রায় ৯০ হজার মানুষ মারা গেছে। বায়ু দূষণজনিত রোগে, মৃত্যুর হিসাবে বাংলাদেশ বিশ্বে পঞ্চম।শুধু ধুলা ও বায়ু দূষণমুক্ত রেখে গাছকে ভালো রাখা সম্ভব এবং সেই সক্ষমতা আমাদের আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, আন্তরিক প্রচেষ্টার দেখা মেলে না আমাদের সংশ্লিষ্ট মহলের।
গবেষক এবং পরিবেশবাদীদের মতে ঢাকায় দরকার দেবদারু আম, জাম ও বটের মত গাছের। যারা অতি দূষণেও টিকে থাকে। সেই সঙ্গে বিদ্যমান গাছগুলোর জন্য চাই সঠিক পরিচর্যা। পাশাপাশি কম পানি দরকার হয় এমন গাছ বেছে বেছে ঢাকা শহরে রোপন করা। শহরের বায়ু দূষণ কমাতে হলে সঠিক গবেষণা ও নীতির কঠোর বাস্তবায়ন অতীব জরুরি। ধুলার আস্তর জমে ধূসর হয়ে গেছে সবুজ গাছ। সঠিক পরিচর্যার অভাবে ধুঁকছে গাছ, কমছে অক্সিজেন এবং মানুষ পড়ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে। গাছ এবং সড়ক পরিছন্নতার জন্য পানি ব্যবহার অবসম্ভাবী নিশ্চিত করা জরুরি। পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্রিয় ভূমিকায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে একটি সমন্বিত কর্মধারায়, ধুলি দূষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার এখনই সময়।
সাধারণত ১০০ থেকে ২০০-এর মধ্যে একিউআই সংবেদনশীল মানুষের জন্য অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচিত হয়। একইভাবে একিউআই ২০১ থেকে ৩০০-এর মধ্যে থাকলে সংশ্লিষ্ট শহরের পরিবেশ বসবাসের জন্য খারাপ এবং ৩০১ থেকে ৪০০-এর মধ্যে থাকলে বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচিত হয়। বাতাসের মান নির্ণয়ের জন্য একিউআই একটি সূচক। সরকারি সংস্থাগুলো একটি নির্দিষ্ট শহরের বায়ু কতটা পরিষ্কার বা দূষিত ও এজন্য মানব স্বাস্থ্যে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে বা তা উদ্বেগের কারণ হতে পারে কি না তা জানতে সূচকটি ব্যবহার করে থাকে।
বাংলাদেশের সামগ্রিক একিউআই পাঁচটি দূষণকারী মানদ-ের ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে কণা পদার্থ (পিএম১০ এবং পিএম২.৫), কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ও ওজোন। ঢাকা দীর্ঘদিন ধরেই বায়ুদূষণ সমস্যায় জর্জরিত। ঢাকার বাতাসের গুণমান সাধারণত শীতকালে অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় এবং বর্ষাকালে উন্নত হয়।
২০১৯ সালের মার্চে পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই) এবং বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ঢাকার বায়ুদূষণের তিনটি প্রধান উৎস হলো ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণাধীন স্থাপনার ধুলা। সাধারণত জুনের মাঝামাঝিতে বর্ষাকাল শুরু হলে ঢাকার বাতাস সতেজ হতে শুরু করে। জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বায়ু নির্মল থাকে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, বায়ুদূষণ বিশ্বব্যাপী মৃত্যু ও অক্ষমতার শীর্ষ ঝুঁকির কারণগুলোর মধ্যে একটি। দূষিত বাতাসে দীর্ঘদিন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের ফলে হৃদরোগ, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ফুসফুসের সংক্রমণ এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায় বলে বিভিন্ন গবেষণায় স্বীকৃত হয়েছে।
অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের কারণে বায়ু দূষিত হচ্ছে। রাজধানীতে প্রচুর নির্মাণের কাজ হচ্ছে যা ধুলা তৈরি করছে। অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণকাজ, আবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা, ইটভাটা থেকে শুরু করে কোনোটাই নিয়ম মেনে করা হয় না। ঢাকা শহরের চারপাশ ঘিরে কমপক্ষে ৫ হাজার ইটভাটা আছে সেগুলো থেকে কার্বন নিঃসরিত হওয়ায় বায়ু দূষিত হচ্ছে। বাতাসে যে পরিমাণ সালফার ডাই অক্সাইড থাকে তা পানিতে মিশে চোখে জ্বালাপোড়া করায়। এতে ফুসফুসে প্রদাহ থেকে শুরু করে অনেক ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দেয়। এসব থেকে উদ্ধার পেতে, যে আইন ও নিয়ম আছে সেগুলো মেনে চলার কোনো বিকল্প নেই।
লেখক: কৃষি ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ