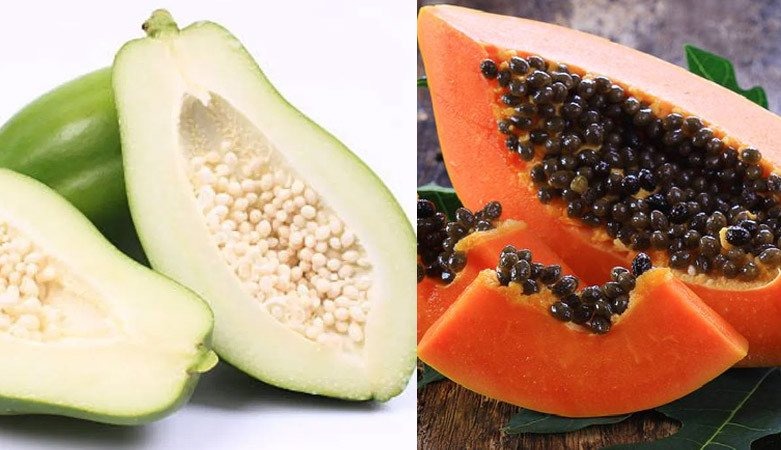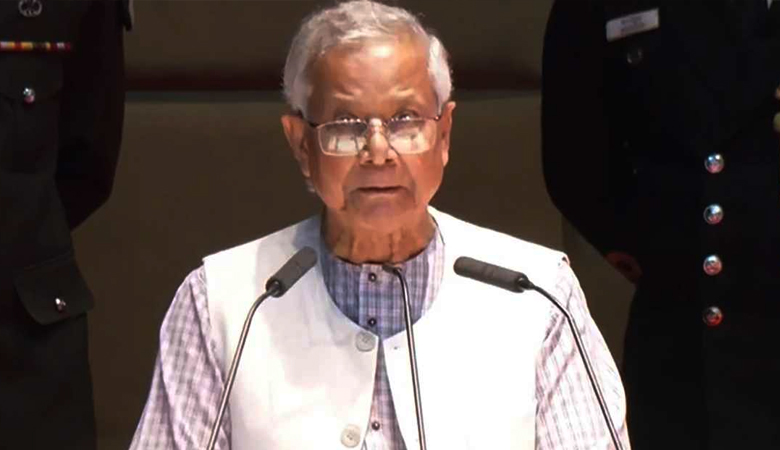মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম : ঘটনাটি মাস কয়েক আগের। ভোরবেলা বিছানা ছাড়তে বেশ কষ্ট হচ্ছিল আমার। প্রায় ১৭ বছরের পুরনো ব্যথা মাথাচাড়া দিয়েছে। তবে কারণ বুঝতে আমার কষ্ট হলো না। আগের দিন বেশ কয়েক ঘণ্টা একনাগাড়ে কেটেছে ল্যাপটপের সামনে চেয়ারে বসে। ক্লাস, পরীক্ষা না থাকায় কর্মস্থলে না গিয়ে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিলাম। সকালের নাস্তা কোনোভাবে সেরে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম আমি। একপর্যায়ে দু’চোখ এঁটে আসে আমার। এর মাঝে আসে বন্ধুস্থানীয় এক বড় ভাইয়ের ফোন। উদীয়মান জাঁদরেল আমলা তিনি। লেখালেখিও করেন। মূলত লেখালেখির সুবাদেই আমাদের খাতির, সংযোগ ও বন্ধুত্ব। যাহোক, শরীরের করুণ অবস্থার কথা শুনে তিনি গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটে এলেন আমার বাসায়। এক রকম জোর করেই নিয়ে গেলেন ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স ও হাসপাতালে। পরিচিত এক ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে গেলেন তিনি। ডাক্তার বেশ আন্তরিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। লিখে দিলেন প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধ। এরপরই শুরু হলো তুমুল আড্ডা।
ওই আড্ডার ফাঁকেই ডাক্তার আমার কাজ ও গবেষণা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি জানালাম। সেই ডাক্তার মশাই বেশ কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন, একটু বুঝিয়ে বলবেন কী? মনে মনে পুলক বোধ করলেও আমি পড়লাম বেশ বিপদে। স্নায়ুবিজ্ঞানের আলোকে আমার কাজের বিষয়টি কীভাবে বোঝানো যায় এই প্রশ্নে। আজকের ওই আলোচনাটি স্নায়ুবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ সেই ডাক্তারের সঙ্গে আমার কথোপকথনের অংশবিশেষ।
প্রথমেই আমি জানতে চাইলাম আপনারা যখন রোগী দেখেন, রোগ নির্ণয় করেন, লক্ষণ বুঝে ওষুধ দেন, তখন আপনাদের ও রোগীর মধ্যে কি শুধু কথার লেনদেন হয়? মোটেও না! এই কথোপকথনের গভীরে লুকিয়ে আছে মস্তিষ্কের এক জটিল খেলা। নিউরনের আলোড়ন, হরমোনের বন্যা আর বিশ্বাসের এক অদৃশ্য সেতু। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ডাক্তারের আন্তরিকতা আর মিষ্টি কথায় রোগীর মস্তিষ্কে ঘটে যায় এক অভাবনীয় পরিবর্তন। কীভাবে? ধরুন, ডাক্তার যখন হাসিমুখে কথা বলেন, রোগীর মস্তিষ্কে যেন আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। ‘অক্সিটোসিন’ নামক হরমোন নিঃসৃত হয়ে তৈরি করে গভীর বিশ্বাস।
অন্যদিকে ডাক্তারের শীতল কণ্ঠ বা অবহেলা, রোগীর মস্তিষ্কে তৈরি করে ব্যথার অনুভূতি। ‘কর্টিসল’ হরমোন বাড়িয়ে দেয় উদ্বেগ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায়, ডাক্তারের ইতিবাচক আচরণ ‘প্লেসিবো ইফেক্ট’ তৈরি করে। মানে, ওষুধ ছাড়াই শুধু ডাক্তারের কথায় রোগী সুস্থবোধ করতে শুরু করেন। মস্তিষ্কের ‘ভেন্ট্রোমিডিয়াল প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স’ আর ‘নিউক্লিয়াস অ্যাকুম্বেন্স’-এর মতো অঞ্চলগুলো তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে, যা রোগীকে আশাবাদী করে তোলে। শুধু কথা নয়, ডাক্তারের স্পর্শও রোগীর মস্তিষ্কে তৈরি করে এক উষ্ণ অনুভূতি। ‘মিরর নিউরন’-এর মাধ্যমে ডাক্তার যখন সহানুভূতি প্রকাশ করেন, রোগীও তা অনুভব করেন। স্পর্শের মাধ্যমে নিঃসৃত হয় ‘ডোপামিন’ যা রোগীকে শান্ত করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ডাক্তার আর রোগীর মস্তিষ্কের মধ্যে তৈরি হয় এক অদ্ভুত সংযোগ। এই ‘সিক্রোনাইজড’ মস্তিষ্কের কার্যকলাপ চিকিৎসার কার্যকারিতা বাড়িয়ে তোলে বহুগুণ। তাই ডাক্তারের আন্তরিকতা শুধু মুখের কথা নয়, এ যেন মস্তিষ্কের এক জাদুকরী স্পর্শ, যা রোগ নিরাময়ে রাখে এক বিশাল ভূমিকা!
রোগ, শোক, যন্ত্রণায় কাতর হয়ে একজন রোগী যখন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ডাক্তারের চেম্বারে যান তখন তার মাথাজুড়ে থাকে হাজারও চিন্তা, উদ্বেগ ও ভয়। গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ যখন চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন থাকে তখন তার মস্তিষ্ক আলাদাভাবে কাজ করে। কেননা এসময় স্ট্রেস হরমোন যেমন কর্টিসল বেড়ে যায়। কর্টিসল মস্তিষ্কের সামনের অংশের স্বাভাবিক ক্রিয়াকে ব্যাহত করে। মানব মস্তিষ্কের এই অংশটি চিন্তা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই হাসপাতালে কিংবা ডাক্তারের চেম্বারে একজন রোগীর পক্ষে কোনও জটিল বিষয়, যেমন- ডাক্তারি তথ্য বোঝা কঠিন হয়ে যায়। কেননা দুশ্চিন্তা মস্তিষ্ককে আবেগ ও কম স্পষ্ট চিন্তার দিকে বেশি মনোযোগ দেয়। ফলে ডাক্তার কী বলেন তা মনে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। উদ্বেগও একই কাজ করে। এটি ব্যক্তির মস্তিষ্ককে বিপদের দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য করে। এতে স্বাস্থ্যেও প্রকৃত অবস্থা বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি মস্তিষ্কের কমে যায়। কাজেই প্রচণ্ড দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উদ্বেগ আক্রান্ত রোগীর পক্ষে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়া কিংবা ডাক্তারের প্রদত্ত তথ্য প্রক্রিয়া করা, স্মরণে রাখা এবং সেটা মেনে চলা কঠিন হয়ে পড়ে।
এদিকে ডাক্তারের ইতিবাচক কথাবার্তা রোগীর মস্তিষ্কের আদল দেয় ভিন্নভাবে। ডাক্তারের আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও সমবেদনাপূর্ণ কথাবার্তা রোগীর মস্তিষ্কে সুখীবোধ জাগ্রত করে। রোগ নিরাময়ের প্রশ্নে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। যখন ডাক্তাররা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলেন ও সদয় হন, তখন রোগীর মস্তিষ্কে ক্রিয়াশীলতা সঠিকভাবে ঘটে। চিকিৎসা ও আরোগ্য সম্পর্কিত ভালো সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাসের জন্য মস্তিষ্কের একটি বিশেষ এলাকা ব্যবহার করে। এই এলাকার নাম ভেন্ট্রোমিডিয়াল প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স। স্বাভাবিক সময়ে ব্যক্তির মস্তিষ্ক একটি বিশেষ এলাকা ব্যবহার করে। এলাকাটি মনের ভেতর পুরস্কারবোধ জাগ্রত করে। এই এলাকার নাম হলো নিউক্লিয়াস অ্যাকুম্বেন্স। মস্তিষ্কের এই অংশটি কোনও কিছুতে গভীর মনোযোগ দেওয়া ও ভালোভাবে মনে রাখতে সহায়তা করে। তখন রোগীর মনে হয় ডাক্তার তাকে ভালোভাবে বুঝতে পারছেন। এর জন্য টেম্পোরোপ্যারাইটাল জাংশন নামক এলাকাটি ব্যবহৃত হয়।
অন্যদিকে ডাক্তারের কথাবার্তা যদি ইতিবাচক না হয়, তাহলে রোগীর মস্তিষ্ককে চিন্তিত ও দুঃখী করে তোলে। যখন ডাক্তাররা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেন বা রোগীর কথা না শোনেন, তখন রোগীর মস্তিষ্কে নেতিবাচক জিনিস ঘটে। এসময় মস্তিষ্ক ব্যথা অনুভব করে এমন এলাকাগুলো ব্যবহার করে। যা শারীরিক ও সামাজিক উভয় ব্যথাই অনুভব করতে পারে। এই এলাকাগুলোর নাম ডরসাল অ্যান্টেরিয়র সিঙ্গুলেট কর্টেক্স এবং অ্যান্টেরিয়র ইনসুলা। রোগীর মনে হতে পারে তিনি প্রত্যাখ্যাত বা অবহেলিত হচ্ছেন। এতে রোগীর খারাপ লাগে। কাজেই ডাক্তারের এই যোগাযোগ দক্ষতা, আঙ্গিক ও তার কথাবার্তা রোগীর নিজেকে নিয়ে ধারণাকেও বদলে দেয়। ডাক্তারের কথাবার্তা খারাপ হলে, মস্তিষ্ক ডাক্তারি তথ্যকে জীবনের গল্পের সঙ্গে ভালোভাবে মেলাতে পারে না। তখন রোগী এসব তথ্য কম মনে রাখতে পারেন।
ডাক্তারদের সদয় কথা আসলে রোগীর মস্তিষ্ক কীভাবে ব্যথা অনুভব করে এবং ভালো হয়ে ওঠে, তা পরিবর্তন করতে পারে। একে প্লেসিবো ইফেক্ট বলে। যখন ডাক্তাররা ইতিবাচক ও যত্নশীল হন, রোগী মস্তিষ্ক প্রাকৃতিক ব্যথানাশক নিঃসরণ করে। এদের অপিওডস বলে। রোগীর মস্তিষ্ক ব্যথা নিয়ন্ত্রণকারী এলাকাগুলো ব্যবহার করে। এই এলাকাগুলো ব্রেইনস্টেম ও মস্তিষ্কের সামনের অংশে থাকে। মস্তিষ্ক ডোপামিন নামক একটি সুখী রাসায়নিকও নিঃসরণ করে। এটি মস্তিষ্কের পুরস্কার এলাকায় ঘটে। ডাক্তার কী বলেন এবং কীভাবে বলেন তার কারণে রোগী ভালো বোধ করতে শুরু করেন। সদয় ডাক্তারের কথাবার্তা রোগীর মস্তিষ্ককে আবেগ ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এটি তার মস্তিষ্কের উদ্বেগের অংশ, অ্যামিগডালাকে শান্ত করে। এটি উপসর্গগুলোকে কম ভীতিকরভাবে দেখতে সাহায্য করে। উষ্ণ ও যত্নশীল ডাক্তাররা এমনকি রোগীর মস্তিষ্ক তার শরীরকে যেভাবে অনুভব করে তাও পরিবর্তন করতে পারে। কেননা মস্তিষ্ক শরীরের সংকেতগুলোকে আরও ইতিবাচকভাবে দেখতে শুরু করে। যখন ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে ভালো সংযোগ স্থাপিত হয়, তখন তাদের মস্তিষ্ক এমনকি সিন্ক্রোনাইজডভাবে কাজ করতে পারে। এই মস্তিষ্কের সংযোগ চিকিৎসার কার্যকারিতা বাড়াতে পারে। ডাক্তারের কথাবার্তা থেকে প্লেসিবো ইফেক্ট বেশ কিছু সমস্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কাজ করে। আর তা হলো ব্যথা, দুঃখ ও নড়াচড়ার সমস্যা ইত্যাদি।
ডাক্তাররা কথা ছাড়াও আরও অনেক উপায়ে রোগীর প্রতি যত্নশীলতা দেখাতে পারেন। আর যত্নশীলতা প্রদর্শনের প্রশ্নে তারা কীভাবে রোগীর দিকে তাকান, কীভাবে দাঁড়ান এবং তাদের কণ্ঠস্বর কেমন- এগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডাক্তারকে বিশ্বাস করবেন কি না, তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নে রোগীর মস্তিষ্ক এই বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দেয়। মানুষের মস্তিষ্কে মিরর নিউরনস নামে বিশেষ কোষ আছে। এই নিউরনসগুলো ডাক্তার কী করছেন এবং কেমন অনুভব করছেন তা নকল করে। ডাক্তার চিন্তিত দেখালে, রোগীও কারণ না জেনেই চিন্তিত বোধ করতে পারেন। হাসিখুশি মুখ রোগীকে আরও আরামদায়ক ও বিশ্বাসী বোধ করাতে পারে। অক্সিটোসিন নামক একটি মস্তিষ্কের রাসায়নিক বিশ্বাস তৈরি করতে সাহায্য করে। যখন ডাক্তাররা চোখের দিকে তাকান বা সদয়ভাবে রোগীর কাছে আসেন, তখন অক্সিটোসিন নিঃসৃত হয়। অক্সিটোসিন রোগীর মস্তিষ্ককে নিরাপদ এবং আরও বেশি বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করে।
যদি ডাক্তারকে নকল মনে হয়, তাহলে রোগীর মস্তিষ্ক তা বুঝতে পারে। এক্ষেত্রে মস্তিষ্ক সমস্যা ও অনিশ্চয়তা খুঁজে বের করে এমন এলাকাগুলো ব্যবহার করে। এই এলাকাগুলোর নাম অ্যান্টেরিয়র সিঙ্গুলেট কর্টেক্স এবং অ্যান্টেরিয়র ইনসুলা। রোগীর মনে হতে পারে কিছু ভুল হচ্ছে। এমনকি রোগী ব্যাখ্যা করতে না পারলেও। ডাক্তারের কণ্ঠস্বর কেমন শোনাচ্ছে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিষ্কে কণ্ঠস্বরের আবেগ বোঝার জন্য বিশেষ এলাকা আছে। এগুলো টেম্পোরাল লোব ও মস্তিষ্কের সামনের অংশে থাকে। রোগীর অনুভূতিকে প্রভাবিত করার প্রশ্নে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডাক্তারের কণ্ঠস্বর উষ্ণ ও যত্নশীল হলে রোগীর মাঝে ডাক্তারের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার প্রবণতা বেড়ে যায়। অন্যদিকে শীতল কণ্ঠস্বর বা তাড়াহুড়ো করলে ডাক্তারের প্রতি বিশ্বাস ভেঙে যেতে পারে। এছাড়া সঠিক ও সম্মানজনকভাবে রোগীকে মৃদু স্পর্শ করলে রোগীর আস্থা ও বিশ্বাসের মাত্রা বাড়ে। কেননা সদয় স্পর্শের ফলে রোগীর মস্তিষ্ক স্পর্শ এলাকা ও পুরস্কার সক্রিয় হয়। স্পর্শ প্রাকৃতিক সুখী রাসায়নিক নিঃসরণ করতে। রোগীকে শান্ত করতে পারে। আর হাসপাতাল ব্যস্ত ও গোলমালপূর্ণ জায়গা। সব শব্দ, আলো এবং গন্ধ রোগীর জন্য চিন্তা করা কঠিন করে তুলতে পারে। এখানে ব্যক্তির মস্তিষ্ক একসঙ্গে অনেক বেশি তথ্য পায়। এতে ডাক্তারের ওপর মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। এছাড়া মস্তিষ্ক সবকিছুতে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে। এতে মস্তিষ্কের শক্তি খরচ হয়। ডাক্তার কী বলছেন তা বোঝা কঠিন হয়ে যায়। এত মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টায় রোগী ক্লান্ত হয়ে যেতে পারেন। হাসপাতালের চাপও পরিষ্কারভাবে চিন্তা করা কঠিন করে তোলে। তখন মস্তিষ্ক শেখার পরিবর্তে বিপদের জন্য প্রস্তুত হয়। তবে ডাক্তাররাও মানুষ। যখন ডাক্তাররা খুব চিন্তিত বা ক্লান্ত থাকেন, প্রচণ্ড কাজের চাপ তাদের মস্তিষ্ককে বদলে দেয়। স্ট্রেস হরমোন তাদের ডাক্তারদের মস্তিষ্কের সামনের অংশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে ডাক্তারদের ভালোভাবে শুনতে এবং রোগী কেমন অনুভব করছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয়। যখন রোগী ব্যথায় থাকেন তখন ডাক্তাররাও খুব বেশি ব্যথা অনুভব করতে পারেন। একে সহানুভূতিজনিত কষ্ট বা এমপ্যাথিক ডিসট্রেস বলে। তাদের মস্তিষ্ক আবেগিকভাবে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করে। সময়ের সঙ্গে অতিরিক্ত স্ট্রেস ডাক্তারের মস্তিষ্কের গঠন পরিবর্তন করতে পারে। এটি সহানুভূতি ও মনোযোগের জন্য প্রয়োজনীয় এলাকাগুলোকে সংকুচিত করতে পারে। স্ট্রেসের মধ্যে থাকা ডাক্তাররা তাদের মস্তিষ্কের অন্য অংশ ব্যবহার করতে পারেন। তারা রোগীকে মানুষ হিসেবে বোঝার চেয়ে বিপদের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে পারেন।
পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়াও ডাক্তারের মস্তিষ্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটি তাদের মস্তিষ্কের পক্ষে আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও সহানুভূতিশীল হওয়া কঠিন করে তোলে। ডাক্তাররা ক্লান্ত থাকলে তারা সহজে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারেন। রোগীকে, রোগীর প্রেক্ষাপটকে কম বুঝতে পারেন। এছাড়া ডাক্তাররা খুব ব্যস্ত থাকলে কিংবা একসঙ্গে অনেক কিছু নিয়ে ভাবলে তাদের মাঝে সহানুভূতি দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় মস্তিষ্কের শক্তি কমে যায়। তারা অনুভূতির পরিবর্তে কাজের ওপর মনোযোগ দিতে পারেন। তবে ডাক্তাররা স্ট্রেস ভালোভাবে সামলাতে এবং যত্নশীল কৌশল শিখতে পারেন। প্রশিক্ষণ ডাক্তারদের কঠিন পরিস্থিতিতেও তাদের মস্তিষ্কের সুখী ও সংযোগকারী অংশগুলো ব্যবহার করতে সাহায্য করতে পারে। এটি তাদের চাপের মধ্যেও সহানুভূতিশীল ও সহায়ক থাকতে সাহায্য করে।
লেখক: সিনিয়র লেকচারার, মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)