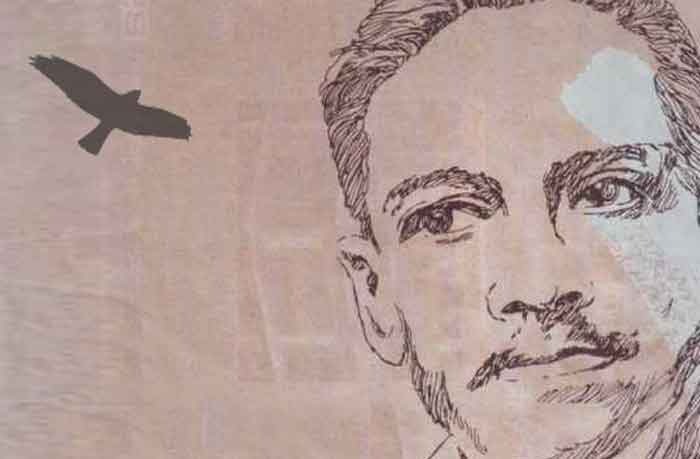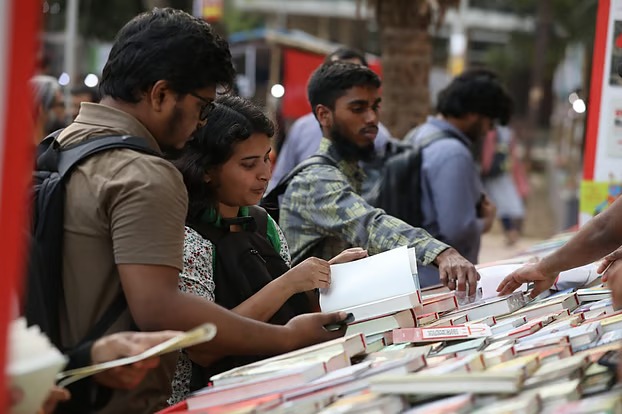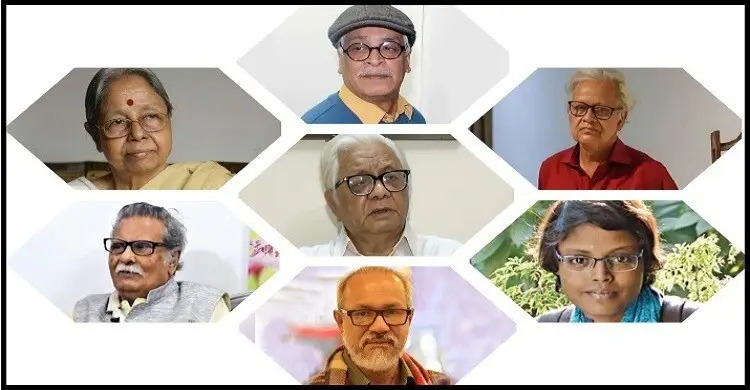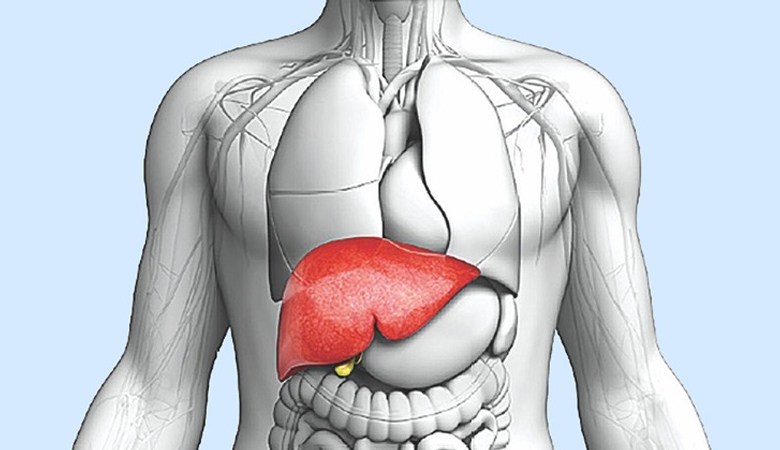বাংলা সাহিত্যে কয়েকজন কবি আছেন- যারা স্বকীয়তা, গভীরতা ও ভাবনার অভিনবত্ব দিয়ে সাহিত্যের ভুবনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ তেমনই একজন কবি। তিনি বাংলা আধুনিক কবিতার অন্যতম স্তম্ভ, নিঃসঙ্গ ও নিঃশব্দ এক নক্ষত্র। তার কবিতা যেমন স্বপ্নময়; তেমনই গভীর জীবনবোধে পরিপূর্ণ। বাংলা কাব্যভাষাকে তিনি দিয়েছেন নতুন দিগন্ত, ভাঙন ঘটিয়েছেন প্রচলিত কাব্যরীতির। তার কবিতা নিঃসন্দেহে চিত্রময় ও ভাবনায় তীব্র। প্রকৃতি, নিঃসঙ্গতা, স্মৃতি, মৃত্যু ও অস্তিত্বের প্রশ্ন তার কবিতায় ঘুরেফিরে আসে। তার কবিতায় এক ধরনের নির্জনতার আবরণ থাকে; যা পাঠককে এক নিঃসঙ্গ সৌন্দর্যের জগতে নিয়ে যায়। এ বিষয় নিয়েই এবারের সাহিত্য পাতার প্রধান রচনা
জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম সত্যানন্দ দাশ এবং মাতার নাম কুসুমকুমারী দাশ। তার মা নিজেও একজন কবি ছিলেন। যিনি ‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে’—এই অমর কবিতার রচয়িতা। এই সাহিত্যিক আবহেই জীবনানন্দের বেড়ে ওঠা। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে তিনি শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হন।
জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরা পালক’ প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। এই কাব্যগ্রন্থে তার কবি প্রতিভার সূক্ষ্মতা ও বিশেষত্ব ফুটে ওঠে। যদিও তা সমসাময়িক পাঠকদের কাছে ততা প্রশংসিত হয়নি তবুও সময়ের ব্যবধানে তার কবিতার সৌন্দর্য পাঠক মনে ধীরে ধীরে আলোড়ন তোলে। ‘আট বছর আগে একদিন’, ‘বনলতা সেন’, ‘সুরঞ্জনা’, ‘আবার আসিব ফিরে’- এসব কবিতা কেবল ভাষার কারুকার্য নয়, গভীর জীবনবোধেরও নিদর্শন।
‘বনলতা সেন’ কবিতায় জীবনানন্দ দাশ শুধু নারী নয়, এক অনন্ত শান্তির প্রতীককে খুঁজে পান। এই বনলতা তার জীবনের ক্লান্ত যাত্রার শেষে একটি আশ্রয়, যাকে তিনি খুঁজেছেন হাজার বছর ধরে। কবি বলেছেন, ‘হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,/সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে/অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে-/সেখানে ছিলাম আমি; আরও দূর অন্ধকার বিদর্ভ নগরে/আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,/আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।’
জীবনানন্দ দাশকে অনেকেই ‘নবজীবনের কবি’ বলে অভিহিত করেন। তিনি প্রচলিত কাব্যপ্রবাহ থেকে নিজেকে আলাদা করে এক নতুন কাব্যভাষা নির্মাণ করেন। যেখানে ধ্বনি, ছন্দ, অলংকারের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে কবির অন্তর্জগত। তার কবিতা গভীর, জটিল। কিন্তু এতে এক অপার সৌন্দর্য আছে। তার কবিতায় যেমন আছে পল্লীবাংলার প্রকৃতিচিত্র, তেমনই আছে নাগরিক জীবনের বিষাদ এবং ইতিহাস সচেতনতা।
‘আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়’- পঙ্ক্তিতে তার আত্মিক বন্ধন প্রকাশ পায় নিজের দেশ, নিজের মাটি ও নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি। জীবনানন্দ দাশের কাব্যভাষা একেবারেই আলাদা। তার শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, চিত্রকল্প নির্মাণ সব কিছুতেই তিনি নতুনত্ব এনেছেন। এই নতুনত্ব শুরুতে অনেক পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকলেও পরে তা-ই হয়ে ওঠে বাংলা কবিতার অমূল্য সম্পদ।
জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুও ছিল ট্র্যাজিক- কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। এই মৃত্যুর মধ্যেও যেন ছিল তার কবিতারই এক অনিবার্য পরিণতি, এক নীরব বিদায়।
আজ যখন আমরা বাংলা কবিতার দিকে তাকাই; তখন জীবনানন্দ দাশ এক অনিবার্য আলো হয়ে ধরা দেন। তিনি কেবল একজন কবি নন, তিনি এক নিঃসঙ্গ অনুভব, এক বিমূর্ত স্বপ্ন, এক নিঃশব্দ বিপ্লব। তার কবিতা আমাদের শেখায় কীভাবে নিস্তব্ধতার মধ্যেও শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়, কীভাবে নিঃসঙ্গতার মধ্যেও সৌন্দর্য আবিষ্কার করা যায়।
জীবনানন্দ দাশের কবিতা নিয়ে সমসাময়িক সাহিত্যিকরা অনেকটাই দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। কবি বুদ্ধদেব বসু প্রথমদিকে তার কবিতাকে দুর্বোধ্য মনে করলেও পরবর্তীতে স্বীকার করেন—‘জীবনানন্দ দাশই আধুনিক বাংলা কবিতার প্রকৃত প্রবর্তক।’ আবার কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, ‘তার কাব্য যেন নিঃশব্দ কোনো জ্যোতিষ্ক, যা ধীরে ধীরে নিজের আলোয় আলোকিত হয়।’
আসলে জীবনানন্দের কবিতা তাৎক্ষণিকভাবে হৃদয়গ্রাহী না হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনের গভীরে প্রবেশ করে। তার কবিতার সৌন্দর্য এক আত্মিক স্তরে অনুভব করতে হয়। যদিও জীবনানন্দ দাশ মূলত কবি হিসেবেই পরিচিত। তবে গদ্য সাহিত্যেও তিনি ছিলেন দক্ষ। তার রচনায় রয়েছে উপন্যাস (মাল্যবান এবং সতীর্থ), ছোটগল্প ও অসংখ্য প্রবন্ধ।
উপন্যাসগুলোয় জীবনানন্দ দাশ যেমন সমাজবাস্তবতার একটি করুণ চিত্র আঁকেন, তেমনই চরিত্রগুলোর মনোজাগতিক টানাপোড়েন তুলে ধরেন নিপুণভাবে। বিশেষ করে ‘মাল্যবান’ উপন্যাসে যে নিস্তব্ধ, নির্ঘুম, আত্মজিজ্ঞাসাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা বাংলা গদ্য সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন।
জীবনানন্দের কবিতায় নারী কখনো প্রকৃতির মতো কোমল, শান্তিময় আশ্রয়স্থল, আবার কখনও রহস্যময় ও অপ্রাপ্য। বনলতা সেন, সুরঞ্জনা, সুচেতনা, সুধা—এসব নাম যেন কেবল ব্যক্তি নয়, এক একটি বিমূর্ত রূপ, কবির নিঃসঙ্গতার আশ্রয়। তবে এ-ও ঠিক, তিনি নারীর রূপ নয় বরং তার মানবিকতাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তার নারীরা নিছক প্রেমিকা নন, তারা এক একটি দর্শনের প্রতিচ্ছবি।
জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতায় অনন্য ভাষার উদ্ভাবক। তিনি কাব্যভাষায় এনে দেন নীরবতা, যেখানে শব্দের চেয়ে ছায়া, রূপের চেয়ে অনুভব বেশি কার্যকর। তার কবিতায় ব্যবহৃত উপমা ও রূপকগুলো অপ্রচলিত, অথচ চিত্রময়। যেমন- ‘শালিক দেখেছে সন্ধ্যার দিকে তার ছায়া যায় ডুবিয়া/ ধানসিঁড়ির জলে—তারপর হাওয়ায় উড়িয়া গেছে তারা…’। এমন ভাষায় তিনি পাঠককে টেনে নিয়ে যান অনির্বচনীয় আবেশে।
জীবনানন্দ দাশ আজীবন নিঃসঙ্গ থেকেছেন কিন্তু তার কবিতা আমাদের হৃদয়জগতে এক গভীর সঙ্গী হয়ে থাকে। বাংলা কবিতা যতদিন থাকবে; জীবনানন্দ দাশ ততদিন অনিবার্যভাবে আলো ছড়াবেন নিঃশব্দে, নিঃসঙ্গভাবে, ঠিক তার কবিতার মতো।
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ