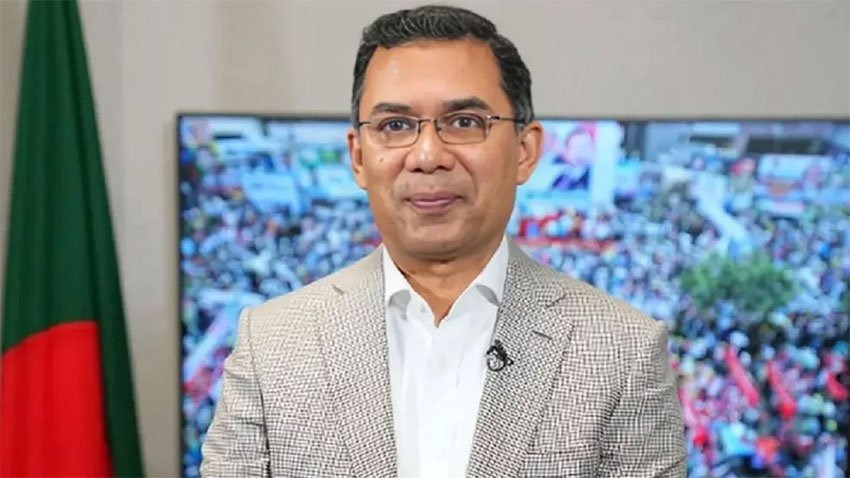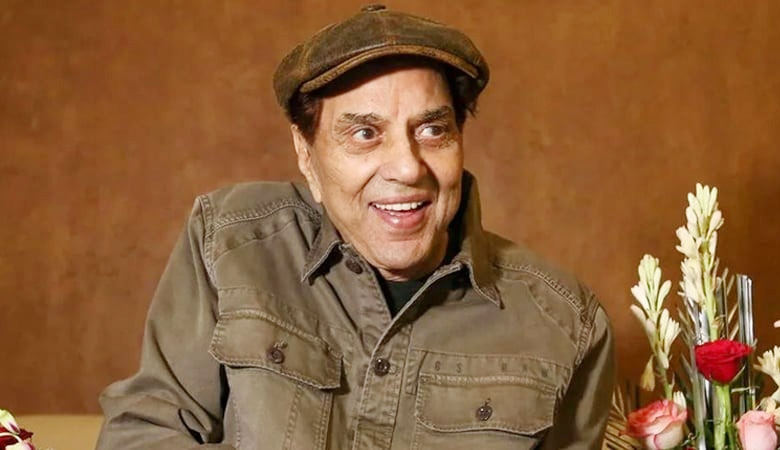আমীন আল রশীদ : পৃথিবীতে নানারকম দিবস আছে। তার মধ্যে কিছু দিবস অদ্ভুত। যেমন– ‘ঘুম দিবস’, ‘ডিম দিবস’, ‘চকলেট দিবস’, ‘জগিং প্যান্ট দিবস’ ইত্যাদি। সেরকমই একটি ‘সাইলেন্ট ডে’ বা ‘নৈঃশব্দ্য দিবস’। এই দিনটি নিঃশব্দে, নিরিবিলি কোথাও কাটানোকে উৎসাহিত করা হয়। অনেকে এই দিনটিকে ‘চুপ থাকা দিবস’ বলেও অভিহিত করেন।
দিনটি নিঃশব্দে উদযাপিত হলো গত ২৫ ফেব্রুয়ারি। ফলে আমাদের আজকের আলোচনা নৈঃশব্দ্য বা চুপ থাকার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে। প্রসঙ্গত, ২৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে আরেকটি কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো ২০০৯ সালের এই দিনে রাজধানীর পিলখানায় তৎকালীন বিডিআর সদর দফতরে ‘বিদ্রোহ’ হয়েছিল, যে ঘটনায় ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন। তবে আমাদের আজকের আলোচনা সেটি নয়। আজকের বিষয় ‘নৈঃশব্দ্য’। দিনটির তাৎপর্য হলো, প্রতিদিনকার ব্যস্ততা আর কোলাহলকে সাময়িক ছুটি দিয়ে নিজের মতো করে নীরবতা উদযাপন। কেননা, নীরবতারও একটা ভাষা আছে। সেই ভাষা মহানগরে, শহরে কিংবা যাপিত জীবনের ব্যস্ততায় উপভোগ করা যায় না। এজন্য চলে যেতে হয় নিরিবিলি কোনও জায়গায়। হতে পারে সমুদ্রের ধারে, বনে-জঙ্গলে কিংবা পাহাড়ে এবং অবশ্যই একা। মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও এভাবে একা একা নিজের সঙ্গে কথা বলা বা বোঝাপড়া তথা নিজেকে জানার জন্য মাঝে মধ্যে ছুটি নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। চুপচাপ থাকার ওপরে তারা গুরুত্ব দেন।
নৈঃশব্দ্য বা চুপচাপ থাকার অন্য আরও অনেক অর্থ আছে। সেই সঙ্গে চুপ থাকার অনেক সুবিধা যেমন আছে, তেমনি অসুবিধাও অনেক। বলা হয়, ‘বোবার কোনও শত্রু নেই’। অর্থাৎ যিনি কথা বলতে পারেন না, তার কোনও শত্রু তৈরি হয় না। যে কারণে বলা হয়, যার জিহ্বা যত সংযত, তার কাছ থেকে মানুষ তত নিরাপদ। অর্থাৎ কম কথা বলা বা চুপ থাকা মানুষেরা তুলনামূলক অন্যের জন্য কম বিপজ্জনক—এটি সাধারণ ধারণা।
কিন্তু সবসময় কি চুপ থাকা যায় বা সব ক্ষেত্রে চুপ থাকাটা কি নাগরিকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে? সমাজে ও রাষ্ট্রে, আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যে অন্যায় ও খারাপ কাজগুলো দেখা যায়, সেসবের ব্যাপারেও কি মানুষ চুপ থাকবে? নাকি প্রতিবাদ করবে। আবার যখন প্রতিবাদের প্রশ্ন ওঠে তখন সেই প্রতিবাদের ভাষা কী হবে—সেটিও বিবেচনায় নিতে হয়। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় থাকা এবং ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য প্রতিবাদের যে ভাষা ব্যবহার করে, একজন সাধারণ মানুষও সেই ভাষায় প্রতিবাদ করবে?
সোশাল মিডিয়ায় অনেক বিষয় নিয়েই মানুষ খুব সোচ্চার হয়। যেমন, নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে মানুষ অনেক কথা লেখে। অর্থাৎ এই ইস্যুতে সবাই কথা বলে। এখানে নৈঃশব্দ্য নেই। একইভাবে সামাজিক অনেক সমস্যা নিয়েও মানুষ কথা বলে। কিন্তু সেই সমাজ ও রাষ্ট্রের আরও অনেক বড় বড় সমস্যা আছে, যেগুলো নিয়ে মানুষ কথা বলে না; বলতে চায় না বা বলতে ভয়। রাষ্ট্রও চায় সেসব ইস্যুতে মানুষ চুপ থাকুক। আবার মানুষ যাতে চুপ থাকে বা চুপ থাকতে বাধ্য হয়, সেজন্য রাষ্ট্র অনেক সময় তার অনেক আইনি কাঠামোও গড়ে তোলে।
পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও সহনশীল রাষ্ট্রের বাইরে স্বৈরতান্ত্রিক এমনকি উঠতি বা আধা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মই হলো সে তার নাগরিকদের কাছ থেকে নিঃশর্ত আনুগত্য প্রত্যাশা করে। রাষ্ট্র চায় তার নাগরিকরা সবকিছু বিনা প্রশ্নে মেনে নেবে এবং কোনও অন্যায় দেখলেও চুপ থাকবে। আর যাতে সে চুপ থাকে সেজন্য বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও গড়ে তোলে। একটা ভয়ের পরিবেশ জারি রাখে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে যারা নিখোঁজ বা গুম হয়েছেন, ফিরে আসার পরে তারা সবাই চুপ হয়ে যান। তারা নিখোঁজের দিনগুলোয় কোথায় ছিলেন, কেমন ছিলেন, কারা তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল—এসব বিষয়ে সাধারণত তারা কথা বলেন না। হয়তো কথা না বলা তথা চুপ থাকার শর্তেই তাদের জীবিত ফেরত দেওয়া হয়। অর্থাৎ তখন ওই ব্যক্তিরা নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থেই হয়তো চুপ থাকেন। তাদের এই নৈঃশব্দ্য বা চুপ থাকার রাজনীতিটা ভিন্ন। অনেক সময় নাগরিকরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে চুপ থাকলে সেটি অপরাধীদের জন্য সুবিধা তৈরি করে। কারণ, অপরাধীরা ধরে নেয়, এটা নিয়ে নাগরিকদের তরফে কোনও প্রতিবাদ তৈরি না হলে তারা রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত লোকদের ‘ম্যানেজ’ করে ফেলবে। এভাবে কোনও একটি অন্যায় শুধু মানুষের নীরবতার কারণে প্রলম্বিত হয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ে নাগরিকরা নীরবতা পালন করলে সেটি অনেক সময় রাষ্ট্রের জন্য আরও বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন, রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা জানতে পারলে হয়তো ওই সমস্যাটির দ্রুত সমাধান করতেন, কিন্তু মানুষের নীরবতার কারণে সমস্যাটি রাষ্ট্রের অগোচরেই বেড়ে উঠতে থাকে এবং একসময় সেটি বিরাট আকার ধারণ করে। মূলত নাগরিকরা ছোটখাটো সমস্যা নিয়েও অনেক সময় চুপ থাকার নীতি অবলম্বন করে। কারণ, ওই ঘটনার সঙ্গে সমাজের প্রভাবশালী কোনও অংশ জড়িত থাকে। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত দেশ তুরস্কের একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন ইউনুস এমরে। নীরবতা নিয়ে তার একটি কবিতার লাইন এরকম: ‘চুপ থাকাই বাকপটুতা, সবাই সেরা; বাচালতা হৃদয়জুড়ে মরচেপড়া।’
তবে বাচালতা নয়; অন্তত যখন যে কথাটি বলা দরকার, সেই কথাটি নাগরিকরা বলতে পারছে কিনা এবং কথা বলা বা সরবতার কারণে তাকে কোনও ধরনের আইনি, সামাজিক, রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কিনা—রাষ্ট্র বোঝার সেটিও একটি তরিকা।
লেখক: কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এডিটর, নেক্সাস টেলিভিশন।