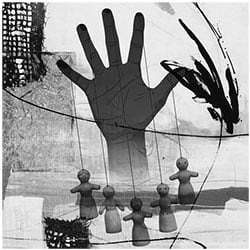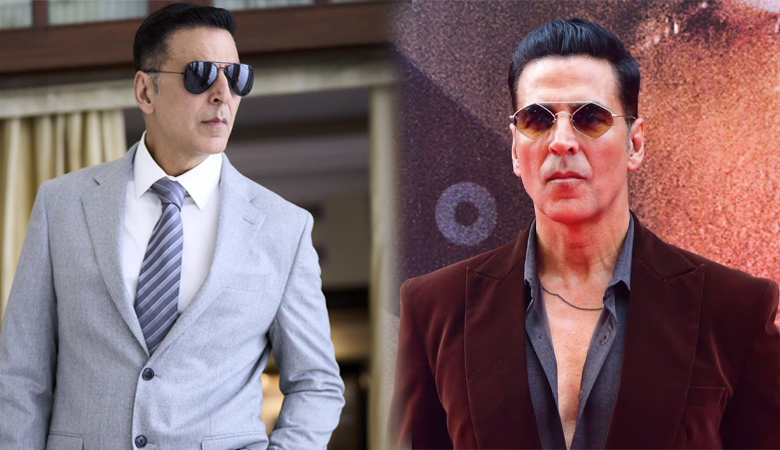হাসান মামুন : নতুন বাজেট দেওয়ার দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেছে। ২ জুন ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করবেন অর্থ উপদেষ্টা। দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে এভাবে বাজেট প্রদানের কোনো বিকল্প নেই। সামরিক শাসনামলে সংসদ অনুপস্থিত থাকাকালে এভাবেই বাজেট দেওয়া হতো। ওয়ান ইলেভেন সরকারের সময়ও পরপর দুটি বাজেট এভাবে ঘোষণা করতে হয়েছিল।
সংসদ থাকলে একটা বাজেট অধিবেশন হতো। তবে এতে ‘প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে আলোচনা’ কতটা হতো, সন্দেহ রয়েছে।
বাজেট অধিবেশনে বাজেট ধরে অর্থবহ আলোচনা এ পর্যন্ত হয়েছে কমই। এ নিয়ে অভিযোগও কম ছিল না। সংসদ সদস্যরা এর থোড়াই কেয়ার করতেন। তাদের সিংহভাগ নিজেদের মতো করেই পার করতেন বাজেট অধিবেশন। সত্যি বলতে, বাজেট নিয়ে আলোচনা হতো সংসদের বাইরে। তারপর কিছু সংশোধনীসহ এটি পাস হতো জুনের শেষে।
এবার গোটা জুন মাস বাজেট নিয়ে আলোচনা কম হবে না। সংসদের অনুপস্থিতিতে, এর বাইরে যেসব আলোচনা হবে, তাতে মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার কম সাড়া দেবে বলেও মনে হয় না। প্রধান উপদেষ্টা একজন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। মানুষের উন্নয়ন ঘিরে তার রয়েছে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা। অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা দু’জন সুযোগ্য অর্থনীতিবিদ। এ টিমকে সহায়তা জোগাতে বিদেশ থেকে ক’জন পেশাদার অর্থনীতিবিদও এসে যুক্ত হয়েছেন। বাজেট প্রণয়নের পাশাপাশি হালে বড় করে আয়োজন করা হয়েছিল বিনিয়োগ সম্মেলনের। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অর্থনীতিতে এক ধরনের স্থবিরতা চলার কথা সরকারও স্বীকার করছে। এ অবস্থায় বিনিয়োগ সম্মেলন আয়োজনের উদ্দেশ্য কার না জানা। যে কোনো অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বিনিয়োগ বাড়ানো অবশ্য বোধগম্য কারণেই কঠিন। তারপরও এ ধরনের উদ্যোগে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হলে সেটা ইতিবাচক বৈকি।
নতুন বাজেটেও সরকারকে বিশেষত বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে স্পষ্ট কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। যে কোনো সরকারের বাজেটেই এটা সাধারণ লক্ষ্য হিসেবে থাকে। সেটি অর্জিত হলে কিছু বাড়তি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তাতে মূল্যস্ফীতির মধ্যেও মানুষের টিকে থাকাটা হতে পারে সহজতর।
অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে সামনে রেখে বাজেট প্রণীত হচ্ছে। জীবনযাত্রা যেন সহজ হয়, বাজেটে সে প্রয়াস তারা নেবেন। কর্মসংস্থান বাড়ানোর পাশাপাশি বছরের পর বছর উচ্চ পর্যায়ে থাকা মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা গেলে বিশেষত নি¤œ আয়ের মানুষের জীবনযাত্রা সহজ হবে বৈকি। জীবনযাত্রা সহজ হলে দেশে একটা স্বস্তি আসবে। জনজীবনে স্বস্তি এলে মানুষ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে সরকারের। গেল রমজানে পণ্যবাজার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্য ছিল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও ছিল কিছুটা নিয়ন্ত্রণে। এ কারণে ঈদের সময়টা ভালো কেটেছে মানুষের। তবে এর সপ্তাহ দুয়েক পর থেকে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে শুরু করেছে। ভোজ্যতেলের দাম নতুন করে বাড়ানোর প্রস্তাবে সরকার যেসব কারণে সম্মত হয়েছে, তার একটি হলো– বেশিদিন রাজস্ব ছাড় দিয়ে রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন। চালের বাড়তে থাকা দামও সরকার কিছুতেই রোধ করতে পারছে না। আমদানি করেও না। এদিকে শীতের পর গ্রীষ্মের সবজির দাম বাড়ছে। মুরগি, ডিমসহ কিছু পণ্যের দাম কমে আসা কিংবা স্থিতিশীল থাকার ঘটনা সেটাকে কতখানি ‘ব্যালান্স’ করবে, সে প্রশ্ন অবশ্য রয়েছে। ঈদ উপলক্ষে রেকর্ড রেমিটেন্স এসেছে; একইসঙ্গে বাজারে অর্থের সরবরাহ বেড়েছে ঈদের সময়টায়। সামনে আরেকটি ঈদ। তখনও একই ঘটনা ঘটবে। এর মধ্যে বাজারে বোরো ধান-চাল চলে এলেও মূল্যস্ফীতি কমবে কিনা, কে জানে। জীবনযাত্রা সহজ করার ক্ষেত্রে সফল বোরো উত্তোলনটাও সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জিং।
এ অবস্থায় ঘোষিত বাজেটে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা কত ধরা হবে, সে বিষয়ে ধারণা পাওয়া গেছে। আগামী অর্থবছর শেষে মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নাকি থাকবে। মূল্যস্ফীতি সহনীয় করে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টার কথাও আমাদের জানা। সব দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটা বড় কাজ মূল্যস্ফীতিকে সিংহভাগ মানুষের জন্য সহনীয় করে রাখা। সেজন্য ব্যবহৃত হয় তার আর্থিক হাতিয়ার। বাংলাদেশ ব্যাংক চেষ্টা করছে ‘সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি’র মাধ্যমে বাজারে অর্থ সরবরাহ কমিয়ে মূল্যস্ফীতি কমাতে। আমাদের মতো দেশে এককভাবে মুদ্রানীতি এ লক্ষ্য অর্জনে কতটা সহায়ক, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজস্বনীতিকেও একই ধারায় পরিচালনার ওপর জোর দেওয়া হয়। বাজেটে সরকার একটা বড় সুযোগ পায় রাজস্বনীতিকে তার লক্ষ্য অর্জনে নতুনভাবে প্রয়োগের। সরকার তার ব্যয় নির্বাহে কতটা অর্থ রাজস্ব খাত থেকে আহরণ করবে, তার বর্ণনাই বেশি থাকে বাজেটে। এবারও সেটাই থাকবে। প্রয়োজনের পুরোটা অর্থ রাজস্ব খাত থেকে তোলা যাচ্ছে না বলে আমাদের সব বাজেটই কিন্তু ঘাটতি বাজেট। ঘাটতি নিয়ে তাই প্রশ্ন নেই; প্রশ্ন ঘাটতির পরিমাণ নিয়ে। পরিমাণটা এবারও বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা এজন্য যে, রাজস্ব আহরণে অসাফল্য যেন এক চলমান প্রক্রিয়া। এদিকে আইএমএফের ঋণের কিস্তি আটকে আছে রাজস্ব আহরণ শর্ত অনুযায়ী না বাড়ায়। চলতি অর্থবছরের মধ্যভাগে সরকার শতাধিক পণ্যে একযোগে ভ্যাট বাড়ানোর মতো কা- করেছিল অনেকটা এ বাধ্যবাধকতাতেই। ওই পদক্ষেপ থেকে আবার তাকে কিছুটা সরে আসতে হয় মূল্যস্ফীতিতে ঘৃতাহুতি পড়ার যুক্তিতে। এমন গ্যাঁড়াকলে নতুন বাজেটে জীবনযাত্রা সহজ করার কাজটা সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না।
অন্তর্বর্তী সরকার বাজেটের আকার অযৌক্তিকভাবে বাড়াবে না, এটা বলে এসেছে। চলতি বছরের মূল বাজেটের চেয়েও এর আকার কিছুটা ছোট হবে বলে জানা যাচ্ছে। চলতি বাজেটের অনেকখানি আবার থেকে যাবে অবাস্তবায়িত। আমাদের বাজেট বাস্তবায়নের হার অসন্তোষজনক এবং এটা বৃদ্ধির প্রবণতায় রয়েছে। এক্ষেত্রে আবার বেশি অবাস্তবায়িত থাকছে উন্নয়ন বাজেট (এডিপি)। রাজস্ব বাজেটের তুলনায় এডিপি ছোট হচ্ছে আরও এবং সেটাও বেশি করে থাকছে অবাস্তবায়িত। মার্চ শেষে এডিপি বাস্তবায়নের যে হার (প্রায় ৩৭ শতাংশ) দেখা যাচ্ছে, তা গত পাঁচ বছরে সর্বনি¤œ। এডিপির বড় কাটছাঁটের পরও বাস্তবায়নের এ অবস্থা এককথায় উদ্বেগজনক। এজন্য অবশ্য অন্তর্বর্তী সরকারকে বেশি দায়ী করা যাবে না। দায়ী সার্বিক পরিস্থিতি।
চলতি অর্থবছর শুরু হতে না হতেই রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থানে পতন ঘটে হাসিনা সরকারের। নতুন সরকারের আট মাস অতিবাহিত হলেও পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। এর মধ্যে আবার গেছে প্রবল বর্ষাকাল। শীতেও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ছিল ধীর। বেশ কিছু প্রকল্পের পরিচালক ও ঠিকাদার লাপাত্তা। অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, কম প্রয়োজনীয় প্রকল্পে অর্থ ছাড় বন্ধও করে দেওয়া হয়। সরকার গ্রহণ করে সাশ্রয়ী নীতি। এটা পরিচালন ব্যয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। তার সুযোগও বোধকরি ছিল না। নানান দাবি-দাওয়া পরিপূরণে পরিচালন ব্যয় বেড়েছে। বকেয়া দায়দেনা, ভর্তুকি, প্রণোদনা বাড়াতে হয়েছে বরং। এ কারণেও উন্নয়ন ব্যয় বেশি করে কাটছাঁট এবং প্রকল্পে অর্থ ছাড় হ্রাসের ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা। এতে আবার প্রকল্পে পণ্যসামগ্রী সরবরাহকারীদের ব্যবসা কমেছে; ওইসব ক্ষেত্রে কমেছে কর্মসংস্থান। অর্থনীতি এ কারণেও কিছুটা স্থবির হয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, প্রকল্প বাস্তবায়ন খুবই কম হওয়ায় বেসরকারি খাতের বিকাশে যে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারতো, তা থেকে বঞ্চিত থাকতে হলো। এখন অর্থবছরের বাকি সময়ে এডিপির কতটা বাস্তবায়ন হয়, সেটি দেখার অপেক্ষা। তবে আশা, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে শেষ সময়ের তড়িঘড়ি বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় অন্তত আগেকার মতো করে হবে না।
এমন অভিজ্ঞতার নিরিখেই সম্ভবত নতুন বাজেটে গেলবারের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ছোট এডিপি নেওয়া হবে। দলীয় রাজনৈতিক সরকারের মতো বড় এডিপি নিয়ে ‘উন্নয়নের’ পক্ষে দৃঢ় অবস্থান দেখানোর আবশ্যকতাও নেই অন্তর্বর্তী সরকারের। তবে ছোট এডিপি নিলেও তারা পারেন সেটা সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করে ‘ফুটপ্রিন্ট’ রেখে যেতে। রাজনৈতিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে কী ধরনের প্রকল্প নেওয়া অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক, সেটা তারা করে দেখাতে পারেন নতুন বাজেটে। বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলনে এবং তার পরেও বিভিন্ন ফোরামে তারা সেটা বর্ণনার অবকাশ পাবেন। এডিপি কাটছাঁটের সময় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত বেশি অর্থবঞ্চিত হয়েছিল। এবার এসব খাতে কী ধরনের প্রকল্প গৃহীত হয়, সেদিকেও সবার নজর থাকবে। মানবসম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে এ দুই খাতের সম্পর্ক তো নিবিড়। অন্যান্য খাতেও রাষ্ট্রীয় অর্থের সদ্ব্যবহার অর্থনৈতিক কর্মকা- কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবে। বিনিয়োগ আর ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ উন্নত করতেও এর ভূমিকা কম নয়।
‘অধিকতর সংস্কার’ করে নির্বাচনে গেলে অন্তর্বর্তী সরকার আগামী অর্থবছরের পুরোটা জুড়েই থাকার কথা। ততদিন না হলেও শীত শেষ হওয়া (অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ) পর্যন্ত সরকার থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। এ অবস্থায় এমন বাজেট দিতে হবে, যার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন তার পক্ষে সম্ভব। পরিচালন ব্যয়ের ক্ষেত্রেও সাশ্রয়ী হয়ে দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারে সরকার। সেক্ষেত্রে তাকে ‘ঘাটতি অর্থায়ন’ করতে হবে কিছুটা কম। উন্নয়ন সহযোগীরা এ সরকারকে উদারভাবে ঋণ-সহায়তা জুগিয়ে যাবে, এমন আশাবাদ কিন্তু সত্য হয়নি। আইএমএফ বেঁকে বসলে এ ধারার অন্যান্য সংস্থাও ঋণ জোগাতে বেশি উৎসাহী হবে না। সরকার তখন দেশীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণে বেশি উদ্যোগী হবে। তাতে মার খাবে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুসৃত মুদ্রানীতি। বেসরকারি খাত তখন চাহিদামতো ঋণ পাবে না। এ অবস্থায় মূল্যস্ফীতি না কমার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধিও মার খেতে পারে। চলতি অর্থবছরে ভালো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে না, এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যাচ্ছে। আগামী অর্থবছরে এটা কিছুটা হলেও বাড়াতে হবে, সে দাবি কিন্তু থাকছে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে। প্রবৃদ্ধি যেন কিছুটা ‘ইনক্লুসিভ’ বা অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়, সে ফুটপ্রিন্ট রেখে যাওয়াটাও গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীকালে জরুরি।
লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট