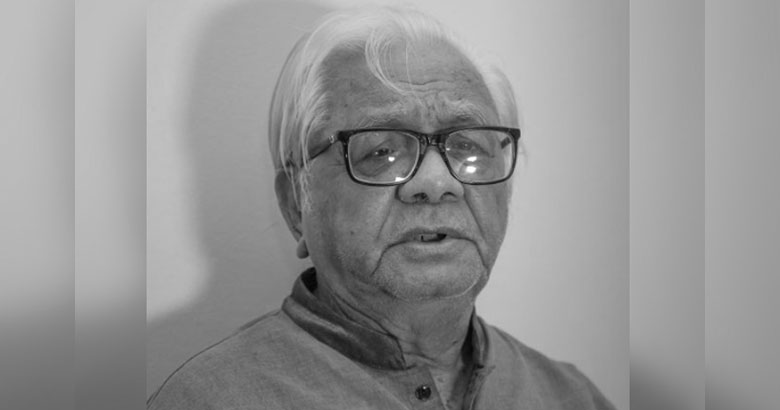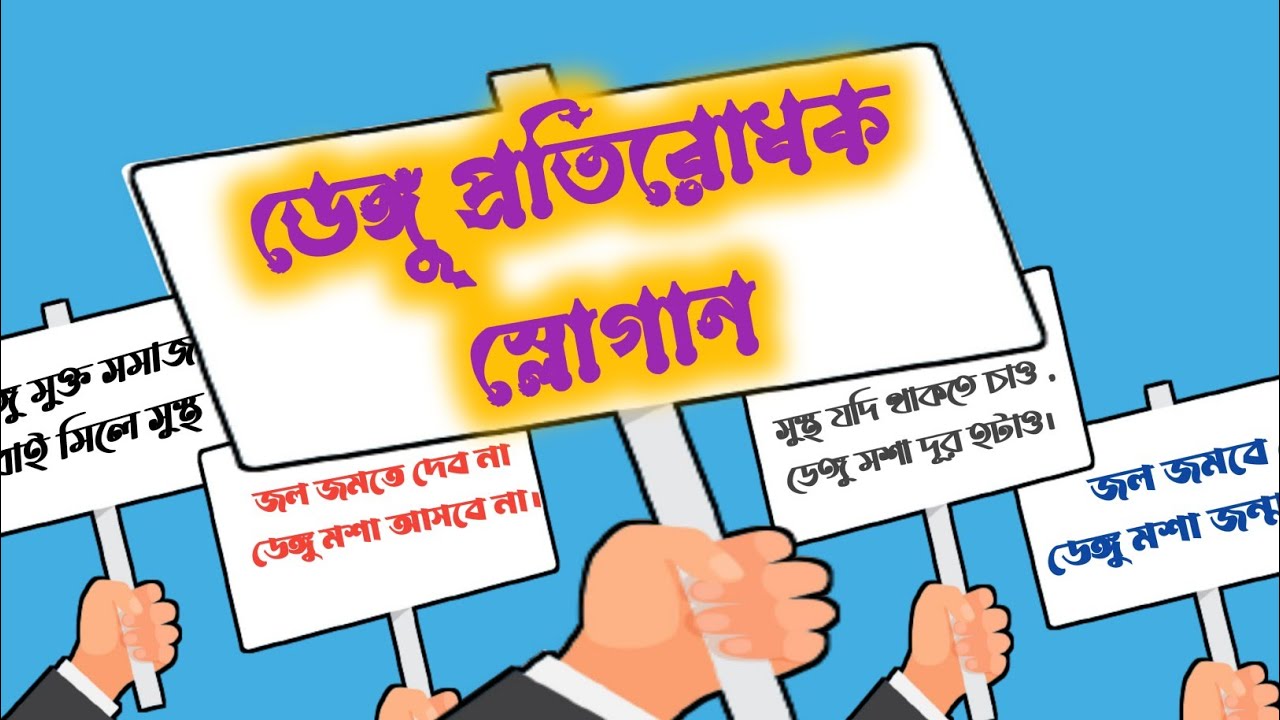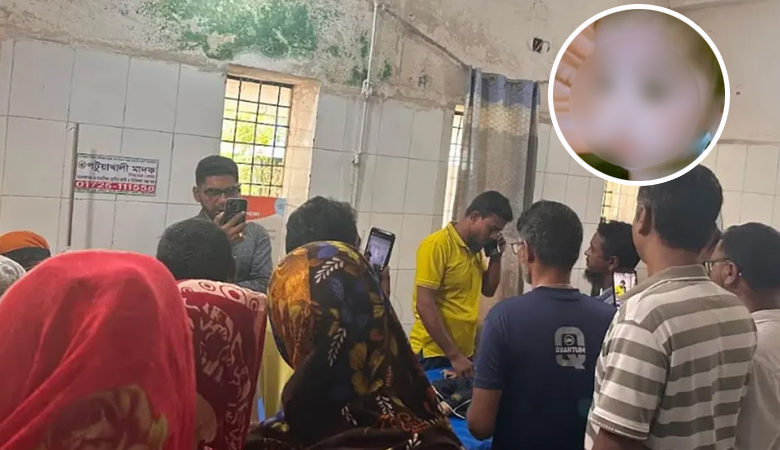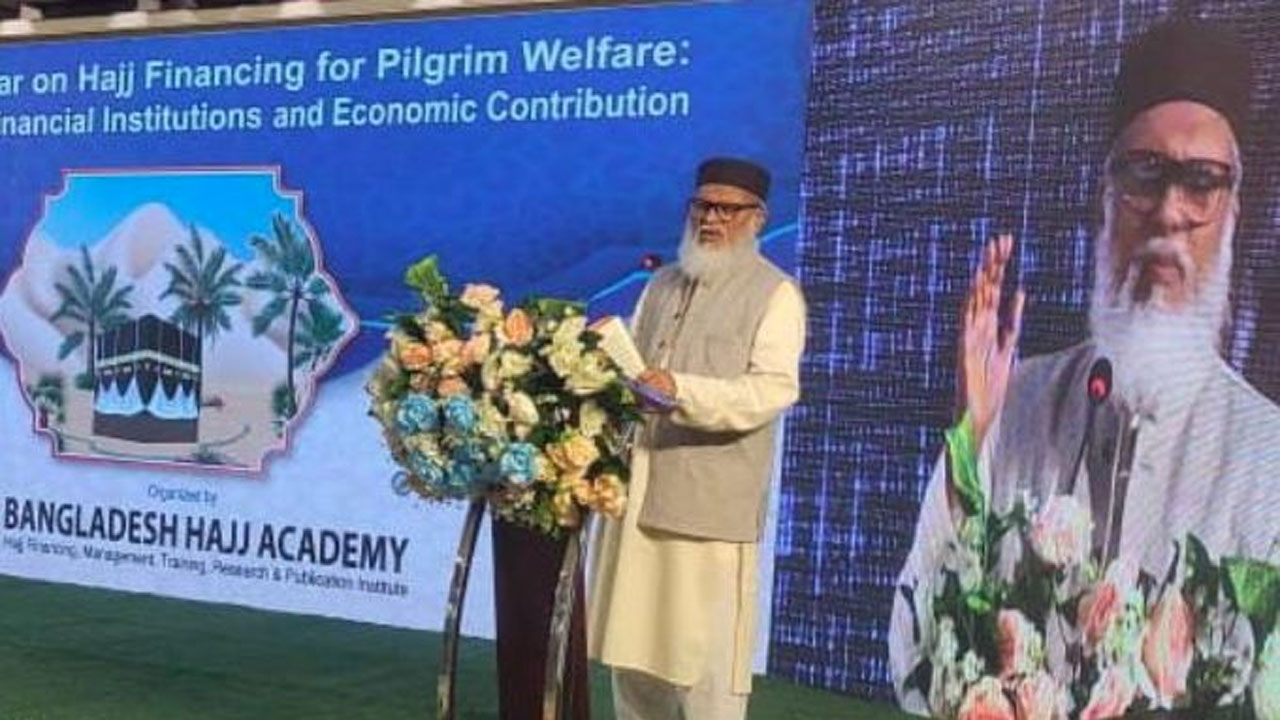ড. শায়খ আহমদ
১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাত কোটি। ২০২৫ সালে জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আঠারো কোটির কাছাকাছি। জনসংখ্যা অর্ধেকের কম থাকা সত্ত্বেও এ দেশ ১৯৭৪ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সাক্ষী হয়েছিল। খাদ্যাভাবে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অর্ধাহারে-অনাহারে দিনপাত করেছে লাখ লাখ মানুষ। বিগত অর্ধশতাব্দীর অল্প একটু বেশি সময়ে এ দেশের জনসংখ্যা আড়াই গুণ বেড়েছে। কিন্তু জনসংখ্যার বিশাল প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বিগত পঞ্চাশ বছরে আর দুর্ভিক্ষ হয়নি। বরং দৈনিক মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ১৯৭২ সালে ১৮৪০ কিলোক্যালরি থেকে ২০২৫ সালে ২৪০০ কিলোক্যালরিতে উন্নীত হয়েছে। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধির মাধ্যমে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের তথ্য অনুসারে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে বার্ষিক ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় এক কোটি টন, ২০২৪ সালে এসে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় তিন কোটি ষাট লাখ টন। দেশের প্রধান খাবার হিসেবে ভাতের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের তৃতীয় অবস্থান ধরে রাখার মূল কৃতিত্ব এ দেশের নিবেদিতপ্রাণ কৃষি গবেষক ও কৃষকদের।
বন্যা, খরা, ভূপৃষ্ঠের পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে কৃষকরা দেশের মানুষকে তিন বেলা আহার জুগিয়ে চলেছেন। কেবল ধান নয় বরং গম, ভুট্টা, তেলবীজ, ডাল, আলু, শাকসবজি, মসলা, ফলমূল, ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, বনৌষধি, পাট, তামাক, আখ, তুলা ও ফুল উৎপাদনে বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষিবিদরা বিগত পঞ্চাশ বছরে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন। বছরে দুই-তিনবার চাষাবাদ উপযোগী উন্নত বীজ উদ্ভাবন, সেচ, সার, কীটনাশক, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং পশু-পাখি-মৎস্য খাদ্য ও ভ্যাকসিন উদ্ভাবন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। একসময়ের পাট, আখ ও তামাকনির্ভর কৃষি শিল্প এখন বহুমুখী কৃষি শিল্পের অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কৃষিতে প্রভূত উন্নয়ন সত্ত্বেও বিশাল সম্ভাবনার অনেকটাই এখনো কাজে লাগানো বাকি রয়েছে। এদিকে কৃষি খাতের সম্ভাবনার পাশাপাশি কিছু কিছু আশঙ্কা ও চ্যালেঞ্জ সামনে উঠে আসছে। এ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় আমাদের পতিত জমি ব্যবহার, মানসিকতার পরিবর্তন, কৃষিতে উদ্যোগ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কৃষিবিমা সহজীকরণ ও ব্যাপক প্রসার, টেকসই দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার, ব্যাপক ভিত্তিতে কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও হিমাগার স্থাপন এবং উৎপাদন ও খুচরা মূল্যের পার্থক্য কমিয়ে আনা এখন সময়ের দাবি।
জনসংখ্যা দ্রুত প্রবৃদ্ধির কারণে ভৌত অবকাঠামো তথা বাড়িঘর, বাজার-হাট, অফিস-আদালত, শহর-নগর, সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণে কৃষিজমির পরিমাণ দ্রুত সংকুচিত হয়ে আসছে। বিশ্বখ্যাত পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান ম্যাক্রোট্রেন্ডসের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে ৯৪ লাখ হেক্টর আবাদযোগ্য কৃষিজমি ছিল; যা ২০২০ সাল নাগাদ ৮০ লাখ হেক্টরে নেমে এসেছে। মাত্র ত্রিশ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ ১৪ লাখ আবাদি জমি হারিয়েছে। একই সময়ে আবাদি জমির পরিমাণ দেশের মোট ভূমির ৭২ দশমিক ৬৪ শতাংশ থেকে কমে ৬১ দশমিক ৪৬ শতাংশে দাঁড়ায়। বর্ধিত জনসংখ্যা ও নগরায়ণের ফলে আবাদযোগ্য জমি হ্রাস অব্যাহত রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আবাদি জমি হ্রাসের পাশাপাশি আরেকটি উপাত্ত সামনের দিনগুলোয় এক ভয়াবহ আশঙ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কৃষি পরিসংখ্যান ২০২৩ থেকে জানা যায়, দেশে ২০১৯-২০ অর্থবছরে আবাদযোগ্য কিন্তু পতিত জমির পরিমাণ ছিল ৪ দশমিক ৩১ লাখ হেক্টর, যেটি যথাক্রমে ২০২০-২১ সালে বেড়ে ৪ দশমিক ৫২ লাখ হেক্টর এবং ২০২১-২২ সালে ৪ দশমিক ৮৮ লাখ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। এতে বোঝা যায় বাংলাদেশ ক্রমহ্রাসমান আবাদযোগ্য জমির ৬ শতাংশ জমিতে কোনো চাষাবাদ করছে না, প্রতি বছর পতিত জমির পরিমাণ বাড়ছে। আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে চরম খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে, এতে খাদ্যনিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়ে যাবে। বিকল্প হিসেবে খাদ্য আমদানি করতে গেলে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে বিশাল চাপ পড়বে, যেটি অবশ্যই শুভ পূর্বাভাস নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ বাড়ছে?
আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ বাড়ার কারণ হলো প্রান্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে কৃষি এখন আর লাভজনক পেশা নয়। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান স্ট্যাটিস্টার প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১২ সালে বাংলাদেশে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণের হার ছিল যথাক্রমে ৪৫ দশমিক ৯, ১৯ দশমিক ৬২ ও ৩৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ। দশ বছরের মধ্যে এ হারের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ২০২২ সাল নাগাদ কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণের হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৬ দশমিক ৮৬, ২১ দশমিক ৮৮ ও ৪১ দশমিক ২৬ শতাংশ। অর্থাৎ কৃষি খাত থেকে ৯ শতাংশ শ্রমজীবী শিল্প ও সেবা খাতে পেশা স্থানান্তর করেছে। কৃষি থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে স্থানান্তরের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করা গেল না। তবে উল্লেখিত উপাত্ত থেকে এটি নিশ্চিতভাবে বলা চলে কৃষির চেয়ে অন্যান্য পেশা আর্থিকভাবে লাভজনক বলেই এ স্থানান্তর ঘটেছে। আর্থিক দিক ছাড়াও কৃষি থেকে পেশা স্থানান্তরে পরিবেশগত ও সামাজিক কারণ রয়েছে। নদীভাঙন, দীর্ঘ খরা, অকালবন্যার কারণেও অনেকে কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য পেশা বা শহর-নগরে অভিবাসনে বাধ্য হয়েছেন এমন তথ্য রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের হাত নেই, পরিবেশগত কারণে পেশা পরিবর্তনে শ্রমজীবী মানুষ বাধ্য হয়েছেন এটা মেনে নিতেই হবে। কিন্তু শত শত বছর ধরে সামাজিক কারণে কৃষি থেকে পেশা স্থানান্তর অত্যন্ত পরিতাপের।
কৃষকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে খাদ্য উৎপাদন করে মানুষের জীবন বাঁচান। অথচ সামাজিকভাবে আমরা কৃষকদের অত্যন্ত অবমাননার চোখে দেখি। অনেকের চোখে কৃষক একজন অসভ্য, অশিক্ষিত ও হতদরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের প্রতিচ্ছবি। যে পেশার মানুষদের শ্রমে আমাদের খাদ্যের জোগাড় হয়, সে পেশাকে অনেকেই গালি হিসেবেও ব্যবহার করেন। এ সামাজিক বঞ্চনা, অবহেলা ও অনাদরের কারণে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী কৃষিকাজ করতে লজ্জাবোধ করেন। অনেক শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত অহমিকা জন্মে যে পড়ালেখা করে কৃষিকাজ করা যায় না। আবার শিক্ষিত তরুণদের যারা কৃষিকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে চান পরিবার ও সমাজ তাদের নিরুৎসাহিত করে, কটু কথা শোনায়। এ জন্য কৃষক তার শিক্ষিত সন্তানদের কৃষিকাজে নিয়োজিত করতে চান না। সামাজিক কারণেও কৃষিজীবীর সংখ্যা কমছে, আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ বাড়ছে।
কৃষি শ্রমিকের সংকট এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। বাংলা, ইংরেজি ও মাদ্রসা শিক্ষার মাধ্যমে কৃষি এবং কৃষকদের অবদান পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। শিশুকাল থেকেই শিক্ষার্থীদের কৃষিমুখী করার জন্য তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কৃষি শিক্ষাকে একটি বাধ্যতামূলক বিষয় করতে হবে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী যেন কৃষিকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে উৎসাহিত হয়; এ জন্য মাধ্যমিকে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগের পাশাপাশি কৃষি এবং গার্হস্থ্যবিদ্যার দুটি স্বতন্ত্র কর্মমুখী বিভাগ পুনরায় চালু করা যেতে পারে।
কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষি ঋণের পরিমাণ খুব নগণ্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের সব তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে বেসরকারি খাতে ১৫ দশমিক ৬৬ লাখ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করে। এর মধ্যে কৃষি খাতে সম্মিলিত ঋণ প্রদানের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৭ দশমিক ১৫ হাজার কোটি টাকা, যা মোট বেসরকারি ঋণের মাত্র ২ দশমিক ৩৭ শতাংশ। কৃষি ঋণের আবার একটি বৃহৎ অংশই করপোরেট ও মাঝারি আকারের খামারিদের প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে। এদিকে ঝুঁকিপূর্ণ ও ঋণ আদায়ে ফসল ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় বলে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী এনজিওগুলোও কৃষি ঋণ বিশেষ করে শস্য ঋণ প্রদানে উৎসাহী হয় না। ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকেরা এখনো উচ্চসুদে শস্য ঋণের জন্য গ্রামীণ মহাজনদের ওপর নির্ভরশীল। এদিকে একশ্রেণীর ফড়িয়া উৎপাদনের আগেই অগ্রিম প্রদান করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছ থেকে কম মূল্যে ফসল কেনার চুক্তি করে রাখে।
বাজারে দাম বাড়লে ফড়িয়া লাভবান হয়, কৃষক হয় না। এতে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারিরা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হতে পারেন না। ফলে শস্য উৎপাদনে অনাগ্রহের কারণেও আবাদি পতিত জমির পরিমাণ বাড়ছে। এ দুরবস্থা থেকে বের হতে হলে প্রচলিত ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে কৃষি ঋণের পরিমাণ মোট বেসরকারি ঋণের ন্যূনতম ১০ শতাংশ করতে হবে। শস্য ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ফসল উৎপাদনের সময় থেকে ছয় মাস দিতে হবে যেন কৃষক দাম বাড়ার জন্য এক-দুই মাস অপেক্ষা করে লাভবান হতে পারেন। কৃষি ঋণ আদায়ে ঝুঁকি কমানোর জন্য কৃষি বিমার ব্যাপক প্রসার করতে হবে। ঋণ প্রদানকারী পক্ষ সুদের সঙ্গে বিমার প্রিমিয়াম কৃষক থেকে আদায় করবে এবং কৃষক সংগত কারণে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে পাওনাদার প্রতিষ্ঠান বিমা কোম্পানি থেকে সুদসহ ঋণের অর্থ আদায় করে নিতে পারবে। কৃষি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, কৃষি বিমার প্রসার, ঝুঁকি হ্রাস এবং ঋণ আদায়ের সময়সীমা বাড়ানো হলে মহাজন এবং ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্য অনেকাংশে কমে আসবে এবং ফসলের উচ্চমূল্য পাওয়ার কারণে কৃষক সরাসরি লাভবান হবেন।
কৃষিতে আধুনিকায়নের নামে বিদেশ থেকে বিভিন্ন প্রযুক্তি আমদানি করা হয়। এতে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়সহ দেশের পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এ জন্য বাংলাদেশের মাটির গড়ন, আবহাওয়া, জীববৈচিত্র্য, কৃষকের মনন ও দক্ষতা উপযোগী দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কৃষি বিজ্ঞানীদের নিয়োজিত করে গবেষণা খাতে বার্ষিক বরাদ্দ বাড়াতে হবে। মাটির উর্বরতা বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে জৈব সার ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে। কম্পোস্টসহ প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপায়ে জৈব সার উৎপাদনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার গড়ে তোলা যেতে পারে। এদিকে কচুরিপানা, অন্যান্য বর্জ্য এবং দেশীয় উৎস ব্যবহার করে পশু ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। রাসায়নিক কীটনাশকের পরিবর্তে চায়না ও থাইল্যান্ডের মডেল অনুসরণ করে হাঁস ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিকর কীট দমন করা যায়। এসব প্রাকৃতিক ও দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
সেচ, জমি চাষ, ফসল কাটা, মাড়াই, বরফকল, চালকল, স’মিল, তেলকল, হ্যাচারি, ইনকিউবেটর, মাছ আহরণের ট্রলার এবং খাদ্য পরিবহনে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং সেসব যন্ত্রাংশ মেরামতে কারিগরি ডিপ্লোমাদের সহজ শর্তে এসএমই ঋণ প্রদান করে কৃষি সেবা তথা গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি করা সম্ভব। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা এসব উন্নতমানের কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়ায় ব্যবহার করে তাদের উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হবেন। তা ছাড়া স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি গ্রামে যদি ছোট আকারের পাকা গুদাম ঘর ও হিমাগার স্থাপন করা সম্ভব হয়, তাহলে কৃষকরা ভাড়ার বিনিময়ে সেখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফসল সংরক্ষণ করতে পারবেন। বাজারে ফসলের দাম বাড়লে সেটি বিক্রি করে কৃষকরা সরাসরি লাভবান হয়ে তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারবেন। কৃষি ঋণ ও কৃষি বিমার প্রসার গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করবে। কৃষি পরিসেবাগুলো কৃষক, খামারি ও জেলেদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করলে উৎপাদনকারী থেকে মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে খুচরা ব্যবসায়ী পর্যন্ত মূল্যের তারতম্যে একটা ভারসাম্য চলে আসবে। এতে কৃষক ও ভোক্তা উভয়ই উপকৃত হবেন।
বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছর কর্মবাজারে লাখ লাখ কর্মশক্তি যোগ হচ্ছে। এ বিশাল জনশক্তিকে চাকরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান দেয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে একমাত্র কৃষিই হতে পারে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির এক বিশাল কর্মক্ষেত্র। বর্ধিত জনসংখ্যার মৌলিক খাদ্য চাহিদা পূরণে এ জনশক্তিকেই ব্যবহার করা সম্ভব। আবাদযোগ্য প্রতি ইঞ্চি ভূমি ব্যবহার করে খাদ্যশস্য, ফলমূল, শাকসবজি, মাছ, মাংস, দুধ, ডিমসহ সব খাদ্যপণ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারলে আমরা আমদানিনির্ভরতা থেকে রফতানি বহুমুখীকরণের দিকে এগিয়ে যাব। বঙ্গোপসাগরের নীল জলের অতলে ছড়িয়ে থাকা সামদ্রিক সম্পদ এবং বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড ও দ্বীপপুঞ্জের অবারিত সবুজ ফসলের মাঠ দেশের অর্থনীতি, খাদ্যনিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের অপার সম্ভাবনার ডালি সাজিয়ে বসে আছে। আমাদের এখন প্রয়োজন সঠিক নীতিমালা গ্রহণ করে কাজে নেমে পড়া।
লেখক: সহকারী অধ্যাপক, অ্যাডজাঙ্কট ফ্যাকাল্টি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ