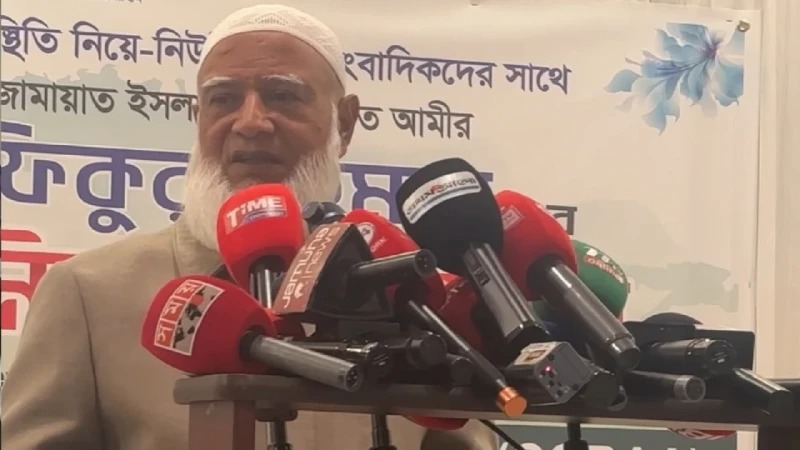ড. মো. আজিজুর রহমান
ওষুধের ভুল ও অযৌক্তিক ব্যবহার কতটা ভয়ানক তা বুঝতে একটি বাস্তব ঘটনা দিয়ে শুরু করা যাক। রাজশাহীর মেহেরুন নাহার (ছদ্মনাম) নামের একজন ৫৫ বছর বয়সের গৃহিণী দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের ওষুধের সঙ্গে প্রায় তিন বছর যাবৎ প্যান্টোপ্রাজল নামক একটি পিপিআই (প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর) ক্লাসের গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাচ্ছিলেন। সম্প্রতি তার প্রস্রাবের সমস্যা দেখা দেয়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বমি বমি ভাব তৈরি হয়। পরে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে তার কিডনির প্রদাহ ধরা পড়ে; যার অন্যতম কারণ দীর্ঘদিন প্যান্টোপ্রাজল ব্যবহার।
সাম্প্রতিক সময়ের বেশ কিছু উচ্চমানের গবেষণা বলছে, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ব্যবহৃত প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর (পিপিআই) শ্রেণির ওষুধগুলো কিডনির প্রদাহ ও ক্রনিক কিডনি ডিজিজ তৈরি করতে পারে। শুধু তাই নয় দীর্ঘমেয়াদে (ছয় মাসের বেশি) এ ওষুধগুলো খেলে অস্টিওপোরেসিস (ঙংঃবড়ঢ়ড়ৎড়ংরং বা হাড় ক্ষয়), ভিটামিন বি১২ এর ঘাটতির কারণে বিভিন্ন সমস্যা (যেমন অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বলতা বোধ করা, বমি বমি ভাব, বমি বা ডায়রিয়া, হাত ও পায়ে অসাড়তা বা কাঁপুনি, জিহ্বায় ব্যথা বা আলসার, রক্তস্বল্পতা ইত্যাদি) তৈরি করে। গ্যাস্ট্রিকের জন্য ব্যবহৃত ওষুধগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে খাওয়া উচিত যেমন এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, চার সপ্তাহ ইত্যাদি। চিকিৎসকরা প্রেসক্রিপশনে ‘চলবে’ লেখার কারণে অনেক রোগী হয়তো ভাবছেন এগুলো খাওয়া বন্ধ করা যাবে না। অনেকে নিজে নিজে এসিডিটির সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন এসব ওষুধ খেয়ে যাচ্ছেন এবং জটিল সব রোগ বাধিয়ে ফেলছেন। শুধু গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ নয়। আমাদের দেশে ভয়াবহভাবে প্রায় সব ওষুধেরই ভুল ব্যবহার ও অযৌক্তিক ব্যবহার হচ্ছে এবং এর সাথে ওষুধজনিত রোগ তৈরি হচ্ছে। ফার্মেসিতে ফার্মাসিস্ট না থাকা ও কাউন্সিলিং প্রথা না থাকার কারণে মানুষ বুঝতে পারছে না ওষুধই সেসব রোগের কারণ। যেমন- কিছু অ্যান্টিবায়োটিক (যেমন- সিপ্রোফ্লক্সাসিন, অ্যাজিথ্রোমাইসিন ইত্যাদি) তীব্র অ্যালার্জি, র্যাশ, ডায়রিয়া তৈরি করতে পারে এবং কিডনি ও লিভারের ক্ষতি করতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক সঠিক ডোজে সঠিক সময় পর্যন্ত না খেলে রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়। ব্যথানাশক ওষুধ পেটের ক্ষত, অন্ত্রে রক্তপাত, কিডনি সমস্যা তৈরি করতে পারে।
স্টেরয়েড (যেমন-ডেক্সামেথাসন, প্রেডনিসোলন) অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে ওজন, রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং হাড় ক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে। স্ট্যাটিন বা লিপিড-লওয়ারিং ড্রাগস যেমন অ্যার্টভাস্টাটিন, রসুভাসটেটিনের কারণে লিভারের সমস্যা দেখা দিতে পারে ও মাংসপেশিতে ব্যথা হতে পারে। এ রকম প্রায় সব ওষুধের হালকা থেকে বেশ জটিল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে। ডাক্তার ও ফার্মাসিস্টের দায়িত্ব হলো রোগীকে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানলে রোগী ভয়ে ওষুধ খেতে চাইবে না এরকম ধারণা করা উচিত নয়। যে কোনো ওষুধের ক্ষেত্রে তার ডোসেজ রেজিমেন অর্থাৎ ওষুধের ডোজ (কতটুকু খেতে হবে বা প্রয়োগ করতে হবে তার পরিমাণ), কত সময় পর পর এবং কতদিন পর্যন্ত রোগীকে দেওয়া হবে; তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো ওষুধের ডোসেজ রেজিমেন নির্ভর করে রোগের প্রকৃতি ও তীব্রতা, রোগীর বয়স, ওজন ও কিডনি/লিভারের অবস্থা, ওষুধের হাফ-লাইফ বা অর্ধ-জীবন, থেরাপিউটিক ইনডেক্স, ওষুধের ফার্মাকোকিনেটিক ও ফার্মাকোডাইনামিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির ওপর। চিকিৎসক ও ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্টগণ উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা নিয়ে এবং আদর্শ চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করে, ওষুধের ডোসেজ রেজিমেন নির্ধারণ করেন। কিন্তু, আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষ ওষুধের ভুল ব্যবহার, অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার ও অতিব্যবহারের ঝুঁকি নিয়ে এতটা অসচেতন যে, মানুষ অহরহ প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ কিনছেন, হাতুড়ে ডাক্তার ও ওষুধের দোকানদাররা ইচ্ছামতো রোগীদের ওষুধ দিচ্ছেন। এ যেন টাকা দিয়ে বিষ খাওয়ার মতো অবস্থা।
আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। এসব জায়গায় আদর্শ চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে তা করা হয় না। এর ফলে প্রতিনিয়ত ঘটছে ভুল ওষুধ প্রয়োগে হাসপাতালে ভর্তি এবং এমনকি মৃত্যুর মতো ঘটনা। এর খুব কমই মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়, যথাযথ তদন্ত হয় এবং শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
ওষুধের অস্বাভাবিক দাম কেন: অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বছরের পর বছর ধরে খাওয়ার ফলে ওষুধজনিত রোগ ও এসব রোগের কারণে মৃত্যু বাড়ছে তা নয়। একই সঙ্গে বাড়ছে খরচ। ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ প্রথম আলোয় প্রকাশিত ‘বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসা ব্যয়ের ৬৪ শতাংশ চলে যায় ওষুধের পেছনে’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশের মানুষের নিজের পকেট থেকে যে খরচ হয়, এর ১০ দশমিক ১ শতাংশ খরচ হয় হাসপাতাল ও ক্লিনিকে, ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ ডাক্তার দেখাতে, ১১ দশমিক ৭ শতাংশ রোগনির্ণয় করতে, শূন্য দশমিক ১ শতাংশ চিকিৎসা সামগ্রীতে এবং ৬৪ দশমিক ৬ শতাংশ ওষুধের পেছনে অর্থাৎ চিকিৎসার জন্য মোট খরচের চারভাগের প্রায় তিনভাগই চলে যায় ওষুধের পেছনে। অনেক পরিবার কিডনি, ডায়াবেটিস, উচ্চ-রক্তচাপ এরকম দীর্ঘস্থায়ী অসুখের চিকিৎসা চালাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছেন। অসংখ্য মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন। গবেষণা বলছে, ওষুধের পেছনে মোট খরচ বৃদ্ধির একটি মূল কারণ ওষুধের অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক ব্যবহার। এর পাশাপাশি পলিফার্মেসি (প্রেসক্রিপশনে একসাথে ৫-৬টি বা তারও বেশি ওষুধ থাকা), জেনেরিক ও কমদামি ওষুধ লিখতে চিকিৎসকদের অনীহা, ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় ওষুধ সরবরাহের ঘাটতি, ওষুধ কোম্পানিগুলোর অসুস্থ প্রতিযোগিতা, স্বাস্থ্যবিমা কাঠামোর অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণও দায়ী। যদিও এটা নিয়ে এখনো দেশে কোনো গবেষণা হয়নি, তবুও আমার ধারণা আমাদের জনগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ওষুধজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছে। কিডনি ও লিভারের জটিলতায় আক্রান্ত রোগীর একটি বড় অংশ ওষুধের অতিরিক্ত ও ভুল ব্যবহারের ফলাফল বলে মনে করি।
২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা বলছে, শুধু আমেরিকায় ভুল ওষুধের কারণে বছরে প্রায় আড়াই লাখ মানুষ মারা যায় এবং এটি মৃত্যুর কারণ হিসেবে তিন নম্বর। যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশে ওষুধের ভুল ব্যবহারের কারণে এত মানুষ মারা গেলে আমাদের দেশে কত হবে, তা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা একটি ওষুধ সংক্রান্ত দুষ্ট চক্রের মধ্যে পড়ে গেছি। এক রোগ সারাতে গিয়ে ভুল ব্যবহার ও অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে আরেকটি রোগ বাধিয়ে ফেলছি। সে রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে আরেক রোগ তৈরি হচ্ছে। অনেকসময় এটা রোগীর মৃত্যুর কারণ হচ্ছে। মনে রাখা দরকার, সব ওষুধই ঠিক ডোজে, ঠিক সময় ধরে খেলে সেটি রোগ সারাতে পারে, কিন্তু এর ব্যবহারে ভুল হলে তা মারাত্মক রকমের বিষ হয়ে শরীরে প্রতিক্রিয়া করে। ওষুধের কারণে সৃষ্ট রোগ থেকে বাঁচতে রোগীদের সচেতন করা, চিকিৎসকদের অপ্রয়োজনীয় ও ভুল ওষুধ প্রেসক্রিপশন বন্ধে প্রেসক্রিপশন অডিটের ব্যবস্থা করা, প্রেসক্রিপশন ছাড়া ‘প্রেসক্রিপশন ওষুধ’ বিক্রি বন্ধ করতে কঠোর হওয়া, হাসপাতাল ও ফার্মেসিতে ফার্মাসিস্ট নিয়োগের মাধ্যমে ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। তাহলে ওষুধের কারণে সৃষ্ট রোগের সংখ্যা কমে আসবে, স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর চাপ কমবে এবং রোগীদের ওষুধের পেছনে খরচও বহুলাংশে কমে যাবে।
লেখক: অধ্যাপক, ফার্মেসি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ