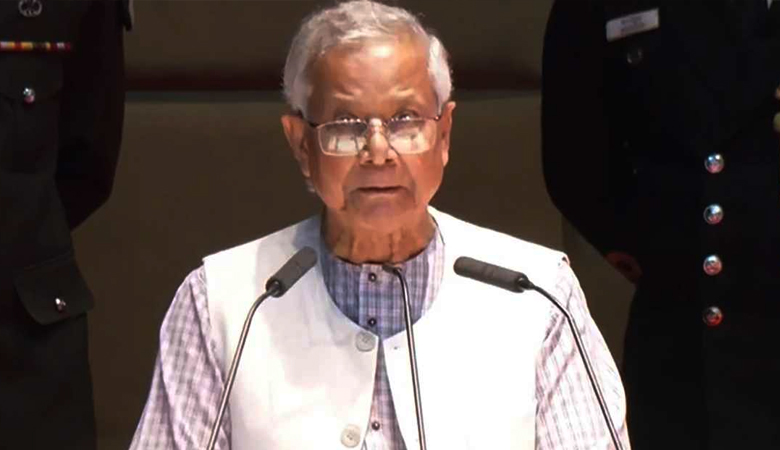সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কিছু ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে, আরও লেখা হবে, লেখার দরকার পড়বে। এই রকমের ঘটনা আমাদের জীবনে আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি, হয়তো আর ঘটবেও না। এর ইতিহাস লেখা দরকার, নিজেদের জানা ও বোঝার জন্য এবং অগ্রগতির পথে পাথেয় সংগ্রহের জন্যও। এক্ষেত্রে কথক কোনো একজন নন, অনেক কজন। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে লেখকদের যে অভিজ্ঞতা, তা ছিল মর্মান্তিক। এ নিয়ে ভুক্তভোগীরা বড়াই করেননি। করুণা আকর্ষণের চেষ্টা করেননি, বেদনার সঙ্গে সেই অতিদুঃসহ দিনগুলো স্মরণে রেখেছেন, যেগুলো তারা ভুলতে পারলে খুশি হতেন, কিন্তু সেগুলো এমনই গভীরভাবে স্মৃতিতে প্রোথিত যে ভুলবার কোনো উপায় নেই। তারা দেখেছেন, জেনেছেন, বুঝেছেন এবং সহ্য করেছেন। তাদের স্মৃতিকথনে অনাড়ম্বর নেই, অতিকথন নেই, আভরণ নেই, বক্তব্য একেবারে সাদামাটা এবং সে জন্যই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।
পাকিস্তানি হানাদাররা যা করেছে, তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু সেটি ঘটেছে। বাস্তবতা ছাড়িয়ে গেছে কল্পনার ধারণক্ষমতাকে। হানাদারদের বংশধরেরাও কল্পনা করতে পারবে না, তাদের পরমাত্মীয় নরাধমেরা কী করেছে। তারা বিস্মিত হবে কেবল বর্বরতা দেখে নয়, মূর্খতা দেখেও। ওই মূর্খরা কী করে ভাবল যে হাজার মাইলের ব্যবধান থেকে উড়ে গিয়ে একটি জনগোষ্ঠীকে তারা অধীনে রাখবে, যাদের সংখ্যা তাদের তুলনায় বেশি এবং দুই অঞ্চলের মাঝখানে তাদেরই শত্রুভাবাপন্ন একটি বিশাল রাষ্ট্র বিদ্যমান। বংশধরদের লজ্জা পাবার কথা।
মূর্খ বর্বররা ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীন ও হতাশাগ্রস্ত। তারা কেবল মারবেই ভেবেছিল। কিন্তু যখন তারা দেখল মার খাচ্ছে, তখন হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে বদ্ধ উন্মাদের মতো আচরণ করেছে। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, সম্ভব-অসম্ভব সবকিছু করেছে। সর্বাধিক বর্বরতা ঘটেছে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে। অন্য কিছুর বিবরণ না দিয়ে কেবল যদি ধর্ষণের কাহিনিগুলো স্মরণ করা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে কেমন অধঃপতিত ছিল এই দুর্বৃত্তরা। মার খাওয়া হানাদাররা ধর্ষণকে তাদের বিনোদন ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিল। জবাবদিহির দায় ছিল না। পালের গোদা শার্দূলবেশী মেষ জেনারেল নিয়াজি থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি হানাদারই ছিল একেকটি ধর্ষণলোলুপ নারকীয় কীট। জবাব দেওয়া দূরের কথা, তারা পরস্পরকে উৎসাহিত করেছে ওই কাজে।
যুদ্ধের দিনগুলোয় নারীরাই ছিলেন সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে। তাদের দুর্ভোগ ছিল সর্বাধিক। একে তারা বাঙালি, তদুপরি নারী। পুরুষেরা অনেকে পালিয়ে যেতে পেরেছেন। প্রাণভয়ে তারা নারীদের ফেলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। যারা যুদ্ধে গেছেন, তাদের বাড়ির নারীরা বিপদে পড়েছেন, অন্তঃসত্ত্বারা সন্তান প্রসব করেছেন বনে-জঙ্গলে। কারণ নারীদের পক্ষে পলায়ন ছিল দুঃসাধ্য। দেহের গঠন, জামাকাপড় ও নারীত্ব- সবই ছিল তাদের বিপক্ষে। সর্বোপরি হানাদাররা ওত পেতে থাকত তাদের অপহরণের জন্য। পুরুষকে তবু কখনো ছেড়ে দিয়েছে, নারীকে ছাড় দিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। নারীরা কেউ কেউ ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা, সে অবস্থাতেই তারা ধর্ষিত হয়েছেন। ধর্ষণের পরে তাদের অনেককে হত্যা করা হয়েছে, অনেকে আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ কোথায় হারিয়ে গেছেন, কেউ জানে না। লজ্জায় অনেকে স্বীকার করেননি যে, তাদের সম্ভ্রমহানি ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীদের এই যন্ত্রণার কথা আসবেই। এসেছেও। সর্বাধিক মর্মন্তুদ কাহিনি পাওয়া যায় বীরাঙ্গনা মমতাজ বেগমের জবানিতে। তার ওপর যে নির্যাতন ঘটেছে, সেটি আমাদের সবার জন্য লজ্জা। অচেতন অবস্থায় তাকে আখখেত থেকে উদ্ধার করে আনা হয়। তার স্বামী জমিজিরাত বিক্রি করে তার চিকিৎসা করান।
মমতাজ বেগমকে বীরাঙ্গনা উপাধি দেওয়া হয়েছিল। নির্যাতিত নারীদের ওই উপাধি যারা দিয়েছিলেন, তারা জানতেন না যে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলো মলিন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের ওই পুরুষমন্য সম্মান প্রদর্শন অসহায় মেয়েদের জন্য দুঃসহ বোঝায় পরিণত হবে। মমতাজ বেগম সে নিয়ে কোনো অভিযোগ করেছেন কি না জানি না। কারণ তার যন্ত্রণাগুলো ছিল অসম্মানের চেয়ে কঠিন। তার দুটি মেয়ে। মেয়েদের তিনি ভালোভাবে বিয়ে দিতে পারেননি। অসত্য নয়, বীরাঙ্গনার মেয়েকে কে বিয়ে করতে চায়? তার শারীরিক ক্ষত সারেনি। তার পক্ষে সম্ভব হয়নি স্বাভাবিক জীবন যাপন করা। দীর্ঘ বছর ধরে এই নির্মম কষ্ট ভোগ করেছেন এবং বীরাঙ্গনা নাম নিয়ে জীবনের শেষ দিনটির প্রহর গুনেছেন। এটাই কি প্রাপ্তি; তার এবং তাদের মতো অসংখ্য নারী; যারা তাদের কথা বলতে পারেননি লোকলজ্জায়।
লাঞ্ছিত নারীদের একটি ধ্বনি আছে, সেটি আর্তনাদের। মুক্তিযুদ্ধকে আমরা নানা বিশেষণে ভূষিত করে থাকি। বলি, এ যুদ্ধ ছিল মহান। তা ছিল বৈকি। অত্যন্ত বড় মাপের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহস ও উদ্ভাবনশক্তির প্রকাশ ঘটেছে যুদ্ধে। সেসবের পরিচয় তো রয়েছে। তবে আর্তনাদ ছিল মস্ত বড় সত্য। প্রাণভয়ে মানুষ পালিয়েছে। আত্মীয়স্বজন, আপনজন, বিষয়সম্পত্তি, সবকিছু ফেলে পালাতে বাধ্য হয়েছে। তবে আর্তনাদের পাশাপাশি নীরব একটা ধিক্কার ধ্বনিও রয়েছে। ধিক্কার শুধু পাকিস্তানিদের নয়, ধিক্কার আমাদের নিজেদেরও। ওরা ছিল অল্প কিছু দস্যু, লাখখানেক হবে সব মিলিয়ে, আমরা ছিলাম সাড়ে সাত কোটি। আমরা কেন এভাবে মার খেলাম ওদের হাতে? হ্যাঁ, ওদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল। কিন্তু তার সুযোগ তো আমরাই করে দিয়েছি। ওদের হাতে বোমারু বিমান পর্যন্ত ছিল। কিন্তু বিমানগুলো তো ছিল আমাদের ভূমিতে। সেগুলোকে বিকল করে দেওয়ার সুযোগ তো আমাদের ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা; আমরা আক্রমণ করতে পারিনি। আমাদের দিক থেকে কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছিল না। যোগাযোগ ছিল না পারস্পরিক। জনমত সৃষ্টি করা হয়নি আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে।
যুদ্ধের প্রস্তুতি যুদ্ধে যাওয়ার আগে নয়, পরে নেওয়া হয়েছে। পলিটিক্যাল মোটিভেশন তৈরির দায়িত্বে ছিলেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, তারা ওই দায়িত্ব আগে পাননি; পেয়েছেন যখন শত্রু তাদের গণহত্যা শুরু করে দিয়েছে, তারপর। গণহত্যা যে শুরু হয়েছে, সে খবরটি পর্যন্ত পাওয়া গেছে বিদেশি রেডিও থেকে এবং তার প্রকোপ টের পাওয়া গেছে হানাদাররা যখন একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, তখন। বস্তুত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মতো প্রস্তুতিহীন, অসংগঠিত ও রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি আধুনিক ইতিহাসে কমই পাওয়া যাবে।
লজ্জা আমাদেরই। কিন্তু সেই লজ্জা ব্যক্তির নয়, সমষ্টির; এবং সমষ্টি যেহেতু চলে নেতৃত্বের পরিচালনায়, লজ্জাটা তাই শেষ বিচারে নেতৃত্বের। একাত্তরে নীরব ধিক্কার ধ্বনিটি ছিল আসলে ওই নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই। প্রধান নেতাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাকিস্তানে, অন্য নেতারা চলে গেছেন ভারতে। অনেকে যুদ্ধ করতে যাননি, গেছেন আশ্রয়ের খোঁজে। এবং সবাইকেই নির্ভর করতে হয়েছে ভারতের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর। শুরুতে আন্দোলন ছিল স্বায়ত্তশাসনের জন্য, পরে দাবি উঠেছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের; তারপরে স্বাধীনতার। এই রূপান্তর নেতৃত্বের পরিকল্পনায় ঘটেনি, ঘটেছে ঘটনাপ্রবাহে। ওই প্রবাহে দুটি বিপরীত স্রোত ছিল। একটি হলো ক্ষমতা হস্তান্তরে পাঞ্জাবি সেনাপতিদের অসম্মতি, অপরটি হলো আপসের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসীর অনড় অবস্থান। দুই স্রোতের সংঘাতে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছিল। যার ভুক্তভোগী হয়েছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রত্যেকে- কোনো না কোনোভাবে। কেউই নিরাপদে ছিল না। মীরজাফরেরা ছিল, ভালোভাবেই ছিল; কিন্তু তারাও যে নিশ্চিত ছিল, তা নয়।
ব্যর্থতা নেতৃত্বেরই। যদি কর্তব্য ও প্রস্তুতির নির্দেশ পাওয়া যেত, তাহলে যুদ্ধের প্রকৃতিা দাঁড়াত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। শুরুতেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত। কারণ হানাদাররা ক্যান্টনমেন্টগুলোতে আটকা পড়ে যেত। তারা ভাতে মরত, পানিতে মরত, মরত অস্ত্রাঘাতেও। কেন্দ্রীয় নির্দেশ ছাড়াও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ ঘটেছে। ঘটেছে প্রতিটি ক্যান্টনমেন্টে এবং প্রস্তুতিহীন অবস্থাতেই প্রাথমিকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙালি সেনারা অবাঙালিদের কোণঠাসা করে ফেলেছিল। সংঘবদ্ধ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেটি ঘটলে হানাদারদের পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়ে যেত অনায়াসে।
লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব)
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ