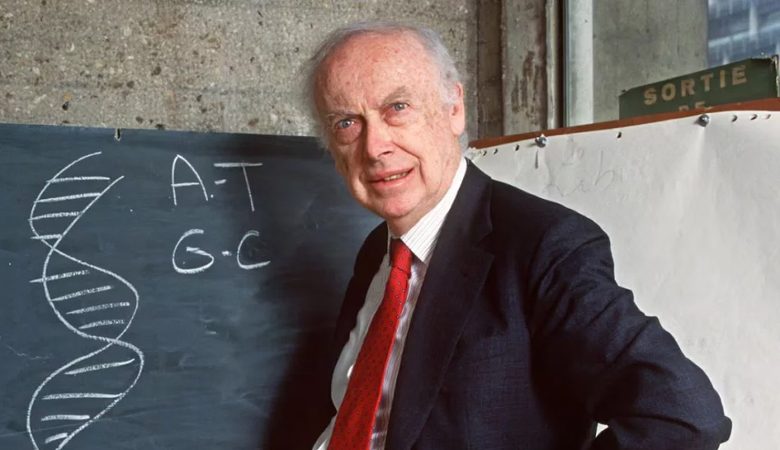আবু তাহের খান : সর্বসম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) অর্থনৈতিক জরিপ ২০২৪-এর প্রাথমিক তথ্য থেকে জানা যায় যে গত ১১ বছরের ব্যবধানে দেশে উৎপাদন (ম্যানুফ্যাকচারিং) শিল্পের সংখ্যা ২৪ শতাংশ কমে গেছে। ২০১৩ সালে দেশের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উৎপাদন শিল্পের সংখ্যা যেখানে ছিল ১১ দশমিক ৫৪ শতাংশ, সেখানে ২০২৪ সালে সে হার এসে দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৭৭ শতাংশে। আর উৎপাদন শিল্পের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া এ জায়গাটি দখল করে নিয়েছে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বিষয়টির অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে দেশে কাঙ্ক্ষিত হারে উৎপাদন শিল্পের বিকাশ ঘটছে না অর্থাৎ এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের গতি ক্রমেই শ্লথ ও নিম্নমুখী হয়ে পড়ছে।
দেশে বর্তমানে একটি শিল্প মন্ত্রণালয় আছে। তদুপরি শিল্পোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য রয়েছে একাধিক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। আর তাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াসে দেশের শিল্প খাত একটু একটু করে হলেও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, সেটাই সাধারণ প্রত্যাশা। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের তথ্যই নিশ্চিত করছে যে এ খাত এগোতে তো পারছেই না, এমনকি এর আগে অর্জিত অবস্থানটুকুও টিকিয়ে রাখতে পারছে না। বরং গত ১৩ বছরে এ খাত তার অর্জিত হিস্যার ২৪ শতাংশই হারিয়ে ফেলেছে এবং চলমান ধারা ও সরকারের বিদ্যমান নীতি অপরিবর্তিত আকারে অব্যাহত থাকলে নিকট ভবিষ্যতের দিনগুলোয় পতনের এ ধারা নিশ্চিতভাবেই আরো বেগবান হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করার কারণ রয়েছে। কিন্তু সরকার তথা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের এ ব্যাপারে কোনো উদ্বেগ বা নিজস্ব কোনো মূল্যায়ন আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। অথচ প্রমাণিত বাস্তবতা যে সরকারের ভ্রান্ত নীতির কারণেই শিল্প খাত ক্রমান্বয়ে এভাবে উদ্বেগজনক হারে পিছিয়ে পড়ছে। তবে এর দায় বহনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর অজুহাত খোঁজার একটি বড় সুযোগ এই যে ভুলটি কেবল কোনো একটি সরকার একা করেনি, স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রতিটি সরকারই তা সমান তালে করে চলেছে। আর এ কাজে তাদের তোষামোদমূলক নিরন্তর সহযোগিতা জুগিয়ে যাচ্ছেন আমলাতন্ত্রের মুৎসুদ্দি সদস্যরা।
১৯৯১ সালের আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রের শিল্পনীতিতে শিল্প বলতে খুব স্বাভাবিকভাবে উৎপাদন শিল্পকেই বোঝানো হতো। কিন্তু ১৯৯১ সালে এসে অনেকটা আকস্মিকভাবেই শিল্পের সংজ্ঞা আমূল পাল্টে ফেলে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডকেও (ট্রেডিং ও অন্যান্য) শিল্পের আওতাভুক্ত করা হয়। সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে শিল্পনীতি ১৯৯১-এর খসড়াটি অত্র লেখক কর্তৃক প্রণয়নের সুযোগ হয়েছিল বিধায় এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, খসড়াটি আসলে প্রণীত হয়েছিল ১৯৯১-পূর্ববর্তী সরকার আমলের শেষ দুই বছরে এবং সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে শুধু উৎপাদন শিল্পকেই শিল্প হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর হঠাৎ করেই সেখানে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আবির্ভাব ঘটে এবং তাদেরই পরামর্শে সরকারের শিল্পনীতিতে সেবা খাতকে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সর্বনাশা যে ঘটনাটি ঘটানো হয় তা হচ্ছে উৎপাদন শিল্প ও সেবা কার্যক্রমকে অভিন্ন হারে ও মাত্রায় রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করা হয়। এখন তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, উৎপাদন শিল্প ও সেবা কার্যক্রম উভয়কেই যদি একই হারে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়, তাহলে ব্যবসা ও মুনাফা সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা রাখেন এমন কোনো ব্যক্তি কি কখনো স্বল্পমেয়াদি সহজ ট্রেডিং ছেড়ে দীর্ঘমেয়াদি জটিল উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইবেন? যে কাজের আওতায় রাতে পণ্য কিনে সকালে বিক্রি করলে সঙ্গে সঙ্গেই নগদ মুনাফা পাওয়া যায়, সে কাজ ছেড়ে কোন উদ্যোক্তা কোন বিবেচনায় ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন? তার পরও যে কিছুসংখ্যক উদ্যোক্তা ঝুঁকি নিয়ে এ কাজে যুক্ত হয়েছেন বা হচ্ছেন, এজন্য তাদের অবশ্যই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। এবং তারা এটুকু করেছেন বলেই তো বিবিএসের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান শুমারিতে উৎপাদন শিল্পের সংখ্যা এখনো ৮ শতাংশের নিচে নেমে যায়নি।
১৯৯১ সালের শিল্পনীতিতে সেবা কার্যক্রমকে শিল্পের আওতাধীন করার কাজটি শুরু হয়েছিল সীমিত পরিসরে। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য ও হতাশার বিষয় এই যে পরবর্তী প্রতিটি সরকার এসে ট্রেডিংকে শিল্প বানানোর সে অপধারায় লাগাম টানা তো দূরের কথা, সেটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং তা নিতে নিতে দেশের প্রায় সব সেবা কার্যক্রম ও ট্রেডিংই এখন শিল্প, ধারণাগতভাবে যা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। কোনো সরকার তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অর্থনৈতিক নীতিমালার আওতায় ট্রেডিং ও সেবা কার্যক্রমকে উৎপাদন শিল্পের অনুরূপ সুবিধাদান করতেই পারেন এবং সে ব্যাপারে তারা স্বতন্ত্র নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সেটি না করে ট্রেডিংকে শিল্পের আওতায় নিয়ে আসা বস্তুত উৎপাদন শিল্পকে হত্যা করারই শামিল এবং সেটাই বস্তুত এখন বাংলাদেশে ঘটছে। আর এর দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল যে আত্মঘাতী হতে বাধ্য, সে ব্যাপারেও কোনোই সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় দেশের শিল্প খাতকে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য উচিত ছিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সর্বাগ্রে এ মর্মে আপত্তি উত্থাপন করা যে শিল্পবহির্ভূত যেসব কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব নীতিগত ও ধারণাগতভাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওপর বর্তায় না, সেগুলোকে যেন কোনোভাবেই শিল্পের বা শিল্পনীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা না হয়। কিন্তু সে আপত্তি উত্থাপিত না হওয়ার কারণেই আজ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান শুমারির ফলাফলে উৎপাদন খাতের সংখ্যা ২৪ শতাংশ কমে যাওয়ার দায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওপর গিয়ে বর্তাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় যতই যুক্তি দিক না কেন যে উৎপাদন শিল্পের হার হ্রাস পেলেও ট্রেডিং বৃদ্ধি পাওয়ার কৃতিত্ব তারা দাবি করতে পারে, যা খুবই খোঁড়া যুক্তি। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মূল কাজ হচ্ছে দেশে উৎপাদন শিল্পের বিকাশ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা—সেবা খাতের দায় তাদের নয়। কিন্তু নিজেদের আসল কাজ ফেলে অন্যের কার কী উপকার হলো সেটি দেখা শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের আওতায় পড়ে না।
শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যেসব আর্থিক ও নীতিগত সহযোগিতা ও সুযোগ-সুবিধার বিধান রাখা হয়েছে, সেগুলো মূলত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে উৎপাদন শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার কথা বিবেচনা করে। কিন্তু সেই একই সুবিধা যখন ঝুঁকিবিহীন ট্রেডিং ও সেবা কার্যক্রমকেও সমান হারে দেয়া হচ্ছে, তখন সেটি রাষ্ট্রীয় সম্পদের চরম অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ জনগণের কষ্টার্জিত করের পয়সায় গড়ে তোলা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সে ধরনের অপচয়মূলক ব্যয় গত সাড়ে পাঁচ দশক ধরেই বিরামহীন গতিতে ঘটে চলেছে, যার পরিমাণ হাজার হাজার কোটি টাকা নয়, লাখ লাখ কোটি টাকা। এই লাখ লাখ কোটি টাকার অপচয় রোধ করা সম্ভব হলে সরকারকে আজ আর বিভিন্ন নিত্যপণ্যের ওপর বর্ধিত হারে ভ্যাট আরোপ করতে হতো না; বরং রাজস্ব উদ্বৃত্ত বাড়ানোর মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেটে বাড়তি অর্থ জোগান দেয়া সম্ভব হতো। কিন্তু শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কোনো রাষ্ট্রীয় দপ্তরই বিষয়টিকে আমলে নেয়নি, বরং এক ধরনের অদৃশ্য আপসরফা ও সমঝোতার মাধ্যমে ট্রেডিং ও সেবা খাতের ব্যবসায়ীদের স্বার্থকেই তারা নিরলসভাবে সুরক্ষা দিয়ে গেছে। আর তার বিপরীতে উৎপাদন শিল্পের ওপর পদে পদে নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও তাদের ওপর নানা ধরনের রাজস্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের অসম প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে।
উৎপাদন শিল্প একটি দীর্ঘমেয়াদি, জটিল ও তুলনামূলকভাবে স্বল্প মুনাফার ও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ কার্যক্রম। ফলে পৃথিবীর সব দেশেই উৎপাদন শিল্পকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অগ্রাধিকারমূলক বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু বিস্ময়ভরা এ বাংলাদেশে। এখানে শিল্পের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা, ট্রেডিং, ফাটকা ব্যবসা কিংবা অন্যান্য সেবামূলক শিল্পের জন্যও তাই। ফলে নতুন কিংবা পুরনো উদ্যোক্তা, সবাই দ্রুত মুনাফার লোভে ট্রেডিংয়ের দিকে ঝুঁকছেন। তবে কেউ যদি এক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের নাম উল্লেখ করে ট্রেডিংকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রমাণিত কৌশল হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন তাহলে কৌশল হিসেবে সেটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ উৎপাদন শিল্প স্থাপন উপযোগী কোনো ভূমিই না থাকা ছোট্ট নগররাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের পক্ষে বন্দর ভাড়াদানের বাইরে ট্রেডিংকে মূল কৌশল হিসেবে গ্রহণের কোনোই বিকল্প নেই (অবশ্য বন্দর ভাড়াদানও এক প্রকার ট্রেডিংই বৈকি)। ফলে ট্রেডিংভিত্তিক সিঙ্গাপুরের উদাহরণ বাংলাদেশের জন্য একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে শিল্পনীতিতে উৎপাদন শিল্প ও সেবা খাতকে সমান্তরাল হিসেবে দেখানোর বিষয়টি এত সহজে সিদ্ধান্ত আকারে উপনীত হলো কীভাবে? এক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বলি, শিল্পনীতির খসড়া যখন শিল্পমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনের জন্য গেছে তখন কি সংশ্লিষ্ট রাজনীতিকরা যথেষ্ট বুঝেশুনে এতে সই করেছেন? কিংবা সংশ্লিষ্ট আমলারা কি এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও পেশাদারির পরিচয় দিতে পেরেছেন? অন্যদিকে রাজনীতিক ও আমলাদের বাইরে এক্ষেত্রের অন্যতম অংশীজন হচ্ছেন উদ্যোক্তারা এবং বাংলাদেশের প্রচলিত সংস্কৃতিতে তাদের শীর্ষ প্রতিনিধি হচ্ছে বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (এফবিসিসিআই)। কিন্তু বাস্তবে এফবিসিসিআই তো বস্তুত ট্রেডারদেরই প্রতিনিধি, উৎপাদকদের নয়। ফলে ট্রেডিংকে শিল্পের সমান্তরাল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে প্রণীত শিল্পনীতির খসড়ার ওপর যখন তাদের মতামত চাওয়া হয়, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই সোৎসাহে তারা এতে তাদের সমর্থন ঘোষণা করেন। আর খসড়ায় যদি এমনটি নাও থাকত তাহলেও তারা শিল্পনীতিতে এটি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানাতেন। কারণ এফবিসিসিআইয়ের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা আসলে ট্রেডারদেরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। এমনি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের উৎপাদন খাতের উদ্যোক্তারা যতদিন না সংগঠিত হয়ে দেশব্যাপী নিজস্ব শিল্প চেম্বার ও তাদের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র শিল্প-চেম্বার ফেডারেশন গড়ে তুলতে পারবেন, ততদিন পর্যন্ত শিল্পনীতিতে ট্রেডারদের প্রাধান্য থেকেই যাবে।
অন্যদিকে শিল্পনীতির খসড়া প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত আমলা-সদস্যরা যদি যথেষ্ট মাত্রায় পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান ও কার্যকর দক্ষতার অধিকারী না হন তাহলে তাদের পক্ষে কখনই একটি জনস্বার্থানুগামী ও উৎপাদন খাত সহায়ক শিল্পনীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না। আর তেমনটি না হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উৎপাদন শিল্প খাতের ভূমিকা ক্রমেই আরো সংকুচিত হয়ে আসবে বলে আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু নিজেদের ওপর অর্পিত দায় এড়ানোর জন্য কিংবা নিজেদের যথেষ্ট দক্ষ ও যোগ্য প্রমাণের জন্য কিংবা দক্ষতার সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার কারণে দেশ দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এরূপ বোঝোনোর জন্য যতই বলা হোক না কেন যে দেশের অর্থনীতি শনৈঃ শনৈঃ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, আসলে তা মোটেও এগোচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে দেশের অর্থনীতি যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রকৃত কৃষকের অংশগ্রহণভিত্তিক কৃষি খাত ও উৎপাদননির্ভর শিল্প খাতের যৌথ ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ দেশ একটি টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থার সারিতে দাঁড়াতে পেরেছে বলে মনে করাটা হবে নিছকই বাগাড়ম্বর। কিন্তু দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য বাগাড়ম্বর নয়, প্রয়োজন সাধারণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদাগুলোর তৃপ্তি ও সন্তুষ্টিদায়ক পরিপূরণ, যে ক্ষেত্রে উৎপাদন শিল্পের ভূমিকা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, অপরিহার্যও বটে।
লেখক: সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)