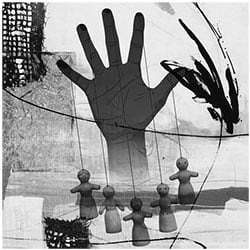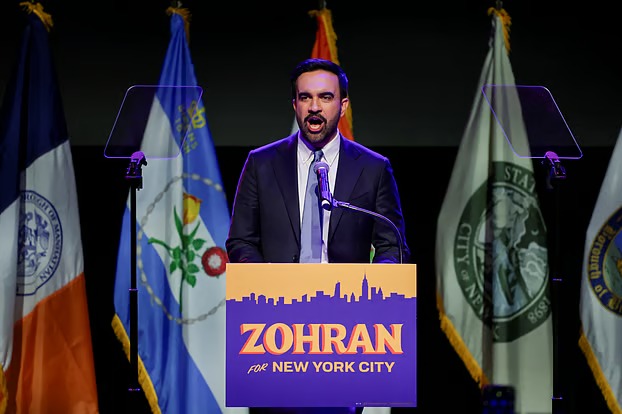মোস্তফা মোরশেদ : অর্থনীতির একটি নতুন শাখা হিসেবে ১৯৪০ এর দশকে উন্নয়ন অর্থনীতির যাত্রা শুরু হয়। এর উত্থানের পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসন শেষে পরিবর্তিত পৃথিবীতে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোকে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জের হাত থেকে রক্ষা করা। নতুন তত্ত্ব ও মডেলের সমন্বয়ে শুরু হওয়া এ ধারাকে অনেকেই ব্রিটিশদের সৃষ্টি (ইৎরঃরংয অভভধরৎ) বলে অভিহিত করেন।
এ লেখায় উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত ইস্যুগুলো আলোচনা করা হয়েছে। একটি দেশের উন্নয়নের পরিকল্পনা কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে যারা বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত তাদের জন্য উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হয়। উন্নয়নের সাথে যে সব চলক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সেগুলো সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা এবং এ চলকগুলোর সম্ভাব্য পরিবর্তন পরিমাপ করার মাধ্যমে উন্নয়ন অর্থনীতির পাঠ সফলতা লাভ করে। নীতি নির্ধারকদের পাশাপাশি অর্থনীতির শিক্ষার্থীদেরও এসব জানার অবকাশ রয়েছে। প্রসঙ্গত, ব্যাখ্যা করার সুবিধার্থে এবং যথার্থ পরিভাষার অভাবে এ লেখায় অনেকগুলো ইংরেজি শব্দ সরাসরি ব্যবহার করা হয়েছে।
উন্নয়ন একটি বহুমুখী ধারণা। খুব স্বল্প পরিসরে এর ব্যাখ্যা বা বর্ণনা অসম্ভব। উন্নয়ন আলোচনায় অনেক বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়। সংক্ষেপে বললে, উন্নয়ন মানে মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্কিত সকল চলকের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং সামগ্রিকভাবে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। উন্নয়নের সাথে জড়িত চলকগুলোর তালিকা করলে মানুষের জীবন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পৃক্ত সকল বিষয় চলে আসে। চলকগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক এতটাই নিবিড় যে এদের একটির পরিবর্তন হলে আরেকটি বিভিন্ন মাত্রায় পরিবর্তিত হয় যা অর্থনীতির ভাষায় অন্তর্জনিষ্ণু (ইস্যু ১) (বহফড়মবহরঃু) হিসেবে বিবেচিত। বাস্তবিক অর্থে, উন্নয়ন অর্থনীতির ধারণায় বহির্জনিষ্ণু (বীড়মবহড়ঁং) চলক বলতে কিছু নাই। উন্নয়নের রুপরেখা প্রণয়নে চলকের সংখ্যা যত সমস্যা সৃষ্টি করে তার চেয়ে বেশি সমস্যা তৈরি করে এদের পারস্পরিক অন্তর্জনিষ্ণু সম্পর্ক।
চলকের দুটি প্রকার রয়েছে; পরিমাণগত (ইস্যু ২) ও গুণগত (ইস্যু ৩)। পরিমাণগত চলকগুলোর তালিকায় যে সকল চলক থাকবে সে তালিকা অনেক দীর্ঘ। আলোচনার সুবিধার্থে ধরা যাক, এ তালিকায় পঞ্চাশটি চলক রয়েছে। তবে এ তালিকার প্রথমেই আসবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (ইস্যু ৪)। ১৯৮০ এর দশকে ‘উন্নয়ন’ ও ‘অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি’কে দুটি আলাদা ইস্যু বিবেচনা করা হতো। এমনকি এর পক্ষে দুটি আলাদা ংপযড়ড়ষ ড়ভ ঃযড়ঁমযঃ-ও গড়ে উঠে। তবে সময়ের পরিক্রমায় বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (ইস্যু ৫) বিকাশের কারণে এ বিতর্কের অবসান হয়েছে। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ‘অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি’ সকল আয়ের দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চলক হিসেবে উন্নয়ন অর্থনীতির আলোচনায় সর্বাগ্রে স্থান করে নিয়েছে। তালিকার দ্বিতীয় চলকটি একেক দেশের জন্য একেক রকম হবে। যেমন, আফ্রিকার উন্নয়নের তালিকার দ্বিতীয় চলক হয়ত ‘বিশুদ্ধ পানি’, ভারতের ক্ষেত্রে হয়ত ‘স্যানিটেশন’ কিংবা পৃথিবীর অনেক দেশের জন্য সেটি ‘বৈষম্য’। ইস্যু হিসেবে উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত চলকগুলোকে বিবেচনা করার অবকাশ ছিল না, এ লেখার কলেবর বেড়ে যেত।
গুণগত চলকগুলো মূলত উন্নয়ন আলোচনার বিদ্যমান পরিমাণগত চলকের ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। উন্নয়নের চলক হিসেবে ‘শিক্ষার উপকরণ’ বিবেচনা করলে দেখতে হবে এগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য কতটুকু উপকারী। যেমন, নির্দিষ্ট সংখ্যক কলমের বিপরীতে কী মানের কলম সরবরাহ করা হবে সেটিই মুখ্য। পরিমাণগত চলকের গুণগত মান অর্জনের মাধ্যমে গুণগত চলকের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জিত হয়।
উন্নয়ন সরাসরি জনগণের সাথে সম্পৃক্ত (ইস্যু ৬)। নির্দিষ্ট করে বললে, উন্নয়ন শুধুমাত্র মানুষের জন্য। যেখানে মানুষ নাই সেখানে উন্নয়ন নাই। মরুভূমিতে যেখানে মানুষের বসবাস নাই সেখানে উন্নয়ন চিন্তার প্রতিফলন নাই। এ অবস্থাকে আন-ডেভেলপমেন্ট বলা হয়ে থাকে। সম্ভাব্য উন্নয়ন হবার জায়গায় উন্নয়ন কম হলে তাকে আন্ডার-ডেভেলপমেন্ট বলে।
উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য একক কোনো পদ্ধতি বা মডেল পাওয়া যায় না। বিশ্বব্যাংক যেভাবে সংজ্ঞায়িত (ইস্যু ৭) করেছে তাতে শুধুমাত্র মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলার) এর উপর ভিত্তি করে দেশগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়–
১) নি¤œ-আয়ের দেশ (মাথাপিছু জিএনআই ১,০২৫ এর কম);
২) মধ্যম-আয়ের দেশ;
৩) উচ্চ-আয়ের দেশ (মাথাপিছু জিএনআই ১২,৪৭৫ এর বেশি)।
মধ্যম-আয়ের দেশসমূহকে আবার দু’ভাগে ভাগ করা হয়; নি¤œ মধ্যম-আয়ের দেশ (মাথাপিছু জিএনআই ১,০২৬ থেকে ৪,০৩৫) ও উচ্চ মধ্যম-আয়ের দেশ (মাথাপিছু জিএনআই ৪,০৩৬ থেকে ১২,৪৭৫)।
অপরদিকে, জাতিসংঘের বিশ্লেষণ (ইস্যু ৮) অনুযায়ী বিশ্বের দেশসমূহকেও তিন ভাগে ভাগ করা হয়; ১) স্বল্পোন্নত দেশ, ২) উন্নয়নশীল দেশ, ও ৩) উন্নত দেশ। জাতিসংঘ তিনটি সূচকের (মাথাপিছু জিএনআই, মানব সম্পদ সূচক ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক) উপর ভিত্তি করে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের হিসাব করে থাকে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে উত্তরণের কোনও মাপকাঠি নেই। জাতিসংঘ শুধুমাত্র স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তালিকা প্রণয়ন করে। এ তালিকার বাইরের দেশগুলো উন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। উন্নয়ন পরিমাপে মানব উন্নয়ন সুচক বা ঐউও-ও (ইস্যু ৯) ব্যবহৃত হয় যা বহুলভাবে স্বীকৃত। ঐউও এর গঠন অনেকটা পূর্বে উল্লিখিত জাতিসংঘের মানব সম্পদ সূচকের মতো।
এছাড়া উন্নয়ন পরিমাপ করতে হলে আবশ্যিকভাবে সামাজিক খরচ ও লাভের বিশ্লেষণ (ংড়পরধষ পড়ংঃ-নবহবভরঃ ধহধষুংরং) করতে হয়। কারণ প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের (সরকারি ও বেসরকারি) সাথে এক্সটারনালিটির (ইস্যু ১০) গভীর সংযোগ রয়েছে যা টাকার অংকে পরিমাপ করতে হয়। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যে সকল ঋণাত্মক চিত্র উঠে আসে অর্থনীতির আলোচনায় এগুলোকে নেগেটিভ এক্সটারনালিটি এবং ধনাত্মক বিষয়গুলোকে পজিটিভ এক্সটারনালিটি বলা হয়ে থাকে। এ সকল এক্সটারনালিটি পরিমাপের মাধ্যমেই অর্থনীতির পাঠে সামাজিক খরচ ও লাভের বিশ্লেষণ (ইস্যু ১১) করা হয়। কোনও প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যদি নিগেটিভ এক্সটারনালিটি উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক ক্ষতি বেশি হয় তবে বাজার ব্যর্থ (ইস্যু ১২) (সধৎশবঃ ভধরষঁৎব) হয়। বাজার ব্যর্থতা ঠেকানোর জন্য প্রকল্প নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি কর্তৃত্বের (ধঁঃযড়ৎরঃু) দরকার হয়। এ কর্তৃত্বই কার্যত সরকার এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত সরকারের কার্যপরিধির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এভাবেই সরকার উন্নয়ন অর্থনীতিতে ভূমিকা (ইস্যু ১৩) রেখে থাকে।
সামাজিক খরচ ও লাভের হিসাব করা বেশ জটিল ও কষ্টসাধ্য। অনুন্নত দেশের জন্য এটি প্রায় অসম্ভব। এর সবচেয়ে বড় কারণ সরকারের দুর্বল প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি গবেষণা খাতের দুর্বলতা (ইস্যু ১৪)। সরকারি বা বেসরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের সাথে উন্নয়ন সিদ্ধান্তের একটি দারুণ সমন্বয় দরকার যা পূর্বে উল্লিখিত অর্থনীতিতে সরকারের ভুমিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ।
প্রকল্প নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সাথে অনেক বিষয় জড়িত। মোটাদাগে যদি পুরা অর্থনীতিকে তিনভাগে ভাগ করা হয় (কৃষি, শিল্প ও সেবা) তবে প্রকল্প নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবগুলোকে সমান প্রাধান্য দিতে হবে কারণ একটি আরেকটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। একটি অন্যটির চেয়ে তুলনামূলক বেশি অনেক এগিয়ে গেলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন (ইস্যু ১৫)।
উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের অনেক দীর্ঘ তালিকা থাকতে পারে তবে সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকায় উন্নয়ন প্রকল্পের একটি অগ্রাধিকার তালিকা থাকা আবশ্যক।
অগ্রাধিকার তালিকা হতে অর্থনৈতিক প্রভাবের (বপড়হড়সরপ রসঢ়ধপঃ) (ইস্যু ১৬) আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হয়। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে যুক্তিসঙ্গত কারণে অনেকক্ষেত্রেই সরকার ব্যক্তিখাতের মতো আচরণ করে না। ব্যক্তিখাত যেমন মুনাফা (ঢ়ৎড়ভরঃ) কেন্দ্রিক আচরণ করে সেখানে সরকারের পরিকল্পনায় থাকে মানুষের সেবা (ংবৎারপব) বাড়ানোর ব্রত। তাই ব্যক্তিখাতে ব্যবহৃত বিনিয়োগের পরিমাপকগুলো (ইস্যু ১৭) যেমন, এনপিভি, আইআরআর, প্রফিটাবিলিটি ইনডেক্স, ইত্যাদি দ্বারা সরকারি বিনিয়োগের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। প্রায় সকল আয়ের দেশের জন্য অবকাঠামোগত বিনিয়োগ (ইস্যু ১৮) উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এর পাশাপাশি অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশের জন্য অনেকক্ষেত্রেই প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (ইস্যু ১৯)।
প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে আরেকটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে কোনও উন্নয়ন কর্মকা-ের সাথে এর সাথে সম্পর্কিত চলক বা চলকগুলোর ঃৎধফব-ড়ভভ (ইস্যু ২০) রয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই একটি চলকের উন্নতি হলে অন্য একটি বা একাধিক চলক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একটি ধ্রুপদী উদাহরণ হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) দুটি গোলের পারস্পরিক সম্পর্ক। এসডিজি গোল-৮ এ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও সুন্দর কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে গোল-১০ এ সব ধরনের বৈষম্য কমানোর (ইস্যু ২১) লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের (গোল- ৮) সাথে বৈষম্যের সরাসরি ঋণাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। বাস্তবে দেখা যায়, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলে দুটি বিপরীতধর্মী বিষয়ের অবতারণা হয়; এক) দারিদ্র্য কমে (ইস্যু ২২), কিন্তু, দুই) আয় এবং আয় বহির্ভূত বৈষম্য বাড়ে।
উন্নয়ন সংজ্ঞায়িত করার জন্য চলকের যে দীর্ঘ তালিকা রয়েছে সেখানে বৈষম্য নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে দুর্বোধ্য এবং কঠিন কাজ। পৃথিবীর সকল আয়ের দেশের জন্য উন্নয়ন তালিকার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং চলক হচ্ছে বৈষম্য কমানো যা দীর্ঘসময় ধরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। একটি অর্থনীতিতে দু’ধরনের বৈষম্য দেখা যায়, আয় ও আয়-বহির্ভূত। আয় দ্বারা সৃষ্ট যে বৈষম্য সেটি সহজেই অনুমেয়। আয়-বহির্ভূত বৈষম্য হচ্ছে সামাজিক প্রথা, নিয়ম, শিক্ষা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট বৈষম্য। সত্যি বলতে, আয়ের বৈষম্য অন্যান্য বৈষম্যের প্রায় সমান বদলি (ঢ়ৎড়ীু) হিসেবে কাজ করে। বৈষম্যের কারণে উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তিমূলক (রহপষঁংরাব) (ইস্যু ২৩) হয় না। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে দারিদ্র্য কমানোর পাশাপাশি বৈষম্যও কমাতে হবে।
সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (ইস্যু ২৪) থাকতে হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের হাত ধরে আমরা এরূপ দুটি পরিকল্পনা দেখেছি, রূপকল্প -২০২১ ও রুপকল্প-২০৪১। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো উন্নয়নের জন্য সব দেশের আলাদা আলাদা কৌশল (ইস্যু ২৫) থাকবে। সম্পদের ভিন্নতা থাকায় প্রত্যেক দেশের আলাদা ভিশন ও কৌশল থাকা স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত। যদিও অনেকক্ষেত্রেই আমরা উন্নয়নের তত্ত্ব ও মডেলকে সবার জন্য একইভাবে (মবহবৎধষরুব) ব্যবহার (ইস্যু ২৬) করার চেষ্টা করে থাকি যা বাস্তবে অসম্ভব।
উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরকার সম্পদের স্থানান্তর (ইস্যু ২৭) করে থাকে। এ প্রক্রিয়া যত স্বচ্ছ হবে উন্নয়নের গতি (ইস্যু ২৮) তত বেশি হবে। সময়ের পরিক্রমায় সকল আয়ের দেশেই উন্নয়ন হয়। তবে এর গতিটাই মুখ্য। উন্নয়নের গতির সাথে কার্যত এ লেখায় বর্ণিত সকল চলকই সম্পৃক্ত। সম্পদের স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী উপস্থিতি এবং এসব প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিকরণ (ইস্যু ২৯) প্রয়োজন। এর পাশাপাশি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (ইস্যু ৩০) গুরুত্বও অনেক। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে উপকার বা সুবিধাভোগী (ংঃধশবযড়ষফবৎ) পর্যায়ে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশের একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করা। এটি করতে হলে সামজিক ন্যায়বিচার (ইস্যু ৩১) নিশ্চিত করতে হয়। আর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও (ইস্যু ৩২) তখন উন্নয়নের চলক হয়ে উঠে।
সম্পদ স্থানান্তরের বিষয়টি বর্তমান প্রচলিত উন্নয়ন মডেলে নতুন রূপ লাভ করেছে। এনজিওদের মতো যদি উপকারভোগীদের মাঝে সম্পদের মালিকানা বা স্বত্ব (ড়হিবৎংযরঢ়) (ইস্যু ৩৩) সৃষ্টি করা না যায় তবে স্থানান্তরিত সম্পদ কার্যত কোনো কাজে আসে না। ধরুন, সরকার একটি নলকূপ স্থাপন করল। যারা এর উপকারভোগী তারা যদি এর রক্ষনাবেক্ষণ না করে তবে কিছুদিন পর এর অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে। যদি উপকারভোগীরা এর পেছনে ব্যয় (খুব সামান্য হলেও) এবং রক্ষনাবেক্ষণ করে তবে নলকূপটির ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হবে। বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে এরকমই স্বত্ব তৈরি করার নজির রয়েছে।
উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত আরও অনেক ইস্যু রয়েছে। বৈষম্যের মতো যে চলকটি আজকের দিনে উন্নয়ন অর্থনীতির আলোচনায় অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক সেটি হলো পরিবেশ সংরক্ষণ (ইস্যু ৩৪)। উন্নয়ন টেকসই করতে হলে এর বিকল্প নেই। উন্নয়ন মাত্রই টেকসই হবে তাই আমার মতে ‘টেকসই উন্নয়ন’ শব্দটি বাহুল্য দোষে দুষ্ট! সমষ্টিক অর্থনীতির আলোচনায় রাজস্ব ও মুদ্রানীতির একটি চমৎকার ভারসাম্য (ইস্যু ৩৫) থাকা বাঞ্ছনীয়। দুই ঘরানার দু’দল অর্থনীতিবিদগণ যা-ই বলেন না কেন দু’টির কোনও একটি অপরটির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। বিশেষ করে, একটি স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কর্তৃত্বপূর্ণ মুদ্রানীতি আজকের এ বিশ্বে অনেক বেশি প্রয়োজন।
উন্নয়ন অর্থনীতির ব্যপকতা ও বিষয়বস্তুর গভীরতা বিবেচনা করলেও লেখাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে কারও কাছে ইস্যু হিসেবে কোনও কিছু বাদ পড়েছে বলে মনে হতে পারে। যেমন, একটি অর্থনীতিতে সরকারের গঠন (গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক না-কি একনায়কতান্ত্রিক) কেমন হবে উন্নয়ন অর্থনীতির আলোচনায় সেটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তবে সরকারের গঠন বিষয়টি সামাজিক ন্যায় বিচার ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্বারা (যা ইস্যু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রতিস্থাপন করা যায়। প্রসঙ্গত, এখানে কিছু ইস্যুকে যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে আবার কিছু ইস্যু বাদ দিতে হবে। সম্ভাব্য সকল ইস্যু বিবেচনায় নিয়ে একটি পরিপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। হুশিয়ার করে দেওয়া যেতে পারে, উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নে বর্ণিত ইস্যুগুলোকে বিবেচনা করতেই হবে। অন্যথায়, উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের শ্রম ও অর্থ সবই ফবধফ-বিরমযঃ ষড়ংং (ইস্যু ৩৬) হিসেবে গণনা করতে হবে।
লেখক: উন্নয়ন অর্থনীতি গবেষক