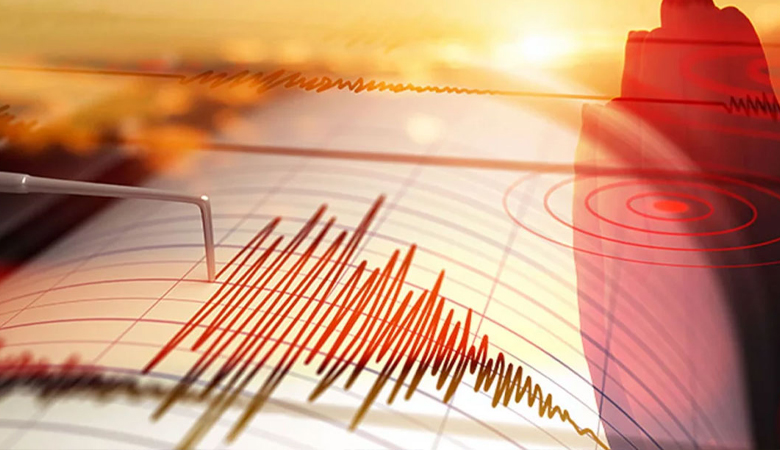মো. সামসুল ইসলাম : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার মিডিয়া বিশেষজ্ঞদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশে তো বটেই, বিশ্বজুড়ে মানুষ সামাজিক মাধ্যম, যেমন- ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদিতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে যেন এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক মাধ্যমে রাশিয়ার ইউক্রেনের যুদ্ধের বিভিন্ন ভিডিও নিয়ে বিভিন্ন দেশের নাগরিকেরা বিতর্ক করছেন। নিজেদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শেয়ার করছেন। এটি আসলে অভাবনীয় বটে। বিশ্বখ্যাত ফোর্বস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক নিবন্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ইউক্রেনের যুদ্ধ বিশ্বের ‘ফার্স্ট সোশাল মিডিয়া ওয়ার’ বা সামাজিক মাধ্যমের ‘প্রথম যুদ্ধ’ কিনা। নিউ ইয়র্কার পত্রিকায় একজন লিখছেন, এটি প্রথম ‘টিকটক ওয়ার’ বা যুদ্ধ! মার্চের ৭ তারিখ পর্যন্ত টুইটারে ইউক্রেন ওয়ার হ্যাশট্যাগ দেওয়া ভিডিও দেখা হয়েছে ৬০০ মিলিয়ন বারেরও বেশি।
আমার মনে পড়ছে ২০০১ সালে ইরাক আক্রমণের এক দশক পূর্তিতে আমি ঢাকার এক ইংরেজি দৈনিকে একটি আর্টিক্যাল লিখেছিলাম ‘ফার্স্ট ইনফরমেশন ওয়ার’ শিরোনামে। মূলত সেই যুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ও সাইকোলজিক্যাল অপারেশনের ব্যবহার নিয়ে। সেই যুদ্ধ যা গালফ ওয়ার নামে পরিচিত, তখন আলোচিত হয়েছিল প্রথম ইনফরমেশন ওয়ার হিসেবে। স্প্যানিশ-আমেরিকান সিভিল ওয়ার পরিচিত ছিল ফার্স্ট মিডিয়া ওয়ার বা প্রথম মিডিয়া যুদ্ধ হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্রের লেখক, দার্শনিক সুসান সন্টাগ ২০০৩ সালে লিখিত এক প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেন স্প্যানিশ-আমেরিকান সিভিল ওয়ার কীভাবে ফটোজার্নালিজমের বিস্তার ঘটায়। ভিয়েতনাম ওয়ার খ্যাতি পায় ফার্স্ট টেলিভিশন ওয়ার বা প্রথম টেলিভিশন যুদ্ধ হিসেবে। প্রথমবারের মতো সেই যুদ্ধ টেলিভিশনের মাধ্যমে পৌঁছে যায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নাগরিকদের ড্রয়িংরুমে।
তবে এবারের সামাজিক মাধ্যমের যুদ্ধের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যুদ্ধের ভিডিও যে কেউ শেয়ার করতে পারছেন। মুহূর্তের মধ্যে পুরো বিশ্বে তা ছড়িয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এটা যুদ্ধ নিয়ে প্রাচীনতম উক্তি যে ‘যুদ্ধের প্রধান বলি হচ্ছে সত্য’ – এ ধারণাকে অনেকটা মিথ্যা পরিণত করছে। মানুষের জন্য যুদ্ধের সঠিক সংবাদ পাওয়াটা এখন খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। যদিও সামাজিক মাধ্যমে ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে অনেক ফেইক নিউজ, তথ্য বিকৃতি ঘটছে। আরমা থ্রি ভিডিও গেমসের ফুটেজকে অথবা গাজায় ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যুদ্ধের ছবি ইত্যাদি রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের ছবি বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তারপরও এটা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর মানুষ এখন সরাসরি রিয়েল টাইমে যুদ্ধ দেখছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত ‘এমবেডেড জার্নালিজমের’ কার্যকারিতা নিয়েও হয়তো এখন প্রশ্ন উঠবে। যুদ্ধ নিয়ে সাংবাদিকদের দিয়ে নিজের পছন্দমতো তথ্য প্রচারের দিন বোধহয় শেষ হয়ে আসছে। আমরা দেখছি এই যুদ্ধে পশ্চিমাদের সঙ্গে রাশিয়ার ‘ইনফরমেশন ওয়ার ফেয়ার’ এর পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যম ইউক্রেনের জন্য ‘ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার’ হিসেবে কাজ করছে। অর্থাৎ তারা এই যুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমের সহযোগিতা পাচ্ছে। সনাতন যুদ্ধাস্ত্রের সহযোগী হিসেবে সামাজিক মাধ্যম কাজ করছে। সামাজিক মাধ্যমে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির বারবার ভিডিও শেয়ার তাকে নায়কের মর্যাদা দিয়েছে।
কয়েক দিনের ব্যবধানে তার টুইটার অ্যাকাউন্টের ফলোয়ারের সংখ্যা তিন লাখ থেকে বেড়ে ৫০ লাখে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক মাধ্যমের দ্বারা বিশ্ব জনমতকে কাছে টানার প্রচেষ্টায় ইউক্রেন যে অনেকটাই সফল তা বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে। অপরপক্ষে পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত সামাজিক মাধ্যম রাশিয়ার জন্য গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়ায় ফেসবুক নিষিদ্ধ করা হয়েছে, টুইটার নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। পুতিনকে নতুন আইন করতে হয়েছে জনমত নিয়ন্ত্রণ করতে। এই আইন অনুসারে ইউক্রেনে রাশিয়ার কার্যক্রমকে ‘যুদ্ধ’ বলা যাবে না। ‘মিথ্যা তথ্য’ প্রচারের জন্য ১৫ বছরের কারাদ-ের বিধান রাখা হয়েছে। এবার আমাদের দেশের প্রসঙ্গ। আমাদের দেশেও ইউক্রেন যুদ্ধে নিয়ে নেটিজেনরা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। ওয়ার অন টেররের নামে মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পশ্চিমা দেশগুলোর ধ্বংসযজ্ঞে আতঙ্কিত অনেকেই পশ্চিমের গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ে গালগল্প আর পছন্দ করেন না। ইউক্রেনসহ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত দেশগুলোকে ন্যাটোভুক্ত করার প্রচেষ্টাকে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর ষড়যন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা হিসেবে দেখছেন অনেকেই।
আবার আমাদের নেটিজেনদের আরেক বিশাল অংশ ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখছেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই আক্রমণকে মেনে নিতে পারছেন না। এই যুদ্ধ নিয়ে জাতিসংঘের ভোটাভুটি দেখলে বোঝা যায় বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্রই সরকারিভাবে এই মতের সমর্থক। আমাদের দেশে এবং বিদেশে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি সামাজিক মাধ্যমে বেশ ভালোভাবেই আলোচিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে পৃথিবী আবার সেই স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে ফিরে গিয়েছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সেই সময়ে ছিল এক বড় ইস্যু। বাংলাদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান ‘ঝবপঁৎরঃু ড়ভ ঝসধষষ ঝঃধঃবং রহ ঞযরৎফ ডড়ৎষফ’ গ্রন্থের মাধ্যমে দেশে বিদেশে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে এটা অস্বীকার করার উপার নাই যে করোনা পরবর্তী পৃথিবীতে পুতিনের এই আক্রমণ এক নতুন মতবাদ বা ডকট্রিনের জন্ম দিয়েছে – একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ইচ্ছে করলেই এক দুর্বল রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে পারে। যা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। সামাজিক মাধ্যমে এই বিষয়টিকে অনেকে তুলে ধরতে চাইছেন। স্ট্র্যাটেজিক বা কৌশলগত কারণ তো রয়েছেই, কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর পক্ষে স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে প্রক্সি ওয়ার-এর স্মৃতি হয়তো ভোলা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় এই সতর্কতা থেকেই ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ জাতিসংঘে সরাসরি রাশিয়ার বিপক্ষে অবস্থান নেয়নি। এটি নিয়েও নেট দুনিয়ায় ব্যাপক বিতর্ক চলছে।
তবে যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের নেটিজেনরা বোধহয় একটু কম আলোচনা করছেন তা হচ্ছে আমরা এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি কিনা বা এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার স্বরূপ কেমন হতে পারে। ইউক্রেন নিয়ে পুতিনের উচ্চাশার যদি বাস্তবায়ন ঘটে, এবং রাশিয়ার অর্থনীতি যদি স্থিতিশীল থাকে এবং রাশিয়ার প্রতি চীনের সমর্থন যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবেই এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা পেতে যাচ্ছি। যদিও এই বিষয়ে এখন মন্তব্য করা কঠিন। তবে আমাদের দেশের নেটিজেনরা সামাজিক মাধ্যমে এই বিষয়ে আরও লেখালেখি করবেন এই প্রত্যাশাই করছি।
লেখক: কলামিস্ট; বিভাগীয় প্রধান, জার্নালিজম, কমিউনিকেশন ও মিডিয়া স্টাডিজ, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।