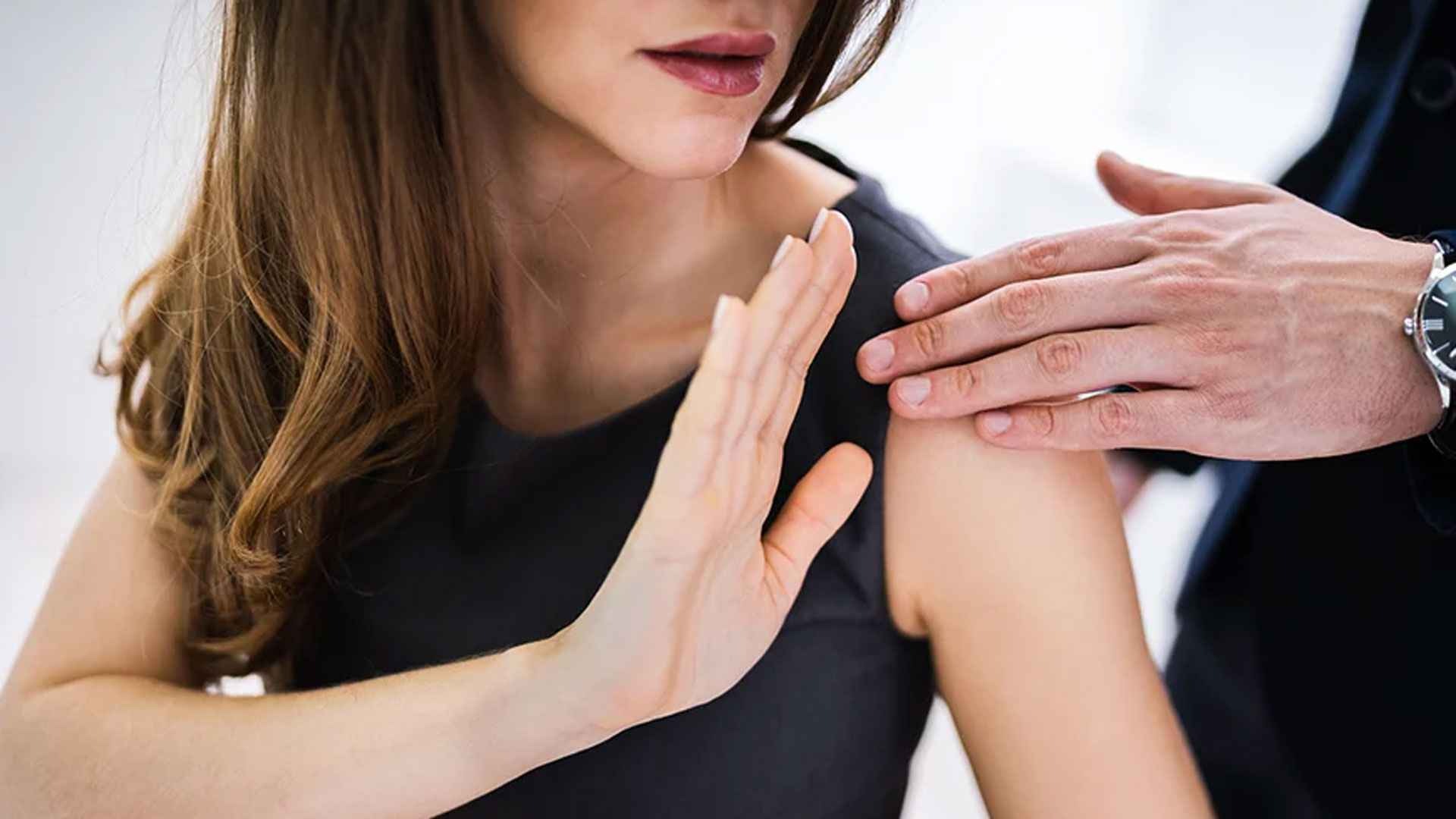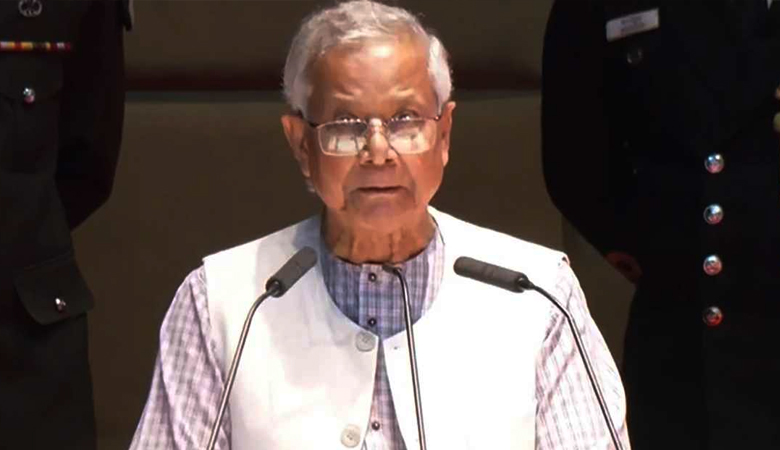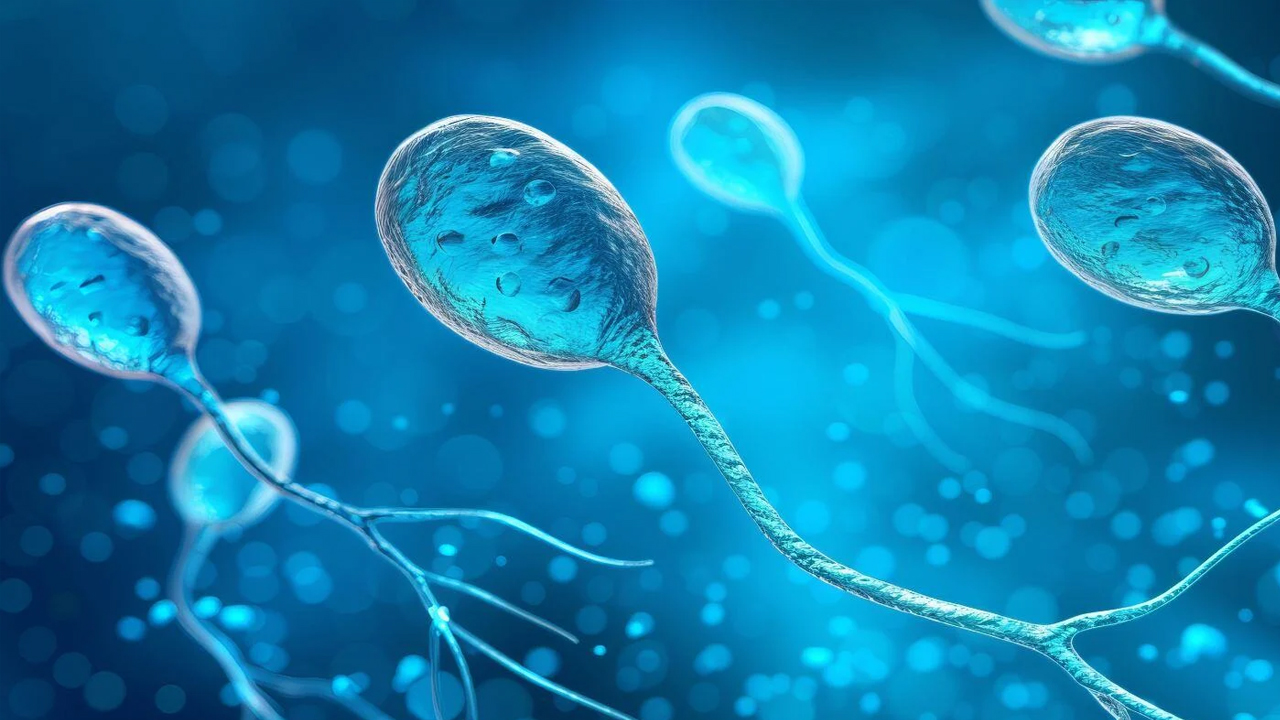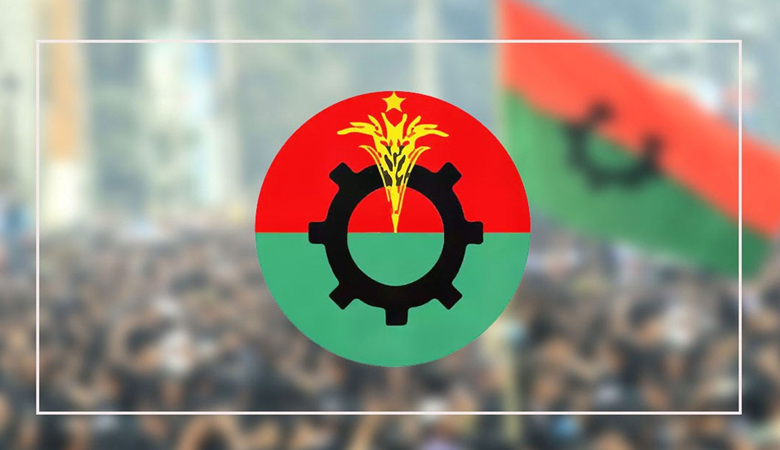নারী সংশ্লিষ্ট যে কোনো ঘটনায় প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় নারীকে। পুরো পৃথিবীতে বিষয়টি প্রায় একই রকম। পরিস্থিতির শিকার হলেও সমাজ তাকেই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। এই ব্যাধির পালে হাওয়া দিচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো। এখন অনেক ক্ষেত্রে নারীর বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হয়রানির প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে এগুলো। ছবি বা ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া, ভিকটিম ব্লেমিং, গুজব, গালাগাল- এসব ক্ষেত্রে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত নারীরা। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী অনলাইনে নারীদের প্রতি সহিংসতা বৈশ্বিক এক ‘ডিজিটাল মহামারি’ হয়ে উঠেছে। এ বিষয় নিয়েই এবারের নারী ও শিশু পাতার প্রধান ফিচার
প্রযুক্তিকে নারীবান্ধব না করে তাকে নারীর বিপক্ষে ব্যবহারের প্রবণতা বিশ্বব্যাপী। নারী যখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেকে দৃশ্যমান করেন, তখন তাকে ‘অতিরিক্ত সাহসী’, ‘উগ্র’ বা ‘অশ্লীল’ বলে উল্লেখ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে একদল মানুষ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চাইলেই নারীকে যেকোনো কিছু বলা যায়। বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত মনে করেন, ইন্টারনেট নারীকে দমিয়ে রাখার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। তিনি বলেন, ‘নারীর সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব তার নিজের- এটাই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি।’
বেশি ঝুঁকিতে কারা: অ্যাকশনএইডের এক জরিপে দেখা গেছে, ৬৪ শতাংশ নারী ফেসবুক, মেসেঞ্জার ও ইনস্টাগ্রামে বিভিন্ন পর্যায়ের অশ্লীল বা হিংস্র মন্তব্যের শিকার হন। এই হয়রানির কোনো বয়সসীমা কিংবা বিশেষ কোনো ক্ষেত্র নেই। অনলাইনে সরব যে কোনো নারী হয়রানির শিকার হন। ইউএনএফপিএর এক জরিপে বলা হয়েছে, ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সীরা সক্রিয়ভাবে এই ধরনের হিংসার শিকার হচ্ছেন।
এ বিষয়ে অধিকারকর্মী মারজিয়া প্রভা বলেন, ‘আমি আগে মনে করতাম, ১৮ থেকে ৩৫ বছরের নারীরা বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। একজন নারী—সে কতা ভোকাল, সে কী করছে, তার কার্যক্রম, একটুও এস্টাবলিশমেন্ট ধ্যানধারণা কিংবা কাঠামোকে ধাক্কা দিচ্ছে কি না!’ বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি মনে করেন, ১২ থেকে ৪০ বছর বয়সী নারীরা বেশি ঝুঁকিতে।
অনুমতি ছাড়া ছবি শেয়ার, ডিপফেক ভিডিও বানানো, অশালীন বার্তা পাঠানো, প্রকাশ্যে হেয় করা, গুজব ও হুমকি-এ বিষয়গুলো অনেক বেশি নারীকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে প্রতিনিয়ত। এসব বিষয় থামাতে আইন থাকলেও তার সঠিক ব্যবহার না জানার কারণে সমাজ থেকে এগুলো সরিয়ে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না।
মানসিক অবসাদ: ভুক্তভোগী যে-ই হোক, যে কোনো ঘটনা শুনলে সেটির প্রভাব থেকে যায়। কোনো ডিপফেক ভিডিও ভুক্তভোগীকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি যে সেটি দেখে, তার ওপরে প্রভাব ফেলে। অনলাইনে নারীদের ক্রমাগত বুলিং, ডিপফেককরণ, ছবি ও ভিডিও ভিন্নভাবে শেয়ার করা মানসিক অবসাদের বড় কারণ। ডিজিটাল অনিরাপত্তা নারীদের ভীষণভাবে হতাশাগ্রস্ত করে, আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়, নারীকে ঘরমুখী করে এবং গুটিয়ে যেতে প্রভাব রাখে। অধিকারকর্মী মারজিয়া প্রভা বলেন, ‘আমরা যারা জনপরিসরে অ্যাকটিভিজম করি, এই রিস্কগুলো নিয়ে অবগত, দেখা যায়, সারা দিন ঘটনাগুলো স্ক্রল করছি, জবাব দিচ্ছি। একটা এন্ডলেস চক্রে ঢুকে গেছি। যখন বের হতে চাই চক্র থেকে, তখন দেখা যায়, দিনের একটা বড় সময় এর পেছনে চলে গেছে। তখন আরও বেশি অবসাদে ভুগতে থাকি।’
সচেতনতা ও প্রতিরোধ কতটা সচল: আইনের প্রয়োগ, সচেতনতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বদল আনতে হবে। আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা, স্কুল পর্যায়ে অনলাইন আচরণ বিষয়ে শিক্ষা ও ডিজিটাল লিটারেসি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়ানো এবং সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশে ডিজিটাল সুরক্ষা আইন গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রয়োগ এবং নাগরিক সচেতনতায় ঘাটতি রয়েছে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সাইবার সিকিউরিটি ও ডিজিটাল অধিকারবিষয়ক বিশ্লেষক তানভীর হাসান জোহা। তিনি বলেন, ‘প্রশাসন এআই প্রযুক্তির বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক। তবে ডিপফেক, অনুমতি না নিয়ে শেয়ার করা ছবি কিংবা ভিডিও এবং নারীর ডিজিটাল হয়রানি প্রতিরোধী কাঠামোতে আরও সচেতন ও কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন। আইনি স্বচ্ছতা ও সহায়তার মাধ্যম সহজলভ্য করা; নাগরিক হিসেবে ঘর থেকে স্কুল, কর্মক্ষেত্র—সব জায়গায় প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রসার এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর বেশি দায়িত্ব নেওয়া—সব মিলিয়ে নারীদের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।’
দোষ কোথায়: অনুমতি ছাড়া ছবি শেয়ার, ডিপফেক ভিডিও বানানো, অশালীন বার্তা পাঠানো, প্রকাশ্যে হেয় করা, গুজব ও হুমকি—এ বিষয়গুলো অনেক বেশি নারীকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে প্রতিনিয়ত। এসব বিষয় থামানোর জন্য আইন থাকলেও তার সঠিক ব্যবহার না জানায় সমাজ থেকে এগুলো সরানো সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে প্রথমে যাঁরা প্রতিবাদ করেন, ধীরে ধীরে তারা চুপ হয়ে যান। এমনকি অনেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। কারণ অনলাইনে অপমানিত হওয়া মানে এখন পরিবার বা সমাজে ‘বিব্রতকর ব্যক্তি’ হয়ে যাওয়া।
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ