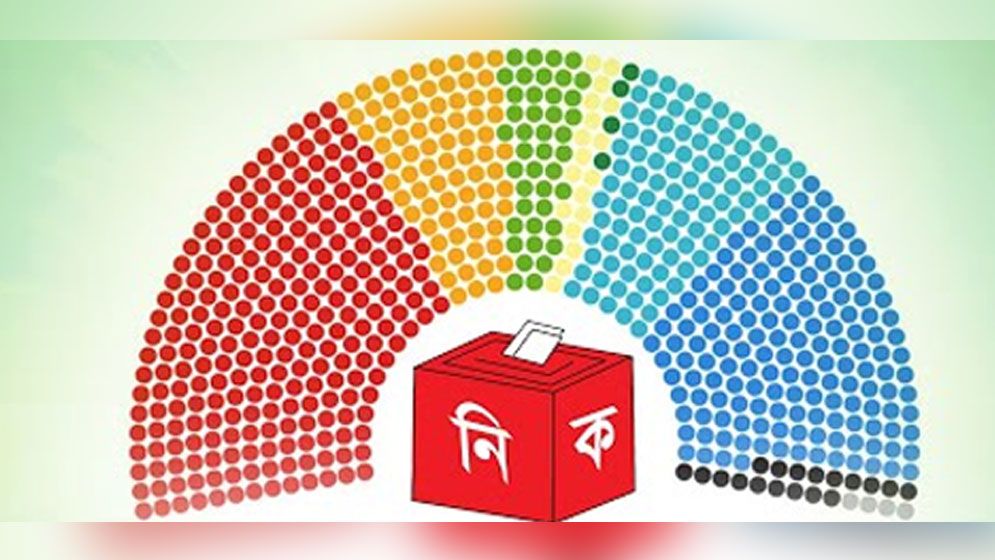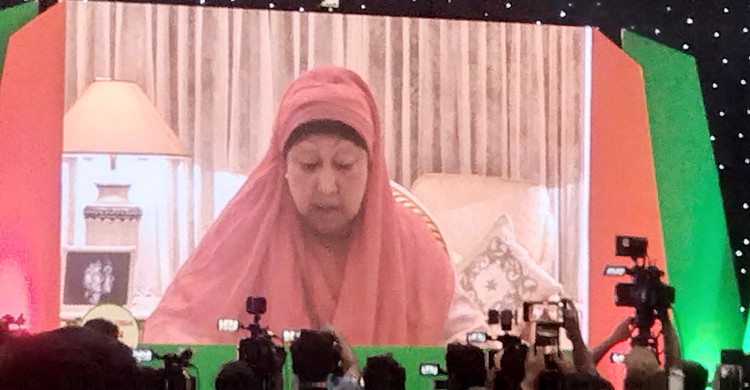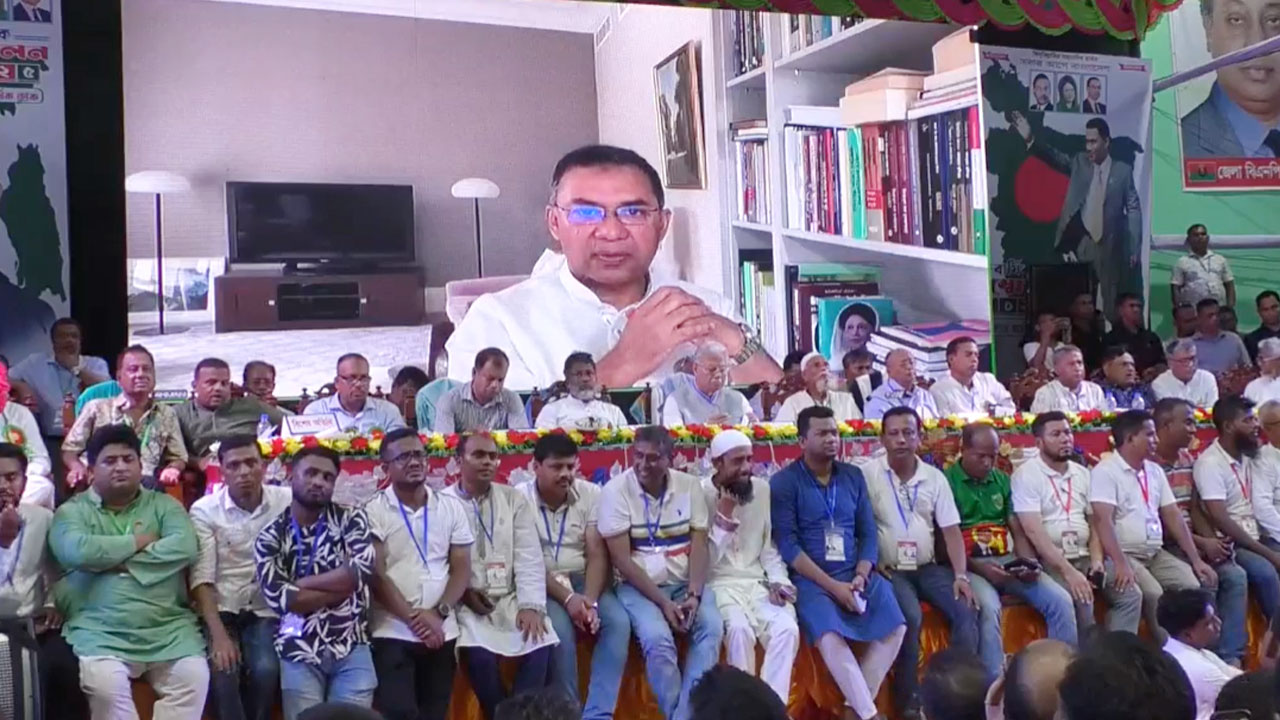ইতিহাসের করুণতর অধ্যায় রক্তাক্ত জুলাই-আগস্ট পেরিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন মনে খানিকটা আকাক্সক্ষা নিয়ে লিখতে বসা। শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর জনমনে সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তনের আকাক্সক্ষা কাজ করছে। যদিও তিন মাসে খুব বেশি পরিবর্তন দেখা যায়নি। তবে স্বপ্ন দেখার জোরালো সাহস রয়েছে। কেননা বাংলাদেশ এই মুহূর্তে একটি মোহনায় এসে পৌঁছেছে; যেখান থেকে তৈরি হবে নতুন গতিপথ। বলতে গেলে সবকিছুরই পুনর্জন্ম ঘটার সন্ধিক্ষণে বার বার পোড় খাওয়া মানুষের এই দেশটি। নতুন রাষ্ট্র গড়ার প্রত্যয়ে যেকোনো সঠিক সিদ্ধান্ত আগামীতে বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে, এমন প্রত্যাশা জনমনে। ওই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে শিল্পমাধ্যম চলচ্চিত্র নিয়ে এই আলাপ।
বলা চলে দেশীয় চলচ্চিত্র প্রত্যাশিত এক অন্ধকার জগৎ পার করে এসেছে। খুব অল্প কথায় ইতিহাস স্মরণ করলে দেখা যাবে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নানা ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। একদিকে সালাউদ্দিনের ‘রূপবান’র সাফল্যের রেশ ধরে রোমান্টিক-অ্যাকশন ও পোশাকি-ফ্যান্টাসি ধারায় নকল গল্পের প্রাধান্য পায়। সাথে সদ্য স্বাধীন ভূখণ্ডের ধ্বংসযজ্ঞের ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মিত হতে থাকে। এ ছাড়া নবীন একটি রাষ্ট্রের আকাক্সক্ষা নিয়ে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে নিজেদের তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে আলমগীর কবিরের ধীরে বহে মেঘনা, সূর্যকন্যা, সীমানা পেরিয়ে ও রূপালী সৈকত; ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম; বেবী আসলামের চরিত্রহীন, হারুনর রশীদের মেঘের অনেক রঙ; আব্দুস সামাদের সূর্যগ্রহণ ও সূর্যসংগ্রাম; রাজেন তরফদারের পালঙ্ক; সুভাষ দত্তের বসুন্ধরা ও ডুমুরের ফুল; মসিহ্উদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলীর সূর্য দীঘল বাড়ী’র কথা উল্লেখ করতে হয়। এর মধ্যে প্রথম সরকারি অনুদানে নির্মিত সূর্য দীঘল বাড়ী আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়।
স্বাধীনতা-পরবর্তী দশকে বাংলাদেশে বাণিজ্য প্রাধান্যশীল ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের সমান্তরালে একটি ভিন্নধারাও গড়ে উঠতে থাকে। অন্য অর্থে বলতে গেলে দেশীয় চলচ্চিত্র নিয়ে অনেকের অনাগ্রহের পেছনে যে ইন্ডাস্ট্রির মানুষের একটি বিশাল অংশের অদক্ষতা, অসততা, কালো টাকা সাদা করার হাতিয়ার হিসেবে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির ব্যবহারের কারণগুলো উল্লেখ করা হয়, মানে যেসব সংঘাতের মধ্যে দিয়েও এফডিসি জমজমাট ছিল, সেসবের বিপরীতে আগ্রহ জাগানিয়া কিছু কাজও শুরু হয় একই সঙ্গে।
১৯৭৬ সালে হারুনর রশীদের মেঘের অনেক রং নির্মাণের পর বিপত্তিটা শুরু হয়। কারণ চলচ্চিত্রটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর মাত্র তিনদিনের মাথায় প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে কিছু মানুষের ক্ষোভের উদ্রেগ হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে। এই রেশ না কাটতেই ১৯৭৯ সালে মসিহ্উদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলীর সূর্য দীঘল বাড়ীও নাটোরের একটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর ঢাকায় মুক্তি পেতে এক বছর সময় লেগে যায়।
এই যে পর পর ভিন্ন ধারার দুটি চলচ্চিত্রের প্রদর্শন সংকট সৃষ্টি হলো তা। কিন্তু বাণিজ্যিক ধারার ক্ষেত্রে ঘটেনি। ফলে প্রদর্শক সমিতির অভ্যন্তরীণ রাজনীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে চলচ্চিত্র সংসদ করা কিছু তরুণ ১৯৮৩ সালে এফডিসির বাইরে গিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের চিন্তা করে এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, সাংগঠনিক নেতৃত্ব, কিছু সচেতন ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিকে সাথি করে তারা বিকল্প ধারা চলচ্চিত্র আন্দোলন শুরু করে।
স্বল্প ব্যয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ আর নিজেদের মতো করে প্রদর্শনীযাত্রায় ১৬ মিমি ফরম্যাট বেছে নিয়ে ১৯৮৪ সালে মোরশেদুল ইসলাম নির্মাণ করেন ‘আগামী’। এরপর নির্মিত হতে থাকে হুলিয়া, শরৎ ’৭১, আদম সুরত ইত্যাদি।
এই পথে ধীরে ধীরে যুক্ত হন তানভীর মোকাম্মেল, তারেক মাসুদ, তারেক শাহরিয়ার, সালাউদ্দীন জাকি, মানজারে হাসান মুরাদ, জুনায়েদ হালিম, আবু সাইয়ীদ, নূরুল আলম আতিক, গোলাম রাব্বানী বিপ্লবরা। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, এফডিসিবিমুখ এই ধারা শুরু থেকেই স্বাধীনধারার পরিপূরক হয়ে ওঠে। যদিও তা নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলেও পরবর্তীতে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে; তবুও আজকের দিনে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, তৌকির আহমেদ, এনামুল করিম নির্ঝর, কামার আহমাদ সাইমন, রুবাইয়াত হোসেন, ফখরুল আরেফীন, নিয়ামুল হাসান মুক্তা, ইমতিয়াজ বিজনরা সেই ধারার উত্তরাধিকার হয়ে দাঁড়ালেও অনেকে হয়তো কৌশলগত কারণে ৩৫ মিলিমিটার ফরম্যাটে ফিরেছেন। কিন্তু মননে মগজে তারা স্বাধীনধারাকে ধারণ করছেন।
প্রসঙ্গক্রমে এই যে দীর্ঘ আলাপ তুলে ধরতে হলো, আর যাই হোক না কেন, এতে বরং দেশীয় চলচ্চিত্রের পাইপলাইন দ্বিখণ্ডিত করার দগদগে ঘা স্পষ্ট হলো। এই আলাপ না জেনে কোনোভাবে চলচ্চিত্র নিয়ে এগোনো যায় না। কেননা নানা বাস্তবতায় সাংস্কৃতিক দায় নিয়ে সংসদ কর্মীরা এফডিসি ত্যাগ করায় স্বাভাবিকভাবে সেখানকার মেধা-চিন্তা ভাগ হয়ে গেছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ হলো এক সময়কার সংগঠিত মনোভাব আজ ব্যক্তিগত প্রত্যাশায় পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে ধ্বংস হয়ে গেছে পুরোনো ফ্যাক্টরি তথা এফডিসিটাও। দর্শক রুচির নিরিখে ভালো চলচ্চিত্রের অভাবে প্রেক্ষাগৃহগুলো টানা খরায় ভুগে হাতের মুঠোয় থাকা চলচ্চিত্রের বাজার যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। মোদ্দা কথা হলো, অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্রে যা কিছু ঘটেছে তা ইন্ডাস্ট্রিকে ঘিরে ঘটেছে। কেবল বাংলাদেশেই কখনো ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে কখনো বাইরে।
ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংসের আলাপের মাঝে এটিও অনস্বীকার্য যে, ইন্ডাস্ট্রির বাইরের নির্মাতাদের হাত ধরেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক পরিসরে জায়গা করে নিয়েছে/নিচ্ছে। সেই সূর্য দীঘল বাড়ি থেকে মাটির ময়না, টেলিভিশন, স্বপ্ন ডানায়, দ্য টেল অব অ্যা পুলিশম্যান, সাউথইস্ট লাভ, শুনতে কি পাও, ঘেটুপুত্র কমলা, আন্ডার কনস্ট্রাকশন, মেইড ইন বাংলাদেশ, জালালের গল্প, অজ্ঞাতনামা, হালদা, কমলা রকেট, লাইভ ফ্রম ঢাকা, রেহানা মরিয়ম নূর, নো ল্যান্ডস ম্যান, নোনা জলের কাব্য, চন্দ্রাবতী কথা, ঢাকা ড্রিম; প্রামাণ্যচিত্র রিফ্লেকশন; স্বল্পদৈর্ঘ্য কবি স্বামীর মৃত্যুর পর আমার জবানবন্দি, টোকাই ২০১২, আ লেটার টু গড; এমন অনেক চলচ্চিত্র বাঘা বাঘা সব নির্মাতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিভিন্ন পুরস্কার-সম্মাননা অর্জন করেছে। বাংলাদেশকে পরিচয় করিয়েছে তাবৎ দুনিয়ার সাথে। এসব চলচ্চিত্রের আধেয়, বয়ানরীতি পরিবর্তনের লড়াই জারি রেখেছে।
প্রত্যাশার জায়গাও সেটিও যে, ভবিষ্যতে এমন চলচ্চিত্রের হাত ধরেই ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন কিছু ঘটবে। একই সঙ্গে আফসোস থেকে যায়, আমাদের নির্মাতাদের এখনো কিছু প্রবণতার ঘেরাটোপে বন্দি। এই যেমনÑ নিজ দেশে চলচ্চিত্র মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহ, বিদেশি ফান্ড সংগ্রহ, উৎসবকেন্দ্রিকতা এবং এফডিসিকেন্দ্রিক চলচ্চিত্রকে খারিজ করে দেয়ার নাক উঁচু স্বভাব অনেকের মাঝেই কাজ করে। এর মাঝে আবার একটা শ্রেণির টেলিভিশন কেন্দ্রিক চিন্তাও দেখা যায়। বিশেষ করে চলচ্চিত্রের ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞাপন দেখানোর সুযোগ থাকায় হয়তো ব্যক্তিগত স্বার্থে তারা সেই পথ বেছে নেয়। তাই প্রথম এবং শেষ কথা একটাই, এসব প্রবণতা পরিহার করে নিজেদের হাল ধরার সময় এসেছে।
আমরা যদি বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্রের কথা বলি, গত দুই দশকে কী বানিয়েছি, ঘুরে ফিরে ওই মনপুরা, আয়নাবাজি, পোড়ামন-২, ঢাকা অ্যাটাক, স্বপ্নজাল, পরাণ, হাওয়া, শান, গলুই, সুরঙ্গ, প্রিয়তমা, রাজকুমার, ক্যাসিনো, প্রহেলিকা, কাজলরেখা, ওমর, দেয়ালের দেশ, লাল শাড়ি, লিপস্টিক, রিভেঞ্জ, আগন্তুক, তুফান, ময়ূরাক্ষী এই তো। এর মধ্যে কয়েকটি ভালো ব্যবসা করেছে।
এ দেখে অনেকেই দাবি করছেন, বাংলা চলচ্চিত্র আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। ব্যবসাসফল হচ্ছে। সুদিন ফিরছে। কিন্তু আরেকটু গভীরে তাকালে দেখা যায়, দর্শকরা বিক্ষিপ্ত কিছু চলচ্চিত্র দেখলেও তা ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারছে না। আবার এসব চলচ্চিত্রের গল্পে উঠে এসেছে প্রেম, সহিংসতা, ঢাকা শহরকেন্দ্রিক গল্প। কন্টেন্টগত জায়গা থেকে ভিন্ন ধরনের কিছু আমরা করতে পারিনি। তার ওপর সারা বছরের শূন্য গোয়ালে দুটি ঈদকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র মুক্তি দেয়ার তোড়জোর ভালো কিছু বয়ে আনেনি। এ কারণে বেশিরভাগ চলচ্চিত্র প্রত্যাশিতভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে।
ভরসার জায়গা হলো, প্রাযুক্তিক উৎকর্ষতায় সংস্কৃতিগত দিক থেকে চলচ্চিত্রিক পরিসরের ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। কেননা চলচ্চিত্র দেখা এবং দেখানোর পথ উন্মুক্ত হয়েছে ওভার দ্য টপ বা ওটিটির হাত ধরে। পরিবর্তিত সময়ে গল্প বলার জন্য সেসব সাপোর্ট দরকার তা হাতের নাগালে চলে এসেছে। এ কারণে চলচ্চিত্রের বাজারের পরিসর বেড়েছে। করোনা মহামারির সময় থেকেই শক্তভাবেই চলচ্চিত্রের বাজারের বড় অংশ দখল করেছে ওটিটি।
হই চই, নেটফ্লিক্স, জি ফাইভ, চরকি, প্রিমিয়াম, বঙ্গ ইত্যাদি নামে অন্তত ১০টি ওটিটি প্লাটফর্ম দর্শক-নির্মাতা-কলাকুশলীর সামনে বিশ্ব চলচ্চিত্রের দুয়ার যেমন উন্মোচন করেছে, তারা স্বল্প খরচে হাতের মুঠোয় চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ পাচ্ছে; তেমনই স্বাধীনধারার নির্মাতা যারা চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সুযোগ পেতো না বা কম পেতো, তারাও নির্দ্বিধায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করার সাহস পাচ্ছে। অর্থাৎ ওটিটিতে বাজার-বাজেট যেমন বাড়ছে, তেমনি নির্মাতার স্বাধীনতাও রয়েছে। ফলে দর্শকের রুচিতেও পরিবর্তন এসেছে।
পরিবর্তন এসেছে শ্রেণিগত জায়গাতেও। গার্মেন্টস শ্রমিক, রিকশাচালক বা নিম্ন আয়ের মানুষ নয় বরং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিই চলচ্চিত্রের প্রধান দর্শক বনে গেছে। আবার টিকে থাকার স্বার্থে তাবৎ দুনিয়ার ইন্ডাস্ট্রির কথা মাথায় রেখেই প্রতিযোগিতায় শামিল হচ্ছেন নির্মাতারা। পরিবর্তন আসছে তাদের গল্প বলার ধরন, নির্মাণ শৈলী, কন্টেনগত জায়গায়। অর্থাৎ নির্মাতাদের গতানুগতিক ধারার বাইরে যেতে হচ্ছে। এর পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সহজলভ্যতার সুবাদে তরুণরাও এগিয়ে আসছে; যার বড় উদাহরণ হতে পারে রাজশাহীর আঞ্চলিক ভাষায় অপেশাদার শিল্পীদের নিয়ে নির্মিত শাটিকাপ ও সিনপাট। দিন শেষে দেশীয় চলচ্চিত্রের পাইপলাইন সচল হচ্ছে।
দেশের চলচ্চিত্র ঐতিহাসিকভাবেই বাজার হারিয়েছে। একটা জায়গা ধ্বংস হয়ে গেছে। এটি অনিবার্য ছিল। বলা যায় নতুন কাঠামো, নতুন সময়ের সঙ্গে টিকতে পারেনি বিধায় এটিই পরিণতি কাম্য ছিল। কিন্তু ভাবার জন্য নতুন পরিসর তৈরি হয়েছে। কাজেই ধ্বংসের ছাই বুকে তুলে রেখে দুঃখবিলাসের মানে হয় না; বরং চলচ্চিত্রের গণবিনোদন চরিত্রটি আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়; এমন বাস্তবতা মেনে নিয়ে এখান থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে। এই পথে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনই রাষ্ট্রেরও কিছু দায়বোধ থাকা প্রয়োজন।
প্রথমত, স্বাধীন নির্মাতাদার নাক উঁচু ভাব পরিহার করে ব্যক্তিগত প্রত্যাশা মাটিচাপা দিয়ে সার্বিক পরিসরে মনোনিবেশ করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে, এখনই সময় নতুন করে হাল ধরার। তাই ইন্ডাস্ট্রি পুনর্গঠনে, দেশীয় বাজার পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের পাশাপাশি নিজ দর্শকদের প্রাধান্য দেওয়াটাও কাম্য।
দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের দায়িত্ব শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া। অথচ অদ্ভুতভাবে আমাদের দেশে সরকার ক্ষমতায় যারাই যায়, তারাই নানা কৌশলে চলচ্চিত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে।
নতুন বাংলাদেশে অন্যতম কাজ হবে, চলচ্চিত্রকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা মুক্ত করা। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, শিল্প হিসেবে যেসব দেশে চলচ্চিত্র স্বাধীনভাবে চলতে পেরেছে, সেসব দেশে চলচ্চিত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। অথচ শিল্প ঘোষণার পরও দেশের কোথাও চলচ্চিত্রের কারিগরি দিক থেকে চিত্রনাট্য লেখার কৌশল কিংবা নির্মাণশৈলী তথা চলচ্চিত্র অধ্যয়নের কোনো স্কুল গড়ে ওঠেনি। তাই দেশে অন্যান্য সংস্কারের পথে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের এই দাবিটিও জোরালো হয়ে উঠতে পারে।
তৃতীয়ত, হাল আমলেও চলচ্চিত্রের প্রধান সঙ্কটের জায়গা গল্প লেখকের অভাব। আমাদের দেশে ভালো গল্পের অভাব থাকলেও কেউ চিত্রনাট্যকার হয়ে ওঠার আগ্রহ দেখাচ্ছে না। কেনো হয়ে উঠছে, সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। সেটি সমাধানে উদ্যমী হওয়া জরুরি। এমনটা নয় যে, দেশে গল্প লেখক নেই। কিন্তু গল্প থেকে চিত্রনাট্য করবার অভাব। বরং আমাদের দেশে সৃজনশীলতা ও মৌলিক কাজের কদর কম। চলতি কাঠামোয় তরুণ যুবাদের, নতুন মুখ খুঁজে নেয়ার প্রবণতা তৈরি হওয়া জরুরি।
চলচ্চিত্র নির্মাণের মতো অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ায় ক্যামেরার পেছনের সব মানুষকেও সঠিক মূল্যায়ন করে নতুনদের আগ্রহ বৃদ্ধির বিষয়ে দায়িত্বজ্ঞান থাকা দরকার। একই প্রবণতা অন্যান্য কারিগরি দিকগুলোর ক্ষেত্রেও। চতুর্থত, মান্ধাতার আমলের প্রেক্ষাগৃহ দিয়ে আর প্রদর্শনী চলবে না এটুকুও স্পষ্ট। তাই অনলাইন বাজারের পাশাপাশি মাল্টিপ্লেক্স কালচারে মনোযোগ দেয়াটা জরুরি। এদিক থেকে সরকারি কিংবা ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে মাল্টিপ্লেক্স নির্মাণ করা যেতে পারে। যেখানে দর্শককে চলচ্চিত্র দেখার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের সুযোগ করে দিতে হবে এবং চলচ্চিত্রের বাইরে নাটক, স্থানীয় চলচ্চিত্র, গানের আসর বসার সুযোগ থাকবে এসব মাল্টিপ্লেক্সে। এক কথায়, কালচারগত জায়গায় নতুন কিছু ভাবা প্রয়োজন।
পরিশেষে বলতে হয়, যে তরুণরা ক্ষমতাসীনকে টেনে নামাতে পারে, যারা নতুন প্রত্যয়ে দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখে, তারা আরো অনেক কিছুর মতো চলচ্চিত্রেও উত্থানের গল্প লিখতে পারে। আমাদের স্বপ্নবান তরুণরা অনেক আগে থেকেই নিজেদের সক্ষমতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। প্রয়োজন আরেকটু সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ, একটি চলচ্চিত্রিক পরিসর। কেবল সেন্সর বোর্ড থেকে সার্টিফিকেশন আইন নয়, চলচ্চিত্রকে বাঁচাতে নিজেদের গল্প বলা, নিজস্ব বয়ানরীতি আর একটি সংগঠিত ইন্ডাস্ট্রি এখন সময়ের দাবি। সেটি পূরণ হলে ছাত্রজনতার রক্তঝরা এই উর্বর ভূমিতে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখতেই পারি, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশের চলচ্চিত্রেও নিউ ওয়েভ তৈরি হবে।
আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ