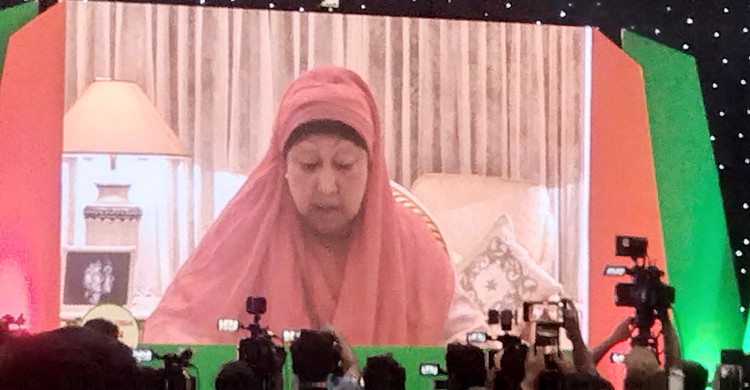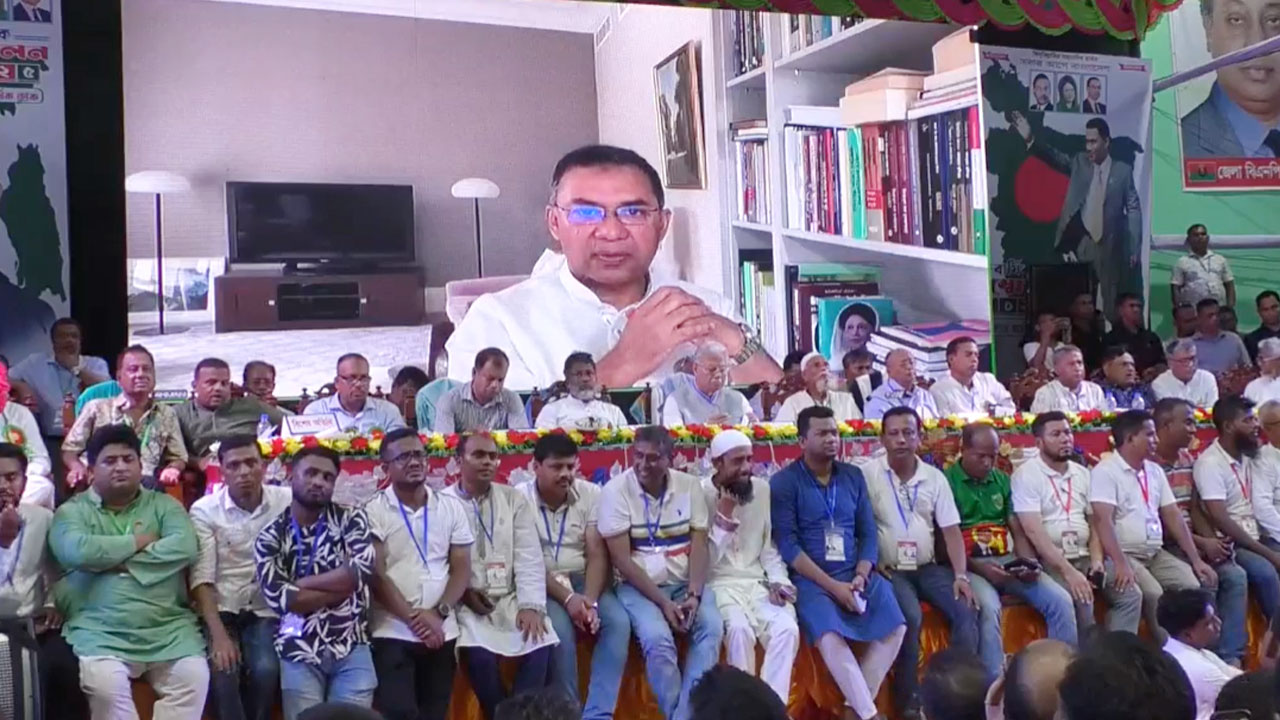ড. আজিম ইব্রাহিম : রোহিঙ্গা সংকট বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বেদনাদায়ক মানবিক ট্র্যাজেডিগুলোর মধ্যে একটি। বৈশ্বিক মনোযোগ অন্যত্র সরে যাওয়ায় আজ বাংলাদেশে আটকা পড়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দুর্দশার কথা সামনে আসছে না। রোহিঙ্গা ইস্যুতে বৈশ্বিক সম্মেলনের জন্য নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের সাম্প্রতিক আহ্বানের পাশাপাশি এই ইস্যুটি অবিলম্বে আন্তর্জাতিক মনোযোগ দাবি করে।
বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। বিশ্বের বৃহত্তম এই শিবিরে ১ মিলিয়নেরও বেশি রোহিঙ্গা বসবাস করে যারা মিয়ানমারে নিপীড়ন ও গণহত্যা থেকে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে এসেছে। নতুন আগমন এবং উচ্চ জন্মহার উভয়ের কারণেই এই শিবিরে জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। রোহিঙ্গাদের সংকটের কথা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন, তবুও এটি মোকাবেলার জন্য বিশ্বব্যাপী কার্যত কোনো প্রচেষ্টাই হচ্ছে না । আঞ্চলিক প্রতিবেশী বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ন্যূনতম সমর্থনে বাংলাদেশকে এই বিশাল বোঝা নিজের কাঁধে বহন করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
এই সংকটের একমাত্র টেকসই সমাধান হচ্ছে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের তাদের স্বদেশে নিরাপদ ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তন। কিন্তু এ সমাধানকে বাস্তব রূপ দেয়া কার্যত অসম্ভব। ২০১৭ সালে তাদের বিতাড়নের পর থেকে, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের পুরো রোহিঙ্গা গ্রামগুলিকে পরিকল্পিতভাবে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।
জমিগুলো স্থানীয় রাখাইন সম্প্রদায় এবং মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর অনুগতদের মধ্যে পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে। এমনকি যদি প্রত্যাবাসনের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা বিদ্যমান থাকে (যা বর্তমানে নেই) তাহলেও রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য কোনো অবকাঠামো আর বিদ্যমান নেই।
এই জটিলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মিয়ানমারের মধ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের গতিশীলতা।যে জান্তা ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা অভিযান পরিচালনা করেছিল তারা রাখাইনে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। আরাকান আর্মি, একটি শক্তিশালী জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠী এখন এই অঞ্চলের বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও এক্ষেত্রে সংলাপের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে, তবে দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ রোহিঙ্গা সংকটের যে কোনো সমাধানকে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তোলে।
বাংলাদেশকেও তার কৌশলগত ভুলগুলো বিবেচনা করতে হবে। মিয়ানমারের বেসামরিক সরকার এবং সামরিক উভয়ের সাথে একটি প্রত্যাবাসন চুক্তি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে, ঢাকা মিয়ানমারের সাথে তার সম্পর্ক রক্ষা করতে চেয়েছিল, কারণ তখন বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই সংকটের দিকে। কিন্তু এই কৌশলটি ব্যর্থ হয়।
মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী কখনোই কোনো চুক্তিকে সম্মান জানাতে চায়নি এবং বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিয়ানমারের ওপর সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগের সুযোগ হাতছাড়া করেছে।
মাত্র কয়েক বছর পরে বৈশ্বিক স্পটলাইট থেকে এ ইস্যুটি সরে যাবার পরে গণহত্যার অভিযোগ তুলে মিয়ানমারকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে টেনে নিয়ে যায় গাম্বিয়া। ততক্ষণে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের গতি কমে গিয়েছিল। একই সঙ্গে বাংলাদেশকে রোহিঙ্গা সঙ্কটের ধাক্কা বহন করতে হচ্ছিলো।
রোহিঙ্গারা নিজেরাই আরেকটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি: একটি ঐক্যবদ্ধ, বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত নেতৃত্বের অভাব।রোহিঙ্গা সম্প্রদায় বিভক্ত, একাধিক দল তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করে। এই অনৈক্য বিশ্বে তাদের সংকটের কথা উপস্থাপন করার এবং তাদের অধিকারের জন্য সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। একটি বৈশ্বিক সম্মেলন এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করতে পারে। এর মাধ্যমে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় আয়োজক দেশ, দাতা দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের সামনে নিজেদের কথা তুলে ধরে সামনের পথ নির্ধারণ করতে পারে।
জাতিসংঘের কমিটি দ্বারা সমর্থিত ড. ইউনূসের এই ধরনের একটি সম্মেলন আয়োজনের উদ্যোগ রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি রোহিঙ্গা সঙ্কটের উপর বিশ্বব্যাপী মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার এবং আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ তৈরি করতে পারে। এই স্কেলের একটি সম্মেলন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে সাধন করতে পারে।
প্রথমত, এই সম্মেলন বিশ্বকে বাংলাদেশের শিবিরে চলমান মানবিক বিপর্যয় এবং টেকসই সমাধানের জরুরি প্রয়োজনের কথা মনে করিয়ে দেবে।
দ্বিতীয়ত, এটি সম্মেলনে উপস্থিত দেশগুলিকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে আইনি পদক্ষেপে সমর্থন দিতে এবং নিরাপদ ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের সুবিধার্থে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী এবং আরাকান আর্মির মতো উদীয়মান শক্তিগুলিকে চাপ দিতে পারে।
তৃতীয়ত, এটি বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সমর্থন নিশ্চিত করতে পারে। ঢাকার পক্ষে একা এই ভার বহন করা সম্ভব না। তাই সম্মেলন মারফত বর্ধিত আর্থিক সহায়তা, পুনর্বাসনের বিকল্প এবং আঞ্চলিক শক্তি যেমন ভারত, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির সদস্যদের থেকে শক্তিশালী সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।
চতুর্থত, ভিন্ন ভিন্ন রোহিঙ্গা গোষ্ঠীকে একত্র করে সম্মেলনটি একটি ঐক্যবদ্ধ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নেতৃত্ব তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে; যা কার্যকরভাবে সম্প্রদায়ের অধিকারের পক্ষে সওয়াল তুলবে।
রোহিঙ্গা সংকটের প্রতি অব্যাহত অবহেলা শুধু মানবিক বিপর্যয়ই নয়, তাৎপর্যপূর্ণভাবে আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার ঝুঁকিও তৈরি করে। রোহিঙ্গা জনসংখ্যার মধ্যে রাষ্ট্রহীনতা এবং বঞ্চনা তাদের মৌলবাদের দিকে পরিচালিত করতে পারে; যা ইতোমধ্যেই অস্থিতিশীল অঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতাকে আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে।
একই সঙ্গে উদ্বাস্তু এবং স্বাগতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা বাংলাদেশের সম্পদ এবং সামাজিক কাঠামোর উপর চাপ সৃষ্টি করছে।
সময় ফুরিয়ে আসছে। তাই রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে একটি বৈশ্বিক সম্মেলন শুধু নৈতিক আবশ্যিকতার জন্যই নয় বরং কৌশলগতভাবেও প্রয়োজনীয়। অমানবিকতার শিকার একটি সম্প্রদায়ের মনে ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি পালনের সুযোগ এনে দিয়েছে।
ইউনূসের এ ধরনের সম্মেলনের আহ্বান করা যথার্থ। এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করছে তারা এই আহ্বানে কিভাবে সাড়া দেবে। কারণ রোহিঙ্গাদের নতুন করে হারানোর কিছু নেই।
লেখক: পরিচালক, বিশেষ উদ্যোগ, নিউলাইনস ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পলিসি, ওয়াশিংটন ডিসি আমারিকা